by Jahid | Jan 13, 2022 | কর্পোরেট অবজার্ভেশন, লাইফ স্টাইল
কিছুদিন আগে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে অক্ষর পরিচয়ে ‘ও’ অক্ষরের জন্য ‘ওড়না চাই বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। বছরের শুরুতে প্রাচীন ও প্রগতিশীলদের মধ্যে শুরু হয়েছে বাদানুবাদ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে যে কোন ইস্যু নিয়ে হৈচৈ দুই-একদিনের বেশী থাকে না। এখন যেহেতু ব্যাপারটা সবাই ভুলে যেতে বসেছে , আমি আমার কর্পোরেট অবজার্ভেশনে ওড়না ও নারীদের কর্ম পরিবেশ নিয়ে দুয়েক কথা বলতেই পারি।
পারিবারিক মূল্যবোধ থেকেই কন্যা-শিশুদেরকে ওড়না ও ওড়না দিয়ে বুক ঢেকে রাখার ব্যাপারটা শেখানো হয়। পুরো ব্যাপারটি নারীর দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকত্ব, তাঁর নিরাপত্তাহীনতা, ধর্মীয় অনুশাসন ও মা-খালাদের অতীত তিক্ত অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে হয়ে থাকে। আমাদের অবদমনের পুরুষ শাসিত সমাজে একজন বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বেশ একটা অদ্ভুতুড়ে উপায়ে তৈরি হয় । প্রথমত: যৌনতা ও তার যে কোন আলোচনা আমাদের সমাজে নিষিদ্ধ ও ট্যাবু। আগেও ছিল , এখনো এই মুক্ত অন্তর্জালের সময়েও আছে। দ্বিতীয়ত: নারী-শিশুটি যে নিজের পরিবারের পিতা ও ভাই ছাড়া পৃথিবীর অন্য সকল পুরুষের কাছে অনিরাপদ সেটা মা, খালারা গ্রামের একটি শিশুকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে একদম দেরী করেন না।
একই সঙ্গে গ্রামের একটি ছেলে কীভাবে যেন জেনে ফেলে– অকর্মণ্য , অপদার্থ পুরুষ হলেও, শুধুমাত্র পুরুষ হওয়াও একটা বিশাল সৌভাগ্য ও গুণ। এবং মেয়েটির ক্ষেত্রে ঠিক উল্টো। পুত্রসন্তান প্রসবকারী জননীদের দাম বেশী। ৩/৪ টি কন্যা সন্তানের পর একটি পুত্রসন্তানের জন্ম অথবা আরেকজন তরুণীকে সম্ভোগ করে পুত্রলাভের ঘটনা হরহামেশাই ঘটছে। গ্রামে বিয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের বিচার-মূল্যে সবচেয়ে নির্বোধ, উন্মাদ যাই হোক না কেন, একজন যুবকের জন্য পাত্রী ঠিকই জুটে যায়। অথচ, সচ্ছল পরিবারের মাঝারি চেহারার বা শ্যামলা মেয়েদের পাত্রস্থ করতেও হিমসিম খেতে হয় পুরো পরিবারকে।
কয়েকটি শিক্ষিত সংস্কৃতমনা জেলা ছাড়া বেশিরভাগ জেলা শহরগুলোর সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার জায়গাটা ভীষণভাবেই দুর্বল। না আছে ভালো কোন ক্লাব, না আছে লাইব্রেরি না আছে সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা। বাংলাদেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা ছেলেরা কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সহপাঠী ছিল। এঁদের সঙ্গে চলে বুঝতে পারি ওঁদের কৈশোর আর আমাদের ঢাকা শহরের বেড়ে ওঠা কৈশোরে বড় কোন পার্থক্য নেই। তবে কিছু জেলা শহরে ধর্মের প্রকোপ বেশী, পর্দাপ্রথা বেশী। সেখানে অনেককে শৈশব কৈশোরে বড় একটা অংশে বেড়ে উঠতে হয়ে নারী-পুরুষের স্বাভাবিক সম্পর্কে একমুখী অজ্ঞানতা নিয়ে। মফঃস্বলে বেড়ে ওঠা আমার এক দুঃসম্পর্কের মামার কথা মনে পড়ছে। তিনি সারাজীবন বয়েজ স্কুল, বয়েজ কলেজ করে প্রায় নারী বিবর্জিত জীবন যাপন করেছিলেন। বিয়ের পরে নতুন মামীর প্রতিটা চালচলন ও কর্মকাণ্ড তাঁর কাছে বিস্ময়কর মনে হত। একজন অধরা আকাঙ্ক্ষিত নারীও যে খাওয়া দাওয়ার পাশাপাশি আর সবার মতো মল-মূত্র ত্যাগ করে, বায়ু ত্যাগ করে সেটা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল ! নতুন মামীকে নিয়ে তাঁর আদিখ্যেতা ছিল দেখার মতো। প্রায়শ: আমাদের শুনতে হোতো, জানিস আজ তোর মামী এইটা করেছে ! জানিস, আজ তোর মামী সেইটা করেছে। আমরা কিশোর বয়সেই বিরক্ত বোধ করতাম।
আমাদের শহুরে ছেলেদের কৈশোরের দুঃসহতা ছিল। তবুও সংখ্যা গরিষ্ঠরা একটা মানসিক স্থিতির মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছি। মধ্যবিত্ত বাবা-মায়েরা, মহল্লার মুরব্বীরা, কো-এডুকেশন অথবা কোচিং লেভেলেই মেয়েদের সংগে চলাফেরা একটা স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। অল্পবিস্তর বিকৃতি যে ছিল না , তাও বলব না।
কিছুদিন আগে আমি, আমার স্ত্রী, আর দশ বছরের কন্যা বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার স্ত্রী হঠাৎ করে মেয়েকে আরো কাছে টেনে নিয়ে ওর পরিধেয় কাপড় ঠিক করে দিল আর আমাকে নিয়ে একটু দুরে গিয়ে দাঁড়াল। আমি একটু অবাক চোখে তাকালে তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর পাওয়া গেল না। ফেরার পথে জানালো, আমার ঠিক পিছন থেকে এক মাঝবয়সী বিকৃত পুরুষ নাকি জুলজুল করে কন্যার দিকে তাকিয়ে ছিল! কেউ তাকালে কী করবেন ? আমার সহপাঠিনীরা সেই সময়ে পাবলিক বাসে করে মিরপুর থেকে ইডেন , হোম ইকোনমিকস্ , সিটি কলেজে যাওয়ার সময় তাঁদেরকে কি পরিমাণে বিব্রত হতে হত জানি। বাসে কন্ডাকটর থেকে শুরু করে প্রৌঢ় , যুবক, কিশোর সবার চেষ্টা থাকত তাঁদের গা ঘেঁষে দাঁড়ানোর। অনেক সহপাঠিনীই ব্যাগ ও বই দুই হাতে বুকের সামনে চেপে ধরে রাখত। কিন্তু শরীরের অন্য স্পর্শকাতর অংশগুলোতে কারো না কারো অবাঞ্ছিত ,অনিচ্ছাকৃত(!) শারীরিক চাপ পড়তই। আবার এটাও ঠিক , সেই সময়েও অনেক সচেতন পুরুষ এই ব্যাপারটাকে বুঝে আমাদের সহপাঠিনীদেরকে নিরাপদ জায়গায় , মানে ড্রাইভারের বাঁ পাশের সিটে বসার ব্যবস্থা করতেন।
এখন তো অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। উন্মুক্ত-স্থানে বা পাবলিক বাসে একজন স্বাভাবিক পোশাকের তরুণীকেও জুলজুল করে, অশ্লীল বাঁকা চোখে পুরো বাসের পুরুষগুলো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কয়জনকে বলবেন দৃষ্টি বদলাতে ? ধার্মিকরা ধরেই নিয়েছেন , এর সমাধান বেশী করে বোরখা ও হিজাব পড়া। সেটি করেও যে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না সে উদাহরণ ভুরিভুরি।
আমাদের বাঙালী পুরুষের সামগ্রিক আচরণ কতখানি সভ্য ও শ্লীল হওয়া উচিৎ সেটা পরিবার থেকে, বিদ্যালয় থেকে তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয় নি। ইঁচড়েপাকা বন্ধু, কাজের ছেলে আর পাড়ার ডেঁপো ছেলে কাছ থেকে তার কুশিক্ষা শুরু হয়। এক পর্যায়ে নারীকে যোনি ও স্তনের সমন্বিত একটি ভোগ্যপণ্যের বাইরে কিছুই সে ভাবতে পারে না ! প্রতিটি নারী , সে যে বয়সেরই হোক না কেন তাদের কাছে ভোগ্য ও রমনযোগ্য মনে হয়।
আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমার দশ বছরে কন্যা শিশুকে বোঝাতে হচ্ছে সে এই সমাজে কোথাও নিরাপদ নয়। তাঁর চারদিকে বসবাস করছে কুৎসিত, বিকৃত ও মুখোশ-ধারী পুরুষ পশু ; এর চেয়ে আফসোসের আর কি হতে পারে।
এবার দেখি আমাদের কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে নারীদের সামাজিক অবস্থা কিরকম । একযুগ আগেও ক্যারিয়ার সচেতন মেয়েটিকে স্কুল, কলেজ , ব্যাংক ছাড়া অন্য কোথাও চাকরি করতে দিতে পারিবারিক বাঁধা আসত। এখন কর্পোরেট পরিবেশ অনেক নারীবান্ধব হয়েছে। নানা ধরণের প্রযুক্তির( মোবাইল ফোন ) উৎকর্ষতায় তাঁদের জীবন নিরাপদ। কিন্তু ঠিক উল্টো অবস্থা হয়েছে বাইরের রাস্তায় । অফিসে একটা শৃঙ্খলিত নিয়মনীতির ভিতরে একজন নারী যতোখানি নিরাপদ ; রাস্তা-ঘাটে সে ততোখানি অনিরাপদ।
আমার যে কাজের ক্ষেত্র–মার্কেটিং মার্চেন্ডাইজিং , সেখানে আমরা বহুবার নারী সহকর্মীদের উৎসাহিত করেছি দীর্ঘমেয়াদী ক্যারিয়ার পরিকল্পনার কথা ভাবতে । কিন্তু এখানেও সেই পুরুষ আধিপত্যের প্রচ্ছন্ন বাঁধা।
প্রথমত: পুরুষ কর্মকর্তারা নারীদেরকে তাঁদের নিজেদের বিভাগে নিতান্ত ঠেকায় না পড়লে নিতে চান না। যুক্তি হিসাবে তারা নারী কর্মচারীদের অফিস টাইমের শেষেই তাড়াতাড়ি বাসায় যাওয়ার প্রবণতাকে তুলে ধরেন। নারী কর্মচারী হয়তো কাজের চাপে ইচ্ছে করলেই আরো ঘন্টাখানেক থেকে যেতে পারেন অফিসে, কিন্তু বাইরের রাস্তার পরিবেশ ও স্বামী-সন্তানের চাপ , তাঁকে বাড়তি সময়দানে নিরুৎসাহিত করে।
দ্বিতীয়ত: পশ্চিমা দেশের সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অনেকসময় সন্ধ্যার পরও অফিসে থাকার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অথবা ক্রেতা আসলে তাঁদের সঙ্গে রাতের খাবারে উপস্থিত থাকার সৌজন্যতা থাকে। বাংলাদেশ ছাড়া অন্য সব গার্মেন্টস উৎপাদনকারী দেশে সামাজিক অবস্থান ভেদে মার্চেন্ডাইজিং এর পুরো দখল নিয়ে রেখেছেন নারীরা।ব্যতিক্রম আমাদের দেশে। পুরুষ-শাসিত বলেই তাদের প্রাধান্য বেশী। যদিও গার্মেন্টস কারখানায় নারী শ্রমিকের জয়জয়কার।
তৃতীয়ত: একজন পুরুষ সহকর্মীকে দিনের যে কোন সময়ে যে কোন কারখানায় প্রোডাকশন ফলো আপের জন্য পাঠানো যায়। নারী সহকর্মীর জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব যানবাহন ছাড়া ও দিনের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া কারখানায় যাতায়াতের প্রশ্নই ওঠে না।
এছাড়া আরেকটি ভয়ংকর অমানবিক দিক আছে, যেটা আমাদের কর্পোরেট কর্মকর্তারা মুখে উচ্চারণ করেন না। কিন্তু ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ঠিকই বের হয়ে আসে। সেটা হচ্ছে, নারী কর্মচারীদের অন্তঃসত্ত্বা কালীন কর্মবিরতির সময়টি। এটা কেউ বিবেচনা করতে রাজী নয় যে মাতৃত্বের মতো একটা মহৎ বিশাল কর্মযজ্ঞে নারী তাঁর শরীর ক্ষয় করে বংশরক্ষার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। পশ্চিমা দেশে প্রায় বছর খানেকের বেতনসহ মাতৃত্ব কালীন ছুটি ছাড়াও ইচ্ছেমতো বেতন-বিহীন ছুটি প্রযোজ্য। আবার প্রতিষ্ঠানগুলোও ছুটির বিরতির পরে নারী কর্মচারীকে তাঁর আগের অবস্থানে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। আমাদের দেশে কর্পোরেট নারীদের অবস্থান ঠিক তার বিপরীতে। একজন দক্ষ নারী কর্মচারীর বিয়ে হয়ে যাওয়া মানেই, তাঁর নতুন অভিভাবক স্বামী –শ্বশুরকুলের নিত্যনতুন সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ। আর তারপরে তাঁর ক্যারিয়ারের বড় ধরণের ধাক্কা আসে মাতৃত্ব কালীন সময়টিতে। মাতৃত্ব কালীন ছুটিতে যাওয়া মানেই ধরে নেওয়া যায় তাঁর ক্যারিয়ারের বিদায় ঘণ্টা বেজে গেল। একটা বিরতি দিয়ে ফিরে এসে, নারী কর্মচারী তাঁর আগের অবস্থান ফিরে পান না । তাঁকে শূন্য থেকে শুরু করতে হয়। তা ছাড়া পারিপার্শ্বিক চাপে তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান হয়ে পড়ে নতুন শিশুটি। এইসব বহুমুখী সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে কর্পোরেট উচ্চপদস্থরা যতোই নারীবান্ধব কথাবার্তা বলেন না কেন ; নিয়োগদানের ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য থাকে পুরুষ কর্মচারীর দিকে।
কর্পোরেট পরিবেশ নিয়ে আমার মতামতের সঙ্গে অনেকের মিলবে না ; কারণ আমার দেখা পরিস্থিতির চেয়ে অনেক ভালো পরিবেশ যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আছে ; ঠিক তেমনি অনেক খারাপ পরিবেশও আছে। মোটা-দাগে, একটা সময় ছিল কর্পোরেট জগতের মেয়েদেরকে তাঁদের ঊর্ধ্বতনরা ও সহকর্মীরা সহজলভ্য ভাবতেন। মেধাবী ছাত্রীরা শিক্ষকতা করবে ; নিরাপদ পেশা। আর মোটামুটি সুন্দরী মেয়েরা সুপাত্রের গলায় ঝুলে পড়বে। নিজের আত্মসম্মানবোধ নিয়ে অনেক মেধাবী মেয়েরা বেসরকারি অফিসে কাজ করা শুরু করেছেন গত তিন দশকে। কিন্তু, এখনো নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে নিজের স্বামীর পায়ে দাঁড়ানোকে পরিবার থেকে উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে।
ঢাকায় বেড়ে ওঠা ছেলেদের একটা সুবিধা ছিল, নারী সহকর্মী হেসে কথা বললে আমাদের হাসিমাখা প্রত্যুত্তর ছিল। কিন্তু মফস্বল থেকে আসা অনেকে হাসি মুখে কথা বলাকে প্রেমের প্রাথমিক প্রশ্রয় বলে ধরে নিতেন। এই সমস্যার পাশাপাশি ছিল, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও নারী কর্মচারীদেরকে সহজলভ্য ধরে নিতেন। অনেক লোভী ঊর্ধ্বতনকে নারী কর্মচারীকে দৈহিকভাবে না হলেও মানসিকভাবে অপদস্থ করতে দেখেছি। আমার এক নারী সহকর্মী একবার এক কর্মকর্তার রুম থেকে বের হয়ে যা বললেন, তার সাদা বাংলা দাঁড়ায় –কথা বলার চেয়েও সেই পুরুষ কর্মকর্তার চোখ সারাক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছে তাঁর বুকের দিকে নয়তো অন্য কোন বাঁকে।
আমাদের সচেতন সাবধানী কর্মকর্তাদের নারী সহকর্মীর সঙ্গে যে কোন আলাপ আলোচনায় সচেতনভাবে তাঁদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হয়। মুশকিল হচ্ছে, সব পুরুষকেই নারী এক চোখে দেখা শুরু করে বলে যে কোন সাক্ষাতেই তাঁর প্রথম কাজটি হয় ওড়না ঠিক করা।
প্রাথমিকভাবে ওড়না মাথায় দেওয়ার ব্যাপারটি হচ্ছে, মুরব্বী শ্রেণির কাউকে দেখে সম্মান দেখানো। এটি কর্পোরেট জগতে নেই। দ্বিতীয়টি আছে। গলায় ওড়না থাকাটা ক্যাজুয়াল মুডের ব্যাপার। কিন্তু সামনে কোন পুরুষ পড়লেই অবচেতন মনেই তাঁর হাত বুকের অংশের ওড়নাটুকু ঠিকঠাক করে নেয়। নারীরা পুরুষ দেখলেই বার বার ওড়না ঠিক কেন করে তা এক কথায় বলা উচিৎ হবে না। এবং সব পুরুষের সামনেই সবাই এমনটা করে , তাও না। চরিত্র ভেদে পুরুষটির আচরণ ও চোখের আবর্তন দেখে নারীটি বুঝে নেয় তাঁকে কি করতে হবে। এটা মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়। পাঁচ মিনিটের কথোপকথনে কেউ যদি পনের কুড়িবার ওড়না ঠিক করে ; তাঁর দু’রকম অর্থ হতে পারে। হয়, নারীটি অবচেতনে পুরনো দীর্ঘ অভ্যাসের কারণে অস্বস্তি বোধ করছে পুরুষটির সামনে। অথবা , আসলে সে কি করবে বুঝতে না পেরে বা অস্থিরতা ঢাকতে ওড়না ঠিক করে চলেছে। পাশ্চাত্য তো অবশ্যই ; এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার অনেকগুলো দেশেও ওড়না বাহুল্যপ্রায়। আমাদের জীবদ্দশায় বাংলাদেশে ওড়না বিলুপ্তির কোন সম্ভাবনা দেখছি না। আরো কয়েক জেনারেশন ওড়না ব্যাপক ও বহুলভাবেই থাকবে।
প্রকাশকালঃ জানুয়ারি ২০১৭
by Jahid | Feb 18, 2021 | দর্শন, সমাজ ও রাজনীতি
রচনার সারসংক্ষেপ:
‘বাংলাদেশের ধনী: অবদান ও সমালোচনা’ প্রবন্ধে গত কয়েক শতাব্দী আগে থেকে শুরু করে ১৯৭১ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের ধনী ও দরিদ্রশ্রেণির অভ্যুদয় ও পারস্পরিক বিবর্তনের একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
বিদেশি পর্যটক, ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজকদের চোখে পূর্ব বাংলার যে চিত্র ইতিহাসে দেখা যায়, সেখানে নানা অসঙ্গতি আছে। অবিরাম দারিদ্র্যের পাশাপাশি পূর্ব বাংলা স্থানীয় আকাল, খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়েছে বারবার। ইতিহাসের কয়েক পর্যায়ে ধনীদের অভ্যুদয়, কর্মযজ্ঞ , অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে অবদান ও সামাজিক মানবিক ক্ষেত্রে নিশ্চেষ্ট থাকার সমালোচনা -পর্যালোচনা পাঠককে নতুনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করবে।
ব্রিটিশ উপনিবেশের আগের পূর্ব বাংলা, সর্বভারতে তার বাণিজ্যিক অবস্থান। মুঘল আমলে নৌবাণিজ্যের ফলে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচিতি, রপ্তানিবাণিজ্যে মুনাফা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পুঁজির অনুপ্রবেশ। ভূস্বামী ও সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী প্রথার আবির্ভাব। পাটের স্বর্ণযুগে মধ্যস্বত্বভোগী দালাল মুৎসুদ্দিদের পুঁজির আবির্ভাব। ৪৭ এর দেশভাগের পরে হিন্দু জমিদারদের সঙ্গে বড় একটা পুঁজির পশ্চিমবঙ্গে প্রস্থানে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুঁজির সংকট। সেই সুযোগে পশ্চিম পাকিস্তানী অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের পূর্ব বাংলায় অনুপ্রবেশ। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বিমাতাসুলভ আচরণে ধারাবাহিক অর্থনৈতিক বঞ্চনার শিকারে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতায়, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রও সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূলে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কলকারখানার সিদ্ধান্তে ব্যক্তি পর্যায়ে ধনী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের প্রাদুর্ভাব। পরের দশকগুলোতে বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাংক-নির্ভর আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় নব্যধনীদের উত্থান। আশির দশকে গার্মেন্টস শিল্পের শুরু। ব্যবসায়িক পরিবার ও সরকারি কর্মচারী, রাজনৈতিক অনুগ্রহভাজন ধনীদের পাশাপাশি একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা বিশাল এক শিল্পোদ্যোক্তা শ্রেণির অভ্যুদয়। বিরামহীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামরিক শাসনে জর্জরিত বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশ। আমলাতান্ত্রিক দুর্বল রাষ্ট্র, প্রশাসন, রাজনীতি ও ব্যবসায়ীদের দুর্নীতির দুর্ভেদ্য চক্র গড়ে ওঠা। কর্মসংস্থানের ফলে একটা উদীয়মান জাতির কর্মক্ষমতা বেড়েছে, গার্মেন্টস সেক্টরের প্রসারে নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা বেড়েছে। শিল্পোদ্যোক্তা এই ধনীদের অবদানে বাংলাদেশ আজ উন্নত দেশের তালিকাভুক্তির জন্য অপেক্ষমাণ। কিন্তু সামাজিক ও মানবিকক্ষেত্রে এঁদের অবদান অর্থনৈতিক সক্ষমতার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল এবং অকিঞ্চিৎকর।
মূল প্রবন্ধ:
পূর্ব বঙ্গ, পূর্ব বাংলা, পূর্ব পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডে গত দুইশ বছরে ধনীরা বাইরে থেকে এসেছে । আর্মেনীয় থেকে শুরু করে ইংরেজ, মাড়োয়ারী, বোম্বাইয়া বা পাকিস্তানী । খুব সামান্য অংশ থিতু হয়েছে, বেশির ভাগই চলে গিয়েছে। খাঁটি স্বদেশী ধনীদের অভ্যুদয় স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে।
প্রবন্ধে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পরবর্তী ধনীরা আকাঙ্ক্ষিত আলোচ্য হলেও ইতিহাসের ধারাবাহিকতার স্বার্থে অনুক্রম বিবেচনায় চলে আসে। প্রবন্ধে ‘পূর্ব পাকিস্তান’-এর পরিবর্তে অধিক পরিচিত ‘পূর্ব বাংলা’ব্যবহার করা হয়েছে।
ভারতীয় ঐতিহাসিকদের চোখে দেখা বাংলার সঙ্গে বিদেশি পর্যটকের দেখার পার্থক্য ছিল। তাদের চোখে সোনার বাংলা ছিল সুজলা,সুফলা , শস্যশ্যামলা। চৌদ্দ শতকে মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা কিংবা চীনা পরিব্রাজক ওয়াং তু ওয়ান সবাই বাংলায় সস্তা দ্রব্যমূল্যের কথা বলেছেন, সমৃদ্ধ জীবনের কথা বলেছেন। এঁদের পর্যবেক্ষণে বাংলায় কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের সস্তামূল্য বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রমাণ। কিন্তু অর্থনীতির সূক্ষ্ণ মারপ্যাঁচে একটি দেশের দ্রব্যমূল্য অন্য দেশের চেয়ে সস্তা হতে পারে, কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যায়। বস্ত্রের মূল্য সস্তা হলে সেখানে তাঁতির মজুরি কম হয়। কৃষিপণ্যের মূল্য সস্তা হলে শ্রমিকের মজুরি কম হয়। আপাতদৃষ্টিতে অর্থনৈতিকভাবে একটা দেশ সমৃদ্ধ মনে হলেই সেখানে দারিদ্র পুরোপুরি দূরীভূত হয় না, যদি না সম্পদের সুষম বণ্টন না হয়। ধনী দেশেও দারিদ্র্যের সুযোগ থাকে।আমাদের বাংলায় ধনী দরিদ্র্যের প্রকট বৈষম্য গত কয়েকশ বছরের ধারাবাহিকতা।
সর্বভারতে বাংলাদেশের পণ্যের সুনাম ছিল। বাংলার মসলিন ও বস্ত্র সারা ভারতেই যেতো। নৌপথে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার প্রক্রিয়া শ্রেষ্ঠ অবদান রাখে পর্তুগীজরা ষোলশ শতকের শেষের দিকে। কিন্তু কিছুদিন গেলেই দেখা যায় বাণিজ্যের চেয়ে এরা জলপথে দস্যুবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েছে। এরপরে আসে ওলন্দাজরা। ওলন্দাজদের রপ্তানি বাণিজ্যে শরিক হয় ফরাসী, ইংরেজ, ওস্টেন্ডার ( বেলজিয়ান) সহ বহু ইউরোপিয়ান নৌ-জাতি। এছাড়াও ছিল দিনেমার, আর্মেনীয়, হিন্দুস্থানি, মাড়োয়ারী, তামিলরা।
নৌবাণিজ্যের সুবাদে ও মুঘল আমলের আঠারো শতকে আমির-ওমরাহ, জমিদার শ্রেণির বাইরে আরেকটি শ্রেণি প্রভূত ধনসম্পদ অর্জন করে। মূলত বিদেশি বণিকদের সহায়তাকারী হিসাবে দেশীয় দালাল-মুৎসুদ্দির একটা ধনী শ্রেণি গড়ে ওঠে। বিদেশীরা এদেরকে বলত বেনিয়া। বেনিয়ারা ছাড়াও হাট-বাজার পর্যায়ে কয়েক শ্রেণির দালাল, মধ্যস্বত্বভোগী ছিল। লক্ষণীয় যে, এই রপ্তানি বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত মুনাফা দেশের সার্বিক অর্থনীতির উপরে কোন ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি ; যদিও এই মুনাফার উপর ভর করে কিন্তু শহরভিত্তিক একটা বাণিজ্যিক পুঁজিপতি শ্রেণি তৈরি হয়েছিল।
১৭৯০ সালের দশকে ইউরোপে বিদ্যমান নেপোলীয়নীয় যুদ্ধের দামামায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক টানাপড়েনে বাংলার রপ্তানীবাণিজ্য মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮১৩ সালে অবাধ বাণিজ্যনীতিতে বাংলার বস্ত্ররপ্তানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৮২০ এর দশকে ইউরোপ থেকে বস্ত্র আমদানি শুরু হয়। খুব স্বল্প সময়ের এই রপ্তানি পতনে তাঁত শিল্পের সঙ্গের জড়িত তাঁতি সম্প্রদায় ছাড়াও বেনিয়া , আড়তদার, পাইকাররা বেকার হয়ে পড়ে।
এ সময়ে রপ্তানিবাণিজ্য থেকে যে বিপুল অর্থ বাংলায় অনুপ্রবেশ করেছিল, সেই পুঁজি চলে আসে ভূমি নিয়ন্ত্রণে। নবাগত ভূস্বামী ও জমিদার শ্রেণিটি তাদের অর্জিত পুঁজির সামান্য অংশ ব্যয় করেছিলেন ভূমিক্রয়ে বাকী পুঁজি উজাড় হয়েছে রাজ্যের অনুৎপাদনশীল খাতে, যেমন বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা-পার্বণ, মন্দির, ঘাট, পুকুর , প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণে। পুঁজির আরেক অংশ চলে আসে মহাজনী ঋণদান ও শস্যব্যবসায়।
বাংলার তৎকালীন অর্থনৈতিক সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে সবচেয়ে বড় যে সত্যটি আবিষ্কার করি আমরা , সেই সময়ের ধনীদের মনোভাব ছিল সামন্তবাদী, পুঁজিবাদীদের মতো নয়।
সমান্তরালভাবে , আঠারোশ শতকের শুরুতে তুলার চাহিদা হ্রাস পাওয়া শুরু করলে তার জায়গা নেয় নীলচাষ। আবার ১৮৫০ সালের দিকে কমতে থাকে নীলের চাহিদা। নীলচাষীদের সংগঠিত প্রতিরোধের মুখে ইউরোপীয় নীলকরেরা বিনিয়োগ তুলে নেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাটচাষ নগণ্য ছিল। ব্যাপকহারে পাটচাষ এবং পাট-আঁশের বাণিজ্যিকিকরণ শুরু হয়ে ১৮৭০ এর দশকে। এই সময় থেকে শুরু করে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত পাটের স্বর্ণযুগ। ১৯৩০ এর বিশ্বমন্দাতে পাটের বাজার পুরোপুরি ধ্বসে পড়ে।
বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও আধুনিক পুঁজিবাদের চাপে বাংলার অর্থনীতি ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। এক বিকৃত ঔপনিবেশিক অর্থনীতি তৈরি হয়, যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, স্থবিরতা, দারিদ্র, বৈষম্য , ঘনঘন দুর্ভিক্ষ ও পুষ্টিহীনতা। এই অর্থনীতিই ছিল পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের উত্তরাধিকার। এর সঙ্গে যুক্ত হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের বিমাতাসুলভ কেন্দ্রীয় নীতি। ১৯৫১ সালের আদমশুমারি হিসাবে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা ছিল চার কোটি ১৯ লক্ষ্য ৩২ হাজার। এর মাঝে ৬৪টি মহকুমা শহরের অধিবাসী ছিল মাত্র ১৮ লক্ষ ২০ হাজার। শহরের জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ৪.৩ শতাংশ ; মূলত তদানীন্তন পূর্ব বাংলা ছিল গ্রামীণ অর্থনীতির। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পূর্ব বাংলায় খাজনাভোগী কাঠামো গড়ে ওঠে। ছোট আকারের ভূসম্পত্তির মালিক ও একই সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি , যারা অবাণিজ্যিক পেশায় নিয়োজিত হয়। একই পরিবারে খাজনাভোগী জমিদার ও চাকুরীজীবী উভয় ভূমিকায় থাকতে দেখা যায়।
দেশভাগের পরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বুর্জোয়া হিসাবে মুসলমানেরা ছিল অত্যল্প। এই অর্থনৈতিক দুর্বলতা ঐতিহাসিক কারণে সৃষ্ট সামাজিক উৎপাদনে শ্রমবিভাগেরই ফল। বাঙালি মুসলমান ঐতিহ্যগতভাবে কৃষিকাজ ও হস্তশিল্পের ধারক ও বাহক। আর বাঙালি হিন্দুরাই মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য , মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ করত। এমনকি ছোট ছোট শিল্পোৎপাদনেও এঁদের দখল বেশি ছিল। দেশভাগের পরে বহুসংখ্যক হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বিপুল অর্থসম্পদসহ দেশত্যাগের কারণে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও মাঝারি বুর্জোয়াদের অবস্থান শূন্যতা তৈরি হয়। ১৯৪৭ থেকে ৫১ সালে এই শূন্যতার সুযোগে পশ্চিম পাকিস্তানি বুর্জোয়া ব্যবসায়ী শিল্পোদ্যোগীরা এবং প্রবল সহযোগী হিসাবে কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো জেঁকে বসে।
সর্বভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পাকিস্তানে যে শিল্পায়ন হয় তার সিংহভাগ শহরকেন্দ্রিক। সমগ্র পাকিস্তানে এ সময় একচেটিয়া পুঁজিপতি পরিবারের জন্ম হয়। ১৯৬২ সালে সারা পাকিস্তানের ব্যক্তিমালিকানাধীন ফার্মের অধীনে মোট যতো সম্পদ ছিল তার ৭৩ শতাংশ ছিল ৪৩টি পরিবারের দখলে। এই ৪৩টি পরিবারের মধ্যে একটি মাত্র পরিবার ছিল বাঙালি – জনাব এ,কে, খানের পরিবার।
দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় ব্যবসায়িক ও লগ্নি পুঁজিকেই কৃষিতে মূলধন সঞ্চয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে ধরা হয়। যদিও এখান থেকে মুনাফার সামান্য অংশই উৎপাদনে পুনঃ বিনিয়োগ করা হোত। সংগঠিত কৃষিঋণ অপ্রচলিত ও অজনপ্রিয় ছিল, কারণ প্রচলিত কৃষি আইনে জমি হস্তান্তর বা খণ্ডকরণের সীমাবদ্ধতার জন্য ঋণদানকারী সংস্থাগুলো জমি বন্ধক রেখে ঋণদানে আগ্রহ দেখাতো না। ফলে মহাজনী ঋণের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হত কৃষক। ঋণদাতা জমির স্বত্ব লাভ করে, অনেক সময় বন্ধকী জমির ফসল থেকেই ঋণ শোধ হয়ে গেলে, মূল মালিকের কাছে জমি ফেরত যায়। আবার জমির মালিকের অধীনে চাষবাস হয়, উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক ঋণদাতাকে ঋণ কিস্তি হিসাবে দিতে হয়। মহাজনী ঋণ পাওয়ার জন্য কৃষক যে কোন শর্তেই রাজি হতে বাধ্য থাকত। আর ঋণের বেশিরভাগ অংশই ব্যয়িত হতো, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য, কাপড়-চোপড়, ওষুধপত্রের মতো অত্যাবশ্যকীয় কাজে। যে কাজের জন্য ঋণ নেওয়া হয়েছে, হালের বলদ, বীজ, সার তার জন্য সামান্য অংশই অবশিষ্ট থাকত। এই দুষ্টচক্রে পড়ে কৃষক ভূমিহীন হতো। ভূস্বামী মহাজনেরাও জমিতে অর্থ না খাটিয়ে নগদ ঋণদানেই আগ্রহী ছিল। জরিপে দেখা যায়, পূর্ব পাকিস্তানে ৬৬ থেকে ৮৭% পরিবারই ঋণগ্রস্ত ছিল। তৎকালীন বিশ্বের তুলনায় উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সারের ব্যবহারে পিছিয়ে থাকায় জমির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল অনেক কম। জমির স্বল্পতা ও বিক্ষিপ্ত অবস্থান পুরো কৃষি উৎপাদনের চক্রকে অনাধুনিক করে রেখেছিল।
পূর্ব পাকিস্তানে কৃষক পরিবারের ধনী হওয়ার মূল বাসনা ছিল সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা। ধন-সম্পদ, পরিবারের শিক্ষা-দীক্ষা, সম্মান , উচ্চবংশে বৈবাহিক আত্মীয়তা সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি। সঞ্চিত অর্থে জমি কিনে মর্যাদা বৃদ্ধির একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল সমাজে। আবার জমির পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা এবং আর্থিক সচ্ছলতার উৎস হিসাবে দ্বিতীয় প্রধান সম্পদ ধরা হয় শিক্ষাকে। শিক্ষিত লোক স্থানীয় প্রশাসনে, শহরে চাকরি করে পরিবারের সম্পদ বৃদ্ধি করে।
দেশভাগের আগে সম্পদের বড়ো একটা অংশ ছিল হিন্দু জমিদার ও ধনিক শ্রেণির হাতে। হিন্দু ধনীদের পারলৌকিকতার চর্চা ছিল, পূজা পার্বনে দেখনদারি ও অনর্থক অপচয় ছিল। কিন্তু যেহেতু মুসলমানদের আগেই আধুনিক অগ্রসর চিন্তার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছে সেই ১৮শ শতকের শুরুতেই, তাই পারলৌকিকতার বাইরেও তাঁদের সমাজের আধুনিক শিক্ষা, চিকিৎসায় দীর্ঘমেয়াদি । মুসলমান ধনী শ্রেণির হাতে নানা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে টাকা পয়সা আসলেও সেটা তাদের অনগ্রসর মাদ্রাসা শিক্ষা এবং নয়নমনোহর মসজিদ তৈরিতে ব্যয়িত হয়েছে। পুর্ব বঙ্গের নানা ধরণের আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়ের পুরোটাই বলতে গেলে কয়েক শতাব্দী ধরে হিন্দু ধনী শ্রেণির করা। মুসলমান ধনী শ্রেণি যারা অধুনা বাংলাদেশের পরিচালনায় আছেন, মূলতঃ তারা সেই আগের শতাব্দীর পিতামহদের ধারা পালন করে যাচ্ছেন।
চৌধুরীদের গ্রামে মসজিদ আছে, মক্তব আছে, খোন্দকারদের সেটা ভালো লাগে না। একই গ্রাম ১০০ গজের ভিতরে আরেকটি সুদৃশ্য মসজিদ ও তাঁর সংলগ্ন মাদ্রাসা । অথচ নারী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। দূর উপজেলার বাইরে আছে সরকারী চিকিৎসালয়। সুপেয় পানির ব্যবস্থা নেই। এ এক অদ্ভুত ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দ্যোতনার ভিতরে দিয়ে বাঙালি মুসলমানের হিসাব নিকাশ চলে।
দেশভাগের পরে পূর্ব বাংলার উৎপন্ন পাট কোলকাতার পাটকলে রপ্তানি হওয়ার যে নিয়ম প্রচলিত ছিল তা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। সরকার নির্ধারিত পাটের ক্রয়মূল্যের চেয়ে রপ্তানিতে লাভ বেশি হয়, মুনাফা বাড়ে। পাটশিল্পের বড় ধরণের পুঁজি বিনিয়োগকারীদের অনেকেরই বৈদেশিক বাণিজ্যের অভিজ্ঞতা ছিল যেমন আদমজি, বাওয়ানি, ইস্পাহানি। ‘ক্রিসেন্ট জুট মিলস লি ‘ এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিল র্যালি ব্রাদার্স ও ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের খোজা গোষ্ঠী। শুরু থেকেই মুসলিম মেমন সম্প্রদায় ( আদমজি , বাওয়ানি) এবং ইসমাইলিয়া খোজা প্রধান পাট রপ্তানিকারক ও বিনিয়োগকারি হিসাবে দেখা দেয়।
পূর্ববাংলা এমনিতেই পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় শিল্পশক্তি ও অবকাঠামোতে পিছিয়ে ছিল। ব্যাংকিং ছিল অনুন্নত। দেশভাগের আগে পাকিস্তান ভূখণ্ডে ৪৮৭টি ব্যাংকের শাখা ছিল , সেটা কমে ৬৯টিতে দাঁড়ায়। হিন্দু ব্যাংক মালিকদের দেশত্যাগের ফলেই এটা হয়। শূন্যতা পূরণ হয় পাকিস্তানের তিনটি ব্যাংকের কার্যক্রমে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, ‘হাবিব ব্যাংক’, ‘মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক’, ও ‘স্টেট ব্যাংক’ । যদিও প্রত্যেকটি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে শিল্পোৎপাদন, যোগাযোগ ও পরিবহন, বৈদ্যুতিক শক্তি, ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রধান অংশই যে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল তাই নয়, দেশের উচ্চতর বেসামরিক প্রশাসনের (Civil Administration ) পুরোটাই ছিল সেখানে। পূর্ববাংলার সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের প্রশাসনের সকল দায়িত্বশীল পদে পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মচারী নিয়োগ করে।
দেশভাগের পরেও পূর্ব বাংলার পুঁজির শতকরা ১৫ ভাগের মালিকানা ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের। ১৯৫৬ সাল পর্যন্তও কয়েকটি বৃহৎ কাপড়ের মিল, একমাত্র সিমেন্ট কারখানা, ১৭টি চা বাগান, কয়েকটি ব্যাংক হিন্দু মালিকানাধীন ছিল। কোন কোন তথ্যমতে, ৫০টির ও বেশি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, ২০০ অন্যান্য ব্যবসা হিন্দু মালিকানাধীন ছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময় ‘শত্রু সম্পত্তি’ ঘোষণা করে প্রাদেশিক সরকার সেগুলো কুক্ষিগত করে।
মূলত: পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের শুরুর দিকে সরকার ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনই ছিল দেশের অর্থনৈতিক উদ্যোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। সেই উদ্যোগ আবার পরিচালিত হতো প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিকাশেই। যেহেতু ১৯৪৭ এর পরে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প ভিত্তি ছিল অনেক শক্তিশালী, পূর্ববাংলার তুলনায় শিল্পোৎপাদন, বৃহৎ পুঁজি, অবকাঠামো, বাজেটের সিংহভাগ আঞ্চলিক বৈষম্যকে প্রকট করে তোলে। কারণ এখানে মুদ্রা সঞ্চয় এবং পুঁজি বিনিয়োগ দুই ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তান এগিয়ে থাকে। জমির স্বল্পতা এবং শিল্পাঞ্চলে তার উচ্চমূল্য পূর্ব পাকিস্তানে পুঁজি বিনিয়োগের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। সেই দিকে বেশির ভাগ বাঙালি পুঁজিপতিই ছিল ছোট বা মাঝারি। অনগ্রসর অর্থনৈতিক কাঠামোতে সঞ্চয়ের সিংহভাগ আসতো কৃষিখাত এবং ক্ষুদ্র শিল্পখাত থেকে।
১৯৫০-৫২ সালের কোরিয়া যুদ্ধে পাট ও পাটজাত পণ্যের ভারতমুখী প্রবণতা কমে বিদেশি বাজারে চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু কোরিয়ান যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পাকিস্তানের পাট ও তুলার রপ্তানিবাজারের আকাল দেখা দেয়। কাঁচামালের দাম যায় কমে। এর মাঝে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানে ৩৬টি নতুন পাটকল স্থাপিত হয়, কাঁচামাল হিসাবে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পাটের উৎপাদন ৬৫০ হাজার টনের মধ্যে রয়ে যায়। ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রাধান্য দিতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তান পাটবাজারের বিশ্ববাজার হারায়। সামগ্রিকভাবে পূর্বপাকিস্তানের নির্ভরতা এমন ছিল যে, পাটকলের যন্ত্রাংশ বড় কারখানাগুলোর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে তৈরি হতো। আদমজি পাটকল, প্লাটিনাম জুবিলি এবং আরো কয়েকটি পাটকলের এ ধরণের ওয়ার্কশপ ছিল, কিন্তু কারখানাগুলোর মালিক ছিল অবাঙালি বুর্জোয়ারা। সাধারণ বয়নশিল্প ব টেক্সটাইল শিল্পেরও একই অবস্থা , যন্ত্রাংশ নির্মাণের দশটি কারখানার আটটিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।
আদমজি, বাওয়ানি, ইস্পাহানি, আমিন গ্রুপ , খোজা ইসমাইলিরা ছাড়াও হাবিব পরিবার, দাউদ পরিবার, দাদা পরিবার, সায়গল পরিবার, মোহাম্মদ বশীর পরিবার, কলোনি গ্রুপ , নবাব হেতি পরিবার, মাওলা বক্স পরিবার, সাত্তার পরিবার। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিতে আরো উল্লেখযোগ্য গ্রুপ গুলো হচ্ছে, রশিদ এজেন্সিজ, গুল এজেন্সিজ ও গ্লোব এজেন্সিজ নামের পশ্চিম পাকিস্তানি কোম্পানির সম্মিলিত গ্রুপ।
বেশির ভাগ অবাঙালি মালিকই ছিল কতগুলো সীমাবদ্ধ সম্প্রদায়ের সদস্য যা গড়ে উঠেছিল পারিবারিক বা ব্যবসায়িক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। এরা হলো গুজরাটি সম্প্রদায়, মেমন , খোজা ইসমাইলি,পাঞ্জাবি সম্প্রদায়, চিনিয়ট শেখ, বোহরা, পিরাঞ্চা প্রমুখ। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প বাণিজ্যের একটা বড় অংশ একেকজন পৃথক শিল্পপতি বা পরিবারের হাতে আসার মাধ্যমে সম্প্রদায়গত ভাবে অবাঙালি পুঁজিপতিদের ক্ষমতা পূর্ব বাংলার অর্থনীতিতে অনেক বেড়ে যায়। মেমন সম্প্রদায়ের সদস্যরাই অবাঙালি পুঁজিপতিদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি এবং অধিকতর প্রভাবশালী ছিল। মেমনদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং কমপক্ষে তিনটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক এরকম যেসব পরিবারের নাম করা যায় তারা হলো দাদাভাই, বাবা, দাদা, বেঙ্গলি, দাগিয়া, তার মোহাম্মদ, জানু, হাশিম, তাবান, এলাহি, দিনার , দোসা, জিজি, গনি, মোহাম্মদ সেলিম এবং আরো অনেকে।
খোজা ইসমাইলিদের কিছু পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে এক পর্যায়ে বৃহৎ শিল্পপরিবার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, এদের কয়েকটি হলো, মোহাম্মদ আলী মেঘানা, সালেহ ম্যানেজমেন্ট, বরকত আলী পরিবার, আমলানি বরলাপ, আকবর আলী আফ্রিকাওয়ালা, স্টার গ্রুপ। এসব কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ও বড় অংশের মালিকানা ছিল, এদের ইমাম প্রিন্স করিম আগা খান।
ধনী বাঙালি বুর্জোয়াদের উদ্ভব ছিল অসম প্রতিযোগিতায়। পাকিস্তানি বৃহৎ পুঁজিপতিদের তুলনায় বাঙালি মুসলমান বুর্জোয়ারা সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। তাছাড়া ঐতিহ্যগত ভাবে বাঙালি বুর্জোয়ারা পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহী ছিল না। এরা ব্যবসায়ের মধ্যস্থতা, সুদের কারবার ও জমির মালিকানাকেই প্রাধান্য দিত। যৎসামান্য বাঙালি বুর্জোয়াদের অধিকাংশই ছিল শিল্প-বাণিজ্য বুর্জোয়া। সামান্য কিছু শিল্পোৎপাদনে তারা জড়িত ছিল মূলত পাট, সুতা-বস্ত্র, কাগজ, ইট ও দিয়াশলাই এর মতো শিল্পে সীমাবদ্ধ। যেমন ১৯৭১ সালের তথ্য অনুযায়ী বাঙালি মালিকানাধীন ৩৪ টি পাটকলের ২৮টিই কাজ শুরু করেছিল ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। এবং মালিকানার অংশীদার বাঙালি মালিকদের অভিজ্ঞতা ছিল কম, এরা পূর্বে কোন শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে জড়িত ছিল না।
ব্যক্তি পর্যায়ে নিজেদের পুঁজি দিয়ে তারা শিল্পে অংশগ্রহণ করত না বললেই চলে। এ ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো হয় সরকারী কর্পোরেশনের অধীনে ছিল, অথবা গুটিকয়েক অবাঙালি পরিবারের মালিকানাধীন। বাঙালিদের বিনিয়োগের অধিকাংশই ছিল ঋণপুঁজি। অংশীদারিত্বের মোট মূল্যের ৬০ শতাংশই ছিল ঋণ পুঁজি। ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তাদের একটা এলিট শ্রেণি তৈরির নীতি কাজ করতে শুরু করে। যদিও পূর্ব পাকিস্তানে শুধু ২২ পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া বৃহৎ ব্যবসায়ের সংস্পর্শে আসা প্রায় অসম্ভব ছিল।
১৯৭১ সালের জরিপ অনুযায়ী বস্ত্রশিল্পে ৪৫টি চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৪টি ছিল বাঙালি অংশীদারিত্বের। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, এ.কে খান ; ইসলাম ব্রাদার্স, আফিল, ফকিরচান্দ, হাওলাদার, বি রহমান, রহমান-কাউয়ুম, সাত্তার, আলহাজ মুসলিমউদ্দিন ও ফিল্স্ মাশরিকি।
লক্ষণীয় , বাঙালি শিল্পোদ্যোক্তাদের ব্যাংক ঋণের প্রচুর ব্যবহার তাদেরকে অবশ্যম্ভাবী ঋণীতে পর্যবসিত করেছে। অধিকাংশ বাঙালি কোম্পানি বা গ্রুপের অর্থনৈতিক ক্ষমতা তাদের সক্রিয় পুঁজির সামষ্টিক বিচারে যা মনে হতো, বাস্তবিকপক্ষে তা ছিল তার থেকে অনেক কম। আশির দশকে গার্মেন্টস শিল্পের ক্ষেত্রেও সেই একই ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে আমাদের শিল্পপতিরা।
পূর্ব বাংলা এই উপমহাদেশের মূল অর্থনৈতিক বিকাশে সবসময় আঞ্চলিক বৈষম্যের শিকার হয়েছে। পাকিস্তান হওয়ার পরে বৈষম্য প্রকট হয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের স্বেচ্ছাচারিতা ও নিয়ন্ত্রণহীণতা।
পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার আরেকটি কারণ ছিল, এই প্রদেশে ব্যক্তি পর্যায়ের পুঁজির বিকাশের দুর্বল অবস্থা। উল্টোদিকে পশ্চিম পাকিস্তান এগিয়েছিল তার অভিজ্ঞ ব্যক্তিগত খাতের উদ্যোগ ও উঁচু প্রবৃদ্ধির হারের জন্য।
পাকিস্তান সৃষ্টির শুরুতে কৃষিই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির মূল খাত। জনসংখ্যার ৯৩ শতাংশই বসবাস করতো গ্রামে। কর্মক্ষম জনশক্তির ৮০ ভাগ নিয়োজিত ছিল কৃষিকাজে। আর মোট জাতীয় উৎপাদনের ৫৫ ভাগই উৎপাদন করতো তারা। যে টুকু মূলধন সঞ্চিত হতো সেটা কৃষিতেই সীমাবদ্ধ ছিল।
পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, এ,কে,খান ( আবুল কাশেম খান) ; ইসলাম গ্রুপ ( জহুরুল ইসলাম) ; ভুঁইয়া বাঁ গাওসিয়া গ্রুপ ( আলহাজ গুলবক্স ভুঁইয়া ) ; রহমান কাইউম গ্রুপ ( মকবুল রহমান, কাজী জহিরুল কাইউম); ফকির চাঁদ গ্রুপ ( আলহাজ মোহাম্মদ ফকির চাঁদ ), আলহাজ মুসলিমউদ্দিন গ্রুপ , নর্দান পিপলস , আফিল গ্রুপ, রহমান ব্রাদার্স, সাত্তার গ্রুপ, আশরাফ গ্রুপ, ভাণ্ডারি গ্রুপ, ডেলটা , সবদার আলী, আনোয়ার নিউ স্টার, ইব্রাহিম মিয়াঁ অ্যান্ড সন্স।
বাংলাদেশের ধনীদের মোটা দাগে তিনভাগে ভাগ করা যায়, প্রথম ভাগে আছে পারিবারিকভাবে যারা ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তা। ইস্পাহানি, ইসমাইলী, সওদাগর , সাহা গোত্রের লোক এই শ্রেণিতে । দ্বিতীয় শ্রেণিতে আছে, রাজনৈতিক পরিবারগুলো। এঁদের কারো কারো পূর্বপুরুষ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন, সরকারে সকল সুবিধা নিয়ে নৈতিক-অনৈতিকভাবে ধনী হয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হওয়ায় এদের শিল্পকারখানা ও স্থাবর সম্পত্তির হাতবদল হয়েছে। এঁদের অনেকেই কয়েক দশকের বেশি টিকে থাকতে পারে নি। তৃতীয় শ্রেণিতে আছেন তাঁরা , যারা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শুধুমাত্র উদ্যোগ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে , নিজের যোগ্যতায় বিশাল শিল্প-কলকারখানা ও সাম্রাজ্য গড়েছেন। আধুনিক বাংলাদেশের এরাই বৃহত্তম। পূর্বাপর ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিশেষ কিছু অভূতপূর্ব সুযোগ এদের ধনসম্পদ বাড়াতে সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একটা শ্রেণিকে ধনী করেছে। পাকিস্তানের অভ্যুদয় আরেক শ্রেণিকে। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর অবারিত মুক্তবাজার অর্থনীতি, পুঁজিবাদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র, বৈদেশিক সাহায্য সবচেয়ে বড় অংশকে ধনী করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা, ব্যাংকঋণ, আমদানি-রফতানি প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার নিয়ন্ত্রিত ছিল বলে সরকারি কর্মচারী ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবানদের নব্যধনী হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। নব্য-ধনীদের অনেকেই দেশে টিকে গেছেন, কিন্তু অনোপার্জিত অর্থের উপর গড়ে ওঠা শিল্প-কলকারখানা অনেকেই ধরে রাখতে পারেন নাই।
বাংলাদেশের ধনীদের কিছু সাধারণ সাদৃশ্য চোখে পড়ে। এঁরা সকলেই বুদ্ধিমান, সাহসী পরিশ্রমী এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তার অধিকারী। প্রথমদিকের ধনীরা ধর্মভীরু সাধারণ বাঙ্গালী। সকলেই ভাগ্যে বিশ্বাসী , ধার্মিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনেকে নানাধরনের পীর ফকিরের ক্ষমতায়ও বিশ্বাসী।
আশির দশকে বাংলাদেশের রেডিমেড গার্মেন্টস সেকটর গড়ে ওঠে। সস্তা শ্রম ও প্রাকৃতিকভাবে পানির প্রাচুর্যতা টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস সেক্টরকে প্রসারিত করে। সরকার ও রাজনৈতিক অনুগ্রহভাজন ছাড়াও একেবারে শূন্য থেকে শিল্পোদ্যোক্তা একটি শ্রেণি গার্মেন্টস সেক্টরকে দাঁড় করিয়েছেন। দুর্বিষহ আমলাতান্ত্রিক জটিলতার পরেও বাংলাদেশে এই নব্য-ধনীদের শিল্পোদ্যোগ গড়ে উঠেছে অসংখ্য কলকারখানা। বিশাল এই জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে সরকারের অবদান অতি সামান্য। বেসরকারিভাবে সংগঠিত এই কর্মসংস্থান আমাদেরকে বিশ্ববাজারে মাথা উঁচু করেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই শ্রেণিটির বড় অংশই দুর্নীতি না করেই নিজেদের মেধা ও অমানুষিক পরিশ্রমে গার্মেন্টসকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে দীর্ঘ কয়েকদশক পরিচিত করিয়েছে।
অন্যদিকে প্রতিবছর প্রবাস থেকে বৈদেশিক রেমিটেন্স এনেছে যে নিম্নমধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী, এঁরা মূলত: তাঁদের পরিবারের শ্রেণি উত্তরণে নিয়ামকের মতো নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। দেশের নিম্নবিত্ত শ্রেণিটি মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপের কয়েকটি দেশের শ্রমবাজার থেকে প্রতিবছর বিশাল অংকের রেমিটেন্স নিয়ে এসেছেন নিয়মিত। কিন্তু সেই উপার্জিত পুঁজি ও বিত্ত ভূসম্পত্তি ক্রয় ও নানা ভোগবিলাসে ব্যয়িত হয়ে থাকে। প্রবাস থেকে আসা যথেচ্ছ পুঁজি দেশের শিল্পবিনিয়োগে কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না ; বরং মুদ্রাস্ফীতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অবশ্যই স্বাধীন বাংলাদেশের বিশাল নিম্নবিত্তদের বড় একটি অংশের মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটেছে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের পাশাপাশি স্বল্পশিক্ষিত আরো একটি মধ্যবিত্ত সমাজ এখন সাড়া দেশ জুড়ে। পুরো পৃথিবী যখন পুঁজিবাদের চূড়ান্ত ফলন দেখতে পাচ্ছে, এই ভোগবাদী বস্তুতান্ত্রিক সমাজে ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন বিশাল এই মধ্যবিত্তরা দেশের অর্থনীতির বিকাশে অবদান রাখছে বৈকি।
বাংলাদেশের ধনীদের ভেতরে সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে অবদান রেখেছেন এমন দৃষ্টান্ত মাত্র হাতে গোনা কয়েকজনের। এঁদের মাঝে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন রণদা প্রসাদ সাহা। তিনি বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে খাদ্যশস্য ক্রয়ের চুক্তি পেয়ে বিশাল সম্পদের অধিকারী হন। একে একে পাটকল, ডকইয়ার্ড, বেঙ্গল রিভার সার্ভিস, পাওয়ার হাউজ, ট্যানারি ব্যবসা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগে তাঁর সমস্ত ব্যবসা থেকে যে আয় হবে তা দিয়ে একটি দাতব্য ট্রাস্ট গঠন করেন। যা ‘কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট’ নামে সুবিখ্যাত। এছাড়া, মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমস্। কুমুদিনী হাসপাতালে স্কুল অব নার্সিং , কুমুদিনী কলেজ, এস,কে হাইস্কুল, দেবেন্দ্র কলেজ ইত্যাদি। তাঁর মতো সংস্কারমুক্ত অসাম্প্রদায়িক ধনী বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে হিন্দু জমিদারদের পূজাপার্বণে যথেচ্ছ অপচয়ের পরেও হাসপাতাল, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় করে যাওয়ার প্রবণতা আমাদের সমাজকে এগিয়েছে। আধুনিক বাংলাদেশের ধনীদের মাঝে সামাজিক ও মানবিকখাতে অবদান রাখার কোনো প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। রাজস্ব প্রদানেও এদের বড় ধরণের অনীহা কাজ করে। বেশিরভাগ ধনী পরিবার ও শিল্প গ্রুপগুলোর সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সুসম্পর্ক থাকে দেয়া-নেয়ার। ছোট উদ্যোক্তাদের ব্যাপারে রাজস্ববিভাগ খড়গহস্ত থাকলেও বড় ধনীদের ব্যাপারে চরম ঔদাসীন্য দেখায়। সামাজিক দুর্নীতির কথা আগে পত্রিকা অথবা মিডিয়াতে আসার সম্ভাবনা ছিল। জনসচেতনতা ছিল। এখনকার নব্যধনীদের নিজস্ব ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া থাকে। আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, আশির দশকের আগে রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীর দূরত্ব ছিল। পরপর কয়েকটি সামরিক শাসনে জর্জরিত হতে হতে দেখা গেল , দেশের ব্যবসায়ী সমাজের একটি বড় অংশ রাজনীতিতে চলে এসেছে। গত কয়েকটি সংসদের সিংহভাগ সংসদসদস্য ব্যবসায়ী পরিবারের এবং তাদের প্রত্যেকের চলমান শিল্প ,কলকারখানা বিদ্যমান।
দেশের খ্যাতনামা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই মুহূর্তে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, এ কে খান গ্রুপ, বেক্সিমকো , স্কয়ার, আনোয়ার গ্রুপ, আকিজ গ্রুপ, রহিম আফরোজ, প্রাণ আরএফএল , ইউনাইটেড গ্রুপ, সিটি গ্রুপ, যমুনা গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ, বসুন্ধরা গ্রুপ। দার্শনিকভাবে ধনী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের মৌলিক প্রবণতা থাকে পুঁজি বাড়ানো, মুনাফাবৃদ্ধি করে জীবনের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বাড়ানো। কিন্তু তাদের এই উদ্যোগের সাথে সাথে অর্থনৈতিক অবকাঠামো গড়ে ওঠে, সমাজের লাভ হয়, দেশের আর্থসামাজিক পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশ এই ধনী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে খাদ্য উৎপাদনে নিত্যনতুন প্রযুক্তির দেখা পেয়েছে। দেশের বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ শিল্পে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। বহু ক্ষেত্রে আমাদের আমদানি নির্ভরতা একেবারে কমে গেছে। আমরা হয়ে গেছি, রপ্তানিমুখি দেশ। আমাদের বস্ত্রশিল্প, চামড়াশিল্প , কুটিরশিল্প, ঔষধশিল্প দিয়ে বিশ্ববাজারে আমাদের নাম পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশের ধনী সম্প্রদায়ের প্রধানতম অবদান হচ্ছে কর্মসংস্থান। কর্মসংস্থানের ফলে একটা উদীয়মান জাতির কর্মক্ষমতা বেড়েছে, গার্মেন্টস সেক্টরে প্রসারে নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা বেড়েছে এবং শিল্পোদ্যোক্তা এই ধনীদের অবদানে বাংলাদেশ আজ উন্নত দেশের তালিকাভুক্তির জন্য অপেক্ষমাণ। কিন্তু সামাজিক ও মানবিকক্ষেত্রে এঁদের অবদান অর্থনৈতিক সক্ষমতার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল এবং অকিঞ্চিৎকর।
সহায়ক তথ্যসূত্রঃ
১। পুর্ব বাংলাঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য ( ১৯৪৭-১৯৭১)। এস এস বারানভ। সাহিত্যপ্রকাশ। জুলাই ১৯৮৬
২। বাংলাদেশের কয়েকজন শিল্পোদ্যোগীর জীবনকাহিনী। সম্পাদনাঃ আবদুল্লাহ ফারুক। ব্যবসায় গবেষণা সংস্থা। সেপ্টেম্বর,১৯৮৪
৩। বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪ -১৯৭১ ; ১ম খণ্ড রাজনৈতিক ইতিহাস ; ২য় খণ্ড অর্থনৈতিক ইতিহাস ; ৩য় খণ্ড সামাজিক ও
সাংস্কৃতিক ইতিহাস। সম্পাদকঃ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ডিসেম্বর ,১৯৯৩
৪। দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন গবেষণা।
by Jahid | Jan 23, 2021 | দর্শন, লাইফ স্টাইল
এই ধরেন, কয়েকবছর আগেও আরেক মহল্লার বন্ধু আত্মীয়রা কে কেমন ফাঁপরে আছে, কেমন যাচ্ছে দিনকাল ; সেটা জানার সহজ উপায় ছিল না। শাশুড়ির কেলানি, ননদের কূটনামি , স্বামীর সঙ্গে খিটমিট করে গিন্নীরা ডালে পাঁচফোড়ন দিত, বাচ্চাকে খাওয়াতো। আর মাঝেসাঁঝে সুযোগ পেলে বলতো, যেদিকে দু’চোখ যায় চলে যাবে। ঘটক শালা থেকে শুরু করে বাপ ভাইকে শাপান্ত করতো, কোন অলক্ষুণের হাতে মেয়েকে তুলে দিয়েছে বলে ; বিড়াল পার করে আর খোঁজ নেয় না বলে। দুইবাড়ি পরের সমবয়সী কোন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে কোন এক বিকেলে দেখা হলে, খুব মেপে মেপে সেই সাধারণ কথাগুলোই শেয়ার করতো যেগুলো খুব বিপদজনক বড় মাপের না। যেগুলো সারা পাড়া ঘুরে নিজের কাছে উল্টো ফিরে আসার সম্ভাবনা কম। আর রাত হলে স্বামী সোহাগে দিনের কূটকচাল, অভিমান ভুলে যেতে যেতে ভোর হলে, সেইসব গিন্নিরা আবার লেগে পড়তো সংসারে।
সদ্য কৈশোরের বয়ঃসন্ধিকালীন অস্থির , ছাত্রাবস্থায় হালকা ডাব্বা মেরে স্যারের গোষ্ঠী উদ্ধার করতে করতে পাড়ার মোড়ে বিড়ি ফুঁকত যে ছেলেগুলো। আর আড়ে ঠারে মহল্লার সুন্দরী কিশোরী কখন ব্যালকনিতে আসে সেই প্রতীক্ষায় থাকতো যে ছেলেগুলো। সেই ছেলেরাই আবার চাকরি করতে গিয়ে ট্র্যাফিক ঠেলতে ঠেলতে শাপান্ত করতো সরকারকে। অফিসে বসের ঝাড়ি খেয়ে , পকেটমার হয়ে, বাসের ভিড়ে শার্টের হাতা ছিঁড়ে, হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে দরোজায় কড়া নেড়ে প্রিয়মুখ দেখে সব যেতো ভুলে।
আমাদের চিরচেনা সেই ছেলেমেয়েদের বয়স হয়েছে। এখন তারা অবাধ , নিরবচ্ছিন্ন অনলাইন ভার্চুয়াল পৃথিবী পেয়ে চরমভাবাপন্ন হয়ে গেছে। একটা ‘অনাবশ্যক’ হুতাশন আর অস্থিরতায় কাটছে তাদের এইসব দিনরাত্রি।
মানুষতো জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই নিজেকে প্রকাশ ও প্রমাণ করতে চায়। দেখবেন – তুচ্ছ মানবশিশু হামাগুড়ি দিলেও সারা পরিবার উচ্ছ্বসিত হয় ; হাঁটি হাঁটি পা পা করলেও সারা পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। আধো আধো অর্থহীন বুলি ফুটলেও উচ্ছ্বাস, খাবার উগড়ে দিলেও উচ্ছ্বাস , হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেও , বাবা রে সোনা রে, ওরে কে রে বলে উচ্ছ্বাস। এই যে, কোন একটা কিছু করেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা ও মনোযোগ পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া মানবশিশু, বড় হতে হতে যখন দেখে, সে আর দশজন সাধারণ মানুষের মতোই; বাড়ির বাইরে তো তার আর তেমন কোন পরিচয় নেই– তখন সে একটা কিছু হওয়ার জন্যে সে উঠে পড়ে লাগে। তারপর গুচ্ছের পড়াশোনা করে উপার্জনক্ষম হলেও কোথায় যেন মনোযোগের আকাল পড়ে। পাড়ার ডাকসাইটে সুন্দরী তরুণীদের বিয়ের কয়েক-দশক কেটে গেলে চারপাশে আর কোন মুগ্ধ চোখ কিংবা অকারণ উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য থাকে না। সেটা তারা মেনে নিতে শেখে। সংসারে মন দেয়, ঘরকন্না করে, বাচ্চাদের বড় করে, বিয়ে দেয়।
ভার্চুয়াল জগতের আগের জগত ছিল কিছুটা আলোড়নহীণ। ভার্চুয়াল জগতের অনাবশ্যক ক্রমাগত বিস্ফোরক আলোড়ন আর উচ্ছ্বাস সুযোগ এনে দিয়েছে হুমড়ি খেয়ে পড়া শিশুটিকে ! সেই বয়স্ক শিশুটি পড়ে গেছে যেন তেন প্রকারে মনোযোগ পাওয়ার অভ্যস্ততার চিরন্তন চক্রে।
যা ঘটছে, আর যা আপনি ভার্চুয়ালি প্রকাশ করছেন , সেখানে কিন্তু আগেও ফাঁক ছিল। সেই ফাঁক , মাপাহাসি চাপাকান্নার সেই মেকি প্রদর্শনকামিতা ও সহানুভূতিলিপ্সা একইরকম আছে । তেমন কিছু বদলায়নি । পুঁজিবাদ, ভোগবাদিতার অন্য সব সার্বজনীন সুবিধার মতো এ শুধু সংখ্যাতেই বেড়েছে, বিশাল সেই সংখ্যা ! দেখার চোখ থাকলে, সহজেই দুঃখবিলাসী , প্রদর্শনকামী , অতিআত্মপ্রেমি, অস্থির , বিভ্রান্ত, পরশ্রীকাতর,অনাবশ্যক হতাশ, অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ঈর্ষাপরায়ণ সংখ্যাহীন মানুষকে দেখতে পাবেন।
যতোই ইমোজি থাকুক, মানুষের মৌলিক অনুভূতিগুলো কি আর বদলে যাবে এতো সহজে !
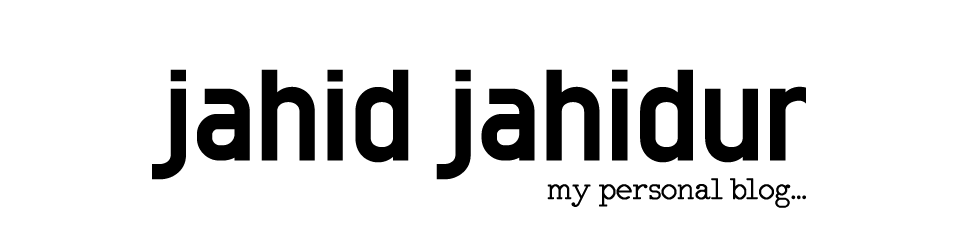
সাম্প্রতিক মন্তব্য