by Jahid | Nov 26, 2020 | সাহিত্য
মেয়েদেরকে নিয়ে বাজারে বহুরকমের ঠাট্টা চালু আছে, তবে তার বেশিটাই নিষ্ঠুর
আমিও খান তিনেক জানি, যেমনঃ
যে মেয়ে সহজলভ্যা তাকে বলা হয় পাপোস
যে মেয়ের বুক নেই তাকে বলে ম্যানচেস্টার
যে মেয়েরা এক মাসের জন্য জীবনে আসে তাদের বলেঃ চায়ের খুরি
অর্থাৎ ইয়ুজ অ্যান্ড থ্রো।
যে মেয়ের বয়স হয়ে এল, যৌবন যাই যাই করছে, তাদের সম্পর্কে
এক অধ্যাপক বন্ধু বলেছিলঃব্যবহার করার আগে ঝাঁকিয়ে নেবেন।
এতো নিচু মাপের ভাষা শুনে আমার গা ঘিনঘিন করে
এ সবই ওই ব্রাহ্মণের প্রভাব, মনু নামে যিনি বিখ্যাত।
ছেলেদের সম্পর্কে ঠাট্টাগুলো তেমন জোরালো নয়
বড়জোর আমরা বলিঃ উওম্যানাইজর , অর্থাৎ আলুবাবু
মেয়েরাও ছেলেদের অনেক নাম দেয় যেমন, ঘুরঘুরে পোকা
হিন্দুস্তান পাকিস্তান
অর্থাৎ যার বাছবিচার নেই
এইসব ঠাট্টার ভেতর ছেলেদের প্রশ্রয় দেবার একটা প্রবণতা থাকে
সেই ঠাকুমার কথাঃ সোনার আংটি আবার ব্যাঁকা?
মেয়েদের নিয়ে বদরসিকতা আমার ভাল লাগে না।
আমি তিন দিদির সঙ্গে মানুষ হয়েছি, সুতরাং
মেয়ে বলতে আমি বুঝি নারী
তার ৩২-৩৬-৩২ আমার বিষয় নয়
সে হয়তো সুদূর কোন নৌকার ভেতর বসে অপেক্ষা করছে
সেই নৌকো কোথায় আমি জানি না
কিন্তু আমাকে সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই হবে।
সূর্যাস্তের আগে আমি কি পারব তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে?
by Jahid | Nov 26, 2020 | সাহিত্য
আমি কোন থিয়োরির গেটকিপার নই। কোনও সৌন্দর্যের দারোয়ান নই। আমার কোন অ্যাটাচি কেস নেই যে তাঁর ভেতরে একটা পর্বতমালা নিয়ে আমি বিমানে উঠে পড়ব। আমি চেয়েছিলাম কবিতাই লিখতে, একটা লোক এসে বলল, আপনি যা লিখছেন, একে কবিতা বলে না, বলে অ্যান্টি-পোয়েট্রি। সেটাই বা কী বস্তু ? সেটা বুঝতেই জীবন চলে গেল।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আমাকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারবেন?
তিনি বললেন , শিয়োর। মিস্টার রামোকৃষ্ণের গল্পটা ধরুন। ফাইভ ব্লাইন্ড মেন অ্যান্ড দ্য এলিফ্যান্ট। যিনি পা ধরে দেখলেন, তিনি হাতিকে ঠাউরেছিলেন একটি ল্যাম্পপোস্ট। যিনি পেট ধরে দেখলেন তিনি ভাবলেন হাতি একটা বালির বস্তা। যিনি কান ধরে দেখলেন, তিনি বললেন, হাতি আসলে একটা কুলো। ব্লা ব্লা ব্লা ।
ভদ্রলোক বিদেশে পড়ান , এক কলমেই বাঘে গোরুতে জল খাওয়ান, আমি তাঁকে বললাম, আমি হাতিকে কী বলে ঠাউরেছি, আপনার কী মনে হয় ? উনি বললেন, আপনি হাতিকে ভেবেছেন ঝাঁটা। অর্থাৎ আপনি হাতির পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন , লেজটাকে ধরেছিলেন।
আপনি কি বলতে চান আমি কবিতাকে ঝাঁটা হিসেবে ব্যবহার করি? ভদ্রলোক বললেন, সে তো কিছুটা সত্যি। আপনি কোথাও ধুলো দেখলেই ঝাঁটা বের করেন, আপনি ঘুষ দেখলেই ঝাঁটা বের করেন, গুজরাত দেখলেই ঝাঁটা বের করেন, বানতলা হলেই ঝাঁটা বের করেন, কামদুনি হলেই ঝাঁটা বের করেন। কোথাও কেওরামি দেখলেই , ধুলো জমলেই আপনি প্রতিবাদের ঝাঁটা নিয়ে নেমে পড়েন।
আমি বললাম, যা বাবা , আমি কোনওদিন গেটকিপার হতে চাইনি, দারোয়ান হতে চাইনি, কিন্তু হয়ে গেলাম ঝাড়ুদার।
…
আমার কবিতা হয়ে উঠল সহজ, আমি ছন্দে না লিখে গদ্যে লিখে যেতে লাগলাম। যে গদ্য কবিরা ফেলে দেন আমি সেই সেই গদ্য কুড়িয়ে নিলাম।যে গল্প বাদ দিয়ে কবিরা লেখেন, আমি সেই গল্প ফিরিয়ে আনলাম আমার কবিতায়। ফলে আমার কবিতা পরে কিছু লোকে বুঝতে পারল, কিছু কবি তাতে রেগে গেল। তাঁরা বললেন, কবিতা বোঝা গেলে সেটা আর কবিতা থাকে না। আমি মন খারাপ করে বসে থাকলাম। মন খারাপ করে কী করব? দশ বছর ধরে মন খারাপ করে বসে থাকা যায় না।আবার উঠে দাঁড়িয়ে লিখতে শুরু করলাম যে লেখা আজও লিখে চলেছি। সম্প্রতি চিন্ময় গুহ আনন্দবাজার-এ লিখেছেন যে ফরাসিতে প্রবাদ আছে, ‘ যা স্বচ্ছ নয়, তা ফরাসি নয়।‘ এতদিন বাদে সান্ত্বনা পেলাম, যাক আমি তাহলে গোপনে গোপনে ফরাসি। অথচ স্বচ্ছ লেখার অপরাধে আমি এতদিন গঞ্জনা সয়ে এলাম।
by Jahid | Nov 26, 2020 | সাহিত্য
এটাই রীতি, এটাই চলে আসছে পৃথিবীতে
পায়ের মাপে তৈরী হয় জুতো
জুতোর মাপে তৈরী হয় না পা।
রাষ্ট্র যখন এগিয়ে দেয় বুট
বলে, ‘ ঢোকাও, পায়ে ঢোকাও ’
চেঁচিয়ে বলি, ‘ ও জুতো আমার পায়ে হচ্ছে না।’
by Jahid | Nov 26, 2020 | শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহিত্য
হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে লেখা একটা বিশদ বিশ্লেষণ ফেসবুকে শেয়ার করে কিছুটা হতাশ হয়েছি। বড় লেখা দেখলে ইদানীং কেউ পড়েও দেখতে চান না মনে হচ্ছে ! পরে ভেবে নিলাম, আমার বন্ধু-তালিকায় হুমায়ূন ভক্তের সংখ্যা সম্ভবত: নগণ্য। আমি আশা করেছিলাম নবীন প্রজন্মের ভক্তকুলের একাংশ আমার শেয়ার দেওয়া এই বিশদ লেখাটা পড়ে হয়তো তাঁদের মতামত জানাবেন। কিন্তু তা হয় নি । আমি ধারণা করছি, বন্ধু-তালিকার বন্ধুরা শুধুমাত্র ২ মিনিটের ম্যাগী নুডলস্ টাইপের একটু হাইকু টাইপ স্ট্যাটাসের সঙ্গে একখানি ছবি টাইপ ‘আরামদায়ক’ স্ট্যাটাস দেখলে দুই এক সেকেন্ড সময় দেন। একটু বড় লেখা হলেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। যাই হোক বন্ধু-তালিকার অনুজ এক ছোটবোনের মন্তব্য ধরে আবার আরেকটি লেখার সূচনা হচ্ছে।
আমি দ্বিধা-হীনভাবে বলতে পারি হুমায়ূন আহমেদ অসম্ভব মেধাবী ও ক্ষমতাধর লেখক ছিলেন। শক্তিমত্তার বিচারে আমাদের এক্সপেকটেশন লেভেল তাঁর কাছে আরও একটু বেশী ছিল ; যেটা তিনি নানা কারণে পূরণ করেননি বা করতে পারেন নি। লেখালেখির বাইরে, নাটক, গান সিনেমা নানাবিধ বাজারি অর্থকরী ব্যাপারে উনি তাঁর মেধাকে ব্যয় করেছেন। ওপার বাংলার কবি, উপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যাপারেও নানা কথা প্রচলিত আছে। সুনীল সস্তা লেখক, ফর্মা ধরে লেখেন, ইত্যাদি। কিন্তু সুনীল ‘ পূর্ব-পশ্চিম’ ‘সেই সময়’ ‘প্রথম আলো’-এর মতো অসাধারণ কিছু লেখা লিখে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন । আমাদের একই আকাঙ্ক্ষা ছিল হুমায়ূন আহমেদের প্রতি। বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বড় মাপের কিছু লেখা আশা করেছিলাম আমরা। সেটা নানা কারণে হয় নি। আমরা তাঁর প্রাথমিক ভক্তরা কিছুটা-তো আশাহত হয়েছি !
ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে মনে হয়েছে–বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে হুমায়ূন আহমেদের ব্যাপারে সবার একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ বা ঈর্ষা কাজ করত । ভদ্রলোক ছিলেন নিখাদ বিজ্ঞানের লোক। মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া দুর্দান্ত একজন ছাত্র। রসায়নের মতো একটা নিরস বিষয়ে ডক্টরেট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর না ছিল সাহিত্যের কোন অভিভাবক, না ছিল কোন সাহিত্য-গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃক্ততা। তাঁর এই অভূতপূর্ব লেখক-খ্যাতি বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনের প্রথিতযশা অনেকেই ঠিক ভালোভাবে নিতে পারেননি ! তাঁকে তুচ্ছ করে দেখানোর, বাজারি, সস্তা লেখক হিসাবে দেখানোর একটা প্রচলিত ধারা এখনো বিদ্যমান। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, হুমায়ূন আহমেদের বিশ্বসাহিত্যের পড়াশোনা ছিল ব্যাপক। তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখাগুলোর মাধ্যমেই আমাদের প্রজন্মের অনেকে পশ্চিমা নানা খ্যাতনামা লেখকের লেখার কথা জানতে পেরেছিলাম।
তাঁর মিসির আলী , হিমু সিরিজের পাশাপাশি সবচেয়ে অনন্য একটা কাজ ছিল বাংলাদেশের সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীকে জনপ্রিয় করে তোলা। তাঁর আগে পরে অনেকে সেটা করেছেন, তাঁর মতো করে পারেননি!
সেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রসঙ্গেই আসি। সুনীল হুমায়ূন আহমেদের কাছের ছিলেন। হুমায়ূনকে সুনীলের মাধ্যমেই পশ্চিমবঙ্গের অনেকে চিনেছেন কিনা জানিনা। তবে, ‘দেশ’-এর মতো প্রধানতম কুলীন পত্রিকায় পরপর ৮ বছর শারদীয় সংখ্যায় হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ছাপা হয়েছে। এটা বাংলাদেশের হুমায়ূন আহমেদ ভক্তদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি বলেই মনে করি। হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পরপরই উনি এক সাক্ষাৎকারে তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা বলেছিলেন। ইউটিউবে আছে। আমি তাড়াহুড়ো করে শুনে শুনে পুনর্লিখন করেছি। আমি সুনীলের সঙ্গে একমত পোষণ করি। হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে যতো তর্ক-বিতর্কই থাক না কেন ; হুমায়ূন আহমেদ আমাদের বাংলা ভাষায় তাঁর স্থান করে নিয়েছেন ,এ ব্যাপারে সবাই নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন।
সাক্ষাৎকারের চুম্বকাংশঃ
সুনীল: তাঁর বুদ্ধিমত্তা তাঁর পড়াশোনা আর লেখার মধ্যে যে হিউমার জ্ঞান , এই সব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি , আমি তাঁর অনেক লেখা পড়েছি । আর মানুষ হুমায়ূন তো আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল।
প্রশ্ন: হুমায়ূন আহমেদের লেখার কোন দিকটা আপনার কাছে বেশী প্রাধান্য পেত? কারণ তাঁর প্রথম দিকের উপন্যাসতো অনেক নাম করেছিল , যেমন নন্দিত নরকে —
সুনীল: আরে ‘নন্দিত নরকে’র সম্পর্কে আমি ‘দেশ’ পত্রিকায় যখন লিখেছিলাম, তখন ওঁকে আমি চিনতামও না। ওঁকে আমি তখন চোখেও দেখিনি, শুধু বইটা পড়েই ভালো লেগেছিল । তারপরে হুমায়ূনকে বাংলাদেশের অনেকে বলত চিপ পপুলার লেখক টেখক কীসব বলত। আমি কিন্তু বইগুলো পড়ে দেখেছি , তাঁর মধ্যে যেমন একটা রসজ্ঞান আছে ,তেমনি অনেক বিষয়ে ওর অনেক গভীর যে পড়াশুনো ছিল , সেটিও জানতে পারা যায় । এগুলি আমার কারোর লেখায় বেশী ভালো লাগে না। হুমায়ূনের জনপ্রিয়তা কত ছিল সবই আমি জানি। আমাদের দেশে শরৎচন্দ্রের একসময় জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁকেও হুমায়ূন ছাড়িয়ে গেছে।
প্রশ্ন: হুমায়ূন আহমেদের যেসব উপন্যাসগুলো ছিল, সেগুলো পাঠক যখন পড়তেন , তাঁরা একটানা পড়ে যেতেন। এবং বলা হত, হুমায়ূন আহমেদের লেখা পাঠককে ধরে রাখতে পারত। এর বৈশিষ্ট্যটা কি ? কেন ?
সুনীল: এটা কিন্তু ভাষার জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। অনেকে যাঁদের ভাষাজ্ঞান কম, তাঁরাই নিজের লেখাকে জটিল করে তোলে। আর যারা, ভাষার আদ্যোপান্ত জানেন, তাঁদের লেখা কিন্তু অতো জটিল হয় না,সহজবোধ্য হয়, রসসিক্ত হয়। কারণ খুব সহজভাবে যারা লেখেন– ওটা মোটেও সহজ কাজ না !
প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যের বিচারে যদি আপনি দেখেন ,ধরেন গত পঞ্চাশ বছরের কথাই যদি ধরি এখানে হুমায়ূন আহমেদকে আপনি কোথায় রাখবেন, কোন অবস্থানে বিচার করবেন ?
সুনীল: আমি হুমায়ূন আহমেদকে বেশ একটা উঁচু জায়গায় রাখব এবং আশা করব ভবিষ্যতের পাঠক এবং গবেষকরা তাঁর কৃতিত্বটা ঠিক ঠিক আরও চিনতে পারবেন ও বুঝতে পারবেন। হুমায়ূন সত্যিই একজন খুব বড় লেখক , বাংলা ভাষার গর্ব, আমি তাই মনে করি।
[ প্রকাশকালঃ ২৬শে নভেম্বর ২০১৬ ]
by Jahid | Nov 26, 2020 | সাহিত্য
বাঁ দিকের বুক পকেটটা সামলাতে সামলাতে
হায়! হায় !
লোকটার ইহকাল পরকাল গেল !
অথচ আর একটু নীচে
হাত দিলেই সে পেত
আলাদ্বীনের আশ্চর্য- প্রদীপ,
তার হৃদয় !
লোকটা জানলোই না !
তার কড়ি গাছে কড়ি হল ।
লক্ষ্মী এলেন
রণ-পায়ে
দেয়াল দিল পাহাড়া
ছোটলোক হাওয়া
যেন ঢুকতে না পারে !
তারপর
একদিন
গোগ্রাসে গিলতে গিলতে
দু-আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে
কখন
খসে পড়ল তার জীবন-
লোকটা জানলই না !
by Jahid | Nov 25, 2020 | সাহিত্য
এইবার চিন্তা স্থির করবার অবসর এসেছে জীবনে
হৃদয় বয়স্ক হল ঢের ;
মোম জ্বলে নিভে যায় অনেক গভীর রাত হলে
অন্ধকারে একআধটা আবছা ইঁদুরের
আসা-যাওয়া টের পাই ঘরের মেঝেয়
হয়তোবা সিলিঙের ‘পরে
বাইরে শিশির ঝরে কুয়াশায়–শীতে
লক্ষীপেঁচার ডানা সজনের ডালে শব্দ করে।
টেবিলে অনেক বই ছড়িয়ে রয়েছে ;
চিন্তাগুলো যেন অনুলোম প্রতিলোম
পরস্পরের প্রতি—ঠাণ্ডা শাদা নারীর মতন
দাঁড়িয়ে রয়েছে চুপে মোম—-
একটি গভীর সূত্রে প্রথিত কি হবে
বইয়ের সকল চিন্তা জীবনের সব অভিজ্ঞতা
সকল নক্ষত্র আর সময়ের অপার গতির
ইতিহাসবৃত্তান্তের আগাগোড়া কথা।
এ সব আশ্চর্য তত্ত্ব ভেবে তবু মন
অনুভব করে এই অন্ধকার ঘরে আজ কেউ
নেই, শুধু এক বিন্দু মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা ছাড়া।
কোনো এক দূর মহাসাগরের ঢেউ
এসে এই অন্ধকার বন্দর স্পর্শ করে চুপে
কোন্ এক দূর দিকে চলে যায়, তবে
সময়ের অন্তিম সঞ্চয়ে প্রেম করুণার বলয় রয়েছে ?
ব্যক্তির ও মানবের সফলতা হবে ?
হয়তো এই ব্রহ্মাণ্ডের অবিনাশ অন্ধকার ছাড়া
মানুষের ভবিষ্যতে কিছু নেই আর ;
সেবা ক্ষমা স্নিগ্ধতা যে আলোর মতন
মানুষের হাতে, তার বুজে –যাওয়া অন্ধ আধার
বারবার বড়ো এক পরিবর্তনীয়তার দিকে
যেতে চায়— সনাতন অন্ধকারে এ প্রয়াস ভালো ;
তবু এই পৃথিবীতে প্রেমের গভীর গল্প আছে
জীবনের রয়েছে তার ( অপরূপ ) প্রতিভাত আলো।
“অগ্রন্থিত কবিতা ।। জীবনানন্দ দাশ।”
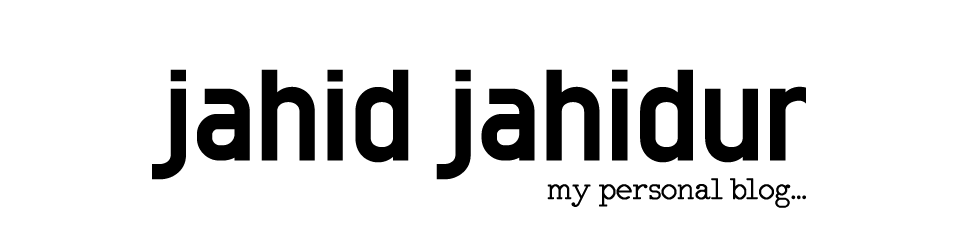
সাম্প্রতিক মন্তব্য