by Jahid | Nov 25, 2020 | দর্শন, শিল্প ও সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি
৫
এই পুঁথিসমূহের দো-ভাষী অর্থ্যাৎ বাংলা এবং আরবী-ফার্সী মিশ্রিত হওয়ার পেছনে একটি অত্যন্ত দূরবর্তী ঐতিহাসিক কারণ বর্তমান। হাদীসে তিনটি কারণে অন্যান্য ভাষার চাইতে আরবীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রথম হলো কোরআনের ভাষা আরবী, দ্বিতীয় কারণ বেহেশতের অধিবাসীদের ভাষা আরবী এবং তৃতীয়ত হজরত মুহম্মদ নিজে একজন আরবীভাষী ছিলেন। এই তিনটি মুখ্য কারণে যে সমস্ত দেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে, সেখানে অপ্রতিরোধ্যভাবে এই ভাষাটিরও অণুপ্রবেশ ঘটেছে। আরব অধিকারের পূর্বে মিশর এবং আফ্রিকার দেশসমূহের নিজস্ব ভাষা এবং বর্ণমালা দুই-ই ছিল। কিন্তু আরব অধিকারে আসার পর আরবী ভাষা এবং বর্ণমালা দুইটিকেই অধিবাসীদের গ্রহণ করতে হয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবী ভাষা এবং ইসলাম অনেকটা অভিন্নার্থক ছিল। আরবী ভাষাকে গ্রহণ না করে ইসলাম গ্রহণ করলে প্রকৃত মুসলমান হওয়া যাবে না, সে সময় এরকম একটা প্রবল মত অতিমাত্রায় সক্রিয় ছিল। অন্য যে-কোনো সেমিটিক ধর্মের মতো ইসলামেও পরলৌকিক জীবনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সারাজীবন মুসলমান হিসেবে জীবন কাটিয়ে পরকালে বেহেশতে যেয়েও ভাষাজ্ঞানের অভাবে একঘরে জীবন কাটাতে হবে এটা ধর্মপ্রাণ মুসলমান মত্রেরই সহ্যের অতীত একটা ব্যাপার। তাই মিশর থেকে শুরু করে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের অধিবাসীরা আরবী ভাষা এবং বর্ণমালা দুটিই গ্রহণ করেছিল।
মিশোরে যেভাবে সহজে আরবী ভাষা জনগণের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পেরেছে, ইরানে তেমনটি হতে পারেনি। কারণ ইরানীরা ছিলেন অতিমাত্রায় ঐতিহ্য-সচেতন এবং সংস্কৃতিগত-প্রাণ জাতি। তাঁদের মহীয়ান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে এ যুক্তি উদ্ধার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি যে আরবী ভাষা না আয়ত্ব করেও প্রকৃত মুসলমান হওয়া যায়। কোরানের প্রকৃত শিক্ষা তাঁদের নিজস্ব ভাষায় বিকশিত করে তোলার মতো ভাষাগত সমৃদ্ধি এবং মনীষা দুই-ই তাঁদের ছিল। আরবী ভাষাকে গ্রহণ-বর্জন প্রশ্নে ইরানী সমাজ যে একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল, কবি ফেরদৌসী, দার্শনিক ইমাম গাজ্জ্বালী প্রমুখ তা গ্রহণ করেছিলেন। ইরানীরা আরবী ভাষা গ্রহণ করেননি, কিন্তু আরবী বর্ণমালা তাঁদের মেনে নিতে হয়েছে। তারপর ইরান থেকে শুরু করে আফগানিস্তান পেরিয়ে ভারতবর্ষ অবধি মুসলিম শক্তির যে জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে তার পেছন পেছন ফার্সী ভাষাও ভারতে প্রবেশ করেছে। এমনকি মোগল বিজেতারা তাঁদের মাতৃভাষা তুর্কীর পরিবর্তে ফার্সীকেই সরকারী ভাষা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। মিশরে আরবী যেমন, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশে ফার্সী যেমন চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, ভারতবর্ষে সেভাবে অনেকদিন রাজভাষা থাকার পরও ফার্সীকে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতের হিন্দুরা বড় আশ্চর্য জাত; তাঁরা দরবারে চাকরী করার জন্য উত্তমরূপে ফার্সীভাষা শিক্ষা করেছেন, ‘দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো’ উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু নিজেদের ভাষা বাদ দিয়ে কখনো ঐ ভাষাটিকে গ্রহণ করেননি। সুতরাং ভারতে ফার্সী ছিল জনগণের দৈনন্দিনতার স্পর্শলেশবর্জিত দরবারবিহারী একটি অভিজাত শ্রেণীর ভাষা। স্থানীয় মুসলিম জনগণের মধ্যেও তার বিশেষ প্রসার ঘটেনি। স্বাতন্ত্র্যগর্বী মুসলমানেরা নিজেদের প্রয়োজনে ফার্সী বর্ণমালাকে গ্রহণ করে ভারতীয় ভাষাসমূহের সমন্বয়ে উর্দু নামে একটা পাঁচমিশালী ভাষা তৈরি করেছেন। ইউরোপীয় পন্ডিতেরা যেমন রেনেসাঁর যুগে জাতীয় ভাষাসমূহের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের পূর্বে ল্যাটিন ভাষাতে সন্দর্ভ ইত্যাদি রচনা করতেন, তেমনি মুসলমান ধর্মবেত্তারা ধর্মগ্রন্থসমূহের টীকা-টিপ্পনী ফার্সী ভাষাতেই রচনা করতেন। সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের পর উর্দু ভাষাতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং ঐ ভাষাতেই ধর্মীয় সন্দর্ভসমূহ লেখা হতে থাকে।
বাঙালী মুসলমানের চোখে ফার্সী এবং উর্দু দুটো আরবীর মতোই পবিত্র ছিল। আর এ দুটো রাজভাষা এবং শাসক নেতৃশ্রেণীর ভাষা হওয়ায়, তাদের শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই আনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এ দুটির একটিকেও পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করার জন্য একটি সমাজের পেছনে যে শক্ত আর্থিক ভিত্তি এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ থাকা প্রয়োজন ছিল দুটির কোনোটিই তাঁদের ছিল না। কলকাতার পার্ক স্ট্রীট এলাকার এ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা যে ধরণের ইংরেজি বলেন কিংবা ঢাকার কুট্টি অধিবাসীরা যে উর্দু বলেন ততটুকু ভাষাজ্ঞান অর্জন করাও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেননা এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ইংরেজ এবং ইংরেজি ভাষার আর ঢাকার কুট্টিদের সঙ্গে উর্দু এবং নবাবদের সামাজিক মেলামেশার যে সুযোগ ছিল, বাঙলার আপামর জনগণের সঙ্গে উর্দু-ফার্সী জানা শাসক নেতৃশ্রেণীর ততটুকুও সামাজিক মেলামেশার সুযোগ ছিল না। কিন্তু বাঙালী মুসলমানেরা নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে আরবী, ফার্সী এবং উর্দু এই তিনটা ভাষার তালিম গ্রহণ করার প্রাণান্তকর প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষাটাও যখন তাঁদের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে রপ্ত করা অসম্ভব মনে হয়েছে তখন ঐ বর্ণমালাতে বাংলা লেখার চেষ্টা করেছেন। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে নেয়ার আছে, কোনো ব্যক্তি বিশেষ একটা ভাষা রপ্ত করতে পারেন, কিন্তু সেটা সামাজিকভাবে রপ্ত করা বলা চলে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও আরবী হরফে বাংলা পুঁথিপত্র যে লেখা হয়েছে সেটাকে ক’জন অবসরভোগী পুঁথিলেখকের নিছক খেয়াল মনে করলে ভুল করা হবে। আসলে তা ছিল বেহেশতের ভাষার প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। যখন দেখা গেল আরবী হরফে বাংলা লিখেও সমাজে চালু করা যায় না তখন পুঁথিলেখকেরা সবান্ধবে পরবর্তী পন্থাটা অনুসরণ করতে থাকলেন। বাংলা ভাষার সঙ্গে এন্তার আরবী-ফার্সী শব্দ মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। জনগণ তাঁদের এই ভাষাটিকে গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু কোন্ জনগণ? এঁরা ছিলেন সেই জনগণ, সংস্কৃত ভাষা যাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, আরবী অজানা, ফার্সীর নাম শুনেছেন এবং উর্দু ভাষা কানে শুনেছেন মাত্র।
সুযোগ পেলে তাঁরা আরবীতে লিখতেন, নইলে ফার্সীতে, নিদেন পক্ষে উর্দুতে। কিন্তু যখন দেখা গেল এর একটাও সামাজিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয় তখন বাধ্য হয়েই বাংলা লিখতে এসেছেন। কেউ কেউ সন্দ্বীপের আবদুল হাকিমের সেই ‘যেসব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সেসব কাহার জন্ম নির্ণএ ন জানি’ পংক্তিগুলো আউড়ে বলে থাকেন যে নিজেদের ভাষার প্রতি পুঁথিলেখকদের অপরিসীম দরদ ছিল। কথাটা সম্পূর্ন সত্য নয়। আবদুল হাকিমের এই উক্তির মধ্যে একটা প্রচন্ড ক্ষোভ এবং মর্মবেদনা লক্ষ্য করা যায়। নিশ্চয়ই সে সময়ে এমন লোক ছিলেন যাঁরা সত্যি সত্যি বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করতেন। আবদুল হাকিম নিজে সে শ্রেণীভুক্ত নন, তাই সে উঁচু ভাষাতে তাঁর অধিকারও নেই। তাই তিনি তাঁর একমাত্র আদি এবং অকৃত্রিম ভাষাতেই লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।
দূর অতীতের কথা বলে লাভ নেই। ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফও মুসলমান সমাজের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে উর্দু ভাষার সুপারিশ করেছিলেন। আবুল কাশেম ফজলুল হক যিনি ছিলেন বাংলার প্রথম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, রাজনীতিবিদ, তিনিও বাড়িতে উর্দু ভাষায় কথাবার্তা বলতেন। ঢাকার কুট্টি অধিবাসীদের অনেকেই অনেকদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করেছেন। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে একটি সত্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে, তা হলো বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশেরই মধ্যে আরবী, ফার্সী, উর্দু ইত্যাদি ভাষার প্রতি একটা অন্ধ অনুরাগ অনেক দিন পর্যন্ত বিরাজমান ছিল।
৬
পলাশীর যুদ্ধের পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অনুসৃত নীতির ফলে যে উঁচুকোটির মুসলিম শাসক নেতৃশ্রেনীটি ছিল তার অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে পড়ে। ভাষাগত দিক দিয়ে তাঁরা বাঙালী মুসলমান জনগণের সঙ্গে কোনরকমে সম্পর্কিত ছিলেন না। এ দেশে অনেকটা বিদেশীর মতোই অবস্থান করতেন। সরকারী চাকুরীই ছিল তাঁদের এই দেশে অবস্থান করার মুখ্য অবলম্বন। নবাবী আমলের অবসানের পর যখন ইংরেজ শাসন কায়েম হলো তাঁরা না পারলেন ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, না পারলেন নিজেদের ধর্মীয় জনগণের নেতৃত্বদান করতে। রক্তগত, ভাষাগত, রুচি, সংস্কৃতি এবং আচরণগত ব্যবধানের দরুণ আপদকালে সমাজের নেতৃশ্রেণীর পালনীয় যে ভূমিকা রয়েছে, বাঙলা দেশে অবস্থানকারী অভিজাত মুসলিম শ্রেণীটির তা পালন করার কথা একবারও মনে আসেনি।
কিন্তু উত্তর ভারতে হয়েছে সম্পূর্ন উল্টো। সেখানেও মুসলিম নেতৃশ্রেণীটি মোগল শাসনের অবসানের পরে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন। অত্যল্পকাল গত না হতেই স্যার সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে তাঁরা নতুন ব্যবস্থাকে মেনে নেয়ার জন্য এবং নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য মনন এবং মানসিকতার পরিবর্তনে লেগে যান। তার ফলশ্রুতি আলীগড় কলেজ। এই কলেজের সবচেয়ে প্রনিধানযোগ্য যে অবদান তা হলো মুসলিম নেতৃশ্রেণীকে পুঞ্জীভূত হতাশা থেকে উদ্ধার করে ব্রিটিশমুখী করা। ব্রিটিশ শাসকদেরও সিপাহী যুদ্ধের সংশয়-সন্দেহের কুজ্ঝটিকা সরিয়ে মুসলিমমুখী করে তোলার ব্যাপারে, ব্যক্তিগতভাবে স্যার সৈয়দ আহমদ নিজে, তাঁর বন্ধু এবং অনুরাগীবর্গ ও প্রতিষ্ঠিত আলীগড় কলেজ বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। তাই সেখানে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের চাইতে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছিলেন। আসলে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে সুযোগ নেয়ার পদ্ধতিটা ভালোভাবে শিখিয়েছিলেন। তার চিন্তা সারা ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এত বেশি শেকড় বিস্তার করেছিল যে আলীগড়-শিক্ষিত মুসলমানেরা কদাচিৎ সুযোগসন্ধানী নীতি পরিহার করতে পেরেছিল; কেননা জনগণ এবং অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, রুচি ও আচারগত শ্রেণীদূরত্ব ছাড়া অন্য কোনো দুরত্ব ছিল না। কিন্তু বাঙলা দেশে ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ন ভিন্নরকম। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত শ্রেণী একেবারে তলিয়ে গেল। কিন্তু তাঁদের আচার-আচরণ, সামাজিক আদর্শ অটুট থেকে গেল। হিন্দু সমাজের প্রতিযোগিতা এড়িয়ে ব্রিটিশ শাসকদের কৃপাকণা সম্বল করে যে সকল মুসলমান ওপরের দিকে উঠে আসতেন, মৃত মুসলিম অভিজাতদের আদর্শকেই তাঁদের নিজেদের আদর্শ বলে বরণ করে নিতেন। এঁরা আবার অনেক সময় আপন মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার জন্য স্যার সৈয়দ আহমদ যা করেছেন বাঙলা দেশের মুসলমানদের জন্য একই কাজ করা উচিত মনে করতেন।
প্রায়শ হালের একগুঁয়ে ইতিহাস-ব্যাখ্যাকারকদের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা বলে থাকেন, ব্রিটিশ শাসনের আমলে বাঙলার মুসলমান সমাজ অধঃপতনের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এটা পুরো সত্য তো নয়ই, সিকি পরিমাণ সত্যও এর মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। সত্য বটে, মুসলিম শাসনের অবসানের পর শাসক নেতৃশ্রেণীটির দুর্দশার অন্ত ছিল না। কিন্তু তাদের সঙ্গে সাধারণ বাঙালী মুসলমান জনগণের একমাত্র ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো যোগসূত্র ছিল কি? আর মুসলমান জনগণের অবস্থা ইংরেজ শাসনের পূর্বে অধিকতর ভালো ছিল কি? নবাবী আমলেও এ দেশীয় ফার্সী জানা যা সকল কর্মচারী নিয়োগ করা হত, তাঁদের মধ্যে স্থানীয় হিন্দু কত জন ছিলেন এবং কত জন ছিলেন স্থানীয় মুসলমান, এ সকল বিষয় বিচার করে দেখেন না বলেই অতি সহজে অপবাদের বোঝাটি ইংরেজদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা দায়িত্বমুক্ত মনে করেন।
উত্তর ভারতেও মুসলিম শাসক নেতৃশ্রেণী একইভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিলেন, অধিকন্তু তাঁদের অনেকেই সিপাহী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার পরেও তাঁরা কী করে এগিয়ে আসতে পারেন এবং তাঁদের মধ্যে কেন সৃষ্টি হলো স্যার সৈয়দ আহমদের মতো একজন মানুষ? বাঙলা দেশের মুসলমানদের মধ্যে তেমন একজন মানুষ জন্মালেন না কেন? এই সকল বিষয়ের সদুত্তর সন্ধান করলেই বাঙালী মুসলমানের যে মৌলিক সমস্যা তার মূলে যাওয়া যাবে।
বাঙালী মুসলমান কারা? এক কথায় এর উত্তর বোধ করি এভাবে দেয়া যায় : যারা বাঙালী এবং একই সঙ্গে মুসলমান – তাঁরাই বাঙালী মুসলমান। এঁদের ছাড়াও সুদূর অতীত থেকেই এই বাঙলা দেশের অধিবাসী অনেক মুসলমান ছিলেন – যাঁরা ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক এবং নৃতাত্ত্বিক ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যানুসারে ঠিক বাঙালী ছিলেন না। আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগুলো তাঁদের হাতে ছিল বলেই বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে কৃষ্টি-সংস্কৃতিগত ভেদরেখাসমূহ অনেকদিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই প্রভুত্বশীল অংশের রুচি, জীবনদৃষ্টি, মনন এবং চিন্তন-পদ্ধতি অনেকদিন পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানের যে ক্ষুদ্রতম অংশ কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে গলে যখন সামাজিক প্রভুত্ব এবং প্রতাপের অধিকারী হতেন, তখনই বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক চুকে যেত এবং উঁচু শ্রেণীর অভ্যাস, রুচি, জীবনদৃষ্টির এমনকি ভ্রমাত্মক প্রবণতাসমূহও কর্ষনে-ঘর্ষণে নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্গীভূত করে নিতেন।
মূলত বাঙালী মুসলমানেরা ইতিহাসের আদি থেকেই নির্যাতিত একটি মানবগোষ্ঠী। এই অঞ্চলে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার পরে সেই যে বর্ণাশ্রম প্রথা প্রবর্তিত হলো, এঁদের হতে হয়েছিল তার অসহায় শিকার। যদিও তাঁরা ছিলেন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, তথাপি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের প্রশ্নে তাঁদের কোনো মতামত বক্তব্য ছিল না। একটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাঙলা মৃত্তিকার সাক্ষাৎ সন্তানদের এই সামাজিক অনুশাসন মেনে নিতে হয়েছিল। যেমন কল্পনা করা হয়, অত সহজে এই বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হতে পারেনি। বাঙলার আদিম কৌম সমাজের মানুষেরা যে সর্বপ্রকারে ওই বিদেশী উন্নততর শক্তিকে বাধা দিয়েছিল – ছড়াতে, খেলার বোলে অজস্র প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষদের বাগে আনতে অহংপুষ্ট আর্য শক্তিকেও যে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার তাঁর বিশ্ববিশ্রুত ‘ভারতের ধর্মসমূহ’ গ্রন্থে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। আর্য অথবা ব্রাহ্মণ্য শক্তি যে সকল জনগোষ্ঠীকে পদদলিত করে এদেশে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতহয়েছে, তাঁদেরকে একেবারে চিরতরে জন্ম-জন্মান্তরের দাস চিহ্নিত করেছে। আর যে সকল শক্তি ওই আর্য শক্তিকে পরাস্ত করে ভারতে শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, তাঁদের সকলকেই মর্যাদার আসন দিতে কোনো প্রকারের দ্বিধা বা কুন্ঠা বোধ করেনি। শক, হুন, মোগল, পাঠান, ইংরেজ যাঁরাই এসেছেন এদেশে তাঁদের সহায়তা করতে পেছপা হয়নি। কিন্তু নিজেরা বাহুবলে যাঁদের পরাজিত করেছিল, তাঁরাও যে মানুষ একথা স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা খুব অল্পই অনুভব করেছে। তবু ভারতবর্ষে এমনকি এই বাঙলা দেশেও যে, কোনো কোনো নীচু শ্রেণীর লোক নানা বৃত্তি এবং পেশাকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে ওপরের শ্রেণীতে উঠে আসতে পেরেছেন তা অন্যত্র আলোচনার বিষয়।
বাঙলা দেশের এই পরাজিত জনগোষ্ঠী যাঁদেরকে রাজশক্তি পাশবিক শক্তির সাহায্যে অন্ত্যজ করে রেখেছিল, তাঁদেরই সকলে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে সে প্রাথমিক পরাজয়ের কথঞ্চিত প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল। শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের ফলে প্রাচীন আর্যধর্মের নবজীবন প্রাপ্তির পর বৌদ্ধদের এদেশে ধনপ্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা যখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, তার অব্যবহিত পরেই এ দেশে মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত বৌদ্ধরা দলে-দলে ইসলাম ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথাই এদেশের সাম্প্রদায়িকতার আদিতম উৎস। কেউ কেউ অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই সাম্প্রদায়িকতার জনয়িতা মনে করেন। তাঁরা ভারতীয় ইতিহাসের অতীতকে শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনের দুশো বছরের মধ্যে সীমিত রাখেন বলেই এই ভুলটা করে থাকেন।
৭
বাঙালী মুসলমানেরা শুরু থেকেই আর্থিক-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দুর্দশার হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই ক্রমাগত ধর্ম পরিবর্তন করে আসছিলেন। কিন্তু ধর্ম পরিবর্তনের কারণে তাঁদের মধ্যে একটা সামাজিক প্রভুত্ব অর্জনের উন্মেষ হলেও জাগতিক দুর্দশার অবসান ঘটেনি। বাঙলা নতুন নতুন রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ধর্মালম্বীর সংখ্যা আশাতীত হারে বৃদ্ধিলাভ করেছে। যেহেতু মৌলিক উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে কোনো পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটেনি, তাই রাজশক্তিকেও পুরনো সমাজ-সংগঠনকে মেনে নিতে হয়েছে। সে জন্যেই মুসলিম শাসনামলেও বাঙালী মুসলমানেরা রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নিগৃহীত ছিলেন। ইংরেজ আমলে উঁচু শ্রেণীর মুসলমানরা সম্পূর্নভাবে সামাজিক নেতৃত্বের আসন থেকে বিতাড়িত হলে উঁচু বর্ণের হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই সে আসন পূরণ করেন।
বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশই বাংলার আদিম কৃষিভিত্তিক কৌম সমাজের লোক। তাঁদের মানসিকতার মধ্যে আদিম সমাজের চিন্তন পদ্ধতির লক্ষণসমূহ সুপ্রকট। বারবার ধর্ম পরিবর্তন করার পরেও বাইরের দিক ছাড়া তাঁদের বিশ্বাস এবং মানসিকতার মৌলবস্তুর মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। দিনের পর দিন গিয়েছে, নতুন ভাবাদর্শ এদেশে তরঙ্গ তুলেছে, নতুন রাজশক্তি এদেশে নতুন শাসনপদ্ধতি চালু করেছে, কিন্তু তাঁরা মনের দিক দিয়ে অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের মতোই বারবার বিচ্ছিন্ন থেকে গিয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই ছিলেন বাঙালী মুসলমান এবং মুসলমান রাজত্বের সময়ে তাঁদেরই মানসে যে একটি বলবন্ত সামাজিক আকাঙ্খা জাগ্রত হয়েছিল তাঁদেরই রচিত পুঁথিসাহিত্যসমূহের মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। কাব্যসাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার অনুসারে হয়তো এ সকল পুঁথির বিশেষ মূল্য নেই, কিন্তু বাঙালী মুসলমান সমাজের নৃতাত্ত্বিক এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় এসবের মূল্য যে অপরিসীম সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।
ইতালীয় দার্শনিক বেনেদিত্তো ক্রোচের মতে প্রতিটি জাতির এমন কতিপয় সামাজিক আবেগ আছে যার মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্যাসের আকারে পুরোমাত্রায় বিরাজমান থাকে। রাজনৈতিক পরাধীনতার সময় সে আবেগ সাপের মতো কুন্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে থাকে এবং কোনো রাজনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলে সে আবেগই ফণা মেলে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। সাহিত্যেই প্রথমে এই জাতিগত আকাঙ্খার রূপায়ণ ঘটতে থাকে। জাতিগত আকাঙ্খার সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে কোনো মহৎ সাহিত্য যে সৃষ্টি হতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য।
পুঁথিসাহিত্যের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই, বাঙালী আদিম কৃষিভিত্তিক কৌম-সমাজের মনটি রাজশক্তির আনুকূল্য অনুভব করে হুঙ্কার দিয়ে ফণা মেলে জেগে উঠেছে। কিন্তু ঐ জেগে ওঠাই সার, সে মন কোনো পরিণতির দিকে ধাবিত হতে পারেনি। প্রতিবন্ধকতাসমূহ সামাজিক সংগঠনের মতোই বিরাজমান ছিল। সমাজ-সংগঠন ভেঙ্গে ফেলে নবরূপায়ণ তাঁরা ঘটাতে পারেননি। কারণ মুসলিম শাসকেরাও স্থানীয় জনগণের মধ্যে থেকে যে নেতৃশ্রেণী সংগ্রহ করেছিল, তাদের মধ্যে বাঙালী মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব একেবারে ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে ভাষাগত, সংস্কৃতিগত, রুচি এবং আচারগত দুরত্বের দরুণ শাসকশ্রেণীর অভ্যাস, মনন রপ্ত করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বাঙালী মুসলমান।
ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পরে এই দেশে হিন্দুসমাজের ভেতর থেকে যে একটি মধ্যবিত্ত নেতৃশ্রেণী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তার মধ্যে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব না থাকার কারণ হিসেবে শুধুমাত্র ব্রিটিশের ‘ডিভাইড এ্যান্ড রুল পলিসি’ কিংবা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজের অন্ধবিদ্বেষকে ধরে নিলে মুসলিম সমাজের তুলনামূলক পেছনে পড়ে থাকার কারণসমূহের সঠিক ব্যাখ্যা করা হবে না।
৮
ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের উত্থান যুগে ইউরোপীয় ভাবধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং নানা আধুনিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক চিন্তারাশি বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের একাংশের মধ্যে যে তরঙ্গ তুলেছিল, তা মুসলমান সমাজকে স্পর্শও করতে পারেনি। আধুনিক যুগের দাবীর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে যে সকল ধর্মীয় এবং সামাজিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক মূল্যচেতনার নেতৃত্ব হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী দান করেছিল, মুসলমান সমাজে তা একেবারে প্রসার লাভ করেনি। জগত এবং জীবনের যে সকল অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্ন নবযুগের আলোকে তাঁরা ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন, মুসলমান সমাজ তার কিছুই গ্রহণ করেনি। সে সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখ যে সকল মুসলিম চিন্তানায়ক মুসলমানদের হয়ে কথা বলছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন, মুসলমান সমাজের প্রকৃত দাবী কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে যথার্থ বোধ তাঁদেরও ছিল না। তাঁরাও নিচুতলার মুসলমান অর্থ্যাৎ বাঙালী মুসলমান সম্বন্ধে চিন্তা করার কোনো অবকাশই পাননি। শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সংস্কার বলতে তাঁদের মনে প্রভুত্ব হারান উঁচু কোটির মুসলমানদের কথাই জাগরুক ছিল।
স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করে যে অধিকারচেতনা অপেক্ষাকৃত পরে জাগ্রত হয়, আসলে তা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু মধ্যবিত্তের আন্দোলন ও অগ্রগতির সম্প্রসারণ মাত্র। তাঁদেরকে তা করতে গিয়ে দু’ধরণের বাধার সম্মুখীন হতে হয়। লেখাপড়া, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থ-স্বার্থের দিক দিয়ে অনেকদুর অগ্রসর হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাঁদের প্রতিদ্বন্দিতা করতে হত এবং অন্যদিকে উঁচু তলার মুসলমানদের মূল্যচেতনা এবং জীবনদৃষ্টিকে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। এ দু-মুখী প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করতে হলে যে শক্ত সামাজিক ভিত্তিভূমির প্রয়োজন ছিল, তাঁদের পেছনে তা ছিল না। তাই বাঙালী মুসলমানদের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে তাঁরা নিজেদের সংযুক্ত করতেন। স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলন থেকে শুরু করে জামালুদ্দীন আফগানীর ‘প্যান ইসলামিজম’ পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে আসা সমস্ত আন্দোলন-প্রবর্তনার সঙ্গে নিজেদের অংশীদার করে নিতেন। কিন্তু স্যার সৈয়দের আলীগড় আন্দোলন একান্তভাবে উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের সংখ্যালঘিষ্ট মুসলমান সামন্তশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। আবার এই সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে জনগণের শ্রেণীগত তফাত ছাড়া ভাষা-সাংস্কৃতিক পার্থক্য যে ছিল না একথা বিংশ শতাব্দীতেও ইংরেজী-শিক্ষিত মুসলমানেরা খুব কমই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁরা বাঙালী মুসলমানের মধ্যে অনুরূপ সমাজচেতনা এবং মূল্যবোধ সঞ্চারের চেষ্টা করতেন। কিন্তু তা বাঙালী জনগণের সঙ্গে এতটা সম্পর্ক বিরহিত ছিল যে ভাবাদর্শিক কোনো জাগরণ আনতেই পারেনি। ধর্মীয় বদ্ধমত এবং সংস্কারকে আঘাত করে এমন কোনো সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন মুসলমান সমাজের ভেতর থেকে জেগে উঠতে পারেনি। মুসলমানদের দ্বারা সংগঠিত প্রায় সমস্ত সামাজিক কর্মকান্ড এই ধর্মীয় পুনর্জাগরণভিত্তিক।
হিন্দু সমাজে যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণমূলক আন্দোলন হয়নি একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু তাঁদের মধ্যে অন্তত কিছুসংখ্যক মানুষ মৌলিক চিন্তা করেছিলেন, এবং সামাজিক অনেকগুলো বদ্ধমতকে শাণিত আক্রমণ করেছিলেন; বাস্তবে না হলেও তত্ত্বগত দিক দিয়ে বেশ কিছুদূর যুক্তিবাদিতার চর্চা তাঁদের মধ্যে হয়েছে। তাঁদের কৃত আন্দোলনসমূহ যে সমুদ্র তরঙ্গের শীর্ষে ফসফরাসের মতো জ্বলেছে, সমাজে গভীরে প্রবিষ্ট হতে পারেনি, তার নিশ্চয়ই কারণ রয়েছে। কিন্তু মুসলমান সমাজে যুক্তিবাদিতার চাষ একেবারে হয়নি। মৌলিক চিন্তা-ভাবনা করেছেন, এমন মানুষ মুসলমান সমাজে খুব বেশি জন্মাতে পারেনি। নতুন যুগের আলোকে জগত এবং জীবনকে ব্যাখ্যা করে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন এমন মানুষ সত্যিই বিরল। মুসলমান সমাজে যে কোনো মনীষী জন্মাতে পারেননি তার কারণ সামাজিক লক্ষ্যের দ্বি কিংবা ত্রি-মুখীনতা। সামাজিক এবং ধর্মীয় সংগঠনসমূহের মধ্যেই বিভিন্নমুখী লক্ষ্যের কারণসমূহ সংগুপ্ত ছিল।
৯
বাঙালী মুসলমান বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা মাত্র দুটি আন্দোলনে সাড়া দিয়েছিলেন এবং অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার একটি তিতুমীরের অনুসারীদের দ্বারা পরিচালিত ওহাবী আন্দোলন। অন্যটি হাজী দুদু মিয়ার ফরায়েজী আন্দোলন। এই দুটি আন্দোলনেই বাঙালী মুসলমানেরা মনেপ্রাণে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু উঁচু শ্রেণীর মুসলমানেরা এই আন্দোলন সমর্থন করেছেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসলেও কৃষক জনগণই ছিলেন এই আন্দোলন দুটির হোতা। আধুনিক কোনো রাষ্ট্র কিংবা সমাজদর্শন এই আন্দোলন দুটিকে চালনা করেনি। ধর্মই ছিল একমাত্র চালিকা শক্তি। সে সময়ে বাঙলা দেশে আধুনিক রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্পর্কিত বোধের উন্মেষ ঘটেনি বললেই চলে। সমাজের নীচুতলার কৃষক জনগণকে সংগঠিত করার জন্য ধর্মই ছিল একমাত্র কার্যকর শক্তি। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই আন্দোলন দুটির ভূমিকা প্রগতিশীল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে পশ্চাদগামী ছিল, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।
এই আন্দোলন দুটি ছাড়া, অন্য প্রায় সমস্ত আন্দোলন হয়তো ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, কিংবা হিন্দু সমাজের উদ্যোগ এবং কর্মপ্রয়াসের সম্প্রসারণ হিসেবে মুসলমান সমাজে ব্যাপ্তিলাভ করেছে। সমাজের মৌল ধারাটিকে কোনো কিছুই প্রভাবিত করেনি। তার ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজের মনটিতে একটু রংটং লাগলেও কোনো রূপান্তর বা পরিবর্তন হয়নি। মধ্যিখানে কয়েকটি শতাব্দীর পরিবর্তন কোনো ভাবান্তর আনতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীতেও এই মনের বিশেষ হেরফের ঘটেনি। বাঙালী মুসলমানের রচিত কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান পর্যালোচনা করলেই এ সত্যটি ধরা পড়বে। কোনো বিষয়েই তাঁরা উল্লেখ্য কোনো মৌলিক অবদান রাখতে পারেননি। সত্য বটে, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দীন প্রমুখ কবি কাব্যের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। একটু তলিয়ে দেখলেই ধরা পড়বে, উভয়েরই রচনায় চিন্তার চাইতে আবেগের অংশ অধিক। তাছাড়া এই দুই কবির প্রথম পৃষ্ঠপোষক ও গুণগ্রাহী ছিল হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ নয়।
মুসলমান সাহিত্যকদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো হয়তো চর্বিতচর্বণ, নয়তো ধর্মীয় পুনর্জাগরণ। এর বাইরে চিন্তা, যুক্তি এবং মনীষার সাহায্যে সামাজিক ডগ্মা বা বদ্ধতাসমূহের অসারতা প্রমাণ করেছেন তেমন লেখক-কবি মুসলমান সমাজে আসেননি। বাঙালী মুসলমান সমাজ স্বাধীন চিন্তাকেই সবচেয়ে ভয় করে। তার মনের আদিম সংস্কারগুলো কাটেনি। সে কিছুই গ্রহণ করে না মনের গভীরে। ভাসাভাসা ভাবে আনেককিছুই জানার ভান করে আসলে তার জানাশোনার পরিধি খুবই সঙ্কুচিত। বাঙালী মুসলমানের মন এখনো একেবারে অপরিণত, সবচেয়ে মজার কথা এ-কথাটা ভুলে থাকার জন্যই সে প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে কসুর করে না। যেহেতু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রসারমান যান্ত্রিক কৃৎকৌশল স্বাভাবিকভাবে বিকাশলাভ করছে এবং তার একাংশ সুফলগুলোও ভোগ করছে, ফলে তার অবস্থা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এঁচড়েপাকা শিশুর মতো। অনেক কিছুরই সে সংবাদ জানে, কিন্তু কোন কিছুকেই চিন্তা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, মনীষা দিয়ে আপনার করতে জানে না। যখনই কোনো ব্যবস্থার মধ্যে কোনরকম অসংগতি দেখা দেয়, গোঁজামিল দিয়েই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় এবং এই গোঁজামিল দিতে পারাটাকেই রীতিমতো প্রতিভাবানের কর্ম বলে মনে করে। শিশুর মতো যা কিছু হাতের কাছে, চোখের সামনে আসে, তাই নিয়েই সে সন্তুষ্ট। দূরদর্শিতা তার একেবারেই নেই, কেননা একমাত্র চিন্তাশীল মনই আগামীকাল কী ঘটবে সে বিষয়ে চিন্তা করতে জানে। বাঙালী মুসলমান বিমূর্তভাবে চিন্তা করতেই জানে না এবং জানে না এই কথাটি ঢেকে রাখার যাবতীয় প্রয়াসকে তার কৃষ্টি-কালচার বলে পরিচিত করতে কুন্ঠিত হয় না।
বাঙালী মুসলমানের সামাজিক কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক সৃষ্টি, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিসমূহের প্রতি চোখ বুলোলেই তা প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সাবালক মন থেকেই উন্নত স্তরের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের উদ্ভব এবং বিকাশ সম্ভব। এই সকল ক্ষেত্রে তার সাবালকত্বের কোনো পরিচয় রাখতে পারেনি। যে জাতি উন্নত বিজ্ঞান, দর্শন এবং সংস্কৃতির স্রষ্টা হতে পারে না, অথবা সেগুলোকে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না, তাকে দিয়ে উন্নত রাষ্ট্র সৃষ্টিও সম্ভব নয়। যে নিজের বিষয় নিজে চিন্তা করতে জানে না, নিজের ভালোমন্দ নিরূপণ করতে অক্ষম, অপরের পরামর্শ এবং শোনা কথায় যার সমস্ত কাজ-কারবার চলে, তাকে খোলা থেকে আগুনে কিংবা আগুন থেকে খোলায়, এইভাবে পর্যায়ক্রমে লাফ দিতেই হয়। সুবিধার কথা হলো নিজের পঙ্গুত্বের জন্য সব সময়েই দায়ী করবার মতো কাউকে না কাউকে পেয়ে যায়। কিন্তু নিজের আসল দুর্বলতার উৎসটির দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করে না।
বাঙালী মুসলমানের মন যে এখনো আদিম অবস্থায়, তা বাঙালী হওয়ার জন্যও নয় এবং মুসলমান হওয়ার জন্যও নয়। সুদীর্ঘকালব্যাপী একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতির দরুণ তার মনের ওপর একটি গাঢ় মায়াজাল বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, সজ্ঞানে তার বাইরে সে আসতে পারে না। তাই এক পা যদি এগিয়ে আসে, তিন পা পিছিয়ে যেতে হয়। মানসিক ভীতিই এই সমাজকে চালিয়ে থাকে। দু’বছরে কিংবা চার বছরে হয়তো এ অবস্থার অবসান ঘটানো যাবে না, কিন্তু বাঙালী মুসলমামের মনের ধরণ-ধারণ এবং প্রবণতাগুলো নির্মোহভাবে জানার চেষ্টা করলে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা পথ হয়তো পাওয়াও যেতে পারে।
by Jahid | Nov 25, 2020 | দর্শন, শিল্প ও সংস্কৃতি
সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ:
[কয়েক লাইন লিখে রেখেছিলাম। করোনা ভাইরাস আর মহামারী নিয়ে এতো হুলুস্থুল শুরু হলো ; সময় করে বসতে পারছিলাম না। ভাবলাম, বাকী লেখাটুকু না হয় আমিও তাড়াহুড়ো করে লিখে শেষ করি ; নইলে শেষ আর হবে না ! লেখা বড় হয়ে গেছে। ]
নিজের যাপিত জীবনের কথা, আমাদের প্রজন্মের উদ্দীপনার , মোটিভেশনের, হতাশার ও আশাবাদের কথা বলে যাই। আজকের প্রজন্মকে মোটিভেট করে চলেছে কিছু আধুনিক মোটিভেশনাল স্পিকার। কারো কারো কথা শোনার সুযোগ হয়েছে। তবে, অধুনা মোটিভেটরদের মোটা দাগে দুইভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণির মোটিভেটর আছেন যাঁদের কথা শুনে শ্রোতা ভাবে সব মানুষেরই অসীম শক্তি আছে শুধু দরকার সামান্য একটু আত্মবিশ্বাস, সেটা হলেই পৃথিবী উল্টে দেওয়া যাবে। এসব শুনেটুনে শ্রোতাদের সাময়িক উত্তেজনা বাড়ে। কিন্তু যতো দ্রুত উত্তেজনা বাড়ে ; ঘণ্টাখানেক পরে তার চেয়েও দ্রুত সেই উত্তেজনা প্রশমিত হয়। আরেক শ্রেণি আছে, মানুষকে উজ্জীবিত করতে গিয়ে এতো বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে পড়েন– ওঠো, জাগো , ঝাঁপিয়ে পড়ো বলার চোটে শ্রোতা উজ্জীবিত হবে কী , উল্টো হীনম্মন্যতায় ভোগা শুরু করে। টেড-এক্স নামে ইউটিউবে একটা চ্যানেল আছে, নানা শ্রেণির , নানা দেশের অভিজ্ঞরা তাঁদের জীবনের সবচেয়ে উদ্দীপনার কথাগুলো । কিছু দেখেছি, ভালো লেগেছে। এই যুগে মোটিভেশন চাইলেই হাতের কাছে পাওয়া যায়। আমাদের সময়টা তেমন ছিল না।
আমাদের ছিল ‘ আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ’ টাইপের অসহনীয় ব্যাকুলতা।
বাবা-মার সঙ্গে সম্মানসূচক দূরত্ব। ঘরে বাইরে আত্মীয় মুরব্বীদের চোখ রাঙানি। সামাজিক ও পারিবারিক চাপ, জীবনে উপার্জনক্ষম হতে হবে। সেইটাই মোক্ষ। তাঁদের প্রজন্মের দুর্বিষহ অনিশ্চয়তা আমাদের মধ্যে সংক্রমিত করা ছিল অবধারিত। আমরা রেডিও টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখতাম ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী। আজ দেখছি, সত্যি ছোট হয়ে গেছে।
ঢাকা থেকে আশির দশকে নানাবাড়ি গেলে দুতিন গ্রাম দূরে আত্মীয়রাও দেখতে আসত। সেই ঢাকা হয়ে গেল পাশের বাড়ি।
অমুকের ভাই এসেছে বাহরাইন থেকে, চলো দেখে আসি। এখন পাশের বাড়ির কেউ নিউইয়র্ক থেকে আসলেও আমাদের ঔৎসুক্য নেই। ইন্টারনেট সারা দুনিয়াকে হাতের তালুর ছোট্ট স্ক্রিনে এনে দিয়েছে। ধারণা ছিল, এই গতিময়তা মানুষের জীবনকে সহজ করবে।
আমার বন্ধুতালিকায় আমার বয়সী অথবা বেশি বয়সী বন্ধুদের ভিড় বেশি। মোটিভেশন প্রতিটি জেনারেশনে কমবেশি প্রভাব রেখেছে। আমাদের প্রজন্মের মোটিভেশন ছিল বাপের চড়-থাপ্পড় অথবা মায়েদের চেঁচামেচি করে অপমান করা। সাথে ছিল, মহল্লার বড় ভাই-বোনেরা যারা স্কুলে ভালো রেজাল্ট করে।
তো হয়েছে কী, পাশের মহল্লায় ভাইয়াদের ব্যাচে ফার্স্ট বয় ছিল মামুন ভাই, আর ডেঁপো ছিল বিদ্যুৎ ভাই। আমরা সদ্য হাইস্কুলে উঠেছি। টুকটাক খোঁজখবর রাখা শুরু করেছি। যতদূর শুনেছিলাম, বিদ্যুৎ ভাই প্রতি ক্লাসে শেষের দিকে আর মামুন ভাই এক্কেবারে প্রথম। সম্ভবত: এই দুই ক্লাসমেট ভাইয়ের বাবারা একই অফিসে কাজ করতেন। মামুন ভাইয়ের প্রতিটা ভালো রেজাল্টে বিদ্যুৎ ভাইয়ের জীবনে নেমে আসতো ঘূর্ণিঝড় !
একবার শারীরিক প্রহারের সময়, তোর রেজাল্ট এতো খারাপ কেন হয়, মামুন কী খায় যে ও পারে তুই পারস না ! এর উত্তর আসল, মামুনের আব্বা ওকে হরলিক্স কিনে দেয়, আপনি দেন ? এই কথায় বিদ্যুৎ ভাইয়ের বাবা পরের কয়েকবছর তাকে নিয়মিত হরলিক্স খাওয়ালেন। এসএসসির রেজাল্ট দিলে দেখা গেল মামুন ভাই মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছেন আর বিদ্যুৎ ভাই টেনেটুনে পাশ ! বিদ্যুৎ ভাইয়ের আব্বা তাকে আর কীভাবে মোটিভেশন দিয়েছিলেন জানি না। কোনদিন দেখা হলে জিজ্ঞেস করব।
আইনজীবী আব্বার ছিল আইনের পুরনো বই কেনার অভ্যাস। মূলত: বাজারে যে বইয়ের দাম অনেক, সেটা এক লোক সংগ্রহ করে আব্বার কাছে বেশ কম দামে বিক্রি করত। নানারকম আইনের সংকলনের পাশাপাশি সাধারণ উপন্যাস, ফিকশন বা প্রবন্ধের একটা দুটো বই আব্বা কিনতেন। তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। পুরনো বইয়ের ফাঁকে একটা নিউজ প্রিন্ট পেপারব্যাক বই দেখলাম আব্বা আলাদা করে অন্য বইয়ের উপরে রেখে দিয়েছেন। ডেল কার্নেগীর বই, দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন। আব্বার বয়স তখন এখনকার আমার মতো। ৪৪/৪৫ হবে হয়তো। বইয়ের মলাটে । এক মধ্যবয়সী লোকের হাসি হাসি মুখ। আমার তখন বাছুর অবস্থা, সামনে যা আসে তাতেই মুখ দিই। যথারীতি ঐ বইয়েও মুখ দিয়ে বসলাম। কিন্তু আমার তো জীবনে দুশ্চিন্তা নাই, এরশাদের আমল, চারিদিকে সকাল বিকাল সবাই কষে বিশ্ব-বেহায়া লেজেহোমো নিঃসন্তান স্বৈরাচার এরশাদকে গালি দেয়। কেননা এর চেয়ে বেশি কিছু করার ছিল না কারো।
কিন্তু সন্ধ্যা হলেই আমাদের জীবনে নেমে আসত দারুণ একটা সময়।
বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে বিটিভি একমাত্র সহায়। কিন্তু তা হলে কী হবে, সেটা ছিল বিটিভির স্বর্ণযুগ। সেই সময়ের সবচেয়ে আধুনিক হলিউডের ছবিগুলো বিকাল বেলায় দেখাত। পৃথিবীর সবচেয়ে দারুণ জনপ্রিয় সিরিয়ালগুলো দেখাতো।
আর হুমায়ূন আহমদের উত্থানের যুগও ছিল সেটা। এইসব দিনরাত্রি, বহুব্রীহি, ঈদের নাটক আরো কত কী !আফজাল সুবর্ণার যুগ ছিল সেটা।রাত জেগে আনন্দমেলা দেখার সময় ছিল সেটা। বিকালবেলা মহল্লায় খেলার সময় ছিল সেটা।এর পাশাপাশি ছিল সেবা প্রকাশনীর ওয়েস্টার্ন সিরিজ, মাসুদ রানা, তিন গোয়েন্দা, কুয়াশা সিরিজ, দস্যু বনহুর।স্বাদ বদলে নিমাই ভট্ট্রাচার্য, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমাদারদের জনপ্রিয় উপন্যাসগুলো।
তো, সেই ডেল কার্নেগীর বই কিছুটা বুঝে না বুঝেই পড়ে ফেললাম। বোঝা গেল জীবনে হতাশা বলে কিছু একটা আছে এবং সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য নানারকম কার্যকরী পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিৎ।
আমার মোটিভেশনের দরকার হয়ে পড়ল ক্লাস সেভেন বা এইটে উঠে।ক্লাসে ভাল করার একটা চাপ পেয়ে বসল। মূলতঃ মেধার দিক দিয়ে আমি খুব বেশি গাণিতিক নই।আমার বরাবর আগ্রহের বিষয় ছিল বর্ণনামূলক বিষয় গুলো। বানিয়ে বানিয়ে লেখার সৃষ্টিশীলতা আমার বরাবরই ছিল।
গল্পবলার প্রবণতা হয়তো সেখান থেকেই এসেছে।
ক্লাস সেভেনে পরীক্ষার রুটিন গুলিয়ে সাধারণ বিজ্ঞান পড়ে গিয়ে দেখি এসেছে সমাজ বিজ্ঞানের প্রশ্ন। আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে স্যারকে বললাম, স্যার আমার কাছে ভুল কোয়েশ্চেন দিয়েছেন তো , আজকে সাধারণ বিজ্ঞান পরীক্ষা ! একবেঞ্চ পিছন থেকে আমাদের সেকেন্ডবয় তুহিন মুখে হাত চেপে ফিসফিসিয়ে বলল, গাধা বস্ , কোশ্চেন ঠিকই আছে, আজকে সমাজ বিজ্ঞান পরীক্ষাই।
আমার পুরো শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল, কেননা সমাজ বিজ্ঞানে ক্লাস সেভেনে বেশ কিছু কঠিন চ্যাপ্টার ছিল ঐ পরীক্ষায়। আর মুখস্থ করা সাবজেক্টে আমি বরাবরই ল্যাজেগোবরে। আমার অবস্থা আন্দাজ করেই তুহিন বলল, কিছু তো মনে আছে, আমি খাতা বাঁকা করে লিখছি তুই দেখে দেখে লেখার চেষ্টা কর।
ঘণ্টাতিনেক ধরে গোটাগোটা হরফে তুহিন লেখে আমিও লিখি।ও একটা লুজ শিট নেয় আমিও নিই। কোনরকমে পরীক্ষা শেষ হল।খাতা দেওয়ার সময়ে দেখা গেল তুহিন পেয়েছে ৫৩ আমি পেয়েছি ৫৮ আউট অভ ৭৫ !
পরীক্ষায় আমার রুটিন গুলিয়ে ফেলার কাহিনী আর তুহিনের খাতা দেখে দেখে লেখার ইতিহাস পুরো ক্লাস জানে। সবাই বাঁকা চোখে বিস্ময় ছুঁড়ে দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আমি বিশাল কোন অন্যায় করে ফেলেছি।আসলে হয়েছে কি, তুহিন গোটা গোটা অক্ষরে লেখে। আর আমার লেখা ওঁর চেয়ে দ্রুত।
ও দুই লাইন লিখে রাখলে আমার সেটা লেখা হয়ে গেলে ওঁর শ্লথ গতির মাঝখানে বসে থেকে কী করব, আরো দুয়েকটা কথা যোগ করে দিই। যা হওয়ার তাই, স্যারেরা পাতা গুণে নাম্বার দিত। আমি ওঁর চেয়ে বেশি পেয়ে গেলাম।
রুটিন গুলিয়ে ফেলার কাণ্ড ঐ একবারই হয়েছিল, পরবর্তীতে সারাজীবন আমার আর কোনদিন রুটিন গোলায় নি।
কিছুদিন পরে সেবা প্রকাশনীর নানা ওয়েস্টার্ন , ক্লাসিক, তিন গোয়েন্দা পাশাপাশি কয়েকটা বই হাতে পড়ল । কাজী আনোয়ার হোসেনের বিদ্যুৎ মিত্র ছদ্মনামে প্রথম কিছু আত্মউন্নয়ন সিরিজের বই হাতে পড়ল আমাদের। সঠিক নিয়মে লেখাপড়া, নিজেকে জানো ; যৌন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান ; সুখ সমৃদ্ধি ইত্যাদি।
বাংলাদেশের কোন লেখকের সেই প্রথম আত্ম উন্নয়নের উপর মোটিভেশনের উপর লেখা বই আমাদের কাছে সহজলভ্য হয়েছিল। আমি জানি আমাদের সেই সময়ে যারা সদ্য কৈশোরে পা দিয়েছিলাম , তাদের জন্য এই বইগুলো আসলেই একটা বড় ব্রেক ছিল। বিদ্যুৎ মিত্রের লেখা যৌন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান বইটি পড়ার পরে আমাদের কাছের বন্ধুবান্ধবেরা নিজের দেহ ও যৌনতা নিয়ে বেশ কিছু বড় ধরণের ভুল ধারণা থেকে মুক্ত হলাম।
সঠিক নিয়মে লেখাপড়া , বিদ্যুৎ মিত্রের বইয়ে লেখা ছিল –‘ক্লাস সিক্স থেকে এম এ ক্লাস পর্যন্ত সব ধরণের ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে লেখা হয়েছে বইটি। এ বই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নয়। ভাল ছাত্র হতে হলে বেশ খাটতে হবে আপনাকে। কিভাবে খাটলে কম সময়ে বেশি উপকার হবে, পরীক্ষার ভাল ফলের জন্যে কোনসব বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার, কেন পড়ায় মন বসে না, দ্রুত পড়া বা লেখার জন্যে কি করতে হবে, সময়টা ভাগ করবেন কিভাবে, নোট নেবেন কিভাবে, মনে থাকে না কেন, পরীক্ষার হলে ঢুকলেন—- তারপর ?— ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশ্নের সদুত্তর রয়েছে এতে। পরামর্শ অনুযায়ী চললে পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হবে, সন্দেহ নেই।’
এই বইয়ের কয়েকটা চ্যাপ্টার আমার ভীষণ প্রভাবিত করেছিল। আমার এখনো মনে আছে, পরীক্ষা নিয়ে যে লেখাগুলো ছিল। দুটো জিনিশ আমি ফলো করেছিলাম। এক, ঠিক পরীক্ষার পরিবেশ তৈরী করে সময় বেঁধে নিজে নিজে পরীক্ষা দেওয়া আমার খুব কাজে দিয়েছিল। আর পরীক্ষার আগে পড়াশোনার চাপ কমিয়ে রিল্যাক্স থাকা। বিশ্বাস করেন, এই বইয়ে আমি শিখেছিলাম পরীক্ষার আগের রাত বেশি না জেগে ঘুমিয়ে রিল্যাক্স হওয়া। এতে আমার আলগা টেনশন কম থাকত, আর আমার যোগ্যতা মাফিক লিখতে পারতাম।
বিদ্যুৎ মিত্রের সুখ-সমৃদ্ধি বইটির মলাটে লেখা ছিল , ‘ জগতের প্রতিটি মানুষ চায় সুখ-সমৃদ্ধি। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষেরই ধারণা, এ ব্যাপারটা একান্তভাবেই ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। চাইলেই কেউ কি আর সুখ-সমৃদ্ধি পায়?
পায়।
অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বিদ্যুৎ মিত্র জানাচ্ছেনঃ পায়। ইচ্ছে করলে আপনিও বাড়ি, গাড়ি, ফ্রিজ, টেলিভিশন- অর্থাৎ, কেবল খেয়ে-প’রে কোনমতে বেঁচে থাকা নয়, অঢেল প্রাচুর্যের উপকরণ ও অসামান্য গুণ ও ক্ষমতা অর্জন করে নিতে পারেন। সুখ-সমৃদ্ধি আসলে আমার-আপনার আয়-আয়ত্তের মধ্যেই রয়েছে।
যে চাইতে জানে, সে পায়। কি ভাবে ? সহজ পথ-নির্দেশ রয়েছে এই বইয়ে।
সুখ-সমৃদ্ধি আর প্রাচুর্যের জন্য ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হবে না আর আপনাকে। সহজ কয়েকটি নিয়ম পালনের মাধ্যমে অর্জন করে নেবেন আপনি যা চান, তাই ! ’
ওই বইটি উচ্চমাধ্যমিকের পরেও কয়েকবার পড়া হয়েছিল। নিজের উপর আস্থা এনে কিছু যে পাওয়া যায়, চাওয়া যায় ঐ বইটি আমাদের শিখিয়েছিল।
বাংলায় প্রেরণা দেওয়ার মতো বই ঐ কয়েকটিই আমদের চোখে পড়েছিল।
এমন না যে সব মোটিভেশনের বই থেকেই কিছু শেখা যায়। পরবর্তিতে বেশ কিছু বাংলা অনুবাদের বই নেড়ে চেড়ে দেখার সুযোগ হয়েছিল। কিছু কিছু বই এতো দুর্বল ভাষায় অনূদিত যে মনে হয়েছে, আমি অনুবাদ করলেও এর চেয়ে ভালো করতাম।
ঐ যে একটা বয়স থেকে আশাবাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন একটা অনুরক্তি ছিল, সেটা আজো রয়ে গেছে। সেই আশাবাদের আকাশ আরো বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার। ১৯৯০ সালে আমরা যখন সদ্য কৈশোরত্তীর্ণ ঢাকা কলেজে। সেই সময়ে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমাদের আনাগোনা শুরু হল। তখন জীবন যে অমূল্য সেটা বোঝার মতো যথেষ্ট বয়স হয় নি। বয়স যতো বেড়েছে, এই জীবন যে এতো ছোট্ট সেটা বুঝতে পারছি মর্মে মর্মে। আমাদের কলেজ কর্মসূচিতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ উপন্যাস পড়তে দেওয়া হয়। শুক্রবারের সকালে স্যার কবি উপন্যাসের নায়ক নিতাইয়ের কয়েকটা লাইন বলতেন,
“এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালোবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
হায়, জীবন এত ছোট কেনে ?
এ ভুবনে? ”
জীবন আসলেই কতো সংক্ষিপ্ত সেটা তো টের পেলাম ৪০ পেরুনোর পরে।আমার প্রিয়জনের একে একে চলে যাওয়া দিয়ে টের পেলাম , যে চেনা পৃথিবীতে আমি ছিলাম, সেটা ধীরে ধীরে কেমন যেন অচেনা হয়ে যাচ্ছে।আচ্ছা ,আবার ফিরে যাই আমাদের স্কুল জীবনে।
আমাদের সময়ে আরেকজন খুব বিখ্যাত মোটিভেটর লেখক ছিলেন লুৎফর রহমান।তাঁর বই আমি অনেকের বাড়িতে দেখেছি। বিয়ে জন্মদিনে অনেকে উপহার দিতেন।
আমাদের স্কুলের পাঠ্যে ছিল ‘কাজ’ নামের প্রবন্ধটি । সত্যি বলতে কী আমরা যখন ক্লাসে ভালো করার চেষ্টা করছি, তখন প্রবন্ধটি আমাদের অনেককে মোটিভেট করেছে, আলস্য ঝেড়ে মনোযোগী হতে। কী যে তীব্র ছিল তাঁর ভাষা ! আমি প্রায়শঃ আলস্য বোধ করলে ওই প্রবন্ধটা পড়তাম।
“ জীবনের মানুষকে কাজ করতে হবে, কারণ কাজের মাধ্যমেই মানব জীবনের সুখ ও কল্যাণ নিহিত। মানব সমাজের সুখ ও কল্যাণ বর্ধন ছাড়া জীবনের আর কিসে আনন্দ পাওয়া যায় ? — সাধনা ও পরিশ্রমের সঙ্গে যদি জ্ঞানের যোগ থাকে , তবে লাভ হয় খুব বেশি। মূর্খ শত পরিশ্রম করে যা না করতে পারে, জ্ঞানী অল্প পরিশ্রম করেই তা করতে পারেন।–— জীবনের অপমান হয় দুটি জিনিসে—প্রথমত অজ্ঞতায়, দ্বিতীয়ত পর নির্ভরশীলতায়।–— জ্ঞানের চরম সার্থকতা – মানুষকে ভালো মন্দ বলে দেওয়া,–তার আত্মার দৃষ্টি খুলে দেওয়া, তাঁর জীবনের কলঙ্ক-কালিমাগুলি ধুয়ে ফেলা।
আত্মাকে অবনমিত করে কে কুকুরের মতো দেহটিকে বাঁচাতে চায়, আত্মাকে পতিত করে ধর্ম জীবনকে ঠিক রাখা যায় না—এ যদি মানুষ না বোঝে , তবে সে কী প্রকারের মানুষ ? কোন ধর্মের লোক সে ? কোন্ মহাপুরুষের দীক্ষা সে লাভ করেছে, অর্থ ও রুটির জন্য দীন-ভিক্ষুক হয়ে মানুষকে সালাম করতে হবে, এর চেয়ে বড় লজ্জা, বড় অপমান জীবনে আর কী আছে ?
কাজ করলে অসম্মান হয় ? – অসম্মান হয় মূর্খ হয়ে থাকায় , পাপ জীবনে , আত্মার সঙ্কীর্ণতায়। জীবনকে কলঙ্কিত করে লোকের সঙ্গে উঁচু মুখ করে কথা বলতে কি লজ্জা হয় না—তস্করকে আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে তোমার মনে ঘৃণাবোধ হয় না ? —- যুবক বয়সে নিষ্কর্মা জীবন যাপন করা খুবই বিপজ্জনক। মেয়েদের পক্ষে আরো বিপজ্জনক। কাজ নাই , কর্ম নাই—অনবরত শুয়ে বসে থাকলে মাথায় হাজার তরল চিন্তা আসে। জীবনে তরল চিন্তার ধাক্কা সামলান বড় কঠিন। যার মাথায় একবার তরল চিন্তা ঢুকেছে, তাঁর আর রক্ষা নাই—অধঃপতন হবেই।”
আমার ধারণা ছাত্রাবস্থায় আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল মনোযোগের। পড়ায় মনোযোগ আসলে পড়াটা তো আর তেমন কঠিন কিছু না। কীভাবে মনোযোগ ধরে রাখা যায় , সেটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। টেবিলে ঠিক সময়ে পড়তে বসতে পারাটা ছিল চ্যালেঞ্জ। এই ব্যাপারে আমাদের মোটিভেশন পেতাম পজিটিভ ও নেগেটিভ দুইভাবেই।
আমাদের স্কুলে প্রতিবছর বিজ্ঞান বিভাগ থেকে কেউ না কেউ মেধাতালিকায় স্থান দখল করত।
৮৭ ব্যাচে সম্ভাব্য মেধাতালিকায় যাওয়ার জন্য ছিলেন দুইজন মহল্লার মহিউজ্জামান মাহমুদ কনক ভাই এবং সৈয়দ সালামত উল্লাহ্ বাবু ভাই। আমরা যেহেতু তাঁদের ৩ বছরের ছোট আমাদের কাছে তাঁরা ছিলেন বিরাট মোটিভেশন। স্যারদের কাছে তাঁদের গল্প শুনতাম। সেই সময় ১০০০ নাম্বারের পরীক্ষা ৮০০ এর উপরে পাওয়া ছিল অতিমানবীয় ব্যাপার । ঘরে ঘরে আমাদের ভাই-বেরাদররা হায়ার সেকেন্ড ডিভিশন বা প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেই মিষ্টি বিলাতেন। কনক ভাই তখন বুয়েটে, ভ্যাকেশনের সময়ে হাতে পায়ে ধরলাম , আমাদের কয়েকজনকে প্রাইভেট পড়াতে। উনি সেই সময় থেকেই কিছুটা খামখেয়ালী, রাজসিক চালে চলতেন। কী মনে করে উনি রাজি হয়ে গেলেন। সম্ভবতঃ মাস তিনেক পড়িয়েছিলেন। তাঁর কাছে ওই কিছুদিনের সাহচর্যের সবচেয়ে বড় ব্যাপার ছিল কোন নতুন পদ্ধতি নয়। উনি আমাদের আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা উসকে দিলেন। ৮০০ নাম্বার পাওয়া আসলে তেমন কিছু নয় সেটা আমাদের বোঝালেন। আমাদের যে মেধা আছে সেটাতেই আরেকটু পালিশ করলে, আরেকটু টেকনিক্যাল হলেই আমরা ৮০০ এর উপরে নাম্বার পেতে পারি। মেধাতালিকার ব্যাপারটা অনেকখানি টসের ভাগ্যের মতো। কনক ভাইয়ের মোটিভেশন ছিল পজিটিভ মোটিভেশন।
নেগেটিভ মোটিভেশন ও আছে আমার জীবনে । আব্বা পুরনো ঢাকা ছেড়ে মিরপুরের পাইকপাড়ায় বসতি গড়েন। সেখানে মিরপুর উপশহর প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে ১১ নম্বরে চলে আসি। এখানে বাড়ি কিনে থিতু হই। পাড়ার বড়ভাইকে ধরে মহল্লার একটা স্কুল জান্নাত একাডেমী হাই স্কুলে ক্লাস টু-তে ভর্তি হওয়ার পরে টের পেলাম ক্লাসের প্রথমদিকের সবাই মেয়ে। নাসরিন ম্যাডাম নামের একজন ক্লাস টিচার ছিলেন। তাঁর অসুস্থতায় একজন বেশ ধার্মিক গোছের যুবক স্যার প্রক্সি দিতে আসলেন কয়েক সপ্তাহের জন্য। স্যারে নাম মনে নেই। স্যার আমাদের পরীক্ষার খাতা দেওয়ার সময় আমাকে কাছে ডেকে বললেন, ওই মিঞা তুমি ছেলে মানুষ হয়ে মেয়েদের সঙ্গে পার না ? স্যারের ঐ নেগেটিভ মোটিভেশন পেয়ে কী মনে করে খুব করে পড়ায় মন দিলাম। আম্মা খুব অবাক। এর পরের পরীক্ষায় ভাল ফল আসল। স্যারের ওই নেগেটিভ মোটিভেশন আমাদের দেশে খুবই কার্যকর একটা ব্যাপার। আমার অনেক বন্ধুদের এই অভিজ্ঞতা আছে।
আমাদের সময়ে মোটিভেশনের আরেকটা উপায় ছিল সম্ভবতঃ ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে উদ্ভূত। মানে শুকরিয়া মেথড।
সাধারণ ভাত খেতে ভাল লাগছে না, আমার খেতে ইচ্ছে করছে পোলাও! তো আমাদের মুরব্বীরা শেখাতেন অনেকে তো খেতে পারছে না , তাদের কথা চিন্তা করতে। আবার খাবারে স্বাদ পাচ্ছি না, ডাস্টবিন থেকে মানুষ খাবার কুড়িয়ে খাচ্ছে সেটা চিন্তা করতে বলতেন। এটা করলে নাকি খাবারে স্বাদ বাড়বে। আমি সেই ছোট্টবেলা থেকে মুরব্বীদের যে কোন উপপাদ্যের মতো সিদ্ধান্তকে মেনে নিই না। আমার কাছে এই উদাহরণ ভালো লাগে নাই মোটেই। আমার বর্তমানের মুহূর্তকে আনন্দময় করতে কেন আমি অতীতের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতাকে টেনে আনব বারে বারে। কোন কিছুকে টেনে এনে কেন বর্তমানকে উপভোগ করব! এই খারাপ কিছু চিন্তা করে বর্তমানকে আনন্দময় করার ব্যাপারটা বড্ডো অস্বাভাবিক মনে হয়েছে।
কাঁধে হাত দিয়ে পথ দেখিয়ে দেওয়ার , বিস্তৃত আকাশ অবারিত করে দেওয়ার যে উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের দরকার সেটা টের পেলাম আরো পরে। ঢাকা কলেজে পড়ার সময় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়। ঐ সময়ে স্যারের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। স্যার আমাদের অনুপ্রাণিত করলেন বিশ্বসাহিত্যের সেরা বইগুলি পড়তে। সেবা, সুনীল, শীর্ষেন্দু, সমরেশ পেরিয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ে আমাদের হাতে খড়ি হল। বছরখানেক ধরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সুরঞ্জনা আর ছাদে ঘোরাঘুরি।
সবচেয়ে আকর্ষনীয় ছিল স্যারের সঙ্গে সময় কাটানো।
একটা উপন্যাস আমরা সবাই মিলে পড়ে এসেছি। আর , স্যার তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের সেই লেখকের সেরা লেখা আর জীবনের ঐশ্বর্য বোঝাতেন। আহা সেই দিনগুলো ছিল অন্যরকম। একদিকে স্যারের আলোকিত সম্পন্ন জীবনের হাতছানি, আরেকদিকে সামাজিক পারিবারিক এক্সপেক্টশনের তীব্র চাপ। এসএসসির রেজাল্ট ভালো , উচ্চমাধ্যমিকে আরো ভাল করতে হবে। এদিকে এতো কম সময়। ফাইনাল পরীক্ষার মাত্র তিনচার মাস আগে টের পেলাম আমার পড়াশোনার প্রিপারেশন ভয়াবহ খারাপ। কিছু সাবজেক্টে পরীক্ষা হলে, আমি ডাহা ফেল করব। ঢাকা কলেজের দুর্নাম শুনেছিলাম অনেক আগেই, বহু নামকরা ছাত্র ইয়ার ড্রপ দিয়েছে। কেউ দুই একটা পরীক্ষা দিয়ে আর দেয় নি। আমিও টের পাচ্ছিলাম, পরীক্ষা দিলে ফেল করব ; কিন্তু পরীক্ষা তো আর পিছাবে না । অনেকে আশা করেছিল, ৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের ঝামেলায় আমাদের ক্লাস ঠিকমতো হয়নি , পরীক্ষা পিছিয়ে হয়তো কিছুটা কনসিডার করবে, সে গুড়ে বালি! সেই সময়ে সেই আগের নিয়মে ফিরে গেলাম। পড়া যাই হোক না কেন এক বড়ভাইকে ধরে পরীক্ষা দেওয়া শুরু করলাম। বেশ কয়েকটা পরীক্ষা দেওয়ার পরে বোঝা গেল, ৮০০ এর উপরে নাম্বার পাওয়া তো দূর কি বাত, আমি কোনভাবে ফার্স্ট ডিভিশন পেলেও পেতে পারি। প্রতিটা সাবজেক্টে বেশ কয়েকটা পরীক্ষা দিয়ে অবশেষে যখন পরীক্ষার হলে বসলাম তখন বুঝতে পারছিলাম কেন ঢাকা কলেজের মেধাবী ছাত্রদের অনেক পরীক্ষা ড্রপ দেয়। যে ছেলে স্ট্যান্ড করেছে, সে যদি ফার্স্ট ডিভিশনের সম্ভাবনা দেখে তাহলে তো নার্ভাস ব্রেক ডাউন হবেই। আমাদের পরীক্ষার সিট পড়তে সরকারী বিজ্ঞান কলেজে, এইবার সিট পড়ল, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজে। স্যারেরা কী কারণে যেন ঢাকা কলেজের ছাত্রদের উপর বেশ ক্ষিপ্ত ছিলেন। একজন তো এসে বলেই ফেললেন, তোমাদের স্যাররা প্রশ্ন তৈরি করেন আর সেই প্রশ্নের শর্ট সাজেশন পড়ে মেধাতালিকায় যাও তোমরা! ছোট্ট রুম ২০-৩০ জনের ক্লাস রুম। একজন স্যার যেখানে পুরো রুমের জন্য যথেষ্ট, সেই রুমে দুইজন করে টিচার। প্রিপারেশন এমন যে, একটু ধরিয়ে দিলেই বাকীটুকু লিখে ফেলতে পারি। মাথা ঘোরানোর সুযোগ নেই। প্রথমদিন সামনের জন, তারপরের দিন আরেকজন করে , দেখা গেল ৩/৪টা পরীক্ষা হওয়ার পরে রুমে আছি আমরা গোটা দশেক। কোনমতে পরীক্ষা শেষ করে বুঝে গেলাম রেজাল্ট বেশ খারাপ হবে। কীভাবে কীভাবে যেন স্টার নাম্বার নিয়ে কানের পাশে গুলি দিয়ে শেষ হল। এর পরে শুরু হলো , ভর্তি যুদ্ধ। সতীর্থদের কেউ কেউ , আগেই মেরিনে পরীক্ষা দিয়ে ভর্তিযুদ্ধ এড়াতে পারল। বুয়েটে হল না, মেডিক্যালে তো সেভাবে মন দিয়ে পরীক্ষা দেওয়া হয় নি, যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হবেই। বিশাল একটা ধাক্কা সামলে পরের বছরে টেক্সটাইলে।
সেই অর্থে খোলা মনে কাঁধে হাত রেখে কথা বলার মতো অগ্রজ কেউ ছিলেন না । আমার এক স্কুল সতীর্থ ছিল মিঞা মোহাম্মদ হুসাইনুজ্জমান শামীম। ওঁর বাবা ছিলেন সরকারী বিজেএমসি এর বড় কর্মকর্তা। সেই যুগে সম্ভবতঃ তিনি কানাডা থেকে সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে এমবিএ করে এসেছিলেন। আমরা বাসায় গেলে আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করতেন। আমাদের মনেই হোত না , তিনি আমাদের শিশু হিসাবে কথা বলেছেন। একইভাবে তাঁর সন্তানেরা বেশ নিয়মকানুন মেনে চলত এবং শামীম আমাদের ভিতরে অন্যতম আশাবাদী ছিল। সময়ে নষ্ট করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া ওঁর পছন্দের ছিল না। আরেক বন্ধু ছিল মাসুদ পারভেজ, ওঁর মামা ছিলেন সেনাবাহিনীর অফিসার। মামা ওকে মোটিভেট করে মেরিনে যাওয়ার জন্য। আমরা যখন নানারকম ভর্তি পরীক্ষার পেরেশানিতে , ও তখন মেরিনের জন্য সিরিয়াসলি পরীক্ষা দিয়ে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। এমনও হয়েছে আমাদের আরেক বন্ধু ২ বছর এদিক সেদিক করে শেষে মেরিনে ঢুকেছে, যেটা সে প্রথমবারেই করে ফেলতে পারত। ক্যারিয়ার বিভ্রান্তি ছিল আমাদের সময়ে চরম। সেটা এখনো আছে।
নানা আশা হতাশার পরে একবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রিতে ঘষাঘষি করে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে আসলাম। খুব ছোট্ট ক্যাম্পাস, তেজগাঁও এর বেগুনবাড়ির মতো অখ্যাত একটা জায়গায় কেমন একটা দমবদ্ধ পরিবেশে। যারা বড় বড় ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়িয়েছি, তাদের জন্য বেশ হতাশার ছিল। বছর খানেক লাগল অ্যাডজাস্ট করতে। ওখানেও অসংখ্য আশাবাদী লোকের সঙ্গে পরিচয়। প্রফেসর মাসউদ স্যার ছিলেন অন্যতম। আমরা যে খুব বড় ধরণের অবদান রাখতে যাচ্ছি দেশের অর্থনীতিতে সেটা অনেক ভালোবাসার সঙ্গে উনি আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। আরেকজন ছিলেন ডঃ নিতাই চন্দ্র সূত্রধর স্যার। ধীরে ধীরে আমাদে সংকোচ কেটে গেল আমরা টেক্সটাইলের মেইন স্ট্রিমে চলে আসলাম।
বেক্সিমকো আর অন্যান্য টেক্সটাইলের কয়েকবছর পেরিয়ে যখন ওপেক্সে জীবন শুরু হলো তখন অসংখ্য মানুষের সঙ্গে চলা শিখলাম। এই ট্রেডের অসম্ভব মেধাবী কিছু উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হলো।
গত দুই যুগে কর্পোরেট জীবনে নানা ঘাতপ্রতিঘাত, নানা প্রাপ্তি , নানা বঞ্চনায় মুষড়ে পড়া আবার উঠে দাঁড়ানো ছিল, এখনো আছে। বছরের বাজেট, প্রতি মুহূর্তে সেলসের প্রেসার, কর্পোরেট কূটচাল, টিকে থাকার সংগ্রাম আছে। নবীন প্রজন্মকে মোটিভেট করার কিছুটা দায়িত্ব ছিল। সেটা পালন করেছি। যদিও কর্পোরেট মোটিভেশনের মূল উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে বেশি করে কোম্পানিকে দেওয়ার জন্য তৈরি করা। যতো বেশি পারা যায় নিজের সমস্ত কিছু উজাড় করে বেশি করে মুনাফা অর্জনে সাহায্য করা। এখানে ব্যক্তিগত আশাবাদের জায়গা নেই। কর্মচারির মানসিক স্বাস্থ্য , আশা-হতাশা, বিষণ্ণতা, আনন্দ-বেদনার জায়গা নাই।
ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ারের করা একটা উক্তি আমার খুব প্রিয়!
‘I disapprove of what you say, but will defend to the death your right to say it.’
‘তোমার মতামতের সঙ্গে আমি হয়তো একমত নাও হতে পারি; কিন্তু তোমার মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে যাব’। কর্পোরেট জীবনে আমার চারপাশের সিনিয়র-জুনিয়র , ক্রেতা-সরবরাহকারী সবার কথা মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করেছি। অনেকের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। কিন্তু মত প্রকাশে দ্বিমত করিনি।
একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর থেকে আমি আশাবাদী হতে শিখেছি। বিশ্বাস করা শিখেছি মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। আমাদের সভ্যতা নৈরাশ্যের ইঁট বালি দিয়ে গড়ে ওঠেনি । এর প্রতিটি গাঁথুনি শক্তিমান আশাবাদী মানুষের তৈরী। নৈরাশ্য এবং হতাশা দিয়ে কাব্য সৃষ্টি করা যায় হয়তো, আর কিছু না। আমি কবি নই। শক্তিমান কেউও নই। আমি শিখেছি, আশাবাদ আপনার পৃথিবী বদলে দিতে পারে । আর হতাশাও ঠিক তাই করবে উল্টোভাবে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, ‘ You will get, what you are afraid of ! ’ আপনি প্রতিমুহূর্তে কোনকিছু খারাপ হবে ভেবে থাকলে, আপনার সাথে তাই হবে। কিন্তু , মাঝে মাঝে আমি হিসাব মেলাতে পারি না। কেউই পারে না। কেননা পৃথিবী আমার আপনার আকাঙ্ক্ষিত নিয়মে চলে না । সে চলে তাঁর নিজের নিয়মে। আমাদের ব্যর্থতার মাপকাঠি আর্থিক অবস্থান দিয়ে। পরে মনে হয়েছে, আশাবাদের সাথে সাফল্যের একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে অবশ্যই ; তাই বলে আশাবাদী মনুষ্যমাত্রই আর্থিকভাবে সফল হবে সেটা বোধহয় অনেকাংশে সুনিশ্চিত বা আকাঙ্ক্ষিত নয়। আমি আশাবাদী মানুষ বলতে হাল ছেড়ে না দেওয়া, উন্নত , উদার, সৌরভময়, উচ্চকিত সম্পন্ন মানুষ বুঝি। ঘরোয়া আড্ডায় সায়ীদ স্যারের বলা একটা কথা বিশ্বাস করি, নৈরাশ্যের ইট দিয়ে দিয়ে বর্তমান সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। সভ্যতার ইমারত গড়ে উঠেছে আশাবাদে। কোটি কোটি নৈরাশ্যবাদী লোকের মাঝে গুটি কয়েক আশাবাদী মানুষ সমাজ ও সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন।
আবার এটাও ঠিক , মানুষের জীবনের সামাজিক অর্থনৈতিক দৌড় অনেকখানি ম্যারাথন দৌড়ের রিলে রেসের মতো। কোন পরিবেশে জন্মালেন, ঠিক ট্র্যাকের কোন জায়গায় আপনার ব্যাটন বুঝে পেলেন সেটা প্রায়শঃ অনেক বড়ো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।তারপরেও অসংখ্য ব্যতিক্রম, বৈপিরিত্য , বিস্ময় আছে বলেই জীবন এতো আরধ্য।
পরিশ্রম, সততা, নিয়মানুবর্তিতা, সঞ্চয়ী, মিতব্যয়ীতা, সুস্থ নীরোগ দেহ, স্বাস্থ্য সচেতনতা, কিছু সাধারণ গুণাবলী মানুষের অত্যাবশ্যক । তারপরেও আমাদের জীবনের নানা লার্নিং থাকে একেবারে গতানুগতিক ; কিন্তু প্রতিটি মানুষের জন্য তা হতে পারে প্রথমবারের মতো ও একান্ত ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়ায় সেই অভিজ্ঞতা। শেখার শেষ নেই, এ পর্যন্ত যা শিখেছি বা শেখা উচিৎ ছিল সেটা সবার সঙ্গে শেয়ার করাই যায় !
১। জাজমেন্টাল না হওয়া। আমার জীবনের বড়ো শিক্ষা। আমি আমার পরবর্তী প্রজন্মকে সেটা জানিয়ে যেতে চাই। একজন মানুষের ব্যাপারে হুট করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার। আমাদের এতোটুকু ধৈর্যও হয় না , একটু অপেক্ষা করতে। অমুক ভালো, তমুক খারাপ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই। একটা মানুষ পুরোপুরি ভালো বা পুরোপুরি খারাপ হতে পারে না। যে কোন পরিস্থিতিও তাই। সাদা কালোর মাঝে একটা রঙিন পৃথিবী আছে, সেটা আমি আমার সন্তানদের হাতে ধরে শিখিয়ে যাচ্ছি।
২।নেগেটিভ লোক এড়িয়ে চলা। এই ব্যাপার আমার স্বভাবজাত ছিল ছোটবেলা থেকেই। কর্পোরেট জীবনে এড়িয়ে চলা যায় না। নিজের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে ক্ষমতাশালী অনেকেই ভয়ঙ্কর নৈরাশ্যবাদী হয়ে থাকেন। কুটিল মনের লোকের সঙ্গে চলার সমস্যা হচ্ছে , তাদের প্রতিটি ভণ্ডামো, চাটুকারিতা কাহিনীকীর্তিতে নিজের মনের উপর কালো দাগ পড়ে। এদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গেলে, নিজেও এদের মতো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আমি সচেতনভাবে এদের সারাজীবন এড়িয়ে চলেছি। নিতান্ত এড়িয়ে চলতে না পারলে, ইগনোর করেছি, তাদের কর্মকান্ডের কিছু নিজের ভিতরে নিইনি।
৩।নিজের সঙ্গে নিজের ও নিজের পরিবারের সঙ্গে সবসময় সমঝোতা ও সুসম্পর্ক রাখা। একজন মানুষকে সার্বক্ষনিক পরিবেশ প্রতিবেশের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। বাইরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে আপনার যে শক্তি দরকার তা আসবে আপনার নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক কেমন। এবং আপনার নিজের পরিবার,বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তানদের সম্পর্ক কেমন তার উপর। নিজের পরিবারে সঙ্গে দূরত্ব ও অসমঝোতায় যে পরিমাণ শক্তিক্ষয় হবে, বাইরের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য শক্তি অবশিষ্ট থাকবে না। আমি যে কোন পরিস্থিতি সে চাকরি জীবনের ব্যর্থতা , অপ্রাপ্তি বঞ্চনা সবকিছুকে অবলীলায় নিজের স্ত্রীর সঙ্গে শেয়ার করি। এমন অনেককে পেয়েছি, চাকরি হারিয়ে নিজের পরিবারে সঙ্গে দিনের পর দিন অভিনয় করে চলেছেন। সকালে অফিসের পোশাক পরে বের হয়ে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরেছেন। আমি তাঁদেরকে বলেছি, যুদ্ধটা আপনি একা করছেন কেন? আপনার পরিবারে জন্য আপনি জীবন সর্বস্ব করছেন, তাদের সঙ্গে কেন অভিনয় করছেন। আপনার জীবনের প্রতিকূল অবস্থাতো চিরস্থায়ী নয়। এই যুদ্ধে আপনি তাদেরকেও সামিল করুন। ঘরে ও বাইরে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে করে নিজে নিঃশেষ করার কোন মানে হয় না। অনেকে ফিরে এসে আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছন ওই সৎ পরামর্শের জন্য।
৪। ডু নট লেট আদার ডিফাইন ইয়োরসেলফ। নিজেকে অন্যের দ্বারা সংজ্ঞায়িত হতে না দেওয়াই শ্রেয়। নিজেকে নিজে বোঝার জন্য আমার প্রতিনিয়ত চেষ্টা ছিল। এটা থাকা উচিৎ। অন্য কেউ এসে আপনার দুর্বলতা চিহ্নিত করে আপনার সব আত্মবিশ্বাসের মূলে বিষ ঢেলে দিচ্ছে সেটা কাম্য নয়। কেউ আপনার অযাচিত সমালোচনা করলে আপনি দেখার ও বোঝার চেষ্টা করেন, সে সমাজের কোন অবস্থানে আছে। তাঁর মন্তব্য আপনার আদৌ নেওয়ার দরকার আছে কী !
৫। প্রতিদিন আমরা শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য নানা অভ্যাস গড়ে তোলার বিজ্ঞাপনে জর্জরিত। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি Make a good habit and habit will make you. Conversely , bad habits destroys you. সুতরাং একটু ধৈর্য ধরে কোন একটা ভালো অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে সেটা সারাজীবনের সহায়। আর একটা বদভ্যাস হয়ে গেলে সেটারও দাম দিতে হয়।
৬। ভুক্তভোগীর পরামর্শ কতোখানি নিবেন আর আর কতোখানি বাদ দিবেন সেটা হিসাব করে চলুন। তবে সব মানুষের কিছু সামাজিক এক্সপার্টিজ থাকে সেখানে তাঁর পরামর্শ মন দিয়ে শোনা উচিৎ । চরমভাবাপন্ন হওয়ার কোন মানে হয় না। আব্বার সবচেয়ে দুর্বল ছিল তাঁর পেট। সারাজীবন সে পেটের গণ্ডগোলে ভুগত। নানা রকম টোটকা আর ওষুধের মহড়া চলত। আমি জেনে শুনে পেটের ব্যাপারে তাঁর মতামত নিতাম না। যদিও সে প্রতিদিন এটা খা, সেটা খা বলে চলত। কিন্তু আইনজীবী হিসাবে তাঁর মতামতকে দাম দিতাম। ঠিক একইভাবে আমার ছোটমামা তেমন স্বাস্থ্য সচেতন ছিলেন না। কিন্তু পড়াশোনায় ভাল ছিলেন। তাই পড়াশোনার ব্যাপারে তাঁর মতামত বিবেচনায় আসত সর্বাগ্রে।
৭। তর্কে কেউ নাকি জেতে না। একজনের উপলব্ধি আরেকজনকে দেওয়া খুব মুশকিল। তর্কে জিততে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় করবেন, সেটা অপচয় না করে চুপ থাকা অনেকাংশে শ্রেয়। যোগ্য তার্কিক না হলে আমি কখনই নিজের শক্তিক্ষয় করিনা। একজন লোক তাঁর পরিবার ও পরিপার্শ্ব থেকে বেড়ে ওঠে, তাকে কোন নতুন মতবাদ, মতাদর্শ শুনিয়ে লাভ নেই।
৮। শুধু বুদ্ধিমান লোকে আর শক্তিশালি লোক বেঁচে থাকবে অন্যেরা মরে যাবে, পৃথিবীটা মোটেও সেই নিয়মে চলে না। বিশ্বের বিখ্যাত ধনকুবের ওয়ারেন বাফেট Ovarian Lottery উভেরিয়ান লটারি বা সৌভাগ্যের কথা বলেছেন। একজন লোক কোথায় জন্মগ্রহণ করছে সেটা তাঁর জীবনের বড় ধরণের প্রভাব রাখে। যে লোকটাকে আপনার আপাতত অযোগ্য , অথর্ব মনে হচ্ছে, কোনভাবে সে হয়তো আগেই কোন লটারি জিতে বসে আছে। আবার কাউকে অসহ্য লাগছে, অযোগ্য মনে হচ্ছে কিন্তু খুঁজে দেখা গেল তাঁর ভিতরে কোন না কোন বিশেষগুণ আছে বলেই সে ওইখানে পৌঁছে গেছে।
৯। সবার ইন্টেলকচুয়াল থাকে না। দুই কলম পড়েই আমরা ভাবি অনেক বুঝে ফেলেছি। এই হচ্ছে পৃথিবী। অথচ হেনরি ফোর্ডের নিরক্ষর মা তাকে সেই বিখ্যাত কথা বলে গেছেন, ‘Whether you think you can, or you think you can’t–you’re right.” জীবনে অভিজ্ঞতার উপরে কিছু নাই। খুব কাজের কোন অভিজ্ঞতা খুব স্বল্প শিক্ষিত লোকের কাছে পেতে পারেন। কেউ হয়তো আপাত দৃষ্টিতে স্থূল বুদ্ধিমত্তার ; কিন্তু তাঁর খুব বড় একটা হৃদয় থাকতে পারে । সে হয়তো নির্দ্বিধায় আপনার জন্য অনেক কিছু করে ফেলেছে বা করতে পারে অথবা সে সমাজের জন্য অনেক উপকারি। আমি একটা জীবনের পরে শুধু ইন্টেলেকচুয়াল দিয়ে মানুষকে বিবেচনা করি না। আমি মানবিক দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করি।
১০। সাফল্য ব্যর্থতায়, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে অতিরিক্ত উৎফুল্ল বা উদ্বিগ্ন না হয়ে অপেক্ষা করা শিখতে হয়। বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে দুইদিন প্রায় নাওয়া খাওয়া বন্ধের উপক্রম। অথচ কয়েকবছর না ঘুরতেই ঐ সময়ে নিজের বোকামিতে নিজেই হেসেছি। এমন না যে আমার উচ্চমাধ্যমিকের পরে ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি খুব ভাল ছিল। র্যাশনালি দেখলে আমার প্রিপারেশনে আমার যেখানে যেখানে চান্স পাওয়ার ছিল আমি তাই পেয়েছি। আমাদের অনেক বন্ধুকে প্রেমে পড়তে দেখেছি। যাকে ছাড়া মনে হয়েছে এই জীবন অচল, ব্যর্থ, অপাঙতেয়, সেই তাকে ছাড়াই কিছুদিন পরে তারা বিয়ে করে ছানাপোনা তুলে ভুলেই গেছে সেই বালখিল্যতার কথা।
১১। শর্টকাট ক্যান কাট ইউ শর্ট। এটা এমনিতেই আমি মেনে চলতাম। খুব দ্রুত কোন কিছুতে আর্থিক লাভ হবে, ফাটকা ব্যবসা, লটারিতে আমার বিশ্বাস নেই। আবার একইভাবে দ্রুত ধনী হওয়ার অনৈতিক কোন কিছুতেই আমি জড়াইনি। পড়াশোনা থেকে শুরু করে ক্যারিয়ার সব ব্যাপারেই আমি স্টেডি অ্যান্ড স্লো ছিলাম। এতে তাৎক্ষণিক লাভ না হলেও , অনেক সম্পত্তির ও পজিশনের মালিক হতে না পারলেও আমি দীর্ঘমেয়াদে হ্যাপি ।
১২। ধর্ম ও নৈতিকতা এই যুগে আলাদাভাবে চলে। ধার্মিক লোক মানেই নৈতিক লোক না। আমি পদে পদে দেখে ও ঠেকে শিখেছি যে , নৈতিক লোক ধার্মিক হতেও পারে, অন্য ধর্মের হতে পারে, ধর্মহীণও হতে পারে। আমার শৈশব বড় একটা বাজারের পাশে। বাড়ির পাশেই মসজিদ। বাজারের সব ব্যবসায়ীরা ওই মসজিদে আসতেন। অথচ তাঁদের নানা দুই নাম্বারি ধান্ধার কথা ছোটবেলা থেকেই জানতাম। জীবনের নানা চড়াই উৎরাইতে আমি অনৈতিক লোকেদের ধর্মের মুখোশে সমাজে দেবদূতের চেহারায় দেখেছি। যেহেতু ধর্মে যে কোন অন্যায় করে কাফফারা বা মুচলেকা দিয়ে মাফ পাওয়ার ব্যাপারটা আছে। তারা সেটা ধরেই বছরের পর বছর একই অর্থলিপ্সু দুর্নীতি চালিয়ে গেছেন। যেমন আমাদের মুসলামানেরা ভাবে দুর্নীতি, নষ্টামি যাই করি না কেন, হজ্ব করে আসলে তো সে দুধে ধোয়া শিশুর মতো অপাপবিদ্ধ হয়ে গেলাম। এই অদ্ভুত চক্র তাকে পুরোপুরি নৈতিক হতে দেয় না বা একেবারে শেষ বয়সে এসে সে ক্ষান্তি দেয় দুর্নীতিতে।
১৩। মানুষের সঙ্গে আন্তঃ সম্পর্কের ব্যাপারে চারপাশের লোকে কী বলল তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ আমি নিজে কী বুঝলাম ; আমার কাছের পরিবারের লোকের কাছে আমার অবস্থান কি সেটা। বাইরের লোকে আমাকে খুব নরম, আত্মবিশ্বাসহীন , নানা অভিধায় অভিষিক্ত করলেও, আমি কী আমি নিজে তা জানি। আমি আমার বাবা-মার কাছে কতোখানি ভাল, আমার সন্তানদের কাছে কতোখানি স্নেহপ্রবণ , আমার স্ত্রীর কাছে কতোখানি ভাল সেটা বাইরের লোকের জাজমেন্টের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ।
১৪। কেউ একজন বা কয়েকজন থাকতে হবে বা খুঁজে নিতে হবে যার বা যাঁদের সঙ্গে সবকিছু শেয়ার করা যায়। অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে শুরু করে নিজের যৌন ব্যর্থতা অব্দি। বিষয়ভেদে শেয়ার করার জন্য কয়েকজন হলেও সমস্যা নেই। কিন্তু নিজের মনের কথা খুলে বলার জায়গা দরকার। যদি কেউ না থাকে, নিজের ডায়রিতে লিখে রাখুন। আমার সেই স্কুল জীবন থেকে একাকী, অসহ্য নিঃসঙ্গতায় নিজের মনে কথা খুলে বলার জন্য ডায়রি ছিল বড় ভরসা। খুলে বললে বা লিখে ফেললে মনের বিষণ্ণতা কেটে যায়। নিজেকে ভারহীণ মনে হয়।
তবে এ ব্যাপারে সাবধানতা থাকতে হবে। নিজের ব্যক্তিগত সাফল্য ব্যর্থতা, দুর্বলতা এমন কোন সহকর্মীর সঙ্গে করবেন না, যা সে নিজের সুবিধার জন্য আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। আমার জীবনে এরকমটি হয়েছে কয়েকবার।
১৫। কৌতুহলী হন, নিজের বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা ধরে রাখুন। শিশুদের সঙ্গে অথবা নিজের চেয়ে কম বয়সী তরুণদের সঙ্গে মেলামেশা করুন। সমবয়সী অথবা বয়স্ক লোকেরা অনেক ক্ষেত্রেই জীবনের ব্যপারে আশাবাদী থাকেন না, একঘেয়েমিতে থাকেন। তাদের সঙ্গে সম্মানজনক দূরত্বের পাশাপাশি তারুণ্যের সাহচর্য দরকার।
১৬। অনিশ্চয়তা বা আনসারটেইনিটি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যতোক্ষণ বেঁচে আছেন, আপনার সমস্যা থাকবে এবং অনিশ্চয়তা থাকবে। আমরা কেউই জানিনা – আগামীকাল কী হবে , আগামী সপ্তাহে বা বছরে কী হবে ! আমরা ভুলে যাই, পৃথিবীর সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি থেকে শুরু করে থেকে আমার মত সাধারণ লোকের জন্য এই অনিশ্চয়তা সমানুপাতিকভাবে আছে। এই অজানা অনিশ্চয়তাকে ঘিরেই আমাদের বৈচিত্রময় লৌকিকতা , আচার-আচরণ,ধর্ম ও সামাজিকতা গড়ে ওঠে। আমরা একেকজন একেকভাবে জীবনকে দেখা শুরু করি। কীভাবে জীবনকে দেখতে হবে আমরা অন্যের কাছ থেকে শিখে ফেলি। আর , অনিশ্চয়তাকে কাটাতে চেষ্টা করি। কিন্তু পেরে উঠি না। অনিশ্চয়তাকে যে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব না, এটাও মেনে নিতে পারি না। তাই, পরিমিত অনিশ্চয়তা শরীর ও মনের জন্য ভালো ; অতিরিক্ত অনর্থক হতাশা ও উদ্বেগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর নষ্টই করবে শুধু।
১৭। নিরাপত্তাহীনতা বা ইনসিকিউরিটি ! একইভাবে জীবনের সবচেয়ে অবিচ্ছেদ্য অনুভূতি হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা । সীমিত আকারে থাকা ভালো। বেশি নয়। আপানার আসল নিরাপত্তা আপনার নিজের কাছে, আপনার পরিবারের কাছে। কোটি টাকা থাকলেও সেটা আপনার জীবনের নিরাপত্তার স্বস্তি দেবে না। যে নিরাপত্তাহীনতায় আমাদের মধ্যবিত্ত অগ্রজরা ভুগেছিলেন, তা আমাদের মাঝে বংশানুক্রমে চলে আসে। পরিশ্রম, প্রতিযোগিতায় নানারকম প্রাপ্তি ও অর্জন দিয়ে আমরা নিজেদেরকে নিরাপদ করার চেষ্টা করি । পড়াশোনা, চাকরি,ব্যবসা , টাকা, গাড়ী, সেভিংস ইত্যাদি ইত্যাদি। মূলতঃ এটার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বা সীমারেখা নেই। মাথাগোঁজার একখানি জমি হলে কি মানুষ নিরাপদ ? সে কী ক্রমাগত আরো জমির মালিক হতে চায় না ! একটা ফ্ল্যাট হয়েছে আরেকটা করে নিরাপত্তা বাড়াতে চায়। নগরীর এই প্রান্তে কিছু থাকলে,অপরপ্রান্তে । একই ব্যক্তির লাখ টাকার ব্যাংক ডিপোজিট যেমন তাকে নিরাপত্তা এনে দিতে পারে না ; কোটি টাকা ডিপোজিটেরও সেই সম্ভাবনা নেই। কোন কিছুতেই আমরা নিজেদেরকে নিরাপদ করতে পারিনা বা নিরাপদ ভাবতে পারিনা। পরবর্তী বংশধরদেরকেও একই ভাবে নিরাপদ করার ক্রমাগত চেষ্টা করে যাই। স্বদেশ থেকে প্রবাসী হয়ে জীবনকে আরো নিরাপদ করতে চাই। একটা উর্ধ্বশ্বাস দৌড় ক্রমাগত আমাদের ত্রস্ত করে। আর , জীবন আমাদের হাতের ফাঁক গলে কখন নীচে পড়ে যায় , আমরা টেরও পাইনা ! নিরাপত্তার প্রস্তুতি নিতে নিতে জীবন শেষ হয়ে যায় !
১৮। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার আমাদের অনেকের সীমাবদ্ধতা বুঝতেন। সামাজিক চাপে , জীবিকার কাছে আমাদের নতিস্বীকারের দুর্বোধ্য বেদনা বুঝতেন। তবুও তিনি আমাদেরকে সবসময় বলতেন যে জীবিকাতেই আমরা থাকি না কেন , আমাদের একটা ইন্টেলেকচুয়াল লাইফ থাকা দরকার। সম্পন্ন জীবনবোধ থাকা দরকার। কেউ যদি দিনের পর দিন কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে তার মন শুষ্ক হয়ে যায়। বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের প্রতি আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন সারাজীবন। ব্যস্ত জীবনের পাশাপাশি আমাদেরকে তিনি প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে বলতেন। বলতেন মানুষ প্রকৃতির কোল থেকে উঠে এসেছে, আমাদের আদি ও অকৃত্রিম প্রবণতা হচ্ছে আবার প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া। আমরা প্রকৃতির কাছে গেলে সবচেয়ে সজীব হয়ে উঠি।
১৯। পরিবারকে সময় দিন, বছরে নিয়ম করে একঘেয়েমি কাটাতে সবাইকে নিয়ে বেড়াতে যান। যদি আর্থিক সামর্থ্য না থাকে, ধারে পাশে কোথাও যান। আর্থিক সামর্থ্য ও সময় না থাকলে কাছে ধারের রেস্টুরেন্টে যান। সেলিব্রেট করেন।
জীবন উদযাপন করতে শিখুন। অনেক আগে যখন OPEX Group এ ক্যারল ব্রাউন নামের এক মহিলা ক্রেতা ছিলেন আশির কাছে বয়স। সিনহা স্যারের প্রিয়ভাজন। খুব ছোট সংখ্যার অর্ডার হলেও আমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে করতে হত।
উনি খুব হাসি খুশী থাকতেন। দারুণ বাহারী রঙের পোশাক পড়তেন। আমি কারণ জিজ্ঞেস করলে উনি আমাকে বলেছিলেন, Jahid , life is not a dress rehearsal , never keep your best wine in the stock for an occasion ! ঠিকই তো , জীবন তো আর মঞ্চ নয় বার বার রিহার্সেল দেওয়ার সুযোগ কোথায়। যা করবার বা বলবার একবারেই বলে ফেলতে হয়। বারবার সেই সুযোগ আসে না। আবার আনন্দ করার জন্য উৎসব বা বিশেষদিনের অপেক্ষা অনেকাংশে বোকামি।
২০। যখন যে প্রযুক্তি এসেছে , তার ভালো দিক মন্দদিক বোঝার চেষ্টা করেছি। সন্তানদের বই পড়তে উৎসাহিত করেছি। কেন টিভি ও ইন্টারনেট আমাদের আসক্ত করে রাখে সেটা বুঝিয়েছি। একবার আমি আমার বড়কন্যাকে বোঝালাম, ধরো তোমার আইকিউ ৯০। কিন্তু টিভির প্রোগ্রাম করছে একক কোন ব্যক্তি নয়। ধরো তাঁদের ভিতরে কয়েকজনের আই কিউ তোমার চেয়ে অনেক বেশি। তাঁদের সম্মিলিত আই কিউ দিয়ে সে অনেক সময় ব্যয় করে একটা অনুষ্ঠান করেছে, সেটা তোমাকে আটকে রাখার জন্য, আসক্ত করার জন্য। যা তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ না, এড়িয়ে যাও। সবসময় নিজের প্রায়োরিটি বুঝতে হবে।
২১। মানুষের জীবনে বিজ্ঞান ও দর্শন দুইটিই সমান গুরুত্বপূর্ণ।
২২। অনর্থক অন্যজনের তৈরি করা টেনশন নিজের ঘাড়ে নেবেন না। যে পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমার নেই। ঢাকার ট্র্যাফিক, দেশের সরকার, গ্রীষ্মের দুঃসহ গরম, প্রযুক্তির অপব্যবহার, অন্যদেশের ভূ-রাজনীতিতে বাংলাদেশের দুরবস্থা, ইত্যাদি। এই রকম অসংখ্য ইস্যু আছে, যা ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে, বদলাবে। প্রকৃতির বিরূপ আচরণ আমার নিয়ন্ত্রনে না। এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে পারেন, দুশ্চিন্তা না। গাড়ীতে বসে আছি, শুরু করলাম দেশের গুষ্ঠি উদ্ধার করতে। ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেল। বাথরুমে যাচ্ছি, ফোন বাজছে, টেনশন বেড়ে গেল। সময় দিন, ধীরে করুন। অযথা প্রেসার বাড়াবেন না।
২৩। যতো বড় অবস্থানেই থাকুক না কেন, যতদূর পারি ভণ্ডদের এড়িয়ে চলেছি। বরং সমাজের নীচু শ্রেণির লোক, কোন দুর্নাম আছে কিন্তু ভণ্ড না তাঁদের সঙ্গে আমি অবলীলায় চলেছি। কারণ আমি জানি সে খারাপ। কিন্তু ভণ্ড লোকেদের মনে হয়েছে গিরগিটির মতো। নিজের স্বার্থে যে কোন সময় ধর্ম বা নিজের অজ্ঞতা দিয়ে নিজের কুকর্মকে ঢাকতে চেয়েছেন। অথবা না জানার ভাণ করেছেন তার ভণ্ডামি নিয়ে।
২৪। উর্ধ্বতনকে কিছু বলতে হলে , সরাসরি বলে ফেলার চেষ্টাটা শিখেছি অনেক পরে। আমি মূলত অন্তর্মুখি। নিজের প্রয়োজনের কথা অনেক সময় বলে ফেলতে দেরি করেছি। অথবা এড়িয়ে গেছি। অনেক পরে এসে বুঝেছি, নিজের কথা অন্যকে দিয়ে বলানোর চেয়ে নিজে বলে ফেলাই ভাল। তবে, এই বলার ব্যাপারটাও সঠিক সময়ে হতে হবে। ভুল সময় হলে মুশকিল।
২৫। টানেলের দুইদিক থেকেই দেখার চেষ্টা করেছি। কোন পরিস্থিতিতে একজন লোক কী ধরণের আচরণ করতে পারে সেটা ঐ ব্যক্তির অবস্থানে না বসলে বোঝা যায় না। অবস্থান পরিবর্তনের এই মানসিক ব্যাপারটা নিজেকে চরমভাবাপন্ন হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে।
২৬। নিজেকে ক্ষমা করতে শেখা। নিজেকে ভালোবাসতে শেখা । সারাক্ষণ নিজেকে দোষারোপ না করা। নিজের সঙ্গে যখন কথা বলেছি, সবকিছুর জন্য নিজেকে সারাক্ষণ দোষ দিই নি। সুযোগ দিয়েছি।
২৭। মানুষকে বিশ্বাস করেছি, তবে পুরোপুরি বিশ্বাস রাখি নি। বিশ্বাস করে বহুবার ঠকেছি। এরপর বিশ্বাস করতে হলে, ভিতরে পুরোপুরি অবিশ্বাস নিয়েই করেছি। রাস্তার ভিক্ষুকদের বিশ্বাসযোগ্যতা নাই। আমি একটা নির্দিষ্ট বয়সের পরে কাউকে ভিক্ষা দিলে চিন্তা করিনি আসল ভিক্ষুক কীনা। আবার কাউকে আর্থিকভাবে সাহায্য বা ধার দিলে ধরে নিয়েছি, সেটা আর ফেরত পাব না। পেলে খুশী হয়েছি । আবার তাঁদের সঙ্গেই আর্থিক লেনদেনে গেছি, যাঁদেরকে দীর্ঘদিন ধরে আমি চিনি।
ফাটকা লাভের কোন কিছুতে কখনো টাকা ইনভেস্ট করি নি। তবে পুর্বাচলে এক টাউটের পাল্টানে পড়ে বেশ কিছু টাকা গচ্ছা গেছে। ওই প্রথম ওই শেষ।
২৮। অফিসের কাজ পারতপক্ষে বাসায় নিই নি। এই ডিজিটাল যুগে সারাক্ষণ ইমেইল না দেখে সাময়িকভাবে কর্মক্ষেত্রে কিছুটা পারফরমেন্সের ক্ষতি হয়েছে, আপডেট থাকতে পারি নি। তবে আখেরে লাভ হয়েছে।
২৯। অফিসে ও পরিবারে সারাক্ষণ দায়িত্ব ডেলিগেট করেছি। যা আমি পারি, খুব ভালোভাবে পারি, তা রোজ রোজ না করে পরের লেভেলের কাছে ডেলিগেট করেছি। আমি অন্যকিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করেছি। তবে আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই ডেলিগেশনের সুফল কুফল দুইই আছে।
৩০। আমার জীবনের অন্যতম ভালো একটা লার্নিং হচ্ছে –‘Changing yourself is much more easier than changing the whole world.’
৩১। নিজের গাট ফিলিং কে দাম দিয়েছি। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলে, সেটা মাল্টিপল চয়েজ থেকে শুরু করে অনেক কিছুতে যেখানে আমি বুঝতেই পারছি না, বা যথেষ্ট ইনফরমেশন নাই। সে ক্ষেত্রে যে উত্তরটা প্রথমে মনে এসেছিল সেটাতে টিক দিয়ে চলে এসেছি। মনের গভীরে ঝাঁপ দেওয়ার যথেষ্ট সময় না থাকলে , এই পদ্ধতি কার্যকর।
৩২। আমি ভালো শ্রোতা। অনেকে আমাকে পছন্দ করেন শুধুমাত্র আমি তাদের কথা মন দিয়ে শুনি বলি। তবে অবশ্যই সেই বক্তার বক্তব্য একটা মিনিমাম লেভেলের হতে হবে। সুতরাং মন দিয়ে কথা শুনুন, কারো ব্যর্থতার গল্প , বিশ্বাসঘাতকতার গল্প, হেরে যাওয়ার গল্প, আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর গল্প শুনুন। আমাদের জীবনের নায়কেরা আমাদের চারপাশেই ঘোরাফেরা করছে !
৩৩। আমি একসময় শুধু বিশ্রামের কথা রিটায়ারমেন্টের কথা চিন্তা করতাম। মনে হতো সব সুখ বোধহয় বিশ্রামে। একটা বয়সে এসে বুঝেছি, রিটায়ারমেন্টের কথা মনে করা মানে নিজেকে সমাজের কাছে মূল্যহীন করার চিন্তা করা। নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারলেই নিজের বেঁচে থাকার স্পৃহা থাকবে। তাই আমরা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজের ভিতরে থেকে নিজেকে মূল্যবান মনে করতে চাই। মধ্যবিত্তের রিটায়ারমেন্ট মানে– পুরোপুরি অপাঙতেয় মূল্যহীন জীবন। ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা। দুইটা রাস্তা খোলা, কবরস্থান আর মসজিদ। তসবিহ্ নিয়া মসজিদে যাওয়া আসা করো এবং সারাক্ষণ সাড়ে তিনহাত অন্ধকার কবরের কথা চিন্তা করো। মানুষ দ্রুত বুড়িয়ে যাবে না কেন ? কাজ নেই , আলো নেই, বাতাস নেই, হাসি নেই, দুরারোগ্য অসুস্থতায় সার্বক্ষনিক মৃত্যুর কথায় কে না বুড়িয়ে যায় !
কয়েক বছর আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। বড়ো কোন অসুস্থতায় না পড়লে, যতদিন পারি কাজের ভিতর থাকব। সেই কাজ অর্থকরী হোক বা সমাজকল্যাণমূলক হোক।
৩৪। You always meet twice in life! আমাদের আবার দেখা হবে। চাকরি ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজনের সঙ্গে আরেকজনের চিরবিচ্ছেদ তো হয় না। যাকে আমি ঘৃণা করলাম , ক্ষতি করলাম, অপমান ও অসন্মান করলাম তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে। তখন চোখ তুলে তাকাতে পারব কী ? অনেকেই পারে। আমি পারি না। আমার অনুজদের সবসময় বলি, ইউ অলওয়েজ মিট টুয়াইস। কারো সঙ্গে এমন কোন আচরণ বা ব্যবহার কোর না যেন বহুবছর পরে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও তোমার লজ্জা লাগে ! সম্পর্কের সুতো রেখেই সম্পর্কের বিচ্ছেদ করা ভাল।
৩৫। হীনম্মন্যতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা কম বয়সে থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে প্রয়োজন ও ভ্যালু পরিবর্তিত হতে থাকে, তখন মানুষ হীনম্মন্যতা কাটিয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আমার চেয়ে সবদিক দিয়ে এগিয়ে থাকা লোক যেমন আছে, আমার চেয়ে পিছিয়ে পড়া লোকও আছে। নিজেকে নিজে ছোট না ভাবলে বাইরের কেউ আমাকে ছোট করতে পারে না। বিশ্বাস করে দেখেছি, ব্যাপারটা কার্যকর।
৩৬। হুট করে কারো কথায় সহজে কনভিন্সড হবেন না। হোক সেটা ইন্টারনেটে অথবা টিভিতে অথবা বইয়ের পাতায়। কারো কথায় প্রথমেই কনভিন্সড হয়ে গেলে আমার নিজের চিন্তা করার জায়গাটা থাকেনা।কর্মজীবনেও সারাক্ষণ আমার কাছে অফিসের ও সামাজিক লোকজনের আনাগোনা থাকে।সবাই কনভিন্সড করতেই চায়। সবার কথা মন দিয়ে শুনে নিজের সিদ্ধান্ত নিজের নিতে হয়।
৩৭। নিজেকে ক্ষমা করতে পারাটা শিখতে অনেক সময় লেগেছে। নানা রকম ছোট খাটো প্রতিজ্ঞা থাকে আমার। এই সকালে ঘুম থেকে উঠব। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেব। প্রোক্যাসিনেশন করব না। সব প্রতিজ্ঞা আর হিসাব নিকাশ ঠিক থাকে না। কিছুটাও যদি থাকে, নিজেকে ধন্যবাদ দেওয়া শিখেছি। নিজেকে ক্ষমা করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছি।
৩৮। আব্বা বলতেন মানুষে ও জীবে ভেদাভেদ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা করেছেন। শেষ বিচারের দিন ৭০ কাতার করেছেন। সাত দোজখ আর আট বেহেশত করেছেন। তো ক্ষেত্র বিশেষে মানুষের অসাম্যে , কৃতকর্মের অপ্রাপ্তিতে মন খারাপ করতে মানা করতেন। আমাদের পাশের গ্রাম ফকির লালনের ছেউড়িয়া। কিছুটা বাউলিয়ানা আমাদের পরিবারের সকলের মাঝেই ছিল।
৩৯। Every Unspoken word gets poisonous!
এটা আমি মেনে চলি। মনের খুব গহীনে কোন কথা কেউ চেপে রাখতে চাইলে বলি , বলে ফেল। বলে হালকা হয়ে যাও। কিছু মানুষ দেখেছি, এরা কথা পুষে রাখে, সাপের মতো বিষাক্ত হয়ে সেই কথা কবে কখন কাকে ছোবল মারবে সে নিজেও বুঝে উঠতে পারে না !
৪০। ঔদ্ধত্য যদি এক্সট্রিম একটা আচরণ হয়ে থাকে, বিনয়ও এক্সট্রিম একটা আচরণ । বিনয়ী লোকজনকে আধুনিক যুগের লোক পাপোষের মতো মাড়িয়ে চলে যেতে চায়। পিষে ফেলতে চায়। এর চেয়ে মধ্যমপন্থা উত্তম । কিছুটা রহস্য থাকা ভালো। নিজেকে সহজেই পড়ে ফেলতে দেওয়া উচিৎ না। ক্ষেত্রবিশেষে কয়েকজন প্রিয়জন ছাড়া। একটা আবরণ ও রহস্য থাকা ভালো। আমার সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা আমার আবেগ আমার চেহারায় ও চোখে ভেসে ওঠে। আমার বিরক্তি বা ক্ষোভ আমার পাশের জন সহজেই পড়ে ফেলতে পারেন। ম্যানেজমেন্ট মিটিং থেকে শুরু করে কঞ্জুষ ক্রেতা, ঘড়েল ফ্যাক্টরী মালিক, আমার নিজের অফিসের বড়কর্তার সামনে আমার বিরক্তি অন্যরা সহজেই পড়ে ফেলতে পারে। ফলে আমাকে পদে পদে বিব্রত হতে হয়েছে । অথচ আমি জানি নিজের আবেগ লুকিয়ে রাখা বিশাল একটা গুণ।
৪১। স্যার একটা কথা বলতেন, অর্থহীণ বেদনার কোন অর্থ নাই। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বিষাদ আসে জীবনে। বিষন্নতা আছে
প্লেটো অভ ফ্রাস্ট্রেশন! জীবনযাপনের ক্লান্তি আছে! জীবনের ক্ষয় আছে, গতিহীনতা আছে, বাঁধা আছে, ক্লেদ আছে। ওই যে হয় না, মেশিন চললে শুধু প্রোডাক্টই হয় না, তাতে অবধারিতভাবে ধুলো জমে, জং ধরে, গতি কমে যায় আর সাথে সাথে কিছু উপজাত বা বাইপ্রোডাক্ট তৈরী হয়। উপভোগ্য জীবনে সারাক্ষণ প্রাপ্তির পাশে দুই একটা অপ্রাপ্তি সবারই আছে ।সকাল থেকে রাত্রি, প্রাতঃকৃত্য, খাওয়া, হেঁটে চলে কর্মস্থলে আসা– গোটা ত্রিশেক কাজতো ঠিকমতোই হচ্ছে ; এর মাঝে ছোটবড় কোনকাজে বাধা আসতে পারে, আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা থাকতেই পারে, সেটাকে বড়ো করে না দেখলেই হয় !
আমি অনেক আগে এক দক্ষিণভারতীয় সহকর্মীর নোটবুকে লেখা ছিল, It doesn’t matter how many times you fall down, all that matters how quickly you are bounced back. মূলতঃ বিষণ্ণতা ও ক্লান্তি জীবনে অবধারিত। কিন্তু আমাদের চেষ্টা থাকা উচিৎ কতো দ্রুত সেটা থেকে আমরা বের হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনের ফিরে আসতে পারি।
কেন ডিপ্রেসন?
কারণ আপনি একটা কিছু হোক চেয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে না বা করতে পারছেন না। একটা বাঁধা , একটা অবস্টাকল আপনাকে বিষণ্ণ করবে। হতাশ করবে।
কিন্তু এটাওতো সত্যি, যে অনেক কিছু হচ্ছে। সারাদিন এই অফিস, গাড়ীতে চলা, খাওয়া, বাচ্চাদের চেহারার আনন্দ, ভালোবাসা, সবতো হচ্ছে। এই নিঃশ্বাস এই বেঁচে থাকা আশ্চর্য নয়, এখানে হতাশা কোথায়? বিষন্নতা কোথায়?
সায়ীদ স্যার ঠিক এই কথাগুলোই ঘরোয়া এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন। সারাদিন আমাদের ২০টা কাজ হচ্ছে, ধরেন তার ১৯টা কাজই তো সাফল্য। সকালে ওঠা, নাস্তা করা, অফিসে আসা, সব। হ্যাঁ, সারাদিনে একটা কাজে হয়তো আপনি ব্যর্থ হচ্ছেন। সারা দিনটাতো ব্যর্থ নয় তাহলে! সুতরাং জীবনের বেশিরভাগ তাই সাফল্যের, আশাবাদের, ভালোবাসার, আনন্দের।
৪২। নানা মতবাদ পড়ে আমি বিশ্বাস করি, প্রকৃতি ধনীগরীব নির্বিশেষে দুইটি জায়গায় কাউকে বঞ্চিত করে নাই। সবাই সমান। দুইটি নেয়ামত বা প্রকৃতিপ্রদত্ত দান হচ্ছে খাদ্যগ্রহন ও যৌনতা। খাদ্য গ্রহন ও যৌনতার মধ্যেই আমরা আমাদের পরিপূর্ণ তৃপ্তি পেতে পারি। অন্য কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাওয়ার সুযোগ সবার জন্য প্রকৃতি রাখে নাই। খাবার নিয়ে এতো কথা হয়। কী খেলে ভাল, কী খেলে খারাপ অথচ সেই তুলনায় যৌনতা নিয়ে আমাদের কোন কথা হয় না । যৌনতাকে নিষিদ্ধ ভেবে নানা ভুল ধারণা নিয়ে না থেকে সেটা নিয়ে আলোচনা করা উচিৎ । আমি ব্যক্তিগতভাবে তাই মনে করি। কেউ ধর্মীয় বিধিনিষেধের কথা তুলতে পারে। তবুও আমি বিশ্বাস করি, খোলামেলা আলোচনা ভাল।
৪৩। আত্মবিশ্বাস জরুরী। নিজেকে বোঝাটাও জরুরী। নিজের মন সবচেয়ে বড় সহায় বাইরের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। পরিপার্শ্বের ব্যাপারে কিছুটা ভাণ করে হলেও আশাবাদী থাকা উচিৎ। এটা কিছুটা ফ্যান্টাসির মতো মনে হতে পারে। কিন্তু মিছেমিছি দুশ্চিন্তা করার চেয়ে অলীক আশাবাদ অনেক ভাল। কেননা, ঐ আশাবাদ আপনার সমস্ত আচার আচরণ, মনোভাব কে এমনভাবে আচ্ছন্ন করবে যে আখেরে সেটা আপনার জন্য ভাল ফল বয়ে আনবে। বেশিরভাগ মোটিভেশনাল স্পিকার এই ভাণ করার কথাটাই ঘুরে ফিরে সবাইকে বলে। যে কোন পরিস্থিতিতে কেউ যদি নিজেকে বিশ্বাস না করে তবে অন্যেরা কীভাবে তাকে বিশ্বাস করবে। কেউ যদি ত্রস্ত এলোমেলো পায়ে চলে, তাকে অনুসরণ করবে কে। কেউ যদি ভাণ করেও আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে চলে, তবে আরেক পথচারী তাকে অনুসরণ করলেও করতে পারে।
৪৪। দৃষ্টিভঙ্গি বদলালে জীবন বদলাবে। বেশ অনেক বছর ধরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের শ্লোগান। আমি অনেক আগে কোন এক বইয়ে পড়েছিলাম, এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হচ্ছে, কেউ যদি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারে, তবে তাঁর জীবন বদলে যাবে। একই শহরের দুই পথচারীর গন্তব্য আলাদা। একই দৃশ্যপটে দুই ব্যক্তির দুই রকম প্রতিক্রিয়া খুব স্বাভাবিক।
৪৫। কখন থামতে হবে এটা বোঝা আমাদের জীবনের সবচেয়ে জরুরী । কখন শুরু করতে হবে, সেটা আমাদের হাতে থাকে না অনেকাংশে। কিন্তু থামানোটা আমাদের হাতেই থাকে। রাজকুমার হিরানি থ্রি ইডিয়টস-এর পরিচালক এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, প্রত্যেকের বোঝা উচিত, ‘প্রয়োজন’ ও ‘লোভের’ মধ্যে পার্থক্য কী। আপনার জানা উচিত, ঠিক কোন জায়গাতে আপনাকে থামতে হবে এবং এটাও জানা উচিত, ‘আর নয়, বহুত হয়েছে’ কথাটা কখন বলতে হবে। অনিশ্চয়তা আপনাকে খতম করে দিচ্ছে? পৃথিবীর সবেচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তির দিকে তাকান, তিনিও বলবেন, ভয় লাগে, কখন সব শেষ হয়ে যায়! আপনি যদি এই অনিশ্চয়তার ভয় কাটাতে পারেন, তবে সেটাই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।
৪৬। পরিমিতিবোধ, আপনাকে জীবনকে স্বস্ত করবে। কথা বলাতে, লেখাতে সব জায়গায় কম কথায় কিছু প্রকাশ করার ব্যাপারটা আমার শেখার চেষ্টা চলছে আমার প্রিয় লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখা থেকে। আরেকটা ব্যাপার লেখাতে বেশি ব্যাখ্যা না দেওয়ার ব্যাপারটাও তাঁর কাছ থেকেই। পাঠককে বুদ্ধিমান ভাবা উচিৎ। যে পাঠক আপনার ইশারা বুঝবে সেই আপনার আসল পাঠক। যে বুঝবে না, তাকে হাজার পাতার ব্যাখ্যা করে দিলেও বুঝবে না।
৪৭। ‘You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exist.’ Friedrich Wilhelm Nietzsche-এর এই বক্তব্য আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে যৌক্তিক ভাষা মনে হয়।
৪৮। Small Changes make big difference! আমার এক ক্রেতার কাছ থেকে শেখা। ও আমাকে প্রায়ই মনে করিয়ে দিত। ছোট একটা বাক্য, সামান্য একটা হাসি যেমন কারো মনে অনেক পরিবর্তন করে। তেমনি সামান্য একটু অবহেলা, কটু কথা ঠিক উল্টোটা করতে পারে। ভাষা ও কমিটমেন্ট যাই হোক না কেন, কিছুটা সৌন্দর্যের ছোঁয়া থাকা ভাল।
৪৯। যে কোন অস্পষ্টতায়, অজ্ঞতায় প্রশ্ন করুন, জিজ্ঞেস করুন। যাকে জিজ্ঞেস করছেন সে আপনার সহকর্মী হতে পারে, আপনার অধস্তন হতে পারে। আপনার অজ্ঞতায় সে হয়তো আপনাকে সাময়িক নির্বোধ ভাবতে পারে। কিন্তু একবার বোকা হয়ে আপনি সারাজীবনের জন্য কিছু একটা শিখে গেলেন। আর যদি না জিজ্ঞেস করেন তবে সারাজীবনের জন্য বোকাই রয়ে গেলেন। একবার বোকা হওয়া সারাজীবনের জন্য বোকা হয়ে থাকার চেয়ে ভাল।
৫০। ‘There is no set rule’ পরিস্থিতি, ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, যুগ ও প্রযুক্তির প্রভাবে যে কোন একটা নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় প্রযোজ্য নয় অথবা একইভাবে কাজ নাও করতে পারে। এই ব্যাপারটা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেউ বুঝে ফেলে, আবার ঠিক বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেউ ‘একই নিয়ম সব জায়গায় চলবে’ – এই ব্যাপারে ভয়ঙ্কর মৌলবাদী হয়ে পড়ে।
নিয়মের ব্যত্যয়, সংস্করণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন মেনে নেওয়ার ব্যাপারে উদারপন্থা কাম্য। একটি পরিবার যে নিয়মে চলে, পাশের বাসার পরিবার কিছুটা পরিবর্তিত রূপে চলে। এক অফিসে যে নিয়মে চলে, একই রকমের পাশের অফিসে সেই নিয়ম চলে না। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও বহুবিধ তন্ত্র একেক সমাজে, রাষ্ট্রে একেক রূপে থাকবে। অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মাচার, জাগতিক সকল আচার ও নিয়ম স্থান-কাল-ভেদে পরিবর্তিত হয়।
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য আছে বিস্তর। ডেল কার্নেগী অথবা নরমান ভিনসেন্ট পিলের লেখা আপনাকে প্রভাবিত করবে, কিন্তু তাঁদের সামাজিক মূল্যবোধ আর আমাদের মূল্যবোধের পার্থক্য আছে। তারপরেও সারা পৃথিবীর মানুষ যখন অন্তর্জালের বিশাল একটা গ্রামের বাসিন্দা ; সেখানে আশাবাদের যে কোন আহ্বান আমাকে আকৃষ্ট করে , সচকিত করে।
পশ্চিমের বিখ্যাত আশাবাদী লেখক Zig Ziglar বলেছেন—‘ Of course motivation is not permanent. But then, neither is bathing ; but it is something you should do on a regular basis! ’ প্রাত্যহিক হতাশার ক্লেদ ও ক্লান্তি দূর করতে প্রতিনিয়ত আশাবাদী হয়ে উঠুন। শুভকামনা।
প্রকাশকালঃ ১১ই মে, ২০২০ [ ৬ই মে ২০২২, সংস্করণ ]
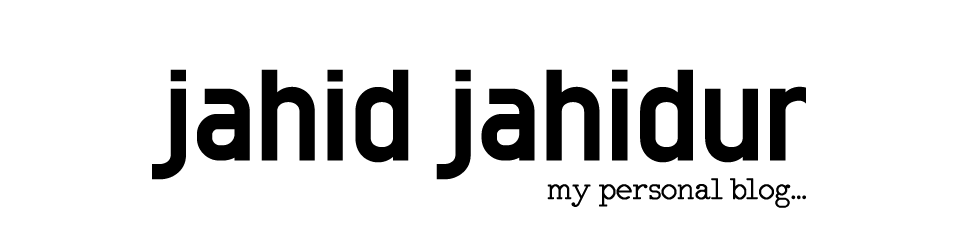
সাম্প্রতিক মন্তব্য