by Jahid | Nov 28, 2020 | দর্শন, সাহিত্য
আমার মুশকিল এই যে , আমি মন্দিরে যখন কিছু বলি তখন নিজেকেই বলি , গুরুর আসনে বসে বাইরের কাউকে বলতে পারিনে। তার ফল হয় যে বলবার কথাগুলো সহজ হয় না। সেইজন্যে আমাকে ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হয়েই কথা কইতে হয়। আমার নিজের কিছু উপকার হয় সন্দেহ নেই—কেননা চিরদিন আমি নিজেকে কথা বলেই শিক্ষা দিয়েছি।
ছয় অগ্রহায়ণ তেরোশো পঁয়ত্রিশ। নিজের কথা।। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠি।
by Jahid | Nov 28, 2020 | দর্শন, লাইফ স্টাইল, সাহিত্য
আমার বোধ হচ্চে সায়ান্সে চিঠিলেখার পাঠই একেবারে উঠিয়ে দেবে—যাকে আজ চিঠি লিখতে হয় সেদিন তাকে তার আওয়াজসুদ্ধ একেবারে সামনে হাজির করে দেবে। কিন্তু সে হলে কি ভালো হবে ?
নয় অক্টোবর উনিশশো আঠাশ। নিজের কথা।। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠি।
by Jahid | Nov 28, 2020 | দর্শন, শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহিত্য
মানুষ চায় তার সৃষ্টিকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে সম্প্রসারিত করে দিতে। এই জন্যই শিক্ষাদানের রীতি প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু পরিচিত জ্ঞানকে হস্তান্তর করার, বা শিক্ষাদান ব্যাপারটির, কোনো বিশেষ স্বয়ংসম্পূর্ণ তাৎপর্য নেই; এর তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করে নিজের সৃষ্টিকে মানুষ ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট কতটা গুরুত্বের সঙ্গে পৌঁছে দিতে চায় তার ওপর। ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে কী হস্তান্তর করতে হবে, তা নির্ধারিত হয় সৃষ্টির মূল্যের দ্বারাই, অর্থাৎ যে-সৃষ্টি যথার্থই মূল্যবান তাই মানুষ পৌঁছে দিতে চায় ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে। শিক্ষকতার কাজটি সাধারণত শৈল্পিক কাজ বলে গণ্য হয় না। শৈল্পিক কাজের গুরুত্ব যথার্থভাবেই আরোপিত হয় সৃষ্টির ওপর—যাকে বলা হয় শিল্পসৃষ্টি।
শৈল্পিক (এবং বৈজ্ঞানিক) সৃষ্টি তাহলে কী?
শৈল্পিক (এবং বৈজ্ঞানিকও) সৃষ্টি হচ্ছে এমন একটি মানসিক ক্রিয়া যা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধ অনুভূতিকে (বা চিন্তাকে) এমন স্পষ্টতার মধ্যে নিয়ে আসে যে, সেই অনুভূতি বা চিন্তা অন্য মানুষের মনের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে।
সৃষ্টির প্রক্রিয়া যেহেতু মানুষের মধ্যেই বর্তমান, সুতরাং আমরা প্রত্যেকেই অন্তরের অভিজ্ঞতা দ্বারা তা উপলব্ধি করতে পারি; তার সংঘটন বর্ণনা করা যায় এ-ভাবে: কোনো ব্যক্তি হঠাৎ হয়তো এমন কিছু কল্পনা বা অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে বসেন যা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নতুন, অপরিচিত ও অশ্রুত বলে মনে হয়। এই নতুন বিষয়টি তাঁর মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তিনি সেই উপলব্ধিকে সাধারণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অন্যের নিকট তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রয়াসের এক পর্যায়ে বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি দেখতে পান, যা তাঁর কাছে স্পষ্ট তা তাঁর শ্রোতাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও নতুন। তিনি তাঁদের কাছে যে-বিষয়ের কথা বলেন তা তাঁরা সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেন না। অন্যদের থেকে এই বিচ্ছিন্নতা বৈসাদৃশ্য, বা যাকে বলা যায় অমিল—তা প্রথমে তাঁকে পীড়া দেয় এবং নিজের উপলব্ধির সত্যতা আরও গভীরভাবে যাচাই করে ঐ ব্যক্তি পুনরায় চেষ্টা করেন, তিনি যা দেখেছেন, অনুভব করছেন কিংবা উপলব্ধি করছেন তা অন্য কোনো উপায়ে অন্য মানুষদের কাছে প্রকাশ করতে। কিন্তু দেখতে পান, এই লোকেরাও তাঁর ঈপ্সিত বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে পারছেন না, কিংবা তিনি তা যে-ভাবে উপলব্ধি বা অনুভব করেছেন সে-ভাবে তাঁরা তা উপলব্ধি করতে পারছেন না, কিংবা তিনি তা যে-ভাবে উপলব্ধি বা অনুভব করেছেন সে-ভাবে তাঁরা তা উপলব্ধি বা অনুভব করেন না। তখন ঐ ব্যক্তি এমন ধরনের একটি আত্মসন্দেহের দ্বারা পীড়িত হন যে, হয় তিনি যা কল্পনা করছেন বা অস্পষ্টভাবে অনুভব করছেন তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই, নতুবা বাস্তব অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও অন্যেরা তা দেখতে কিংবা অনুভব করতে পারছেন না। এই সন্দেহের অবসানকল্পে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করেন তাঁর আবিষ্কারকে এমন স্পষ্টতা দান করতে যেন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করেন তাঁর আবিষ্কারকে এমন স্পষ্টতা দান করতে যেন তাঁর উপলব্ধ বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর নিজের কিংবা অন্য কারও কোনো সন্দেহ না থাকে। যখন এই স্পষ্টতাদান সমাপ্ত হয় এবং ঐ ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, তিনি যা দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন, বা অনুভব করেছেন, তার অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ, তখনই দেখা যায় অন্যেরা তা তাঁরই মতো করে উপলব্ধি এবং অনুভব করতে পারছেন। তাঁর কাছে ও অন্যদের কাছে যা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য ছিল তাকে নিজের ও অন্যদের কাছে স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত করার এই প্রয়াসই হলো মানুষের আত্মিক সৃষ্টিপ্রবাহের সাধারণ উৎস। আমরা শিল্পকর্ম বলে যাকে অভিহিত করি—যা মানুষের মনের দিগন্তকে সম্প্রসারিত করে এবং ইতিপূর্বে অনুভূত ও অগোচর বিষয়কে মানুষের অনুভূতি ও গোচরের মধ্যে নিয়ে আসে—তারও উৎস এই প্রয়াস। (অংশ)
আবুল কাসেম ফজলুল হক অনূদিত
সূত্র: লিয়েফ্ তলেস্তায় প্রয়াণ-শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ/ সংকলন ও সম্পাদনা: হায়াত্ মামুদ (বাংলা একাডেমি, ২০১৩)
by Jahid | Nov 28, 2020 | ছিন্নপত্র, দর্শন, লাইফ স্টাইল
মনে করুন, এই মুহূর্তে আপনার জীবনে পাঁচ ছয় রকমের সমস্যা আছে। আপনার চাকরির ক্যারিয়ার বা ব্যবসা ; পরিবারের ভবিষ্যৎ, আপনার স্বাস্থ্য, পারিবারিক সম্পর্ক, দেশের অসহনীয় পরিস্থিতি।
ধরুন, আপনার চাকরি বা ব্যবসা একটা সহনীয় পর্যায়ে আছে । আপনার সামনে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে পরিবারের নিরাপদ ভবিষ্যৎ। ধরে নিলাম সঞ্চয়-টঞ্চয় করে কোনভাবে আপনার মনে হল পরিবারের ভবিষ্যৎ হয়তো আপনি মোটামুটি একটা শেপে নিয়ে এসেছেন ।
সেটা হলে, এরপরেই আপনি চিন্তিত হয়ে উঠবেন আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে।
স্বাস্থ্য একটা পর্যায়ে আসলে আপনি চিন্তায় পড়ে যাবেন দেশের পরিস্থিতি নিয়ে।
‘প্রকৃতি শূন্যতা পরিহার করে!’ ঠিক এই সূত্রের মতই আপনার বিরাজমান সমস্যাগুলোর একেকটি একেক সময়ে প্রাইয়োরিটি পাবে। একটা কোন রকমে সাইজ করতে না করতেই, আরেকটি বড় হয়ে দেখা দেবে।
সবকিছু গুছিয়ে ফেললে আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে বার্ধক্য ও মৃত্যু !
বেঁচে থাকলে প্রতি মুহূর্তে বিদ্যমান সমস্যার একেকটি মূর্তিমান আতংকের মতো আপনাকে কাবু করে ফেলার চেষ্টা করবে। কীভাবে আপনি সমস্যাগুলোকে ব্যালান্স করে চলবেন ; কোন্ সমস্যায় উদ্বিগ্ন হবেন, আর কোনটাতে হবেন না, সেটাই একটা শেখার ব্যাপার। আমি প্রতিনিয়ত শিখে চলার চেষ্টা করছি। সবার জন্য শুভকামনা।
by Jahid | Nov 28, 2020 | ছিন্নপত্র, দর্শন, সমাজ ও রাজনীতি
1.The freethinking of one age is the common sense of the next.( Mathew Arnold)
2.Education’s Purpose is to replace an empty mind with an open one.(Malcolm Forbes)
3.It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.(Aristotle)
4.I never teach my pupils, I only provide the conditions in which they can learn.( Albert Einstein)
5.Don’t limit a child to your own learning, for he was born in another time.( Rabindranath Tagore)
6.I am a part of everything that I have read.( Theodore Roosevelt )
7.Poor is the pupil who does not surpass his master.( Leonardo da Vinci)
8.If I were again beginning my studies, I would follow the advice of Plato and start with Mathematics.(Galileo Galilei)
9.Education is the most powerful weapon which you can use change the world.(Nelson Mandela)
প্রকাশকালঃ ১০ই জুন, ২০১৭
by Jahid | Nov 28, 2020 | দর্শন, লাইফ স্টাইল, সাম্প্রতিক
কিছুদিন আগে , ২০১৩ সালের একটা স্ট্যাটাস রিপোস্ট করেছিলাম প্রবাস জীবন নিয়ে ।
কেন জানি না , কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মর্মাহত হয়েছেন। কেউ অবলীলায় বলেছে ‘ আঙুর ফল টক’ বলেই নাকি আমি প্রবাস জীবনের সীমাবদ্ধতাগুলোকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়েছি। প্রারম্ভিক ক্ষমা প্রার্থী হওয়া স্বত্বেও আমার লেখায় বিদ্রূপ ও বিদ্বেষের ছোঁয়া পেয়েছেন তাঁরা !
এটাও সত্যি সংখ্যালঘু অনেকেই প্রবাস জীবন বেছে নেওয়ার পরে আবার দেশে ফিরে আসতে চান ; কিন্তু পেরে ওঠেন না । কেন পারেন না , সেটা নিয়ে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন ঘনিষ্ঠের সঙ্গে।
মূলত: অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আমাদের আগের কয়েক প্রজন্মের প্রবাস মুখী হওয়ার মূল কারণ । নতুন করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বাঁধাগুলো আমার দৃষ্টিতে নীচের কয়েকটি ; বিদ্বজ্জনেরা আরো কিছু বের করতে সমর্থ হবেন।
১। একবার উন্নত বিশ্বের দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে নতুন করে বাংলাদেশের অশ্লীল, কদর্য পুতিগন্ধময় পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া কঠিন । যতো দেশপ্রেমের কথাই বলি না কেন, প্রতিনিয়ত নানা অদ্ভুতুড়ে প্রতিকার হীন সামাজিক ব্যাধি ও অন্যায়ের মুখোমুখি হয়ে স্নায়ুক্ষয় করা ছাড়া উপায় থাকে না। আমার অনেক চিকিৎসক ও প্রকৌশলী বন্ধু যাঁদের গায়ে আওয়ামীলীগ ও বিএনপির গাঢ় সীল নেই ; নিতান্তই রাজনীতি বিমুখ –তাঁদের কয়েকজন ছেড়ে গেছেন প্রশাসনের সহ্যাতীত অবিবেচনার জন্য। এমন না যে , তাঁরা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। কিন্তু, তাঁরা ভেঙ্গে পড়েছিলেন ক্রমাগত অন্যায় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ না করতে পারার মনোবেদনায়।
২। পরের সর্বগ্রাসী যে বিষয়টি আমাদের মেধাবী ও অমেধাবী সবাইকে ঠেলে দেয় পশ্চিমের দিকে তা হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। পশ্চিমাদেশের তুলনায় আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা শতভাগের একভাগও নয়। একবার সেই নিরপত্তায় অভ্যস্ত হয়ে গেলে তার মায়া কাটানো মুশকিল।
৩। আমাদের জীবনের অনিশ্চয়তা ছিল, আছে এবং থাকবে । নিতান্ত নির্বোধ ছাড়া আর সকলেই অনিশ্চয়তায় ভোগে। জীবনের অনিশ্চয়তার কাটানোর অলীক কল্পনা আচ্ছন্ন করে রাখে প্রবাসীদেরকে। তাঁদের ধারণা হয়, তাঁদের জীবনের অনিশ্চয়তা অনেক কমিয়ে ফেলেছে পশ্চিমা দেশ। তবে এই অনিশ্চয়তার প্রভাব বেশি দেখা যায় আমাদের উচ্চ-মধ্যবিত্তদের মধ্যে।
৪। প্রথম প্রজন্মের মেধাবী অনেকেই তাঁদের অর্জিত ডিগ্রী ও মেধা নিয়ে ফিরে আসতে চান দেশে। কিন্তু তাঁদের মেধা প্রয়োগের বাস্তবিক কোন সুযোগ থাকে না। কেউ কেউ , বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে তাঁর মেধার কিছুটা বিলিয়ে যেতে পারেন। অন্যদের বাধ্য হয়েই পশ্চিমাদেশের শিক্ষায়তনে ও ইন্ডাস্ট্রিতে দিনাতিপাত করতে হয়।
৫। দ্বিতীয় প্রজন্মকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব ও অমানবিক ।কেউ একটা দেশে জন্মে সেখানে তাঁর কৈশোর কাটিয়ে ফেললে সেটি তাঁর সারাজীবনের স্মৃতি কাতর মাতৃভূমি হয়ে যায়। একটা শিশুর হয়তো স্বদেশ পরিবর্তনে কিছুই যায় আসে না। সে নতুন ভাষা ও কৃষ্টি সংস্কৃতিতে দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু একটা কিশোর বা কিশোরীর বেড়ে ওঠার সময়ে মন দৈহিকতায় পরিপার্শ্বের সবকিছুর ছাপ চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে। লন্ডন, সিডনী, নিউইয়র্ক যাই বলি না কেন, সেখানে বেড়ে ওঠা কাউকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার প্রশ্নই আসে না ! আমার কাছে সেটি বড্ড অমানবিক মনে হয়।
আমার কয়েকজন আত্মীয়পরিজনদেরকে দেখেছি, দেশে ফিরে তাঁরা হয়তো পুনরায় কোন না কোনভাবে আমাদের ধুলাবালিতে অভ্যস্ত হতে পেড়েছেন। মশার কামড়ে তাঁদের তেমন কিছু হচ্ছে না ; কিন্তু প্রবাসে জন্ম নেওয়া বা শৈশবেই চলে যাওয়া শিশু-কিশোরের বাংলাদেশের ধূলায়, লোডশেডিং , ট্রাফিক জ্যামে আর মশার কামড়ে প্রাণান্ত হয়। দেখে মায়া লাগে।
৬। আরেকটি প্রকট বা প্রচ্ছন্ন কারণ আছে। সেটা আমার বেশ কয়েকজন প্রবাসী সতীর্থের সংগে অন্তরঙ্গ আলোচনার উপলব্ধি । আসলে শিক্ষিত বাঙালী মেয়েরা বিয়ের পর নিজের স্বামী সন্তানদেরকেই নিজের পৃথিবী মনে করে। সামাজিকতায় অভ্যস্ত হয়ে, স্বামীর কর্মস্থল যে জেলাতেই হোক, যে দেশেই হোক আপন করে নেয়। তারপরেও প্রবাস জীবনে একাকীত্বের সঙ্গে অবাধ স্বাধীনতা ও মুক্তির স্বাদ থাকে। ছোট্ট নিউক্লিয়াস পরিবারের স্বামীকে দিনে ঘন্টাখানেক সময়, আর বাচ্চাকে কিছুক্ষণ সময় দিলে বাকী সময় একান্ত নিজের ।
ঠিক উল্টোটা বাংলাদেশে। নিজের স্বামী-সন্তান- সংসারের পাশাপাশি, শ্বশুর- শাশুড়ি, দেবর- ননদ, ভাশুর- ভাবী, স্বামীর মামাতো, চাচাতো খালা-মামা-চাচা-ফুফু ; নাই নাই করেও গুচ্ছের বিশাল একটা জনগোষ্ঠীকে সময় দিতে হয় , ম্যানেজ করে চলতে হয়। পাশাপাশি থাকে পারিবারিক রাজনীতি ও কূটকচাল।
শিক্ষিত বাঙালী প্রবাসী গৃহবধূদের শতভাগ তাই দেশে ফিরে নতুন করে বসবাসে সবচেয়ে বড় অনিচ্ছার কারণ হয়ে পড়েন।
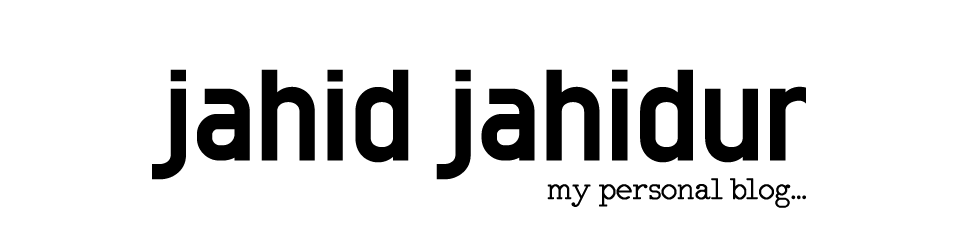
সাম্প্রতিক মন্তব্য