by Jahid | Nov 29, 2020 | কর্পোরেট অবজার্ভেশন
Sustainability, Sustainable Growth Rate, Organic Growth টেকসই বৃদ্ধি, টেকসই প্রযুক্তি কথাগুলো শুনছি ২০০৭-৮ এর বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার পর থেকে। তার আগে এই শব্দগুলো আমার কান পর্যন্ত পৌঁছায়নি । আমার প্রাথমিক শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগে । পদার্থ , রসায়ন, গণিতের চক্র পেরিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং। তারপরে ঘুরে ফিরে দেশের বৃহত্তম রপ্তানীমুখি বস্ত্রশিল্পের কেরানী !
টেকসই বৃদ্ধি কি , কেন , কিভাবে– সেটা একজন অর্থনীতিবিদের কাছ থেকে শোনার আকাঙ্ক্ষা আছে আমার। সে রকম কাউকে পাচ্ছি না আশে পাশে। কিন্তু আমি আমার অত্যল্প অভিজ্ঞতা দিয়ে , পরিপার্শ্ব দিয়ে, যেটুকু বুঝতে পারছি ,বোঝার চেষ্টা করছি– সেটা সবার সঙ্গে আলোচনা করতে দোষ কি !
আশা করছি এই আলোচনা চোখে পড়লে আমার বন্ধু তালিকার কেউ না কেউ বিষয়টিকে আরো জলবৎ তরল করে দিতে পারবেন।
ব্যবসায় টিকে থাকার অন্যতম প্রধানতম শর্ত হচ্ছে ব্যবসা-বৃদ্ধি। প্রতিবছর ব্যবসা বৃদ্ধির টার্গেট থাকতে হবে, সেটার অ্যাচিভমেন্ট থাকতে হবে। মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিবছর উৎপাদন বাড়তে হবে, কর্মচারীর বেতন সুবিধা বাড়াতে হবে ; পরিশেষে মালিকের মুনাফা বাড়তে হবে। এটি এতোই সহজবোধ্য একটা ব্যাপার, যে এই তত্ত্বের আর কোন বিকল্প থাকতে পারে, সেটা নিয়ে আমাদেরকে কেউ ভাবতে বলে নি। আমরা ভাবিও না ! শোনাকথা যেটুকু জানি, সাধারণত: ২০ থেকে ৩০ ভাগ ব্যবসা বৃদ্ধির টার্গেট থাকে মালিক-পক্ষের। তবে ১০ থেকে ১৫ ভাগ বৃদ্ধি হলেই বোঝা যায়, ব্যবসা লাভজনক রাস্তায় আছে। ব্যবসা বৃদ্ধির যথোপযুক্ত পন্থার সঙ্গে সঙ্গে গত কয়েকবছরে আরো কিছু শব্দের সঙ্গে আমি পরিচিতি হয়েছি। Breakeven , Depreciation Cost, Asset, Equity, Liability, Profit Margin, Business Expansion ইত্যাদি ইত্যাদি।
টেক্সটাইল ফ্যাক্টরী থেকে গার্মেন্টসে এসেছি প্রায় দেড়যুগ। গত আঠারো বছরে নানা মাপের গার্মেন্টস মালিকের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। অনেকেই আমাকে তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অনেককে ছোট একটা কারখানা থেকে বৃহদায়তন কারখানায় উন্নীত হতে দেখেছি। গুটিকয়েক আছেন , যারা সুযোগ থাকা স্বত্বেও একটা নির্দিষ্ট আয়তনের বেশী উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ান নি।
দেড়যুগ আগেও গার্মেন্টস ব্যবসার লাভ চোখে পড়ার মতো ছিল। ১টি আমেরিকান ডলার বাংলাদেশের ব্যাংকে এসেই সেটা ৭০ গুন ৮০ গুণের টাকায় পরিণত হতে দেখে উদ্যোক্তার এগিয়ে এসেছেন। পর্যাপ্ত সস্তা শ্রম , গ্যাসের সাপ্লাই, জমি, পানির সহজলভ্যতা আমদের দেশে আছে বলেই নানাধরনের উদ্যোক্তারা তাঁদের পুঁজি ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এই শিল্পে অংশ নিয়েছেন। বছর শেষের লাভের উদ্বৃত্ত টাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কারখানার মালিকরা তাঁদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছেন। বাড়াতে বাড়াতে কেউ কেউ এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন ; এখন তাঁরা না পারছেন সেটা গিলতে না পারছেন উগরাতে !
তাজরিন ফ্যাশানের ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ও রানা প্লাজার ট্র্যাজেডি আমাদের পুরো গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিকে খোলনলচে বদলে দিয়েছে। ছোট মাপের যে কারখানাগুলো বিভিন্ন মার্কেটের শেয়ার বিল্ডিং এ ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেছে ACCORD , ALLIANCE –এর ধাক্কায়। মাঝারি মাপের ( ৬ থেকে ১২ লাইনের) কারখানাগুলোকে অগ্নি নির্বাপণ, বিল্ডিং স্ট্রাকচার ও বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হয়েছে। এতে করে ছোটদের যদি ৭০ লক্ষ থেকে ১ কোটি বাড়তি খরচ লেগে থাকে বড়দের লেগেছে আরো অনেক অনেক বেশী।
ট্রাজেডি হচ্ছে, এতো কিছু করার পরেও ক্রেতাদের মনরক্ষা করা যাচ্ছে না। বৈশ্বিক চাহিদার পতন ( কয়েকবছরে বিশ্বজুড়ে টেক্সটাইল পণ্যের বিক্রয় প্রায় ৪% কমে গেছে) , ক্রেতাদের অন্তঃর্বতী প্রতিযোগিতা , বিশ্ব-মন্দা ; নানাবিধ কারণে ইউরোপ , আমেরিকায় গার্মেন্টস-এর খুচরা মূল্যের দরপতন হয়েছে। এবং সেটার মাশুল দিতে হচ্ছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পকে। জীবনযাত্রার মূল্য ও মান বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি আবশ্যকীয়। গার্মেন্টস-এর মূল উপাদান কাপড় ও অ্যাকসেসরিজ। বিশ্বব্যাপী গ্রিন আন্দোলনের ফলে চীন অনেক রঙ উৎপাদনের কারখানায় বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ফলে সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম গেছে বেড়ে। অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যেরও দাম বেড়েছে একই সঙ্গে। এর প্রভাবে উৎপাদিত কাপড় ও আমদানি করা কাপড়ের দাম ঊর্ধ্বমুখি । শেষের কয়েক সিজনে এতো মন্দ সংবাদের ভিতরে একমাত্র সুসংবাদ ছিল সুতার দামের স্থিতাবস্থা। সুতার সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা লম্ফঝম্প করতে পারছিলেন না ; কারণ বিশ্বব্যাপী তুলার দাম কমতির দিকে। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহে হুট করে কটন সুতার দাম ১০~ ১৫% বেড়ে গেছে। যার যুক্তিসঙ্গত কারণ কি ,সেটা কেউ বলতে পারছেন না !
মোদ্দা কথা গার্মেন্টস শিল্প প্রাথমিক বছরগুলোতে যে পরিমাণ লাভ করতে পেরেছে এখন তা করতে পারছে না ! কিন্তু আমাদের মালিকেরা এমনভাবে তাঁদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন ও করে চলেছেন যে তাঁদের বিশাল কারখানাগুলোকে টিকিয়ে রাখতে হলে খুব সস্তা দরের কাজ হলেও করতে হচ্ছে। খুচরা বিক্রয় মূল্যের সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে , প্রাইস কোটেশন কোনভাবেই মিলাতে পারছেন না কেউ। এখন আমাদের সবাইকে নজর দিতে বলা হচ্ছে , অপচয়ের পরিমাণ কমিয়ে, কর্মদক্ষতা বাড়িয়ে, প্রোডাক্টিভিটি বাড়িয়ে নিজেদেরকে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার চেষ্টা করতে।
আগের কথায় আসি ; যেহেতু আমাদের বস্ত্র-খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি আজকের আলোচ্য । গত তিন দশকে আমাদের বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা Sustainable Growth Rate-এ হয়েছে নাকি সেটা বা Organic Growth ছিল? এটা কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ। ১৫ বছর আগে যে মালিককে বলতে শুনেছি যে , তিনি ১২ লাইনের বেশী কারখানা বাড়াবেন না– পরে সেই মালিককেই দেখেছি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ১০০ লাইনের গার্মেন্টস করতে! আর উচ্চ-সুদে মুফতে পাওয়া মুদ্রার তারল্য নিয়ে বিপাকে পড়া ব্যাংকাররা আরো বেশী উচ্চ-সুদে মালিকদেরকে শিল্প ঋণ দিয়েছেন। মালিকরাও সহজলভ্য ঋণ পেয়ে নিজেদের Asset তো বাড়িয়েছেন, একই সঙ্গে বাড়িয়েছেন তাঁদের Liability !
২০১৪-১৫ সালে শীতবস্ত্রের বড় একটা পরিমাণ বাংলাদেশ থেকে চীনে সরে যায়। আমাদের সোয়েটার কারখানার মালিকরা হতবাক ! ম্যানুয়াল মেশিনের সোয়েটারে আমরা বিনা প্রতিযোগিতায় বেসিক অর্ডারগুলো করছিলাম। একই সঙ্গে প্রায় শতকরা আশি ভাগ মালিক জার্মান , জাপানি ও চীনের জ্যাকার্ড মেশিন নিয়ে এসে নিজেদের সক্ষমতা বাড়িয়েছেন। এতো কিছুর পরেও দেখা গেল, চীনের কিছু কারখানা আমাদের চেয়েও ৩০% বা ৫০% কম সিএম( Cutting & Making) দিয়ে অর্ডার নিয়ে গেছে। বাজারের খোঁজ (Market Information) থেকে দেখা গেল, চীনের কিছু এলাকার মালিকরা হয়তো নিজের পুঁজি ও ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ে কারখানা করেছেন। সেটা একটা নির্দিষ্ট উৎপাদন ক্ষমতার । বছর তিনেকের ভিতরে তাঁদের নিজের পুঁজি ও ঋণ Breakeven-এ পৌঁছে গেছে। তাঁদের জ্যাকার্ড নিটিং মেশিনগুলোর Depreciation/ অবচয় এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সে যদি শুধুমাত্র শ্রমিকের খরচ ও বিদ্যুৎ খরচ হিসাব করে তাঁর সিএম মূল্য খুবই কম দাঁড়ায়। অন্যদিকে আমাদের মালিকের মাথার উপরে আছে ১২ থেকে ১৮% সুদের ব্যাংক ঋণ। আমাদের কস্টিং চীনের ওই সব কারখানার কাছে মার খাচ্ছে। এবং গত কয়েকবছরে আমাদের সোয়েটারের সিএম কস্টিং হু হু করে নীচে নামাতে বাধ্য হয়েছি আমরা।
ব্যাংকার বন্ধুর সাথে কথা বলে যা বোঝা গেল, তাঁরা উদ্যমী মালিকদের উৎসাহ দিয়ে থাকেন, কারখানার ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করার জন্য। একই সঙ্গে মালিকদের ও ব্যবসার নিজস্ব কতগুলো সীমাবদ্ধতা আছে, যেখানে কারখানার ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা ছাড়া উপায় থাকে না।
প্রথমত: মুনাফার টাকার সঙ্গে ঋণের সহজলভ্যতা যোগ করে আমাদের মালিকদের পক্ষে হুট করে কারখানার ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা তেমন দুঃসাধ্য কিছু নয়। তাই, কারখানা Breakeven মূল্যে পৌঁছানোর আগেই তাঁরা আরো বেশী ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ধারণক্ষমতা বাড়িয়ে বসেন। তা ছাড়া এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা গার্মেন্টস। দ্বিতীয় কোন বিকল্প শিল্প নেই , যেখানে তাঁরা নিশ্চিন্তে ইনভেস্ট করতে পারেন।
দ্বিতীয়ত: অনেক ক্রেতাই কারখানা মালিকদের আরো বেশী উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য যুক্তিসংগত ও অযৌক্তিক উৎসাহ দিয়ে থাকেন। কিছু ক্রেতা আছে, যারা বড় কারখানা ছাড়া কাজ দিতে চায় না। বেশী লাভের আশায় মালিকরা তাঁদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেন।
তৃতীয়ত: একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে, ম্যানেজমেন্টের Overhead Cost নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে যায়। যে ধরণের মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট দিয়ে একটা ১২ লাইনের কারখানা চালানো যায় ; ঠিক সেই একই ম্যানেজমেন্ট দিয়ে ৩০ লাইনের কারখানা চালানো যায়। Overhead Cost একই রেখে শুধু মেশিন আর অপারেটর বাড়ালেই চলে। এই ব্যাপারটি অনেক মালিককে উদ্বুদ্ধ করে অপ্রয়োজনীয় উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে।
চতুর্থত: মালিক-পক্ষ চূড়ান্ত লাভক্ষতির হিসাব দূরে থাক ; নিজের সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে নজর না দিয়ে শুধুমাত্র উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে একটা লোভ কাজ করে। সামাজিক অবস্থানের একটা ব্যাপার স্যাপারও আছে, কে কতো বড় কারখানার মালিক ইত্যাদি ! অনেকাংশে দেখা যায়, মালিক যে দক্ষতার সঙ্গে ২০ লাইনের কারখানা চালাচ্ছেন। উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়ে গেলে , তিনি তাঁর মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে সেটা ম্যানেজ করতে হিমসিম খান। ফলশ্রুতিতে কারখানা অলাভজনক হয়ে যায় এবং সস্তা দরের কাজ করতে বাধ্য হন তিনি। অথবা ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে নিতান্তই আইনি ঝামেলা এড়াতে কারখানা চালিয়ে যান।
আমাদের শিল্পমন্ত্রী স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, ২০২১ সাল নাগাদ ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি-মুখী করার ব্যাপারে। আমাদের নিজেদের দক্ষতা, চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা, রাস্তা ঘাট, বিদ্যুৎ, গ্যাসের পর্যাপ্ততা আছে কিনা সেটা যাচাই-বাছাই করা জরুরী। যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, যতোদিন যাবে আমরা বেশী মূল্যের গার্মেন্টস করব। আমাদের উচ্চমূল্যের / High End Garment Product তৈরি একটা বড় ভূমিকা রাখবে ৫০ বিলিয়নের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে। তাছাড়া, সকল বড় কারখানার মালিকরাই, এখন অত্যাধুনিক মেশিন নিয়ে উৎপাদন বাড়াচ্ছেন। সকলেই অপচয় কমানোর দিকে নজর দিয়েছেন। ERP, Lean Method, Industrial Engineering প্রয়োগ করে সবাই কর্মদক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন।
সবকিছুর পরে, ২৭-২৮ বিলিয়নের রপ্তানি ১০~ ১৫% Organic Growth ধরে যদি ৪০ বিলিয়নেও পৌঁছায়, তাতেও আমাদের এই জনবহুল বাংলাদেশের আগামী কয়েক দশক বেশ ভালোই কাটবে।
শেষ করার আগে এই সেক্টরের এক বড়ভাইয়ের প্রয়োজনীয় রসিকতা মনে পড়ে গেল। সেই বড়ভাই আমাকে বলছিলেন, ‘শ্রমিকদের যে রকম নানা ধরণের ট্রেনিং দেওয়া হয়। সময় হয়েছে আমাদের কারখানার মালিকদেরকে বিশেষ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা!’
প্রকাশকালঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
by Jahid | Nov 29, 2020 | কর্পোরেট অবজার্ভেশন
পৃথিবীর আর সব সাধারণ শ্রেণিবৈষম্যের মতই কর্পোরেট জগতেও ক্ষমতাবান, মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ও ক্ষমতাহীন শ্রেণি আছে। আমাদের তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতি অনুযায়ী ক্ষমতাবানদের সীমিত কয়েকজন ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার করেন এবং বেশির ভাগ ক্ষমতাবানেরা সুযোগ পেলেই অপব্যবহার করেন।
যে কোন কারণেই হোক না কেন, ক্ষমতাবানদের ব্যাপারে ক্ষমতাহীনদের একটা চিরস্থায়ী ঈর্ষা কাজ করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ঠিক যে যে কাজগুলো আপাত: দৃষ্টিতে তাদের কাছে দৃষ্টিকটু অসহনীয় মনে হচ্ছে ; কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া- আমি নিশ্চিত ক্ষমতা পেলে ক্ষমতাহীন ব্যক্তিটি ওই একই কাজগুলো অবলীলায় করবে! এটা একটা চক্রের মতো, ‘যে যায় লংকায় সেই হয় রাবণ ’- টাইপ আর কী!
ক্ষমতাহীনের সান্ত্বনার জায়গা হচ্ছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করা বা অভিসম্পাত দেওয়া যাতে ক্ষমতাবানদের মধ্যে যারা অহংকারী , আস্ফালনকারী ছিল , তাঁরা খুব দ্রুত কোন একদিন যেন ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। প্রার্থনা করে এবং তাঁদের জীবদ্দশায় সেটা দেখে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আসলে এ ছাড়া ক্ষমতাহীনদের আর বেশী কিছু করারও থাকে না। ফিদেল ক্যাস্ট্রোকে ৬৩৮ বার হত্যা-প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি ৫০ বছরে শাসনের শেষে ২০০৮ সালে অবসরে যান। পরবর্তীতে ৯০ বছর বয়সে গত ১৬ সালের নভেম্বরে বার্ধক্যজনিত কারণে স্বাভাবিক মৃত্যু।
ক্ষমতাহীনের প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা দেখে আমার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহুল পঠিত ও আলোচিত ‘দেবদাস’ উপন্যাসের কথা মনে পড়ে। উপন্যাসে ট্র্যাজেডির নায়ক দেবদাস। প্রধান নায়িকা একদিকে পার্বতী অন্যদিকে চন্দ্রমুখী । আমার দৃষ্টির প্রক্ষেপণ এঁদের মধ্যে প্রেমের ক্ষমতা কার বেশী ছিল সেই দিকে নয়। সেটা বহুবার কলেজ ,বিশ্ববিদ্যালয় ও নানা ভাষার সিনেমার পর্দায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। আমি বরং আমার পাঠককে কর্পোরেট দুনিয়ার ক্ষমতাহীনের আকাঙ্ক্ষা ও তার পরিণতি নিয়ে কিছু কথা বলি।
বিচ্ছেদের সময়ে পার্বতী দেবদাসকে বলেছিল, তাঁকে ছাড়া সে বাঁচবে না। পার্বতী ও চন্দ্রমুখীর ত্রিভুজ প্রেমে ত্রিশঙ্কু হয়ে বেচারা দেবদাসের মর্মন্তুদ মৃত্যু হয়। তাঁর অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা আর অতিরিক্ত মদ্যপান। আর হ্যাঁ , পার্বতীও বাঁচেনি ! সম্ভবত: পার্বতী মারা গিয়েছিল, আশি বছরের অশীতিপর বৃদ্ধা হয়ে, গুচ্ছের সন্তানাদি ও নাতি নাতনি রেখে !
কি মনে করে, বহুদিন পরে উপন্যাসটাও একটু নেড়ে চেড়ে দেখলাম। উপন্যাসের শেষে শরৎচন্দ্রের কয়েক লাইন পাঠককে স্তব্ধ করে দেয়ঃ
“এখন এতদিনে পার্বতীর কি হইয়াছে, কেমন আছে জানি না। সংবাদ লইতেও ইচ্ছা করে না। শুধু দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়। তোমরা যে-কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হোক, যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহকরস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে-যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও একফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।”
পাঠকের মনোবাসনা পূর্ণ হতো যদি, দেবদাসের সঙ্গে সঙ্গে বা কাছাকাছি সময়ে পার্বতীরও মৃত্যু হোত।
সেটা আসলে হয় না। হয় না বলেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবদাস এতো জনপ্রিয়। পার্বতীর সমস্ত জীবনের রঙ রূপ রস ভোগ করে বৃদ্ধা হয়ে মৃত্যুর মধ্যে মহিমা নেই ; নেই সাধারণ পাঠকের বা জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।
আমাদের কর্পোরেট পৃথিবীতে ক্ষমতাধর কেউ কেউ থাকেন। তাঁদের ক্ষমতা , বৈধ-অবৈধ বিপুল সম্পত্তির প্রাচুর্য নিয়ে অনেকের ঈর্ষা আর কানাঘুষা থাকে। তাঁদেরকে ক্ষমতাহীনরা পছন্দ করেন না সঙ্গতঃ কারণে। আকাঙ্ক্ষা করেন, প্রার্থনা করেন তাঁদের সাম্রাজ্যের পতন হোক, তাঁদের আস্ফালনের সমাপ্তি ঘটুক।
হ্যাঁ, ঘটে ! তাঁদের সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে ! তাঁদেরও বয়স হয়, ক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু সেই দীর্ঘ মেয়াদ শেষে ক্ষমতার পটপরিবর্তনে সান্ত্বনা পাওয়ার কিছু থাকে না
প্রকাশকালঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭
by Jahid | Nov 29, 2020 | কর্পোরেট অবজার্ভেশন
বিষয়টি একটু স্পর্শকাতর মনে হতে পারে। যেহেতু এটি একটি বাস্তবতা এবং আমাদেরকে প্রাত্যহিক এই পরিস্থিতির সম্মুখীন সবাইকে কমবেশি হতে হয় ; তাই কয়েকটা কথা বা আমার নিজস্ব অব্জার্ভেশন সবার সঙ্গে শেয়ার করা মনে হয় অনুচিত হবে না।
ঢাকাকে নগর, মহানগর বা মেগাসটি বলা হলেও, এর সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা এবং অত্যল্প মফঃস্বল শহর থেকে আসা জনগোষ্ঠী। যেমন আমার আব্বা ৬০-এর দশকেই জীবিকার টানে গ্রাম থেকে ঢাকাতে চলে আসেন। কিছুদিন ডেমরার মাতুয়াইলের সরকারী স্কুলের শিক্ষকতা, তারপর আবহাওয়া অফিস, এদিক সেদিক করে ৬৫/৬৬ এর দিকে চলে যান তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে। আম্মার সঙ্গে বিয়ে ৬৮-তে। বিয়ের পরে আম্মা আব্বা করাচীতে বছর খানেক থাকেন। ভাইয়ার জন্ম আমাদের জেলায়। আম্মার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর ঘাঁটি গাড়েন পুরনো ঢাকার ওয়ারীতে। আমার জন্ম মাতুয়াইলে, ডেমরাতে। সেই হিসাবে আমি হচ্ছি ঢাকা শহরের গ্রাম থেকে আগতদের দ্বিতীয় প্রজন্ম।
উঠতি নিম্নমধ্যবিত্ত হিসাবে আব্বাকে কেন্দ্র করে আমাদের পুরো পরিবারের বেড়ে ওঠা। অসচ্ছলতা ও আর্থিক অনটনের পাশাপাশি আব্বা তাঁর অন্যান্য ভাইবোনদেরকেও ধীরে ধীরে ঢাকা-মুখী করে তোলেন।
দ্বিতীয় প্রজন্ম হিসাবে আমার স্কুলের সময়টিতে ঢাকার স্থায়ী, অস্থায়ী বন্ধুদের সঙ্গে কয়েকজন মফঃস্বল আগত বন্ধু ছিল। কেউ হয়তো সদ্যই বড়ভাইয়ের বাড়িতে থেকে পড়তে এসেছে। সিংহভাগ সহপাঠী ছিল ঢাকার স্থায়ী অথবা অস্থায়ী বাসিন্দা। সেই অর্থে মফঃস্বলের ছেলেদের সঙ্গে আমাদের তেমন কোন মিথষ্ক্রিয়া ছিল না।স্কুল পেরিয়ে ঢাকা কলেজে পড়তে গিয়ে জেলা শহরের দুর্দান্ত মেধাবী ছেলেদের সঙ্গে পরিচয়। সেখানেও এতো কম সময় থাকতে হয়েছে, ঠিকমতো পরিচয়ের আগেই আমাদের সবাই এখানে ওখানে ছিটকে পড়েছি। টেক্সটাইলে ভর্তি হওয়ার আগে কিছুদিন ছিলাম রসায়ন বিভাগে। প্রথম ক্লাসে শিক্ষিকার জিজ্ঞাস্য ছিল, কে কে কোথা থেকে এসেছে এবং তাঁদের জীবনের লক্ষ্য কি। মফঃস্বলের ছেলেরা বেশ সপ্রতিভ-ভাবে উত্তর দিলেও আমরা ঢাকার গুটি কয়েক আমতা আমতা করলাম। মূলত: আমাদের সবার লক্ষ্য তখনো আবার বুয়েটে পরীক্ষা দেয়া। সে কথাতো আর ম্যাডামকে বলা যায় না ! রসায়ন বিভাগ ডঃ হুমায়ূন আহমেদের মতো ছাত্র পেলেও আমাদের সময়ের পদার্থ বা রসায়ন নিতান্ত ঠেকায় না পড়লে কারো আকাঙ্ক্ষিত সাবজেক্ট হওয়ার কথাও না।
কেমিস্ট্রিতে পড়ার খুব সামান্য সময়ে বেশ কিছু মফঃস্বলের মেধাবী ছেলেদের সঙ্গে মিশে আমি কীভাবে যেন বুঝে ফেললাম এঁরা দারুণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তবে তাঁদের সঙ্গে আমার মূল মিথষ্ক্রিয়া ও বন্ধুত্বের সুযোগ ঘটল টেক্সটাইলের শহীদ আজিজ হলে ; এঁদের সংগে দীর্ঘ ৫/৬ বছর কাছাকাছি বিছানায় ও আড্ডা মেরে সময় কাটিয়ে। ক্লাসের শুরুর দিকে এক বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হল সে উপজেলার দুঁদে ছাত্র। কথায় কথায় তাঁর জীবনের লক্ষ্য শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর ইচ্ছে টেক্সটাইলে পড়াশোনা করে সে কিছুদিন চাকরি বাকরি করবে, তারপরে নিজেই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হবে।পড়াশোনার পাশাপাশি টেক্সটাইলের ঘরোয়া রাজনীতি করবে সে এবং পরবর্তীতে সে জাতীয় রাজনীতিতে যোগদান করে দেশের মূল শাসন ব্যবস্থায় অংশ নেবে।
আর আমাদের ঢাকার কয়েকজন তখনো এই হুতাশন নিয়ে ব্যস্ত, কই আসলাম, কেন আসলাম , কোথায় যাচ্ছি—এই সব নিয়ে। পরবর্তীতে আমার ঐ বন্ধুটি ঠিকই আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বৃহত্তর প্রকৌশলীদের সংগঠনে জড়িত হয়ে পড়েছে। মাত্র কিছুদিন চাকরি করেই ব্যবসা শুরু করেছে সে এবং আমার ধারণা সে তাঁর ঠিক লক্ষ্যেই আছে। দুই যুগ আগে থেকেই সে জানত ও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল তাঁকে কি কি অর্জন করতে হবে। আর আমি এখনো এই চল্লিশোর্ধ বয়সে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিভ্রান্তিতে ভুগে চলেছি !
মূল কথায় আসি। কর্পোরেট জগতে, ঢাকার বাসিন্দা ও মফঃস্বলের আগতদের মানসিকতা ও কাজের ধরণে একটা বড় পার্থক্য চোখে পড়েছে আমার। যেহেতু, আমি ঢাকার দ্বিতীয় প্রজন্ম , আমার কথায় পক্ষপাতিত্ব থেকে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকছেই। তবু যতোখানি পারি নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার চেষ্টা করি।
মফঃস্বলের যে মেধাবী তরুণটি আরো হাজার-খানেক ছেলেকে পিছে ফেলে ঢাকা শহরের নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসছে, সে কিন্তু তাঁর ছোট্ট পরিমণ্ডলে পরিবার ও পরিপার্শ্বের কেন্দ্রবিন্দু। গ্রামের অমুকের ছেলে তমুক কি করেছে, বা জেলা শহরের আরেক মেধাবী কতখানি সাফল্য অর্জন করেছে, সেটা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। নিজের ভিতরে একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগুন দপদপ করতে থাকে। আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না, জেলা শহরের বা গ্রামের সবচেয়ে মেধাবী ছেলেটি ছিল তাঁর স্কুলের ব্যাঘ্র-শাবক। সুতরাং তাঁর হুংকার হয়তো নাগরিক রাস্তায় ম্রিয়মাণ হয়ে আসে। কিন্তু নিজের আসল পরিচয় সে কোনভাবেই ভুলে যেতে পারে না।
নানাবিধ কারণে মফঃস্বলের তরুণেরা দুর্দান্ত কর্মঠ হয়। ঢাকার তরুণদের হয়তো থাকার একটা সংস্থান আছে, তাঁকে কিন্তু মেসে বা হোস্টেলে সংগ্রাম করে থাকতে হচ্ছে।
ঢাকার তরুণটির হয়তো কেউ না কেউ বড়ভাই, মামা-চাচা আছে কোন খোঁজ খবর দেওয়ার ও নেওয়ার। ঐ তরুণটিকে কিন্তু ‘এসো নিজে করি’ স্টাইলে সব নিজেকেই করতে হচ্ছে। গ্রামের বা মফঃস্বলের বাবা-মার তাঁকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার অবস্থা নেই।
মূলত: ঢাকার তরুণদের মাঝে কিছুটা গা ছাড়া উন্নাসিকতা থাকে, ‘ দেখি কী হয়’ টাইপের। তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ফোকাস থাকে চাকরি বাকরি করে মোটামুটি সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছানো। অমুকের মতো হতে হবে, তমুকের মতো উপরে উঠতে হবে, খুব দ্রুত একটা থাকার সংস্থান ফ্ল্যাট করতেই হবে, গাড়ী না থাকলে চলছেই না—তেমনটি ঢাকার তরুণদের কিছুটা কম থাকে।
আমার সংক্ষিপ্ত চাকরির সময়কালে, ঢাকার সংখ্যা গরিষ্ঠ ছেলেদের, আমি আবারো বলছি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছেলেদের( ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে), ভিতরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অ্যাগ্রেসিভনেস মফঃস্বলের তরুণদের তুলনায় কম দেখেছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কর্মনিষ্ঠতায় , বসের আস্থা অর্জনে, কর্পোরেট মইয়ের ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মফঃস্বলের তরুণদের ডেডিকেশন থাকে প্রশ্নাতীত। এই সব ক্ষেত্রে মালিক-পক্ষ ও সিনিয়র ম্যানেজাররাও তাঁদেরকে বাড়তি সুবিধা দিয়ে থাকেন, এগিয়ে যেতে দেন। বলা-বাহুল্য অনেকাংশে সবাইকে পিছে ফেলে উপরে ওঠার এই প্রবণতা ভুক্তভোগী অনেকের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যে কোন বিজয়ের জয়-রথে রাস্তার পাশের ছোটখাটো লতাগুল্মের পিষ্ট হওয়ার শঙ্কা সব ক্ষেত্রেই থাকে।
আমার কাছে মনে হয়েছে ,একইভাবে ঢাকার কোন একজন তরুণ যখন প্রবাসী হয়ে বিদেশ বিভূঁইয়ে বসতি গড়ে– তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ওই এলাকার স্থানীয় যে কোন তরুণদের চেয়ে বেশীই হবে। তাই আমি পুরো প্রক্রিয়াটিকে স্বাভাবিক ও আশাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই দেখছি।
প্রকাশকালঃ জানুয়ারি ২০১৬
by Jahid | Nov 29, 2020 | কর্পোরেট অবজার্ভেশন
আমি খুব বেশী বড় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বাৎসরিক কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বেতন বোনাস ও পদোন্নতি কীভাবে হয় , দেখার সুযোগ পাইনি।যাঁদের এই ব্যাপারে ব্যাপক পড়াশোনা বা প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী আছে, অথবা যারা ব্যাংক বীমা বা আরও বৃহৎ পরিসরের কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন তাঁরা আলোকপাত করতে পারেন।
আমার স্বল্প কর্মজীবনের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে মাঝারি ও ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোতে যা দেখেছি , তা হচ্ছে কর্মচারীর মূল্যায়ন মালিকের অথবা সিনিয়র ম্যানেজারদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। একেক প্রতিষ্ঠানে একেক রকমভাবে ।কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই ‘ থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড় ’ । কোথাও আত্মীয়তার প্রায়োরিটি তো কোথাও মুখ-চেনাদের , কোথাও তৈল-সিক্তদের। ফাঁকে ফোকরে কিছু যোগ্য লোকের মূল্যায়নও হয় বটে!
আবার এটাও ঠিক, যে পদ্ধতিতেই মূল্যায়ন করা হোক না কেন ; সকল কর্মচারীকে সন্তুষ্ট করা মালিক বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকসময় যথাযথ মূল্যায়িত কর্মচারীও চারপাশে বলে বেড়ায়–তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমার মনে হয়, মালিক ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের জন্য এটা একটি কঠিন কাজ ।
মুশকিল হয়, যখন দেখা যায় কোন একজন কর্মচারী তাঁর নিকট অতীতে সংঘটিত নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড, আচরণ বা অন্যকোন একটি সামান্য ইস্যুর জন্য দীর্ঘদিন ধরে অবমূল্যায়িত হতে থাকেন। একবছরে বঞ্চিত হয়ে , হয়তো সেই কর্মচারী ভালো বেতন বোনাসের আশায় দিনরাত এক করে পরিশ্রম করেও দেখেন তাঁর ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ন এক বিন্দুও বদলায়নি। মূলত: মালিক বা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট দিনশেষে রক্তমাংসের একজন বা একাধিক মানুষ। এবং বেশিরভাগ মানুষ জাজমেন্টাল হয়ে থাকে। কেউ একবার ‘ডান নজরে’ থাকলে , তাঁর হাজার দোষত্রুটি যেমন চোখে পড়ে না। তেমনি একবার কেউ ‘বাঁ নজরে’ পড়ে থাকলে তাঁর কোন দক্ষতাই মূল্যায়িত হয় না।
আরও সমস্যা হয়, যখন মালিক তাঁর অধস্তনদের মূল্যায়নের জন্য গোপনে তথ্য সংগ্রহ করেন। যাকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে, তাঁর ব্যাপারে, তাঁর অধীনস্থদের কাউকে ডেকে গোপনে কৌশলে তথ্য নেওয়া হয়। এখন বাঙালি চরিত্র সহজবোধ্য ; কে কাকে ল্যাং মেরে উপরে উঠবে সেটাই বাঙালির কাছে মুখ্য। কোন অধস্তন যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের সম্মুখীন হয়, তাও আবার তাঁর ঊর্ধ্বতন বসের ব্যাপারে—প্রথমেই, সে যে কাজটি করে– মালিককে বোঝানোর চেষ্টা করে তাঁর ঊর্ধ্বতন আসলে সারাদিন কয়েকটা সামান্য কাজ ছাড়া কিছুই করেন না। যা করার অধীনস্থ হিসাবে তিনি নিজেই করছেন। মোদ্দা কথা, ম্যানেজমেন্টকে বোঝানো হয়, ওই ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি ছাড়াই প্রতিষ্ঠান চলবে। খামোখা এতো বেতন বোনাস দিয়ে শুধুমাত্র ‘ অভিজ্ঞ’ এই নিরর্থক গুণের জন্য গুচ্ছের টাকা খরচ করার মানে হয় না।
এই বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় শেষ পদ্ধতিতে দু’টি ব্যাপার প্রকট ও দৃষ্টিকটু ।
প্রথমত: মূল্যায়ন অধীনস্থদের গোপন আলাপচারিতার ভিত্তিতে করলে ফলাফল সর্বদাই এক আসে। সেটা যে লেভেলেই করা হোক না কেন।
দ্বিতীয়ত: অধীনস্থ দিয়ে মূল্যায়ন করার এই পদ্ধতি মালিক ও সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের ব্যর্থতা, সেটা স্বীকার না করে নিজেদেরকে তাঁরা খুব দক্ষ ও জ্ঞানী ভাবা শুরু করেন। অবমূল্যায়িত কর্মচারীকে তাঁরা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেন, তাঁর ব্যাপারে মালিক-পক্ষের কাছে অনেক ‘ তথ্য’ আছে ! আসলে তাঁদের যে মূল্যায়নের ব্যাপারে যোগ্যতার ঘাটতি আছে সেটা তাঁরা বেমালুম ভুলে যান। নিজেদের অদক্ষতাকে ঢাকতেই অদ্ভুতুড়ে পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। দুঃখজনক হচ্ছে , যাকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে ; সে বেচারা জানতেও পারেন না তাঁর ক্যারিয়ারের সর্বনাশ কে কে বা কারা কারা করল ! অনেকসময় ব্যাপারটা রীতিমত নোংরামির পর্যায়ে চলে যায়। প্রায়শ: ড্রাইভার, পিওনদের কথা শুনে কারো ব্যক্তিগত খোঁজখবর নেওয়া হয় এবং মূল্যায়নে সেই ‘গোপন’ তথ্য মূল ভূমিকা রাখে !
যাই হোক, বেদনা দিয়েই আজকের অব্জার্ভেশন শেষ করতে হচ্ছে।
আমার মতামত, মাঝারি ও ছোট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী মূল্যায়ন পদ্ধতি আমাদের দেশে এখনো শিশুতোষ পর্যায়ে রয়ে গেছে। এই পরিস্থিতির আশু পরিবর্তন হওয়ার আমি কোন সম্ভাবনা দেখছি না।
প্রকাশকালঃ জানুয়ারি,২০১৬
by Jahid | Nov 29, 2020 | কর্পোরেট অবজার্ভেশন, লাইফ স্টাইল
সরকারী কর্মকর্তাদের কথা বলতে পারব না। তবে আমাদের বেসরকারি কর্পোরেট কর্মকর্তাদের মাঝে কয়েক ধরণের লাইফ-স্টাইল আছে । ধরেন, একই বেতনে কাজ করে কয়েকজন সহকর্মী । তাদেরকে মোটা দাগে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।
প্রথম প্রকার: বেতনের টাকা দিয়ে চলে। উপরি ইনকাম নেই, কিন্তু ঢাকার শহরে বউ-বাচ্চা আত্মীয়স্বজন নিয়ে স্ট্যাটাস মেইন্টেইন করতে হিমসিম খায়। মূলত: মধ্যবিত্ত, কিন্তু চালচলন ও মানসিকতা উচ্চ মধ্যবিত্তের।
দ্বিতীয় প্রকার: বেতনের বাইরে ইনকাম নেই, সামাজিক স্ট্যাটাসের দিকে তেমন নজর নেই। মধ্যবিত্তের অনিশ্চয়তা আর নিরাপত্তা হীনতায় ভোগা শ্রেণী। যা বেতন পায়, তার সিংহভাগ ব্যয় করে সন্তানদের শিক্ষায়, বাকিটা সঞ্চয় করে ভবিষ্যতের জন্য। এরা জেনুইন মধ্যবিত্ত মানসিকতার এবং এই মানসিকতা থেকে উত্তরিত হতে পারে না।
তৃতীয় প্রকার: বেতনের টাকার বাইরে নানাধরনের উপরি ইনকাম আছে ; গাড়ীর মডেল , ফ্ল্যাটের সাইজ দেখলে টের পাওয়া যায়। ধর্মকর্মে খুব আত্মনিবেদিত। দেশের বাইরে সেকেন্ড হোম আছে বা করার চিন্তা করে। পরিস্থিতি এদিক সেদিক হলে দেশের বাইরে চলে যাওয়ার সক্ষমতা আছে। উচ্চবিত্ত মানসিকতার, জীবন উপভোগ করে। এতকিছু থাকা স্বত্বেও নানা ধরণের ফালতু অনিশ্চয়তায় ভোগে।
চতুর্থ প্রকার: বেতনের টাকার বাইরে প্রচুর ইনকাম আছে, কিন্তু দেখাতে চায় না বা পারে না, সমাজের নজরে পড়ে যাবে বলে। নামে বেনামে সম্পত্তি করে, অসংখ্য এফডিআর করে। জীবন উপভোগের সবকিছু থাকতেও নিজেদেরকে বঞ্চিত করে চলে। নিম্নবিত্ত মানসিকতার যদিও অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্ত।
পঞ্চম প্রকার: আপনার কাছে কি মনে হয় ? কোন শ্রেণীকে আমি মিস করেছি ?
প্রকাশকালঃ২৮শে নভেম্বর,২০১৯
by Jahid | Nov 28, 2020 | কর্পোরেট অবজার্ভেশন
বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে Job Description বা Job Responsibilities–ব্যাপারটি সূর্যালোকের মত স্পষ্ট ও আবশ্যকীয় হলেও সবচেয়ে অবহেলিত একটা বিষয়। নিয়োগ-দাতা ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দেন না । BDJobs ঘেঁটে আরও কয়েকটি বিজ্ঞপ্তি থেকে Job Responsibilities কপি-পেস্ট করে দেন। আবার যিনি চাকুরিপ্রার্থী, কোন একটি নতুন পজিশনে যোগদান করতে যাচ্ছেন তারও বিষয়টি নিয়ে অনেকাংশে স্পষ্ট ধারণা থাকে না ।
বেশ কয়েকবছর টেক্সটাইল ফ্যাক্টরির প্রোডাকশনে কাজ করে , নানা কারণে মার্চেন্ডাইজিং-এ চলে এসেছিলাম। কীভাবে কীভাবে BEXIMCO নামের সমুদ্র থেকে OPEX নামের মহাসমুদ্রে এসে পড়লাম, সে গল্প আরেকদিন ! ওখানে গিয়ে অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল, অসমবয়স্ক বন্ধু-স্থানীয় কলিগকে জিজ্ঞেস করলাম, কারখানার মার্চেন্ডাইজিং এর Job Responsibilities কী কী ! সে খুব গম্ভীর মুখ করে বলল , ‘ শোন্ ! মার্চেন্ডাইজারদের ক্ষেত্র-বিশেষে ডিমপাড়া ছাড়া সবকাজই করতে হতে পারে!’ আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘ মানে কি ?’ সে তার পূর্বতন কারখানার নানা অম্লমধুর অভিজ্ঞতার কথা বলল। তার ক্যারিয়ারের শুরুতে তাকে প্রায়শ: কারখানার মালিকের বাসায় বাজারও পৌঁছে দিতে হয়েছে ! আমি যারপরনাই হতাশ হলেও ; সৌভাগ্যক্রমে OPEX গ্রুপের কাজের সময়টিতে আমাকে অতদূর নামতে হয়নি !
মূল প্রসঙ্গে আসি। কেন জানিনা, গালভারী কিছু টাইটেলের মাঝে আমাদের কর্মজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার “Job Description বা Job Responsibilities” আলোহীন ছায়ায় অপুষ্ট হয়ে থাকে। এবং বছর-শেষের দেনাপাওনা বা বেতনবৃদ্ধির ব্যাপারগুলো যখন মুখোমুখি চলে আসে, ভুল বোঝাবুঝির শুরু হয় তখনই । ‘ব্যবসা খারাপ’ এটা-তো প্রথম গৎবাঁধা বুলি। এরপর আসে আরও গভীর উচ্চমার্গের কথাবার্তা। মালিকপক্ষ কর্মচারীকে বোঝান, আসলে তাদের এক্সপেকটেশন ছিল ‘ওইটা’ ! ‘সেইটা’ আবার আলোচ্য কর্মচারীটি পূরণ করতে পারে নাই অথবা লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারেননি। ‘আরও ভালো ব্যবসা হওয়া উচিৎ ছিল’ বা ‘Could have been better! ‘ – টাইপ কথাবার্তা ! ভালোর কী আর শেষ আছে ! ওইদিকে কর্মচারীও সারাবছর কী কী ধরণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন , কতখানি পরিশ্রম আর বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন তার স্মৃতি হাতড়ান। সারাবছরের পুণ্য ,ছোটখাটো দুয়েকটা Discount বা Claim-এর পাপে কাটাকাটি হয়ে যায় ! মালিক-পক্ষের সামনে হাস্যকর ভাবে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে হয় যে, শুধুমাত্র বাজারে তার ইজ্জত রক্ষার জন্য হলেও কিছু বেতন বৃদ্ধি করা দরকার !
অধুনা Yearly Business Target, Business Growth, Target Achievement , Appraisal বহুবিধ গালভারী টার্মের প্রচলন হয়েছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে। ঐ পর্যন্তই ! বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মালিক-পক্ষকে কে কীভাবে তৈল-সিক্ত করবে এবং বোঝাতে পারবে , সে সারাবছর সে কী করেছে এবং আরও কী করা সম্ভব !আসলে এই তেল বা প্রেজেন্টেশনের অনেকাংশে নির্ভর করে বেতনবৃদ্ধি, গাড়ীবাড়ি ইত্যাদি । আর, কেউ যদি ভাবে, সে তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে এবং সেটার শতভাগ নিরপেক্ষ পর্যালোচনা হয়ে বছর শেষে সঠিক বেতন বৃদ্ধি বা প্রণোদনা পাবেন ; তাহলে সে আমার মতোই নির্বোধ ! ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে সচরাচর সেটা হয় না। সম্ভবত: উচ্চমাধ্যমিক বা ডিগ্রীতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘ তৈল’ নামের প্রবন্ধটি পাঠ্য ছিল। তেল যে সমাজজীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা তাঁর মতো এতো মধুর করে বাংলা সাহিত্যে কেউ প্রকাশ করতে পারেন নি । এক বন্ধুর কাছে শোনা। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বয়োবৃদ্ধ মালিককে তার এক কর্মচারী নাকি অভূতপূর্ব উপায়ে তৈল-সিক্ত করছিলেন । তো , বৃদ্ধ মালিক এক পর্যায়ে মৃদু হেসে বলেছিলেন , ‘আঁরে তেল দিস্ না রে ; তেল আঁরে ও ধরে!’ ( আমাকে তেল দিস না, তেল আমাকেও ধরে !) সুতরাং আপনি যতো বড় মালিক বা কর্মকর্তা হন না কেন , তেল আপনাকে ধরবেই ! মনে রাখবেন, তেল কর্পোরেট জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ( সময় হলে , নেট ঘেঁটে ‘তৈল’ প্রবন্ধটি পড়ে নিতে পারেন। )
আমার কর্মজীবনে আমি হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছি। নিজের যোগ্যতা নিয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে ! আমার পূর্বতন Boss -রা একে একে সবাই, আমার অযোগ্যতা হাতেকলমে ও অর্থনৈতিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন। এর উপরে আছে আমার বিখ্যাত আলস্য ! সুতরাং ঘনঘন প্রতিষ্ঠান বদলানোর সৌভাগ্য হয়নি আমার। কর্পোরেট অভিজ্ঞতা যাই বলিনা কেন,ঘুরেফিরে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের। আলতোভাবে বলতে হবে ; নতুবা কাছের বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীরা বা পাঠকেরা সহজেই বুঝে ফেলবেন ! কর্মজীবনে কোন এক প্রতিষ্ঠানের ক্রান্তিকালে, প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে নতুন অবস্থানে ফিরে আসতে হয়েছিল আমাকে। ক্রান্তিকালীন সময়ে যা হয়, রীতিমত যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করেনা ; সহকর্মীদের মাঝে নানারকম ষড়যন্ত্র তত্ত্ব । তো মালিকের অনেক অপ্রিয় কাজ করার জন্য ‘ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলোর’ মত কাউকে না কাউকে দরকার । চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে? মালিক বা নবীন অ্যাডমিন ভরসা পাচ্ছেনা সেটা হ্যান্ডেল করতে। নতুন লোক রিক্রুট করতে হবে ? সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নিরপেক্ষ কাউকে দরকার ছিল সেই মুহূর্তে! মাত্রই একটা স্বৈর যুগের অবসান হয়েছে। নতুন অনেক নিয়ম তৈরি করতে হচ্ছে। নানা ধরণের ম্যানুয়াল, ইন্সপেকশনের ফরম্যাট সংশোধন। সাপ্লায়ারদের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্কের ঝালাই ; সে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। ঐ কাজ করতে গিয়ে আমার প্রায় আড়াই-তিন বছর চলে গিয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের বিশাল জাহাজের পালে বাতাস লেগে সেটি বাজারে সুনামের সঙ্গে আবার চলা শুরু করল। আমি ধরে নিয়েছিলাম যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে আমি আমার সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করেছি । প্রতিষ্ঠানকে একটা কিনারায় নিয়ে আসা এবং ঐ মুহূর্তে মালিক পক্ষের জন্য ও প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল আমার অবদান। মুশকিল হচ্ছে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাওয়ার পরে, সেই প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পড়ে গেলাম আমি । অতঃপর সবদিক সবার থেকে গেলাম পিছিয়ে। কেননা , দুটো সহজ ব্যাপার আমি বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম , যেটি আমার এক সুহৃদ অগ্রজ ঝাঁকি দিয়ে মনে করিয়ে দিলেন।
প্রথমত: আমার মূল পরিচয় হচ্ছে –আমি মার্কেটিং বা সেলস্ এর লোক। দিনশেষে মালিক পক্ষ ব্যবসা চাইবে, মুনাফা খুঁজবে, বাকীসব অনাবশ্যক ! ব্যাপারটা অনেকটা এরকম –ধরুন আপনি সঙ্গীত বা চিত্রশিল্পী, যুদ্ধের সময়ে রাইফেল কাঁধে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে দ্রুততার সাথে আবার আপনার নিজের জগতের ফিরে আসতে হবে। আপনি কৃষক হলে মাঠে, জেলে হলে নদীতে। তা না করে, আপনি যদি যুদ্ধস্মৃতি রোমন্থন করেন এবং আশা করেন যে, ক্রান্তিকালীন যোদ্ধার পরিচয়ে আপনার বাকী জীবন চলে যাবে—তাহলে তো হবে না ! যাই হোক! মূল পরিচয়ের বাইরে গিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমি যখন দিনরাত এক করে ছুটছি ; সেই সময় আমার অন্য সহকর্মীরা যার যার ডিপার্টমেন্টের ব্যবসা বাড়িয়েছেন। এবং যথারীতি মালিকপক্ষের কাছ থেকে যাবতীয় সুযোগসুবিধা কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নিয়েছেন। কর্পোরেট ভাবে ও অর্থনৈতিকভাবে আমি গেলাম পিছিয়ে। আমার সহকর্মীরা নিজের পরিচয়ে, নিজের Job Responsibilities নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, ক্রেতাকে সময় দিয়েছেন, ট্রাভেল করেছেন , ব্যবসা বাড়িয়েছেন । তাদের এনে দেওয়া নগদ মুনাফায় মালিক খুশী হয়েছেন; তাদেরকেও সাধ্যাতীতভাবে অফিসিয়ালি ও আনঅফিসিয়ালি লভ্যাংশ দিয়ে খুশী রেখেছেন। ক্রান্তিকালীন সময়ে মার্কেটিং বা সেলস এর থেকেও অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ বা কোম্পানি রিকন্সট্রাকশনের কাজ যে অনেকবেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল ; মালিক পক্ষ তা দিব্যি ভুলে বসে আছেন এবং আমার মনে হয় কর্পোরেট জগতের এটাই স্বাভাবিক নিয়ম!
দ্বিতীয়ত: সেই অগ্রজ বন্ধুটি আমাকে আরও মনে করিয়ে দিলেন–এমন কোন কাজে নিজেকে সারাক্ষণ ব্যস্ত রাখবেন না যেটা মালিক যে কোনও সময় প্রতিস্থাপন করতে পারেন । যেমন অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ কাজ ! এডমিনের কাজ মালিক যে কোন সময় টেক-ওভার করতে পারেন। ইচ্ছে হলেই, একদিনেই তিনি নিজে অথবা তার বংশধর বা নিকটাত্মীয়কে দিয়ে পুরো কোম্পানির অ্যাডমিন ও ম্যানেজমেন্ট বুঝে নিতে পারেন। আপনি মুহূর্তেই গুরুত্বহীন হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু , আপনি যখন মার্কেটিং , সেলস অথবা টেকনিক্যাল কোন কাজে জড়িয়ে আছেন, আপনার নিজের আসল পরিচয়ে টিকে আছেন–আপনাকে এতো সহজে মালিক পক্ষ প্রতিস্থাপন করতে পারবেন না। সুতরাং অবস্থাভেদে সময়ের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের জন্য যে কাজই করেন না কেন, নিজের মূল পরিচয় ভুলে যাবেন না ।
প্রকাশকালঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৬
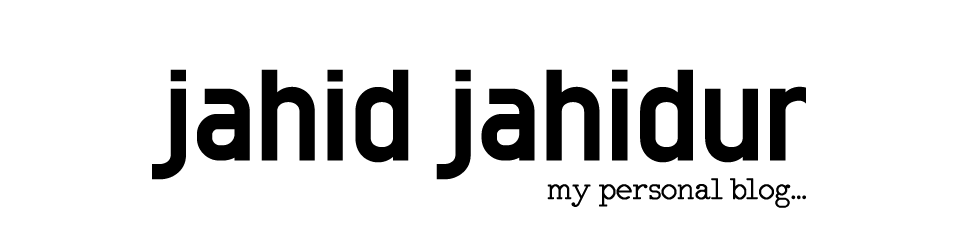
সাম্প্রতিক মন্তব্য