by Jahid | Nov 30, 2020 | দর্শন, সাহিত্য
আহমাদ মোস্তফা কামালঃ —- কিন্তু একজন লেখক হিসাবে বা একজন মানুষ হিসাবে মানুষের জীবনটাকে আপনি কীভাবে দেখেন?
শহীদুল জহিরঃ দার্শনিকভাবে আমি মনে করি, মানুষের জীবন হলো ফলের প্রত্যাশা না করে কাজ করে যাওয়া। কার একটা কাজের ফলাফল কী হবে আপনি তা জানেন না। এটা কোনো ঐশ্বরিক চিন্তা থেকে বলছি না, বলছি বাস্তব চিন্তা থেকেই। হ্যাঁ, নিশ্চিত ফল আপনি পেতে পারেন, যেমন ধরেন, একটা লোককে যদি একটা ঘরের মধ্যে আটকে আমি লাঠি দিয়ে পিটাই তাহলে সে নিশ্চিত মরে যাবে। সেটা আছে। কিন্তু এমনি সাধারণ জীবনে আপনি আসলে কোনো কাজ করে কী ফল লাভ করবেন, তার কিছুই বলা যায় না। ধরেন , আমি লেখাপড়া করছি, এইটা করে কী হবে আমি জানিনা। আমি চাকরি করছি কিন্তু সেটা নিয়ে আমি কত দূর যেতে পারব জানিনা। আমি এখন বেঁচে আছি, কতদিন বেঁচে থাকতে পারবো, জানি না। সর্বত্রই অনিশ্চয়তা। আসলে—আনসারটেইনিটি ইজ লাইফ। আমার এখন সেইরকমই মনে হয়, আগে অত হতো না, এখন মনে হয়। সাহিত্যের একটা ধারা ছিল, মার্ক্সিস্ট ধারা, সেটাতে অনেক ডেফিনিট ওয়েতে বলার ব্যাপার ছিল। জীবনকে জয়ী দেখানো, সমৃদ্ধ দেখানো , বা সম্ভাবনা আছে সেটা দেখানো ইত্যাদি। আমি যে সম্ভাবনা দেখাই না তা না, সঙ্গে ব্যর্থতাও দেখাই। কারণ জীবনের ব্যার্থতাগুলোর মধ্যে সম্ভাবনা থাকে। আমার তো মনে হয় যে , জীবনের ব্যর্থতাগুলোর একধরণের ঐশ্বর্য । এটা দারিদ্র্যকে মহান করার মতো কোনো ব্যাপার না। জয়ী হতে পারলে ভালো, না হতে পারলেও কিছু আসে যায় না। জীবনে কী হবে না হবে কিছুই যেহেতু পরিষ্কার করে বলা যায় না , যেহেতু এই অনিশ্চয়তা নিয়েই জীবন কাটাতে হয়, তাই এই জয়-পরাজয়, সাফল্য-ব্যর্থতার বিষয়গুলো আমার কাছে সমার্থক হয়ে ওঠে।
কামালঃ অনিশ্চয়তাই তাহলে জীবনের মূল কথা।
জহিরঃ হ্যাঁ । অনিশ্চয়তাই মূল ব্যাপার।
(শহীদুল জহিরের সাক্ষাৎকার ; ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০৫)
by Jahid | Nov 30, 2020 | লাইফ স্টাইল, সাম্প্রতিক
টেক্সটাইলের চাকরি ছেড়ে সদ্য গার্মেন্টসের মার্চেন্ডাইজিং-এ ঢুকেছি। ওপেক্স গ্রুপে। মিরপুর ১১ নাম্বারের বাসা থেকে কোনভাবে ১০ নং গোলচত্বরে পৌঁছে সহজলভ্য যানবাহন ছিল শেয়ারের সিএনজিতে সৈনিক ক্লাবে নামা । পাশেই মহাখালী ডিওএইচএসের ২৮ নাম্বার রোডে ছিল ওপেক্স-এর হেড অফিস।
৯৯ সালের কথা বলছি ; সন্ধ্যা হোক, রাত হোক বাসায় ফিরে আসার সময়টাতেও সেই একই উপায়। মিরপুর ১৪ নাম্বার থেকে মিরপুর ১০নং গোলচত্বরের রাস্তা সারাটা দিন বেশ ব্যস্ত থাকলেও সন্ধ্যার পর ঐ রাস্তার স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেলে কেমন যেন থমথমে হয়ে যেত। কোন বড় বাস ঐ রাস্তায় চলত না। রিকশা, সিএনজি আর মাঝে মাঝে কিছু প্রাইভেট কার।
আমার জন্ম ঢাকায়, বেড়ে ওঠাও । মহল্লায় পাশের রোডে আওয়ামীলীগের জাতীয় পর্যায়ের নেতা থাকে। দুই রোড পরে থাকে ঢাকার সেই সময়ের বিখ্যাত ছাত্রনেতা। বড়ভাইয়ের বন্ধুরা কেউ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় নেতা, তো কেউ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা। অনেকের সঙ্গে চেহারায় পরিচয়। ‘এই তুমি সাজুর ভাই না ?’ ‘এই তুমি উকিল সাহেবের ছেলে না?’ ছোটখাটো মস্তানি, ছিনতাই এগুলোকে আমি ও আমাদের প্রজন্মের কেউ গোনায় ধরতাম না। আমাদের গায়ে ঢাকার শহরের কেউ টোকা দিয়ে পার পেয়ে যাবে, এটা ভাবতেই পারতাম না।তখন, সবে মোবাইল ফোন সহজলভ্য হয়ে উঠছে। বেতন পেতাম ৮,৭০০ টাকা ; একমাসের বেতনের টাকা দিয়ে নকিয়া ৩১১০ সেট কিনলাম, সঙ্গে গ্রামীণ ফোনের প্রিপেইড কানেকশন। উফ ! সেই ৬ টাকা প্রতি মিনিট কলরেটের যুগ ; ভ্যাট সহ ৬টাকা ৯০ পয়সা ! ফোন হয়ে গেল জীবনের চেয়েও প্রিয়। বারবার প্যান্টের সঙ্গে মুছি, আর পকেটে ঢুকিয়ে রাখি। দিনে তিনবার করে রিং টোন চেঞ্জ করি। সারাদিনে পিএম, কিউসি আর কিউসি ম্যানেজারদের ফোন আসে । হবু স্ত্রীর সঙ্গে সপ্তাহে একবার কথা হয় কী হয় না।
তো ঐ সময়ে একদিন সন্ধ্যায় সৈনিক ক্লাবের কাছে এসে শেয়ারের সিএনজির জন্য অপেক্ষা করছি। সন্ধ্যার কিছুটা সময় সুপার পিক আওয়ার থাকে। একসঙ্গে এতো লোক কোথা থেকে এসে যে হাজির হয় ! একটা বাহন মোড় ঘুরতে না ঘুরতেই সেকেন্ডের দশভাগের একভাগ সময়ে সেটা ভরে যায়। হুস করে সেটা চলে যাওয়ার পরে অপেক্ষা। কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে হাঁটা ধরে, কচুক্ষেতের মোড় থেকে রিকশা নেওয়ার চিন্তা করে। ফিরতি যাত্রীরা কোনমতে একটা পা বাইরে রাখতে না রাখতেই, দুই পাশ দিয়ে অন্য যাত্রীরা হুড়োহুড়ি করে উঠে পড়ছে।
আমি মিনিট দশেক অপেক্ষা করে একটা ফাঁকা সিএনজি আসতে না আসতেই দৌড় দিয়ে উঠে পড়লাম। দুইপাশ থেকে কাঁধে ব্যাগসহ আরো দুই অফিস যাত্রী উঠে পড়ল। ড্রাইভারের পাশে আরেকজন । ক্যান্টনমেন্ট পার হয়ে , ১৪ নম্বরের মোড় পার হতেই দুইপাশ থেকে দুই আরোহীর চাপ অনুভব করলাম। বাঁ পাশের জন আমার কোমরে লোহার রড বা পিস্তলের মতো কিছু একটা দিয়ে খোঁচা দিয়ে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জিজ্ঞেস করল, ‘ভাই কোথায় আছেন?’ এদিক সিএনজি চলছে এখনকার পুলিশ কোয়ার্টার, পার হয়ে সামনের ন্যাম বিল্ডিং এর পাশে এসে পৌঁছেছি। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বুঝে ফেলেছে আমি ছিনতাইকারীর পাল্লায় পড়েছি। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না, আমাকে ! শেষ পর্যন্ত আমাকে ছিনতাইকারী ধরল ! তাও আমার নিজের এলাকা মিরপুরে, যেখানকার অলিগলি তস্যগলি আমার চেনা! আমি সত্য মিথ্যা মিশিয়ে বললাম , ‘গার্মেন্টসে কাজ করি। ওপেক্স কারখানার ফ্লোরে।’
কথা বলতে বলতেই , ডানপাশের লোকটা একটা ক্ষুর বের করে আমার গলায় ধরল। ঐ রাস্তায় স্ট্রীটলাইট ছিল না। নির্মাণাধীন বিল্ডিংগুলোর ঝাপসা আলোতে ক্ষুরটা আরো চকচক করছিল। বলল, ‘বুঝতেই তো পারছেন আমরা কারা।’ পুরো সময়টাতে আমার দুই হাত তাঁদের পিঠ দিয়ে চেপে ধরে আমার মানিব্যাগ বের করে টাকা গুণে ফেলল । আর অন্য পকেট থেকে আমার সেই সখের নকিয়া মোবাইল বের করে জিজ্ঞেস করল, ‘মোবাইল কার ?’ আমি কী মনে করে বললাম ‘কারখানার মোবাইল, আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে।’ আমি সবচেয়ে ভয় পাচ্ছিলাম যদি মোবাইলটা নিয়ে নেয়। এতো শখের মোবাইল আমার ! কিন্তু আশ্চর্য ! ছিনতাইকারীরা মোবাইলটা শার্টের বুক পকেটে ঢুকিয়ে প্রায় ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল।
এবং ভগ্নাংশ সময়ের মধ্যে নামার ঠিক আগ মুহূর্তে আমার চোখে মলম বা জামবাক কিছু একটা ঘষে দিল। বলল ‘পিছনে তাকাবেন না।’ আমি নীচে হুমড়ি খেতে খেতে টাল সামলালাম কোনমতে। চোখে তীব্র জ্বালা-পোড়া । রাস্তা কোনদিকে, ফুটপাত কোনদিকে ঠাহর করতে পারছিলাম না। ভয়ংকর যন্ত্রণা । একটু দুরেই রাড্ডা বারনেন হাসপাতালের পাশের মুদিদোকান থেকে দুজন কাছে এসেই বুঝল কি হয়েছে। মনে হলো এরা প্রায়ই এসব দেখে অভ্যস্ত। একজন দয়া করে পানি এনে দিল, পানির ছিটা দিতে দিতে, কিছুটা চোখ খুলেই ভাইয়াকে ফোন দিলাম। বললাম ‘ছিনতাই হয়েছে । বেশী টাকা ছিল না , ৩১৫ টাকার মতো ছিল, ৭টাকা ফেরত দিয়ে রেখে বাকী টাকা নিয়ে গেছে।’ বাসায় গেলাম না, মহল্লার আড্ডায় গেলাম।
মহল্লার বন্ধুরা আমাকে শুকরিয়া করতে বলল। কারণ আমার যে গাঁট্টাগোট্টা স্বাস্থ্য, আমার মত লোকেরা নাকি প্রায়ই গাঁইগুঁই করে, প্রতিহত করতে যায় ছিনতাইকারীদের এবং ছিনতাইকারীরাও তাদেরকে ধাওয়া করতে যাতে না পারে সেজন্য এই টাইপের লোকেদের হালকা(!) পাঁড় মেরে যায়। গত কয়েক সপ্তাহে হাসপাতালে এরকম হালকা পাঁড় দেওয়া যাত্রীদের কয়েকজনের অকালপ্রয়াণও ঘটেছে। আমাকে যে শুধু মলম দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে সে আমার কপাল। বড়ভাইদের দিয়ে থানা পুলিশ করলে কী কী হতে পারে সেটা বিবেচনা করা হল। কারণ, ওই সময়ে ঢাকার রাস্তা ভাসমান ছিনতাইকারী ভরে গিয়েছিল। শোনা গেল ঐ রুটের ছিনতাইকারীরা কোন নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের না। এদেরকে ধরার চেষ্টা করা প্রায় দুঃসাধ্য। একই রুটে কেউ দুই তিন মাসের ভিতরে আর ফিরে আসে না। আর টাকার পরিমাণ যেহেতু সামান্য এবং আমার সাধের মোবাইল ছিনতাই হয় নি ; তাই সবার উপদেশ ছিল ছিনতাই নিয়ে থানাপুলিশ আর কেন্দ্রীয় নেতাদের না জড়ানোই ভাল।
যথারীতি রাত করে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।
সারাক্ষণ শুধু একটা কথাই মনে হচ্ছিল, আমার ছিনতাই হয়ে গেল ! আমার !!!
পুরো ব্যাপারটায় একটা সূক্ষ্ণ অপমান ছিল, মনে হচ্ছিল কেউ আমাকে প্রকাশ্যে অপমান করেছে, যা আমি কোনভাবেই নিতে পারছিলাম না। রাতের খাবার ভালোমতো খেতে পারলাম না। কয়েকদিন কেমন যেন একটা অপমানের আবরণ আমাকে ছেয়ে থাকল। এর ফাঁকে আমি মনে মনে অনেক ধরণের চিন্তা করতাম ; সৈনিক ক্লাবে দাঁড়িয়ে ঐ দুই ছিনতাইকারীকে খুঁজতাম। ব্যাপারটা ভুলে যেতে প্রায় ছয়মাস লাগল।আমার সারাজীবনে ছিনতাই, হাইজ্যাক একবারই হয়েছে! ওই প্রথম, ওই শেষ !
প্রতিদিন করোনা ভাইরাসের ক্লিপ আর সাবধানবানী দেখতে দেখতে আজকে বহুবছর আগের ছিনতাইয়ের কথা কেন মনে পড়ল, বোঝার চেষ্টা করছিলাম।
আসলে কিছু কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা নিজের জীবনেও যে ঘটতে পারে ; সেটা আমাদের কল্পনাতেও থাকে না। ঘটে গেলে, গভীর শোকে, দুঃখে, বেদনায় ক্ষোভে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। মিডিয়াতে প্রতি মুহূর্তে আক্রান্ত আর মৃত্যু-সংখ্যা আমাদের অনিশ্চিত, আতঙ্কিত করছে ; কিন্তু মনের গভীরে একটা আশা — অন্যের হলে হবে , আমার কী আর হবে ! আমার প্রিয়জন আর আমি এ যাত্রায় সুস্থই থাকব। এই আশাবাদ একদিক দিয়ে মন্দ না ! আবার অন্যদিক দিয়ে এই অর্থহীন আশাবাদ , অসাবধানতাতে কেউ যদি জীবনে প্রথমবারের মতো কোভিড-19 আক্রান্ত হয়েই যায় ; সেটাও তো তার জন্য শেষবারের মতো হতে পারে ! ছিনতাইকারীর স্মৃতিচারণ করতে পারছি ; অবহেলা, অসাবধানতায় কোন কাহিনী হয়ে গেলে –ফিরে আসার সুযোগ নাও তো থাকতে পারে!
প্রকাশকালঃ ২রা এপ্রিল,২০২০
by Jahid | Nov 29, 2020 | ছিন্নপত্র, দর্শন, সাম্প্রতিক
যথারীতি আমাদের পূর্ববঙ্গের আশির দশকের রিয়েল লাইফ অভিজ্ঞতা। এলাকার সিনিয়রের কাছে শোনা।
তো হয়েছে কী, তাদের গ্রামে একজন মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থ মারা গেলেন হুট করে ; উঠতি বয়সের সন্তানসন্ততিদের রেখে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম লোকের অকালমৃত্যু হলে কী হয় সেটা দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার আছে।
গ্রাম- মফস্বলে প্রথম কিছুদিন প্রতিবেশীদের আহা উঁহু থাকে। ধীরে ধীরে সবাই যার যার জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মৃতের পরিবারে কীভাবে চলছে, কী খেয়ে বেঁচে আছে সেটা দেখার সময় থাকে না সঙ্গত কারণেই।
চারিদিক আঁধার হয়ে এলে ভিটে-বাড়ি বাদে অন্যসব জমি বিক্রি করে পড়াশোনা আর জীবনধারণের প্রাণান্ত চলে।
যথারীতি ঐ পরিবারের বড়ছেলেটি যে কিনা আমার পরিচিতের প্রতিবেশী সেও বাধ্য হয়ে টুকটাক করে বাপের কষ্টের করা জমি বিক্রি করা শুরু করল। প্রতিবেশী মুরব্বীরা ব্যাপারটা তেমন পছন্দ করছিল না। এভাবে জমি বিক্রি করে খেলে আর কতদিন। এক সময় তো হাত পাততে হবে। আবার করারও কিছু ছিল না।
যাই হোক একদিন নদীর ঘাটে কয়েকজন মুরব্বী তাকে ধরল।
‘বাপু হে ! তুমি যেভাবে জমি বিক্রি করে খাতিছ, এভাবে চললি বুড়া হলি কী খায়া থাকবা ?’
সে উত্তর দিল, ‘ কাকা, এখুন আগে আমার খায়া জানে বাঁচতি হবি। খাতি পারলি না তবে বুড়া হতি পারব ; না খাতি পারে মরেই যদি গেলাম ; তালি পর আর বুড়া হব কেম্মা করে !’
প্রকাশকালঃ ৩০শে মার্চ,২০২০
by Jahid | Nov 29, 2020 | সাহিত্য
নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ-
স্বদেশের তরে, যা করেই হোক, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল, ‘আ-হা-হা কর কি, কর কি, নন্দলাল ?’
নন্দ বলিল, ‘বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?’
তখন সকলে বলিল- ‘বাহবা বাহবা বাহবা বেশ !’
নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা !
সকলে বলিল, ‘যাও- না নন্দ, কর না ভায়ের সেবা।’
নন্দ বলিল, ‘ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই-
না হয় দিলাম, -কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক্; ’
তখন সকলে বলিল- ‘হাঁ হাঁ হাঁ, তা বটে, তা বটে, ঠিক !’
নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির,
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির;
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন;
লেখে যতো তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ !–
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল;
তখন সকলে বলিল- ‘বাহবা বাহবা, বাহবা নন্দলাল!’
নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি;
নন্দ বলিল, “আ-হা-হা ! কর কি, কর কি ! ছাড় না ছাই,
কি হবে দেশের, গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাই ?
বলো ক’বিঘৎ নাকে দিব খত, যা বল করিব তাহা’;
তখন সকলে বলিল- ‘বাহবা বাহবা বাহবা বাহা !’
নন্দ বাড়ির হ’ত না বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি;
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উল্টায় গাড়িখানি,
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে ‘কলিশন’ হয়;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয়,
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল
সকলে বলিল- ‘ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল।’
by Jahid | Nov 29, 2020 | সাহিত্য
১
তিন ঘণ্টা পর হঠাৎ তোমার একটা ‘কুহু’
চাই না আমি,–চাই না আমি।
আমি চাই মহুর্মুহু কোকিল আমায়
ডাক পাঠাবে তার বাগানে।
আমি চাই অনন্ত বসন্ত, তুমি
সারাক্ষণ থাকবে জুড়ে আমার প্রাণে।
মুঠোফোনের কাব্য। নির্মলেন্দু গুণ।।
২
ধরা পড়ার আগে পর্যন্ত গভীর জলের মাছ,
শিকারীর সঙ্গে কতরকমের খেলা খেলে-
তারপর যখন শিকারীর বড়শিতে ধরা পড়ে,
তখন চোখের পলকে পাল্টে যায় দৃশ্যপট।
মাছকে নিয়ে শুরু হয় শিকারীর জলখেলা।
আমি জানি, আমি মৎস্য , তুমিই শিকারী-
আমি তোমার কষ্টার্জিত ধন।
আমার সাধ্য কি যে এড়াই তোমার বন্ধন?
আমি তোমার সুখের হাসি , দুখের ক্রন্দন।
মুঠোফোনের কাব্য। নির্মলেন্দু গুণ।।
৩
আমি কান পেতে রই,
প্রাণ পেতে রই,
চোখ পেতে রই স্ক্রিনে।
কখন তুমি গানের মতো,
সর্বনাশা বানের মতো,
রুদ্রকাম উত্থানের মতো
প্রবেশ করো
আমার মুঠোফোনে।
মুঠোফোনের কাব্য। নির্মলেন্দু গুণ।।
৪
তুমি আমাকে চতুর শিয়ালের মতো
পা ছেড়ে লাঠি ধরতে বলো না তো।
আদি রস হচ্ছে কাম, স্নেহ নয়।
স্নেহ তো কামের অনুবর্তী।
প্রেম , বন্ধুত্ব—এগুলো হচ্ছে
কামানুভূতির সংস্কৃত প্রকাশমাত্র।
বুঝতে পারলে, বোকা মেয়ে ?
মুঠোফোনের কাব্য। নির্মলেন্দু গুণ।।
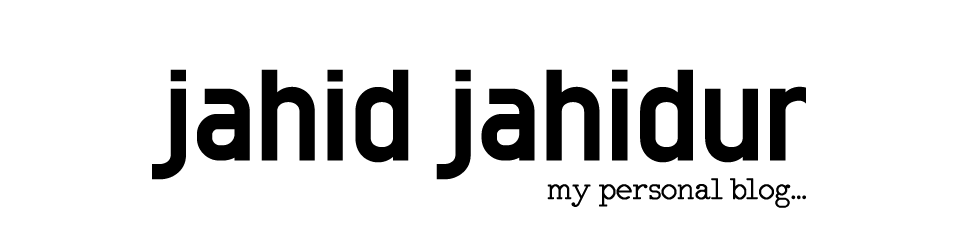
সাম্প্রতিক মন্তব্য