
by Jahid | Nov 30, 2020 | সাম্প্রতিক
‘ভুল এই শহরের মধ্যবিত্তদেরও ছিল।’
এই শিরোনামের একটা লেখা মেসেঞ্জারে ঘুরছে কয়েকদিন ধরে। অনেকে পাঠিয়েছেন। কেন করোনার এই সংকটে মাস ছয়েক পার করার সামর্থ্য নেই মধ্যবিত্তের, তা নিয়ে অভিযোগের আঙুল মধ্যবিত্তদের দিকেই। লেখক বলেছেন, “ একটা অপ্রিয় কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। আমাদের এই শহরে লাইফস্টাইলে প্রব্লেম ছিলো। শো অফ বেশি ছিলো। নইলে অন্তত ছয় মাস বসে খাওয়ার মতো টাকা সব পরিবারেই জমে থাকার কথা। যতটুকু ইনকাম, কালের স্রোতে গা ভাসাতে যেয়ে খরচ তারচেয়ে বেশি হয়েছে। যতটুকু স্ট্যাটাস, যতটুকু সামর্থ্য, মানুষ নগদে তার চেয়ে উঁচু তলায় বাস করেছে।”
নিচে লিংক দিলাম। আগ্রহীরা মূল লেখা পড়ে দেখতে পারেন।
মূল লেখা এখানে
আমার পরিচিতদের অনেকে এই লেখাকে সমর্থন দিয়েছেন , কেউ বা মধ্যবিত্তদের না দুষে, দুষেছেন আমাদের সামগ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে। আমাদের ভোগবাদী সমাজে রাষ্ট্র কোনধরনের অন্ন , বস্ত্র শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের নিশ্চয়তা দিচ্ছে না বলে, এক শ্রেণির মানুষ প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ জমিয়ে পাহাড় করছেন। আরেক শ্রেণি এমনই টানাপড়েনের মাঝে আছেন যে, সামাজিক স্ট্যাটাস বজায় রেখে সন্তানের যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হিমসিম খাচ্ছেন।
সত্যি কথা বলতে কী , আমি নিজেও বিভ্রান্ত! আমার পর্যবেক্ষণ মধ্যবিত্তদের পক্ষে নাকি বিপক্ষে। আমি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আম্মা মফঃস্বলের সচ্ছল পরিবারের আর আব্বা গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে জোড় বেঁধে সংসার এগিয়েছেন বহুদূর।
পুরনো ঢাকার আবাস থেকে উচ্ছেদ হয়ে কয়েকবছর গ্রামে আর তারপরে আবার ঢাকা এসে আমরা যখন মিরপুরে থিতু হলাম, তার মাঝখানে বছর তিনেক ভাড়া ছিলাম মিরপুরের গুদারাঘাট, পাইকপাড়া নামের গ্রাম গ্রাম গন্ধের মফঃস্বল এলাকায়। পুরনো ঢাকার পর নানাবাড়ি , তারপর ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পরে এভাবে জায়গায় জায়গায় ভাড়া থাকাটা আম্মার পছন্দ ছিল না। যে করেই হোক নিজের একটা স্থায়ী বাড়ি ছিল তাঁর স্বপ্ন। সুতরাং সাধ ও সাধ্যের মিল রেখে আমরা বাড়ি কিনে চলে এলাম অবাঙ্গালী অধ্যুষিত মিরপুর ১১ নাম্বারে। এর আগে যেখানেই ছিলাম চারিদিক অনেক খোলামেলা ছিল, এতো ছোট জায়গায় ছিলাম না। এখানে মানিয়ে চলতে হল। মধ্যবিত্ত জীবন শুরু হল নিম্নবিত্তদের মতো সঙ্কুচিত আবাসনে। দীর্ঘ তিরিশ বছরে পৌনে দু’কাঠার বাড়ি একসময় নতুন প্রজন্মের প্রকোপে জনবহুল হয়ে গেল। আমি ভাড়াবাড়িতে চলে এলাম। সেই ভাড়াও বছর বছর বেড়েই চলছিল । মাস শেষে বেতনের বড় একটা অংশ গুণে গুণে দিতে হয়। বুকে বিঁধে। বছর ছয়েক পরে ২০১৪ সালে শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপদেশ দিল যে ভাড়ার টাকার সঙ্গে আর কিছু লাগালেই নাকি মান্থলি ইন্সটলমেন্টে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে! বউ আর সামাজিক চাপে অবশেষে ফ্ল্যাটের চক্করে ফেঁসে গেলাম। এই লোন,সেই লোন আর লোন ফেরতের চক্করে এখনো নাভিশ্বাস।
ট্রেডের এক ছোটভাইয়ের সাজেশনে Robert T.Kiyosaki এর বেস্টসেলার Rich Dad, Poor Dad পড়েছিলাম ২০০৯ এর দিকে। একটা চিন্তা মনে দাগ কেটে আছে।
One believed, “Our home is our largest investment and our greatest asset.” The other believed, “My house is a liability, and if your house is your largest investment, you’re in trouble.”
নিজের একটা ফ্ল্যাট বা স্থায়ী আবাস যখন মানুষের সবচেয়ে বড় ও একমাত্র ইনভেস্টমেন্ট হয় সে তো আসলেই বিপদে আছে। সেই বিপদে আমাদের এশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক। অদ্ভুতুড়ে মধ্যবিত্ত মানসিকতা। মজার ব্যাপার হচ্ছে , মধ্যবিত্তদের এই অনিশ্চয়তা আর নিরপত্তাহীনতার বীজ তাদের বংশধরেরা বহন করে চলে যুগের পর যুগ। কয়েক দশক আগে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বপ্ন শেষ হতো পেনসন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকায় নিজের একটা বাড়ি তৈরি দিয়ে। শেষ হতো বলছি, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যেতো, বাড়ি তৈরির ঝক্কি আর যন্ত্রণা পেরিয়ে পরিবারের কর্তা যখন আরামকেদারায় হেলান দিতেন, তক্ষুনি সেটা স্থায়ী হেলান হয়ে যেত। মানে পরিবারের কর্তা বা কর্তীর জীবনাবসান ঘটত।
ঘুরে ফিরে আমার বাবা-মা, নিকটাত্মীয় সকলের স্বজনদের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল এই ঢাকা শহরে নিজের একটা জমি, সেই জমিতে বাড়ি, সামনে একটা বাগান ইত্যাদি ইত্যাদি। অধুনা, মেগা-সিটিতে সেই সুযোগ নেই বলেই, নিজের ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে ছোট্ট বাগান। সারাজীবন ঘানি টেনে টেনে যে তেল জমে ; তা বের হয়ে যায় একটা নিজের বাড়ি অথবা ফ্ল্যাটে।
আমার পরিচিত একজন উদ্যোক্তাকে জানি ,গত দুই দশক ধরে ভাড়াবাড়িতে থাকেন। তাঁর কথা, ‘এতোগুলো টাকা ব্যবসায় খাটালে ব্যবসার লাভ। বছর দুয়েক পরে পরে বাসা বদলাই , নতুন মোজাইক আর নতুন কমোড ব্যবহার করি। কোন মানে হয় না ঢাকা শহরের সোনার দামে ফ্ল্যাট করার!’ সেই লোক দিব্যি আছে।
আবার আমেরিকায় ও দেশের বাইরে কয়েকজন আধুনিক বাংলাদেশীকে চিনি, এঁরা প্রয়োজনে এক স্টেট ছেড়ে আরেক স্টেটে যাওয়ার সময় সবকিছু গুছিয়ে বিক্রি করে আরেক জায়গায় নতুন বসতি গড়েছেন।
মুশকিল হচ্ছে মফঃস্বল থেকে উঠে আসা মধ্যবিত্তদের। মফঃস্বলের মধ্যবিত্তদের স্থায়ী আবাসনের স্বপ্ন আর আবেগঘটিত সমস্যা আরো জটিল। এঁদের সবার গ্রামে একটা বাড়ি থাকে। সেই ভিটেবাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলেও , সেটাতে ঘুঘু চরলেও সারাজীবন বাল্যস্মৃতি আর নানাবিধ আবেগের পোঁটলা হিসাবে সেটা তারা রক্ষা করে চলেন। এই স্মৃতি ধরে রাখার খরচ কিন্তু নিতান্ত কম নয়। এই মধ্যবিত্তরা অনেকে জেলা শহরে এসেছেন চাকরির স্বার্থে। সেখানে থেকে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করিয়েছেন। সেই হিসাবে জেলা শহরে তাদের একটা আলাদা স্থায়ীবাস থাকে। এরা পড়াশোনা শেষে যখন ঢাকায় আসে, তখন ঢাকায় এসে সেই একই চক্কর। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ঢাকায় আরেকটি স্থায়ীনিবাসের জন্য তাদের প্রাণান্ত। এদের পরবর্তী প্রজন্ম যখন আমেরিকা, ইউরোপ, ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া যায়, মনের গভীরে এদের প্রধানতম লক্ষ্যই থাকে একটা গাড়ি আর স্থায়ী একটা বাড়ির।
এই দুর্ভেদ্য চক্র কোনভাবেই শেষ হয় না ! বাইরের দেশে না হয় এন্তার জায়গা পড়ে আছে ; হোক আপনার দুইটা গাড়ি আর তিনটা বাড়ি। কিন্তু সীমিত সম্পদ আর অসম্ভব জনবহুল বাংলাদেশে কী করে আমাদের মধ্যবিত্তরা তিন চার জায়গায় কয়েকটি স্থায়ী নিবাসের মতো অনর্থক অপব্যবহারে মেতে আছেন, সেই দুষ্টচক্রের বিশ্লেষণ করা সময়ের দাবী !
প্রকাশকালঃ ২৮শে জুন,২০২০

by Jahid | Nov 30, 2020 | সাম্প্রতিক
ইউরোপ আর এশিয়ার লেফট হ্যান্ড রাইট হ্যান্ড ড্রাইভ নিয়ে আমি সবসময় বিব্রত বোধ করি। পরিচিত কেউ ড্রাইভ করলে স্বাভাবিক সৌজন্য হচ্ছে তার পাশের সীটে বসা ; সেটা দেশেই হোক বা বিদেশে। অবশ্যি যদি ট্যাক্সি হয় তাহলে পিছনের সিটে বসা জায়েজ আছে। যেটা হয় ,এবারের ট্র্যাভেলে আমি একাই ছিলাম। ক্রেতা গাড়ি চালাচ্ছিল বলে আমি সৌজন্য করে গাড়ীর প্যাসেঞ্জার সিটে বসতে গেছি , দেখি ওইটা ড্রাইভিং সিট ! আমাদের বাংলাদেশের ঠিক উল্টো !
গত সপ্তাহে হোটেল থেকে ট্যাক্সিতে উঠলাম পিছনের সিটে , উঠে গাড়ির ডান দিকে বসলাম । ড্রাইভার লেফট-হ্যান্ড ড্রাইভে বাঁ দিকে বসে ড্রাইভ করছে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর কী মনে করে অভ্যাসবশত: বামদিকের সিটে চলে গেলাম।
মাঝ রাস্তায় মিররের দিকে তাকিয়ে ড্রাইভার হো হো করে রীতিমতো আর্ত চিৎকার দিয়ে উঠলো আমাকে পিছনে না দেখে ! ব্যাটা খেয়াল করে নাই, আমি কখন যে ডানদিক থেকে বা দিকে ঠিক তাঁর পিছনে চলে গেছি ! পরে তাকে বুঝিয়ে বললাম , আমি গাড়ীর বামদিকে বসে অভ্যস্ত তাই সাইড চেঞ্জ করেছি।
সে ও অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংলিশে যা বলল , তাঁর জীবনে এইরকম ব্যাপার এই প্রথম। সে ভেবে বসেছে , প্যাসেঞ্জার হঠাৎ ভ্যানিস হয়ে গেল কেমন করে !
প্রকাশকালঃ জুন, ২০১৩
by Jahid | Nov 30, 2020 | লাইফ স্টাইল
সারাবছরের অফিসের ট্রাভেলে হঠাৎ হঠাৎ একবার দু’বার বিজনেস ক্লাসে আপগ্রেড পাই, নিতান্তই মাইলেজের বদৌলতে ; তাও হয়তো কোন শর্ট ফ্লাইটে। নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চশ্রেণীতে উত্তরণের এই ব্যাপারটা কিন্তু আমি বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করি।
সারাক্ষণ এয়ারহোস্টেস ব্যতিব্যস্ত আপনাকে নিয়ে। যেখানে ইকোনমি ক্লাসে এক গ্লাস পানি চাইলেও সময় ফেরে এরা এতো ব্যস্ত থাকে যে, পারলে ঢেলে খেতে বলে। তিনবার ডাকলে একবার আসে। খাবার শেষ করে সামনের ট্রে নিয়ে ঘণ্টা খানেক ধরে বসে থাকতে হয়, কখন পরিষ্কার করবে এই আশায়। সেই তুলনায় বিজনেস ক্লাস মানে অন্যরকম কিছু।
কিন্তু আপগ্রেড পাওয়ার পরও একটা জিনিষ আমি বুঝি আমার সাথে জেনুইন বিজনেস ক্লাসের তফাৎ ঘোঁচে না। পাশের ধবধবে পেটমোটা কোট টাই পড়া হাঁসফাঁস যাত্রীটা কিছুটা বিরক্তির চোখে তাকায় আমার দিকে, এইসব মফিজ( পড়ুন জাহিদ) ক্যামন করে যে বিজনেস ক্লাসে আসে !
স্কুল জীবনে আমাদের একটা কমন অভজার্ভেশন ছিল বড়লোকের পোলাপানদের নিয়ে। মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের দুজন ছেলে বা মেয়ে যদি পাশাপাশি একই পোশাক পড়েও হেঁটে যায়, আমরা ঠিকই ওদের আলাদা করতে পারতাম। খেয়াল করে দেখতাম , উচ্চবিত্ত পোলাপানের চামড়ায় একটা আলাদা মসৃণতা, ঔজ্জ্বল্য বা জেল্লা থাকে। এটা কী ঘি মাখন, চর্বিচোষ্য খেয়ে নাকি সারাক্ষণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি ও ঘরে থেকে, কে জানে ! আমরা কিন্তু ঠিক ঠিক টের পেতাম। আমার মনে হয়, সমাজের যে কেউ এটা টের পেয়ে যান।
আবার নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের কাউকে যতই পোশাক ও অন্যকিছু দিয়ে পালিশ করি না কেন, চামড়ার ওই জেল্লা আনা অনেক ডিফিকাল্ট! হঠাৎ বিজনেস ক্লাসে বসেও এবার আমি এইসব চিন্তা করতে করতে ঢাকায় !
প্রকাশকালঃ জুন, ২০১৩
by Jahid | Nov 30, 2020 | লাইফ স্টাইল, সাম্প্রতিক
অনেকগুলো ছোটছোট যুদ্ধের ক্রমানুসারে আসে বড়-যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ। উনিশ শতকে সেটার নাম হয়েছে বিশ্বযুদ্ধ। সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর পুরোটা জুড়ে বিশ্বের পাশাপাশি রাষ্ট্রগুলোর মাঝে যুদ্ধ লেগেই থাকত। বিশ্বব্যাপী অনেকগুলো জাতি একক কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ইতিহাস প্রথম বিশ্বযুদ্ধে।
বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, মানবিক বিপর্যয় এমন হয় যে সেটা মনুষ্য প্রজাতিকে দীর্ঘসময় হতবিহবল করে রাখে। ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে একটা মানবিক সমাজ গড়ায় নজর দেয় তারা। নানাধরনের হম্বিতম্বি থাকলেও , কেউ আর বোকার নতুন করে যুদ্ধে জড়াতে চায় না। বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে সবাই মনে মনে একমত থাকে। যদিও প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝে সময়-পার্থক্য সামান্যই।
তারপরেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমরা একটা দীর্ঘবিরতি পাচ্ছি। জন্ম হওয়ার পর থেকেই শুনে এসেছি; এই শুরু হল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ; এই শুরু হল আমেরিকা-সোভিয়েত রাশিয়ার পারমাণবিক যুদ্ধ। সেটা হয়নি ,আর হওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ।
তেমনি করে সার্স, মার্স, জিকা, সোয়াইন, ইবোলার চিকন ধাক্কা পার হয়ে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খাচ্ছি কোভিড-19 করোনা ভাইরাসের। বিশ্বব্যাপী যে বিপর্যয়টা যাচ্ছে; সেটা পার হয়ে গেলে আমাদের প্রজন্ম আর কোন বড় বিপর্যয় ছাড়াই এই শতাব্দী পার করতে পারবে ; এইসব ভেবে আশাবাদী হতে পারেন।
প্রকাশকালঃ ২৩শে জুন, ২০২০
by Jahid | Nov 30, 2020 | লাইফ স্টাইল, সাম্প্রতিক
ছয় বছর বয়স পর্যন্ত মাতৃস্তন পান করেছি। এত্তো বড় হয়ে যাওয়ার পরেও বুকের দুধ কেন খেতাম, আর কীভাবে সেটা পেতাম সেটার রহস্যের চেয়ে মর্মান্তিক ছিল– কাছের আত্মীয়দের কাছ থেকে খোঁটা শোনা। অনেকদিন পর্যন্ত এই ছেলেমানুষির অপমান সইতে হয়েছে সবার কাছে। দীর্ঘদিন স্বাস্থ্যকর মাতৃদুগ্ধ পানের পরও কেন আমাকে সারাজীবন নানা অসুস্থতায় ভুগতে হয়েছে সেটাও রহস্য।
আমার দৈহিক গড়ন আম্মার মতো, কিছুটা নাদুসনুদুস, ঢলঢল। সামান্য কিছুটা অবয়ব পেয়েছি আব্বার কাছ থেকে। আমার পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতা নিয়েও সারাজীবন সমস্ত কাজিনদের মাঝে বেঁটে দুর্নাম নিয়ে চলতে হয়েছে। আব্বা ছয় ফুট, ভাইয়া ছয় এক। ছোটটি পাঁচ ফিট দশ।
ছোটবেলায় কয়েকবার জ্বর হয়েছে, সেগুলোর স্মৃতি মনে নেই। দাঁতের সমস্যা ও দাঁতব্যথা ছিল আজীবন। সেটা সম্ভবত: নিয়মিত ব্রাশ না করার বদভ্যাসে। নানাবাড়িতে বেদেনীরা আসত। কি একটা গাছের শিকড় দাঁতের ফাঁকে রেখে দিয়ে মন্ত্রতন্ত্র পড়ত। আর পরে মুখের ভিতর থেকে শিকড় বের করে দেখাত। শিকড়ের সঙ্গে থাকত সাদাটে একধরণের পোকা। আমরা ভাবতাম দাঁতের পোকা বের হয়ে গেল আর ব্যথা করবে না। যদিও দুইদিন পরে আবার ব্যথা হতো। বহুদিন পরে জেনেছি, বেদেনীরা কলাগাছের মাঝখান থেকে ঐ সাদাটে পোকা বের করে হাতের কারসাজিতে শিকড়ে লাগিয়ে সবাইকে বোঝাত।
পায়ে ফোঁড়া হয়ে দীর্ঘদিন ভুগেছি, সেটার ক্ষতচিহ্ন আছে। আরেকবার খোসপাঁচড়া টাইপ কিছু হয়েছিল দুই পায়ে, সেটা সারাতে নাকি কয়েকবছর লেগেছে। সেটার চিহ্নও দীর্ঘদিন ছিল।
ক্লাস টু থেকে পেটের অসুখবিসুখ লেগেই ছিল। মিরপুরে আসার পর শুরু হল রক্ত আমাশা, হেন ডাক্তার নাই দেখানো হয় নাই। অবশেষে সামনের বিহারী ক্যাম্পের এক কবিরাজি ওষুধ খেয়ে সেরেছে। দুর্বল পাকস্থলী আমাকে ভুগিয়েছে বহু বহুদিন। এখনো হুট করেই ফুড পয়জনিং হয়। সবার যে খাবারে কোন সমস্যা হয় না, সেইটা আমাকে শয্যাশায়ী করে ফেলে।
স্কুলের সময়, দুপুরের টিফিনে বাসায় খেতে আসতাম। বাসা থেকে স্কুল ৩/৪ শ মিটার দূরে। বাসায় এসে কোনমতে খেয়েই আবার ছুটতাম। এই হুড়োহুড়িতে আর দুর্বিষহ গরমে জন্ডিস বাঁধিয়ে বসলাম।, স্কুল জীবনেই দুইবার জণ্ডিস। একবার সারলো দীর্ঘ বিশ্রামে। আরেকবার ক্লাস ফাইভের দিকে জণ্ডিস হল। সারে না তো, সারেই না। দিনের পর দিন , ডাকঘর অমলের মতো আমি বিষণ্ণ হয়ে বিছানায় ও গৃহবন্দী হয়ে থাকতাম। স্কুল গেছে চুলোয়। মিরপুরের সব ডাক্তার ঘেঁটেও কিছু যখন হল না, তখন আমার ছোটমা খবর পাঠালেন , তাঁর ওখানে, মানে লালকুঠিতে কোন এক ধন্বন্তরি কবিরাজ আছে। রোগীর মাথার উপরে মন্ত্রপূত বিশেষ কোন একটা গাছের শেকড়ের অথবা ডালের মালা রেখে দেন। সেই মালা আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে শরীর বেয়ে নেমে গেলেই জণ্ডিস সেরে যায়। তাই সই ! কবিরাজ এসে আমাকে একটা গাছ তলায় বসিয়ে মাথার উপরে ছোট্ট একটা শিকড়ের মালা রেখে দিল। একদিকে আমি আর আরেকদিকের বারান্দা ভর্তি উৎসুক জনতা , কী হয় কী হয়। কবিরাজ কিছুক্ষণ পরে পরে এসে মালা দেখে যায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে সেই মালা বড়ো হতে থাকল আর মাথা গলিয়ে কাঁধ আর শরীর বেয়ে নেমে গেল। আমি বড়ো হয়ে অনেক ব্যাখ্যা খুঁজেছি ; যেহেতু কুসংস্কারে আমার বিশ্বাস নিতান্তই কম। একটা ব্যাখ্যা হতে পারে, কবিরাজ মালাটা সুতো আর খুব চিকন ডালের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে বানিয়েছিল। সুতার গিঁঠ গুলো এমন যে ধীরে ধীরে তা খোলে আর মালাটা বড় হয়ে যায়।
দান দান তিন দান, আবার জণ্ডিস হলো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে। হলে থাকতে আমরা পানি ফুটিয়েই খেতাম, কিন্তু সারাক্ষণ কী আর সেটা চলে ! বিকালের নাস্তায় হোটেল, দোকানে-টোকানে গেলে এদিক সেদিক হতো। এবারে জণ্ডিস বেশি ভোগাল না, হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন নিলাম। এর পরে আর কখনো সমস্যা হয়নি।
বছর আটেক আগে অফিস ট্যুরে নেদারল্যান্ডে।
এক বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে ঢুকে বিফ স্টেক অর্ডার করলাম। বলে দিলাম ওয়েল ডান। ব্যাটা ওয়েটার, সে কী বুঝল কে জানে ! খাবার সার্ভ করার পরে কেন যেন মনে হচ্ছিল ওয়েল-ডান করে নাই। ছুরি চালাতেই দেখি ভিতরে কাঁচা কাঁচা । এতো টাকার ডিনার তারপরে লেগেছিল ভয়ঙ্কর ক্ষুধা। কিছুটা খেয়ে ভিতরের তরল গোলাপি রক্তের ছিটে দেখে আর খেতে পারলাম না। ফুড পয়জনিং হয়ে গেল। ট্রাভেলে কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ কাছে রাখি। কয়েকটা ফ্লাজিল , অ্যামোডিস ছিল ; দুইদিন খেয়ে মিটিং পার করলাম।
ট্রেনে এলাম জার্মানিতে। কোনমতে হোটেলে পৌঁছে যাচ্ছেতাই অবস্থা। রুমে বা বিছানায় থাকার চেয়ে আমার সময় কাটতে লাগলে রুম লাগোয়া টয়লেটে। পরদিন মিটিং অনেক কস্টিং। অনুজ দুই সহকর্মীকে বুঝিয়ে সুজিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু প্রধান ক্রেতা নিজেই হোটেল থেকে আমাকে পিক করল। আমি বললাম, দেখো দেশ থেকে আনা আমার ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। ফ্ল্যাজিল , অ্যামোডিস তো বুঝবে না, তাই জেনেরিক নাম বললাম, মেট্রোনিডাজল (metronidazole) কি পাওয়া যাবে? সে গুগল করে বলল, এটা তো অ্যান্টিবায়োটিক। ওভার দি কাউন্টার পাওয়া যাবে না। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন লাগবে। আবার তুমি জার্মান নাগরিক না, যে হাসপাতালে নেব। প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে গেল। ভাষান্তর করে সব বোঝার পর আমাকে লিকুইড ওষুধ দিল ডাক্তার। দেখতে হোমিওপাথির খয়েরি বোতলের মতো । সেটা কয়েকদিন খেতে বললেন, আর বললেন বিশেষ একধরণের নোনতা রুটি খেতে। আমি তাই কিনে খেলাম, দুইদিনে সেরে উঠলাম।
একবার সেকেন্ড ইয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার আগে মহল্লায় পক্স, প্রতিবছর মে মাসে হয়। আম্মা আমাদের ঠাণ্ডা জায়গায় থাকতে বলেন, শীতল থাকতে বলেন, করলা ভাজি খাওয়ান। সবচেয়ে বড় ব্যাপার নিজেরাও সাবধানে থাকি, সময়মত খাই। গোসল করি। কিন্তু সেটা আমার ছোট-ভ্রাতা শোনে না। ও পড়ে স্কুলে । ফিরেই ব্যাগ ফেলে দৌড় দেয় খেলতে। আম্মার হাজার বারণেও কাজ হয় না।যথারীতি পক্স বাঁধিয়ে আনল। প্রথমে তিনদিনের মাথায় সেরে উঠল ; ওর পরে বড়ভাই, সে ভুগল এক সপ্তাহের মতো। অবশেষে বাড়ীর শেষ অভিযাত্রী হিসাবে আমার জীবনে বসন্ত এলো। মে-জুনের বিভীষিকাময় গরম। আর আমার রুমের ছাদ ছিল টিনের। সকাল না গড়াতেই চিটচিটে গরমে রুমের প্রতিটা আসবাবপত্র উষ্ণ হয়ে উঠত। বিছানার চাদর হয়ে উঠত গরম। আমার সারা শরীর জুড়ে টসটসে ফোস্কার মতো পক্স। আমি সেই বীভৎস গরমে টিনে চালের রুমে পাক্কা এক মাসের বেশি পক্স নিয়ে জেরবার হলাম। শরীরের হেন জায়গা ছিল না , পক্স হয়নি । সংক্রমণ যাতে না ছড়ায় , সেজন্য আমি সারাদিন রুমে। শুয়ে শুয়ে সময় কাটত না। শারীরিক যন্ত্রণায় কাতরাতাম আর আর যাকে ইচ্ছে তাকে অভিশাপ দিতাম। অভিশাপের বেশির ভাগ আমার অনুজের দিকেই ধাবিত হত। বসন্ত চলে গেল রেখে গেল সারা শরীর জুড়ে তার স্মৃতিচিহ্ন।
অধুনা টুকটাক জ্বরজারির প্রকোপ ছাড়া বেশিরভাগ সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিলাম।
তারপরেও ডেঙ্গু আর চিকনগুনিয়ার সময় এলেই সাবধানে থাকতাম। বেশ কয়েকবছর কোনরকমে পার পেলেও চিকনগুনিয়া ২০১৭ সালে ছুঁয়ে গেল। শুধু প্যারাসিটামল আর বিশ্রামে জ্বর চলে গেলেও ক্লান্তি গেল না। ভয়ংকর ক্লান্তি। প্রতিদিন সকালে উঠে দেহটাকে বয়ে নেওয়া, প্রাতঃকৃত্য সারা, জামাকাপড় পড়ে অফিসে যাওয়া, সবকিছুতেই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। যে আমি প্রত্যেক হাঁটতে যেতাম, সেই আমি এতো লিথার্জিক হলাম যে টানা বছর দেড়েক সবরকম শারীরিক ব্যায়াম থেকে দূরে থাকলাম।
এবছর রোজার শেষপ্রান্তে মে মাসে শ্বশুরকে নিয়ে ডায়ালাইসিসের জন্য হাসপাতালে। ক্যান্টিন বন্ধ। পাশের নামকরা বিরিয়ানির দোকান থেকে বিরিয়ানি নিয়ে আসা হল। তিনজন খেলাম, কারো কিছু হলো না ; আমার হল ফুড পয়জনিং।
সেটা সপ্তাহ খানেক ভোগাল। এই খাই সেই খাই, কোনভাবেই কিছু হচ্ছিল না বলে ডাক্তারের পরামর্শে আবার সেই অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ।
আমি সবকিছুতেই অতিরিক্ত স্পর্শকাতর। সবাই সামান্যতে পার পেয়ে গেলেও , আমি ধরা খেয়ে যাই। শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুর্বল। প্রায় অকেজো দাঁতের পাশাপাশি , জণ্ডিসে লিভার, ধূমপানে ফুসফুস। আব্বা-আম্মা, ভাইয়ার উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিকে কিডনি ফেল । আমার হৃদপিণ্ড ভেবেছিলাম কাজ করছে ঠিকঠাক। গত জানুয়ারি থেকে জানা গেল সেটাতেও ঝামেলা পাকিয়ে বসে আছি। এখন নিয়মিত ওষুধ খেতে হচ্ছে।
কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছে, করোনা থেকে যতোই পালাই ; এটা সবাইকে স্পর্শ করবেই। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু। আগস্টে না হোক, অক্টোবরে। ডিসেম্বরে না হোক জানুয়ারিতে। আমি ভয় কাটিয়ে উঠেছি। হবেই যেহেতু, নিজেকে যতদূর পারি প্রস্তুত রাখি যুদ্ধ করার জন্য। জীবনের এতোগুলো ধাক্কা যেহেতু কাটিয়ে এ পর্যন্ত এসেছি, এ যাত্রায়ও পার পেয়ে যাব আশা করছি।
প্রকাশকালঃ ২৩শে জুন,২০২০

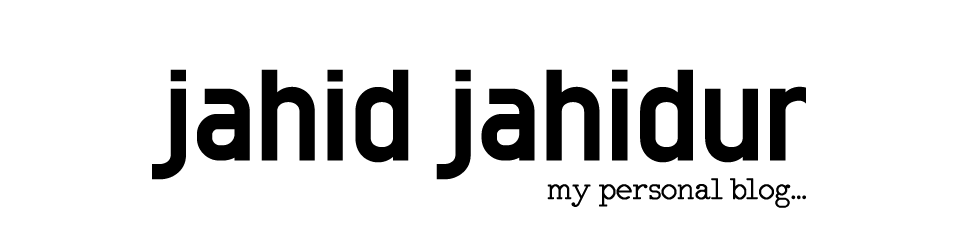

সাম্প্রতিক মন্তব্য