by Jahid | Nov 29, 2020 | দর্শন, লাইফ স্টাইল, সমাজ ও রাজনীতি
আমি প্রথমেই একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে আমার কথার শুরু করি। গল্পটা এ রকম যে, এক হাসপাতালে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে এক রোগী এল। সঙ্গে সঙ্গে তার এক্স-রে করা হলো। কিন্তু একি! রোগীর পেটের মধ্যে শত শত চায়ের চামচ দেখা গেল। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘তোমার পেটে এত চায়ের চামচ এল কী করে?’ সে তখন কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিল, ‘স্যার, ওই যে বিখ্যাত ডাক্তার কাদির সাহেব, এফসিপিএস, এমআরপিএস বলেছেন দিনে দুই চামচ করে তিনবার খেতে।’
তো আমরা এই ডাক্তার কাদির সাহেবের মতো মানুষ দ্বারাই আসলে পরিচালিত হই। তারা যা বলেন, আমরা তা-ই করি। আমরা কখনো দেখি না চায়ের চামচ খাওয়া ভালো, না খারাপ। এটা আমরা ভাবি না। এতে আমাদের কোনো ভালো-খারাপ কিছু হয় কি না, সেটা আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের জীবনে এই ডাক্তার কাদির কারা? এই কাদির হচ্ছেন আমাদের অভিভাবক, আত্মীয়, আমাদের বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীসহ গোটা পৃথিবী। তারা আমাদের যা করতে বলেন আমরা তা-ই করি। যেমন: আমার আব্বার কাছে শুনেছি যে তারা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত তখন বলা হতো যে গণিত আর দর্শনই সেরা বিষয়। তাই এ দুটো পড়তে হবে। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দিলাম, তখন যুগ পাল্টে গেল। তখন সেরা হলো ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং। আবার মানবিকের শিক্ষার্থী হলে ইংরেজি অথবা অর্থনীতি। কারণ ওই দুটো দিয়ে সিএসপি হওয়ার সুবিধা ছিল। তারপর আরও সময় পার হলো। এখন এসে দাঁড়িয়েছে বিবিএ, এমবিএ। একের পর এক চাপের মধ্যে আমরা পিষ্ট হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছি না। কোনোকালেই আসলে কেউ কিছু করে উঠতে পারেনি। আমি কী চাই, আমি কী করতে ভালোবাসি, আমার প্রাণ কী চায়, আমার জীবনের আনন্দ কোথায়—এই খবর কেউ নিতে আসে না। ফলে আমরা সারা জীবন ধরে আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাই।
আমরা আমাদের কোনো দিন চিনতে পারি না। নিজেদের কোনো দিন খুঁজে বের করতে পারি না। আমরা আমাদের আনন্দজগৎকে তাই কোনো দিন আত্মস্থ করতে পারি না। অবশ্য এ রকম হওয়ার কারণ আছে। কেন আমাদের এসব বলা হয়? একটা কারণ হলো দারিদ্র্য। আমাদের দেশে কিছুসংখ্যক মানুষ ছাড়া বাকি সব মানুষ দারিদ্র্যসীমার এত নিচে থাকে যে নিজের ইচ্ছামতো কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। নিজের প্রাণের খোরাক জোগানোর সুযোগ আমরা কমই পাই। সুতরাং যেখানে অর্থ আছে, যেখানে টাকা আছে সেখানে আমাদের চলে যেতে হয়। সেটা আমাদের ভালো লাগুক আর না-ই লাগুক।
আরেকটা সমস্যা হলো আমাদের বাবা–মাকে নিয়ে। যেমন আমরা ১১ ভাইবোন ছিলাম। আমার দাদারা ছিলেন মাত্র ১৮ ভাই এবং ১৪ বোন। এত ছেলে-মেয়ে সেকালে থাকত যে বাবা-মা তাদের ঠিক দেখেশুনে রাখতে পারত না। তাই তাদের নিয়ে তেমন কোনো চাপ ছিল না। তারা নিজেদের যা ইচ্ছা তাই হতে পারত। কিন্তু আজকে ছেলেমেয়ের সংখ্যা ২–এ নেমে এসেছে। সব সময় বাবা-মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে তাঁর ছেলেমেয়ে কী করছে। আজকের ছেলেমেয়েরা যেন বন্দিশালাতে আটকে আছে। সর্বদা নজরদারির কড়া শিকলে বন্দী তারা। আজকের মতো অত্যাচারিত শিশু আমাদের দেশে কখনো ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, বাবা-মা যা হতে পারেননি, ওই ১-২ জন ছেলেমেয়ে দিয়ে তারা তার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেন। এটা তো বড় কঠিন কাজ। এই বাচ্চা ছেলেমেয়ে কীভাবে এই বড় দায়িত্ব পালন করবে।
এরপর এল চাকরি। চাকরি এক মজার জায়গা। এখানে বাণিজ্যিক প্রভুরা তাঁদের মর্জি চালান। তিনজন মানুষ লাগবে। নেবে একজন। তাকে আবার বেতন দেবে দুজনের। তাতে টাকার পরিমাণ বাড়ে। সাথে যে চাকরি পেল সে নিজেও এত টাকা পেয়ে খুশি হয়। কিন্তু সকাল আটটায় অফিসে ঢুকে রাত ১০টা নাগাদ বাসায় ফেরার পর তার মনে আর কোনো শান্তি থাকে না। বাড়ির টেলিভিশনের সামনে টাইটা খুলে দিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে। এই দৃশ্যটা দেখতে মোটেও ভালো লাগে না। তাদেরকে চিপে, পিষে তাদের সমস্ত রক্ত আমরা নিয়ে যাচ্ছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই এটা নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল। তখন কবি বলেছিলেন,
‘হোয়াট ইজ লাইফ ইফ ফুল
অব কেয়ার
উই হ্যাভ নো টাইম টু স্ট্যান্ড
অর স্টেয়ার’
এই যে ঊর্ধ্বশ্বাস জীবন, এই যে কাজ, এই যে ব্যস্ততা—এসব মিলিয়েই কি আমাদের জীবন? আমরা কি একটু দাঁড়াতে পারব না? আমরা কি একবার এই চারপাশের সুন্দর পৃথিবীর দিকে তাকানোর সুযোগ পাব না? এত অসাধারণ–অবিশ্বাস্য পৃথিবীতে আমরা যে এসেছি, সেটার কোনো আনন্দ কি আমরা নিতে পারব না? কেন এই কথা হয়েছিল? ১৮১৯ সালের দিকে ইংল্যান্ডে একটা আইন পাস হয়েছিল। কাউকে ২০ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। কী রকম মারাত্মক আইন আপনি চিন্তা করুন। তখন হয়তো ২২ ঘণ্টা খাটানো হতো। হয়তো কর্মীকে তারা ঘুমাতেই দিত না। এ রকম ভয়ংকর নির্যাতনও সেই সময়ে করা হয়েছে মানুষের ওপর। এই যে ‘মে ডে’তে শিকাগোতে শ্রমিকদের ওপরে গুলি করা হয়েছিল। শ্রমিকেরা কী চেয়েছিল? শুধু ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা ঘুম আর ৮ ঘণ্টা আনন্দ করার সুযোগ চেয়েছিল। কিন্তু প্রভুরা বলেছিল যে ৮ ঘণ্টা আনন্দ করা চলবে না। সেটার ভেতর ৬ ঘণ্টা তাদের জন্য কাজ করতে হবে। এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত এ রকম দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে।
আমি আরেকটা ছোট্ট গল্প দিয়ে শেষ করি। পথে যেতে যেতে একজন যুবকের সঙ্গে দেখা হলো অপূর্ব এক সুন্দরীর। সুন্দরীকে দেখেই সে প্রেমিক যুবক বলে বসল, ‘আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।’ আবার সুন্দরীরও এই যুবককে অপছন্দ নয়। তারও ভালো লেগেছে। কিন্তু সে বলল, ‘আমি একটু অসুবিধায় আছি। আমার বাড়ি হলো সাত সমুদ্রের ওপারে। আমি আমার বাবার সঙ্গে সেখানে যাচ্ছি। এখন তো আর আমাদের বিয়ে সম্ভব নয়। তুমি সেখানে এসো। তখন আমি এই বিষয়ে ভেবে দেখব।’
যুবক তো আর অপেক্ষা করতে পারল না। কিছুদিন পরেই সে সুন্দরীর জন্য সাত সমুদ্রের উদ্দেশে পাড়ি জমাল। প্রথম সমুদ্রের পাড়ে সে যখন গেল, সেখানে এক খেয়া মাঝি সাগর পার করে দেবে। সেই খেয়া মাঝি তাকে বলল, ‘আমি চাইলেই তোমাকে এই সমুদ্র পার করে দিতে পারি। কিন্তু এ জন্য তোমাকে তোমার হৃৎপিণ্ডের সাত ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিতে হবে।’ সে ভাবল যে তার এত গভীর প্রেম। প্রেমের জন্য না হয় একটু ত্যাগ স্বীকার সে করলই। সে রাজি হয়ে যায় মাঝির কথায়। পার হলো সে প্রথম সাগর। দ্বিতীয় সাগরের খেয়া মাঝিও একই কথা বলল। এভাবে দিতে দিতে সাত সমুদ্র সে যখন পার হলো তখন দেখা গেল তার মাঝে হৃদয় বলে আর কিছুই নেই। তার হৃদয় খণ্ড খণ্ড হয়ে হারিয়ে গেছে।
এই যে আমাদের সময়ের ওপর যে নিষ্পেশন, যে টানাপোড়া চলে এই আমাদের ব্যস্ত জীবন নিয়ে, সেটা আমাদের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনে না। আমাদের জীবন যে আনন্দের এক নতুন উৎস, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। জীবনের এই আনন্দ আমরা খুঁজে পাই সময়ের কাছ থেকে। কেউ যদি আমাদের কাছ থেকে এই সময়কেই কেড়ে নেয়, তাহলে আমরা কীভাবে সুখী হয়ে বেঁচে থাকব? আমরাও যদি আমাদের সময়কে অন্য কাউকে দিয়ে দিতে থাকি, তাহলে আমাদের জীবন কোথায়? কীভাবে আমরা আমাদের ভেতরের মানুষকে গড়ে তুলব?
নাসিরুদ্দিন হোজ্জার একটা গল্প আছে যে এটা যদি বিড়াল হয় তাহলে কাবাব কোথায়। আবার এটাই যদি কাবাব হয় তাহলে বিড়ালটা কোথায়। তো এই জীবন যদি জীবন হয় তাহলে আসল জীবন কোথায়? তাই আমি এই তরুণদের কাছে বলব রবীন্দ্রনাথের একটি কথা:
‘বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই
গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।’
এই যে অপরূপ বিশ্ব—তা আমাদের চোখ দিয়ে, আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে আমাদের জীবন দিয়ে যদি উপভোগ না করে যাই তাহলে আর এই জীবনের মানে কী? আমি সবাইকে অনুরোধ করব এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে। কেননা তোমরা এখন জীবনের পথে অগ্রসর হতে যাচ্ছ। তোমাদের এখনই ভাবার সময়। পরে আর এসব ভেবে কোনো লাভ হবে না। তোমাদের আগামী সময়ের জন্য শুভকামনা রইল। সকলকে ধন্যবাদ।
[ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। গত ২৮ মার্চ ,২০১৯ ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (আইইউবি) সমাবর্তনে বক্তা ছিলেন তিনি।]
by Jahid | Nov 29, 2020 | সমাজ ও রাজনীতি
সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ প্রথম দেখি ১৯৮১ সালের দিকে সাদাকালোর বিটিভিতে। ক্লাস টুতে পড়ি। কী কারণে যেন সার্ক দেশগুলোর বেশ কিছু ছবি একবারে দেখিয়েছিল। কিছু কিছু ফিল্ম বা সাহিত্য কেন চিরন্তন বা ক্লাসিক হয়ে ওঠে সেটা বোঝার মতো বয়স আমার ছিল না। পরবর্তী কৈশোরে অনেক বার এই প্রিয় ছবির মুখোমুখি হয়েছি। এখনো অনেক চ্যানেলের ফাঁকে ‘হীরক রাজার দেশে’ প্রচারিত হতে দেখলে আটকে যাই, আবার দেখি।
নিকট অতীতে তাবৎ পৃথিবীর সবদেশের রাষ্ট্র-যন্ত্র ঠিক এইভাবে চলেছে , এখনও চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।
আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা এশিয়া আরব সব এক। শুদ্ধাচারী দেশ হিসাবে যাদের উদাহরণ দেওয়া হয়, সেখানে রাজা ও যন্ত্র-মন্তরের দায়িত্ব নিয়েছে মিডিয়া। আপনি ঠিক ততটুকু দেখবেন যা আপনাকে দেখতে দেওয়া হবে।
পৃথিবীর এক প্রান্তে অর্থহীন যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের খবরের চেয়ে কোন এক এঁদো গলিতে একটা বিড়াল গাছে উঠে নামতে পারছে না, সেটা দমকল বাহিনী এসে উদ্ধার করছে ; সেই লাইভ নিউজ এঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।
ট্রাজেডি হচ্ছে রাজা-উজির-নাজির প্রশাসনের অন্যায় আর বিচারহীনতার প্রতিকার তাঁদের কাছেই চাইতে হয়। এ এক দুর্ভেদ্য চক্র !
প্রকাশকালঃ ১৬ই নভেম্বর,২০১৯
by Jahid | Nov 29, 2020 | দর্শন, সমাজ ও রাজনীতি
‘আমেরিকান ড্রিম’ বলে একটা হাইপ আছে আমেরিকায়।
কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছে। ক্যাপিটালিজমের পক্ষের ও বিপক্ষে এটা নিয়ে বিতর্ক আছে । আমেরিকার নৈতিক-অনৈতিক উত্থানের পক্ষে কথা থাকতেই পারে। তবে আমি খুব কম সময়ের জন্য এই মহাদেশের কয়েকটা প্রদেশে গিয়েছি। এতোটাই সংক্ষিপ্ত সময় যে, তার উপর ভিত্তি করে কোন মন্তব্য করা ঠিক না। আবার সাহস পাই এই কারণে, এতো সেলিব্রেটি আর জ্বলজ্বলে বুদ্ধিজীবীদের মাঝে আমি কিছু লিখলেই কী আর না লিখলেই বা কী !
আমি আমেরিকার শহরে ও গ্রামের পথে চলে ও কিছু লোকের সঙ্গে চলাফেরা করে টের পেয়েছি, আসলেই এই ‘আমেরিকান ড্রিম’ ব্যাপারটা আছে । একজন গড়পড়তা আমেরিকান ; ধরেন আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে নিম্নবিত্ত বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কেউ , যাকে অর্থনৈতিক সক্ষমতার মাপকাঠিতে আমাদের সমাজে নিতান্তই অচল মনে হচ্ছে —আমেরিকাতে কিন্তু তারও একটা গাড়ী আছে; থাকার মতো একটা ঘর আছে। এই আমেরিকান লোকটি যদি আমাদের তৃতীয় বিশ্বের কোন একটা দেশে থাকত ; তাহলে সারাজীবনেও এটা সে অর্জন করতে পারত না !
আমাদের বাংলাদেশের ড্রিম কি ?
১।ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা;
তাহার মাঝে আছে দেশ এক- সকল দেশের সেরা;
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সে যে-আমার জন্মভূমি।
২।সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশ
৩।ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা
আপনার মত কি ?
প্রকাশকালঃ ১৪ই নভেম্বর ,২০১৯
by Jahid | Nov 28, 2020 | লাইফ স্টাইল, সমাজ ও রাজনীতি
পূর্ববর্তী প্রজন্মে প্রচলিত ধারণা ছিল ভ্রমণ হচ্ছে আনন্দের ও শিক্ষার। তাঁরা তীর্থযাত্রা বা পুণ্যস্থান ভ্রমণ বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ভ্রমণ করত । কিন্তু যাত্রাপথের ঝক্কির জন্য অনেকাংশে ভ্রমণ ছিল ক্লান্তিকর, বিরক্তিকর। আগের প্রজন্মে ভ্রমণ-বাতিকগ্রস্ত লোক ছিল না , তা নয়। আগেও ছিল, সেটা ছিল উচ্চবিত্ত ও একেবারে তরুণ সম্প্রদায়ের। এঁদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য যতোটা না ভ্রমণের জন্য ছিল –তার চেয়ে বেশি ছিল জীবনের প্রাত্যহিক বাস্তবতা থেকে পালিয়ে বেড়ানো, কর্তব্য ফাঁকি দেওয়া এবং আত্মীয় স্বজনের উৎপাত থেকে দূরে থাকার জন্য।
মূলত: আগেও যেটা চিরন্তন সত্য ছিল, এখনও আছে ; সেটা হচ্ছে , যে এক জায়গা দশবার দেখে তার দেখা হয় সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন। আর দশটা জায়গা যে একবার করে দেখে তার দেখা হয় অসম্পূর্ণ । আর যে দশ মিনিটে একটা জায়গা দেখে তার দেখা হয় না কিছুই !
বর্তমানে আমাদের ভোগবাদী সমাজের প্রদর্শনকামী বাড়ন্ত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্তের বিনোদন এবং বড় মুক্তির জায়গা বছরে তিন-চারবার ভ্রমণ। আমাদের প্রাত্যহিকতায় আমরা ক্ষয়ে যাই । জীবনের নানাবিধ যন্ত্রণার মাঝে আমাদের বিনোদন ও মুক্তির দরকার ; খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার দরকার। আমাদের মন এই নাগরিক একঘেয়েমিতে শুকিয়ে যায়। ভ্রমণের আনন্দ এক পশলা বৃষ্টির মতো আমাদেরকে সতেজ করে দেয়।
পরিবারের সবাই আমরা আবার ঘুরতে যাব এই আকাঙ্ক্ষা ও আশা আমাদের বুঁদ করে রাখে ! ভ্রমণের সময় আমরা আকাঙ্ক্ষিত উত্তেজনা প্রায়শ:ই পাই না। কিন্তু যে আনন্দ উত্তেজনাই বোধ করি না কেন – ফিরে আসার পর আমরা সেই উত্তেজনায় আরও কিছু আরোপিত প্রলেপ দিই, সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি দিই। পাড়াপড়শির ঈর্ষা-কাতর চোখ আমাদের সাময়িক উত্তেজনা এনে দেয়। এর পরের দিনগুলো আমরা আবার স্মৃতিকাতর হয়ে থাকি ; প্রতিদিনের জীবিকার গ্লানিকে মেনে নিয়ে পরবর্তী ভ্রমণের পরিকল্পনা করি।
এই মানসিক অবস্থাকে ঠিক নেশার সঙ্গে তুলনা করা যায় কিনা আমি জানি না। একবার একটা ডোজের আশু উত্তেজনার বিরতিতে আসক্ত ব্যক্তি যেমন নানা সুখ-কল্পনায় মেতে থাকে, কখন আবার আরেক ডোজ পাবে। ভ্রমণবাতিকগ্রস্থ অথবা ভ্রমণপিপাসু মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্তদের হয়েছে সেই অবস্থা !
প্রকাশকালঃ ২রা নভেম্বর,২০১৬
by Jahid | Nov 28, 2020 | সমাজ ও রাজনীতি, সাম্প্রতিক
ওড়াউড়ির দিন [প্রথম খণ্ড: আমেরিকা] ।। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।
প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০
দেশের জন্যে এই ব্যাকুলতা প্রবাসীদের মধ্যে যে কতখানি প্রবল একটি গল্প শুনিয়ে তা বোঝানোর চেষ্টা করি। আগেই বলেছি, বিদেশে বাস করা সম্পন্ন ও সচ্ছল বাঙালিদের মধ্যে এই ব্যাকুলতা যতখানি তার চেয়ে এ অনেক বেশি পৃথিবীর নানান প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শ্রমিক শ্রেণীর গরিব অসহায় মানুষের মধ্যে । সচ্ছল মানুষদের মনকে জন্মভূমি যে কখনও সখনও উতলা করে না তা নয়। কিন্তু গাড়ি বাড়ি বিলাস বৈভবে ঝল-মল করা তাদের জীবনে সে পিছুটান বড় কিছু নয় । তাছাড়া ইচ্ছা করলেই তো তারা মাঝেমধ্যে দেশে এসে ঘুরে যেতে পারে। তারা তা যায়ও। তাই বিদেশে থাকলেও দেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার কষ্ট তাদের প্রবল নয়। কিন্তু গরিব প্রবাসীদের ব্যাপারে ঘটনাটা আলাদা। আদম ব্যাপারিদের খপ্পরে পড়ে জমি-বাড়ি বিক্রি বা বন্ধক দিয়ে নামমাত্র রোজগারের আশায় অচেনা দূর বিদেশের পথে পাড়ি জমায় তারা। শুধু পায়ের তলায় একচিলতে মাটির জন্যে, ছোট্ট একটু নিরুদ্বেগ ভবিষ্যতের জন্যে এক নিষ্ঠুর আর বৈরী পৃথিবীর সঙ্গে উদয়াস্ত লড়াই করে বছরের পর বছর জীবনকে তারা নিঃশেষ করে। হয়তো এসবই তারা করে সন্তান, স্ত্রী, বাপ-মা ভাই বা বোনের মুখে সামান্য একটুকরো হাসি ফোটানোর জন্যে। দূরদেশের নির্মম আবহাওয়া বা ঝলসানো রোদের ভেতর শরীর আয়ু ক্ষয় করে আমনুষিক শ্রমে তাদের জন্য দূর প্রবাস থেকে এরা বছরের পর বছর টাকা পাঠায়। সেই টাকা দিয়ে তার ভাইয়েরা বাজার থেকে চড়া দামে মাছ-মাংস কিনে নবাবী হালে দিন কাটায়, চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে ফুর্তিতে সময় গুজরান করে। ভাইয়ের পাঠানো টাকায় তার জন্যে জমি কেনার বদলে অনেক সময় গোপনে নিজের নামে রেজিস্ট্রি করে নেয়। এমন খবর ও কম শোনা যায় না যে এদের অনুপস্থিতির সুযোগে এদের পাঠানো টাকায় দামি গয়না শাড়ি পড়ে এদের স্ত্রীদের কেউ কেউ পরপুরুষের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি চালায়—তবু এই মানুষগুলো তাদের মুখ স্মরণ করেই হাজারো শৌখিন জিনিশে বড় বড় ব্যাগ-বস্তা ভর্তি করে বাড়ি ফেরে। প্রিয় পরিজনহীন নিঃসঙ্গ প্রবাসে তাদের ফেলে আসা দেশ, মানুষ, বন্ধু আর আত্মীয়ের মুখ তাদের কাছে স্বপ্নের তুলিতে আঁকা ছবির মতো রমণীয় লাগে। দেশের জন্য স্বপ্ন আর আকুলতা নিয়ে কেটে যায় তাদের হতচ্ছাড়া প্রবাসী জীবনের ভারাক্রান্ত মুহূর্ত।
এমনি একদল দুঃখী মানুষের সঙ্গে বছর তিনেক আগে দেখা হয়েছিল, দুবাই এয়ারপোর্টে। সেবারও আমেরিকা থেকে ফিরছিলাম। দুবাইয়ে প্লেন পাল্টে ঢাকার প্লেনে উঠছি। বোর্ডিং কাউন্টারে গিয়ে দেখি ফ্লাইটে বিদেশি নেই বললেই চলে। কাউন্টারজুড়ে গিজগিজ করছে মধ্যপ্রাচ্যের নানা-জায়গা থেকে জড়ো হওয়া ঘরমুখো বাঙালি শ্রমিকের দল। বুঝলাম, এদের নিয়মিত আনা-নেওয়ার জন্যেই এমিরেটস, ইতিহাদ, কাতার বা কুয়েত এয়ারলাইন্সের এত ঢাকা-মুখো ফ্লাইট। এদের কেউ তিন বছর, কেউ চার বছর , কেউ এমনকি পাঁচ বছর পর দেশে ফিরছে, সবার সঙ্গে বিরাট বিরাট বাক্স-পেটরার ভেতর কেনাকাটা করা সাধ্যমতো জিনিশপত্র। প্রিয়জনদের জন্যে কেনা এই জিনিশগুলো তাদের হাতে তুলে দেওয়ার স্বপ্নে তাদের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। দেশের জন্যে কী ব্যাকুলতা আর স্বপ্ন তাদের চোখে। উদ্বেল হৃদয় দিয়ে ফ্লাইটের পাঁচ ঘণ্টা আকুতি সময়টুকু সহ্য করার শক্তিও যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। যেন পারলে দুবাইয়ে প্লেনে উঠেই সরাসরি ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে যায়। কথা বলে বোঝা গেল এদের অধিকাংশই লিখতে পড়তে পর্যন্ত জানে না। আমার পাশেই বসেছিলেন থ্রি পিস স্যুট পরা ডাকসাইটে এক ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ আলাপের পরে একগাল বিগলিত হাসির সঙ্গে হাতের ইমিগ্রেশন আর কাস্টমসের কাগজদুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ভাবলাম , আমার ওগুলো দরকার ভেবেই হয়তো আমাকে দিচ্ছেন। বললাম, আমার আছে। লাগবে না।
‘একটু ফিলাপ কইরা দিবেন স্যার?’ মুখে দাঁত বের করা বিগলিত হাসি। কী আশ্চর্য ! এরকম একজন স্যুটপরা পুরোদস্তুর ডাঁটপাটওয়ালা ভদ্রলোক লিখতে পর্যন্ত জানেন না ? কিন্তু না, এমন বাঙালি একজন দুজন না, হাজারে হাজারে পাবেন মধ্যপ্রাচ্যের মতো পৃথিবীর নানা দেশের খেটে খাওয়া মানুষদের ভিড়ে।
কথায় কথায় জানলাম তিনিও একজন শ্রমিক। বাড়ি সিলেট, রিয়াদে কাঠমিস্ত্রির কাজ করেন। প্রথমে এসেছিলেন বসরায়, ইরাকে। সেখানে যুদ্ধের তাড়া খেয়ে আরবে পাড়ি জমিয়েছেন।
তার ফর্ম ফিলাপ শেষ হতেই, আরেকটা হাত এগিয়ে এলো সামনের দিক থেকে। তারটা শেষ হতেই দেখি চারপাশ থেকে ডজনখানেক হাত আমার দিকে এগিয়ে আছে। সব হাতেই একই ফর্ম। সবাই যে ভদ্রভাবে অনুরোধ করছে তা-ও না। অনুরোধ করার ভাষাও অনেকের জানা নেই। এ ধরণের দেহাতী মানুষের পক্ষে কী করেইবা তা সম্ভব?
‘এই যে , দেন তো, আমারডা ফিলাপ কইরা দেন।‘
মনে হয় হুকুম করছে।
দুঃখী এই লোকগুলোর জন্য মমতায় মনটা ভরে উঠল। প্লেনযাত্রার পুরো সময়টা এদের ফর্ম ফিলাপ করে চললাম। এদিকে বাংলাদেশ এগিয়ে আসছে। প্লেনভর্তি লোকগুলোর মধ্যে টানটান উত্তেজনা। কখন আসবে বাংলাদেশ। কেন আসছে না। চেহারায় তাদের আগ্নেয় উগ্রতা। সবার কথাবার্তার বিষয় একটাইঃ বাংলাদেশ। ঘরে ফেরার আগ্রহ আনন্দে উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ছে সবাই।
সামনের টিভি পর্দায় প্লেনের ছুটে চলার ছবি চোখে পড়ছে। আরব সাগরের ধার দিয়ে করাচির পাশ কাটিয়ে দিল্লি কানপুর পেরিয়ে প্লেন এখন বিহারের ওপর। এখনও অন্তত ঘন্টাখানেক বাকি। যাত্রীরা অস্থির বেসামাল । উত্তেজনায় যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। কোথায় বাংলাদেশ। কোথায় তুমি? মাতৃভূমি, তুমি কতদূর! অধিকাংশ লোকই মানচিত্র চেনে না। বুঝতে পারছে না ঠিক কোনখানে আছে। হঠাৎ জানালার পাশ থেকে কে একজন চিৎকার করে উঠলঃ ঐ যে ! ঐ যে ।
তার ব্যগ্র চিৎকার সারা প্লেনে যেন কেঁপে কেঁপে বেড়াতে লাগল। সবাই যেন এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ প্লেনের ভেতর ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। প্লেনভর্তি প্রায় সব লোক, একসঙ্গে দাঁড়িয়ে হুড়মুড় করে জানালার ওপর ঝুঁকে কী যেন আঁতিপাঁতি খুঁজছে। গলায় শুধু একটায় চিৎকার—কৈ? কৈ ? ( কোথায় আমার দেশ—ভাই, সন্তান, জীবনসঙ্গী , বাপ, মা, কোথায় তোমরা? ) প্লেনভর্তি এতগুলো লোক পাগলের মতো উঁকিঝুঁকি দিয়ে শুধু বাংলাদেশ দেখার চেষ্টা করছে।
হঠাৎ গোটা প্লেনভর্তি লোক একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলে যে বিমানের বিপদ হতে পারে সে জ্ঞান নেই এই লোকগুলোর। বিমানবালা আর পুরুষ ক্রুরা ধমক দিয়ে চিৎকার করে পাগলের মতো দুই হাতে টেনে-হিঁচড়ে ঘাড় চেপে তাদের বসানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু জানালা থেকে তাদের ফেরানো সোজা নয়।প্রবাসীদের কাছে বাংলাদেশ এমনি এক জ্বলন্ত রূপসী। আমাদের কাছে এর কতটুকু ?
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের এই ভ্রমণকাহিনীর সময়কাল সম্ভবত: ২০০০ সালের আশেপাশে। স্যারের অনেক বক্তৃতা তাঁর লেখায় আছে। অনেক ঘরোয়া আলোচনায় তা আবার নতুন করে তা উঠে আসে। পিনাকী ভট্টাচার্য্যের ( Pinaki.Bhattacharyya) ২০১৮ সালের শেয়ার করা একটা ভিডিও পোস্ট থেকে স্যারের ঘরোয়া বক্তৃতাটি নতুন করে ভাইরাল হয়েছে। সেজান মাহমুদ (Sezan Mahmud ) থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ফেসবুক সেলিব্রেটি এই প্রসঙ্গে আক্রমণাত্মক পোস্ট দিয়ে কুৎসিত অশ্রাব্য গালাগালির সুযোগ করে দিয়েছেন ফেসবুকের আমজনতাকে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বইপড়ার কলেজ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ঢাকা কলেজে আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ আমার শিক্ষক ছিলেন। মূল লেখাটিতে প্রবাসী শ্রমিকদের ব্যাপারে তাঁর গভীর মমতার প্রকাশ। কিন্তু ফেম-সিকার সেলিব্রেটিরা কোনভাবে গুণীজনকে তাচ্ছিল্য করার সামান্যতম সুযোগ হারান না।
আমি পুরো ব্যাপারটিতে মর্মাহত। মূল লেখাটি দাড়ি-কমাসহ পুনর্লিখন করেছি গভীর হতাশা থেকে। যদিও সেলিব্রেটিদের ক্ষমাপ্রার্থনা আজ পর্যন্ত চোখে পড়েনি আমার !
প্রকাশকালঃ ১৩ই জুন, ২০১৯
by Jahid | Nov 28, 2020 | সমাজ ও রাজনীতি, সাম্প্রতিক
আমাদের স্কুলজীবনে আশির দশকেও ঠিক বর্ষাকালের আগেই ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ঘুমন্ত সংস্থাগুলোর মনে পড়ে যেত সারাবছরের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজগুলো তাদের বাকী রয়ে গেছে ! তখন বিপুল উৎসাহে এরা ঢাকার রাস্তাগুলো খোঁড়াখুঁড়িতে মনোনিবেশ করত। আমারা দেখতাম, জুলাই, আগস্ট মাসের শেষের দিকেও কী গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্থাগুলো ঝকঝকে রাস্তাগুলো এলোপাথাড়ি খুঁড়ে খুঁড়ে সবার জীবন কী পরিমাণ দুর্বিষহ করে রাখছে।
সেই সময়ে মহল্লার এক বড়ভাই রসিকতা করে বলছিলেন, যেভাবে এরা গভীর মনোযোগ দিয়ে রাস্তা খুঁড়ছে , মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি ‘তেল’ আবিষ্কার করে ফেলবে ! এই ‘তেল’ হচ্ছে তৎকালীন মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোলিয়াম তেল অর্থে। খোঁড়াখুঁড়ি শেষে দায়িত্বশীল সংস্থাগুলো দীর্ঘ শীত-নিদ্রায় চলে যেত। পুরো বর্ষাকাল থইথই পানিতে রাস্তার খানাখন্দ ভরে থাকতে থাকতে সেগুলো নদীমাতৃক পলিমাটিতে ভরে যেত। শীতের শুরুতে সেই ভাঙাচোরা রাস্তার উপরে দিয়ে গাড়িঘোড়া চলতে চলতে ধূলোয় ধোঁয়ায় নাগরিক জীবনে ব্রংকাইটিস-হাঁপানির আয়োজন হতো !
তিন দশক পরে এসেও এই সংস্থাগুলোর সমন্বয়হীনতা একইরকম রয়ে গেছে। অথর্ব এই সংস্থাগুলো সারা ঢাকার শহর খুঁড়তে খুঁড়তে পেট্রোলিয়াম তেল বের করতে না পারলেও, আমাদের মতো সাধারণ জনগণের তেল যে বের করতে পারছে সে ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ !
প্রকাশকালঃ ১৩ই জুন,২০১৭
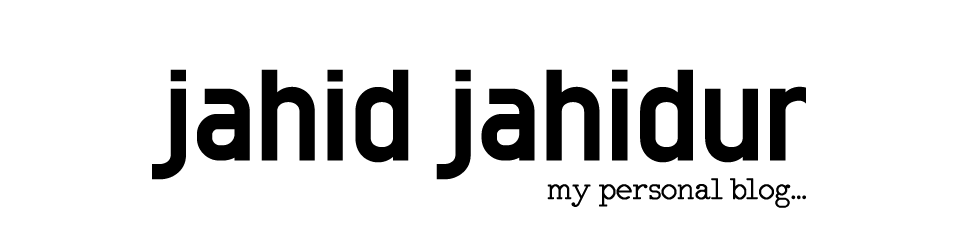
সাম্প্রতিক মন্তব্য