by Jahid | Nov 30, 2020 | সমাজ ও রাজনীতি, সাম্প্রতিক
[সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ: আমার পক্ষে অনেক গবেষণা করে কিছু লেখা মুশকিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি আমার প্রজন্মের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যা উপলব্ধি করেছি, দেখেছি তাই বলার চেষ্টা করি। অনেক রেফারেন্স বই ঘেঁটে ভারী ভারী লেখকের নাম দিয়ে প্রবন্ধ লেখা আমার সাধ্যাতীত। লেখা বড় হয়ে গেছে, তবে আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন। ]
ছোটবেলা থেকে চারপাশে মোটা দাগে তিন রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে আসছি। বাংলা মিডিয়াম, ইংরেজি মিডিয়াম এবং মাদ্রাসা। এছাড়া কারিগরি শিক্ষা নামের কিছু একটা শুনতাম ভাসাভাসা। যে শিক্ষাব্যবস্থা সবচেয়ে ভারী হওয়ার দরকার ছিল, সেটাই ছিল নিভুনিভু !
বাংলা মিডিয়ামে বর্ণবৈষম্য ছিল।
এলাকা ও স্কুলের আভিজাত্য ভেদে সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ছিল। ক্যাডেট কলেজগুলো , গভঃ ল্যাব, ধানমণ্ডি বয়েজ, হলিক্রস, ভিকারুন্নেসাসহ ঢাকার কিছু উঁচু সারির স্কুলকে ব্রাহ্মণ ধরলে প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলগুলো ছিল শূদ্র। অধুনা জাতীয় শিক্ষাবোর্ডের পুচ্ছে আরেক পালক সংযুক্ত হয়েছে ইংরেজি ভার্সন। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও অবকাঠামোর অভাবে কয়েকটি ব্রাহ্মণ স্কুল ব্যতীত বেশির ভাগ স্কুলের ভার্সনের শিক্ষাদান তথৈবচ।
ইংরেজি মাধ্যমেও এই শ্রেণিবৈষম্য আছে।
ইংরেজি মিডিয়ামের শিক্ষার্থীদের প্রথম থেকেই যে অভিযোগ ছিল আমাদের সময়ে , সেটা হচ্ছে এরা নিজভূমে পরবাসী। এরা গুচ্ছের অর্থনাশ করে বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মতো তৈরি হওয়া স্কুলগুলোতে যা শেখে আর যা শেখে না, সে আরেক বিশাল আলোচনা। তবে মূলত: এদের সিলেবাস পশ্চিমের তাই দেশের ব্যাপারে অনেকখানি উদাসীন, নিজের সমাজ ও পরিপার্শ্ব নিয়ে উদাসীন। নিজেদেরকে কুলীন ভাবে । সমাজের সবচেয়ে সম্পদশালী বাবা-মায়ের সন্তান হিসাবে এদের পরিপার্শ্ব থেকে এদের উদ্দেশ্যই থাকে কবে ভালোভাবে পড়া শেষ করে বিদেশে পাড়ি জমাবে।
মাদ্রাসায় আছে প্রধান দুইভাগ, কওমি, ফোরকানিয়া আর আলিয়া। আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাসে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান আছে। কওমি, ইবতেদায়ি, হাফিজিয়া মাদ্রাসাগুলোতে কিছুই নাই। আমার নানা লেখায় কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজের ব্যাপারে তিক্ততা আছে। আমি যে সমাজে বড় হয়েছি, সেখানে বড় একটা হাফিজিয়া মাদ্রাসা ছিল। ছোটবেলা থেকেই এদের ভিক্ষাবৃত্তি আমার মনে সহানুভূতির পাশাপাশি ক্ষোভের কারণ হয়েছে। প্রথম থেকেই মনে হয়েছে, দেশের বিশাল একটা জনগোষ্ঠীকে অনুৎপাদনশীল করে রাখার এই শিক্ষাব্যবস্থার কোন মানে হয় না।
মাদ্রাসা শিক্ষার সবচেয়ে বড় সমস্যা আমার কাছে মনে হয়েছে অর্থনৈতিক পরগাছা হয়ে বেঁচে থাকার পাশাপাশি এরা , জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবকিছুর ব্যাপারে এরা একটা অমূলক বিদ্বেষ নিয়ে বেড়ে ওঠে। এর মূল কারণ স্বল্প শিক্ষিত ধর্মীয় গোঁড়ামি নিয়ে বেড়ে ওঠা এদের শিক্ষকরা। সমাজের সবধরনের প্রগতিশীলতা আর আধুনিকতাকে এরা তীব্র ঘৃণার সঙ্গে দেখে। এভাবেই সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা একজনের সঙ্গে এদের মৌলিক মানসিক পার্থক্য গড়ে ওঠে। যথারীতি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার্থীদেরও মাদ্রাসা-শিক্ষিতদের ব্যাপারে স্পষ্ট তাচ্ছিল্য থাকে।
বেশ কয়েকবছর আগে আমার কাছের এক বড়ভাইয়ের সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে প্রায় সম্পর্ক ছিন্ন করার মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। প্র্যাকটিসিং মুসলমান হিসাবে তিনি তাঁর এলাকায় একটি মাদ্রাসা চালান। তর্কে তো আর কেউ জেতে না। তাই , নানা তর্কের পরে ধর্মান্ধতা, কূপমণ্ডূকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতার বাইরে গিয়ে যে কথা উনি আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে, তিনি কষ্ট করে হলেও গরীব ঘরের বাচ্চাগুলোকে দুইবেলা খাওয়ার ও নৈতিকতার ছায়াতলে আনতে পেরেছেন। মাদ্রাসার বাইরে থাকলে ঐ বাচ্চাগুলো সমাজের অধিকতর ক্ষতির কারণ হতো। ধর্মান্ধতা তো থাকতই, বরং ক্ষুধা ও অভাবে ছিনতাইকারী বা রাজনৈতিক দুষ্কৃতিকারী হয়ে উঠতো। যেমনটা হচ্ছে গ্রামের প্রান্তিক সমাজে ও ঢাকার বস্তির শিশুদের। আমাকে তর্কে ক্ষান্তি দিতে হয়েছিল সম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে। হয়তো আমার ঐ বড়ভাই গভীর মমত্ব থেকেই মাদ্রাসার শিশুদের ব্যাপারে কথাগুলো বলেছিলেন এবং তিনি সেটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মাদ্রাসাটি চালাতেন।
পরবর্তীতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে দেখেছি সাধারণ শিক্ষার ছাত্ররা , হোক সে উপজেলা-জেলা শহরের অথবা ঢাকার ব্রাহ্মণ সমাজের, তারা খুব সহজেই নিজেরা কাছাকাছি হয়েছে, বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ইংরেজি মিডিয়ামরাও কোন না কোনভাবে মূলধারায় মিশে গেছে । সামাজিক সমতা অথবা প্রায় কাছাকাছি শিক্ষাব্যবস্থা এই কয়েকটা শ্রেণির মিলেমিশে কাজ করাতে তেমন বড় বাঁধার সৃষ্টি করে নাই।
সমস্যা হচ্ছে বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মাদ্রাসার। মূলত: কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের। আমার বেড়ে ওঠা ঢাকার শহরতলী মিরপুরে। গ্রামের ব্যাপকতা আমার চোখে ধরা পড়েনি। তবুও একটা ব্যাপারে গ্রাম ও শহরতলীর মিল আছে। বাবা-মা , তাদের কয়েকটা সন্তানের ভিতর থেকে যে কোন একজনকে মাদ্রাসা বা ধর্মশিক্ষায় পাঠানোর দ্বিবিধ কারণ থাকত। প্রথমত: আখিরাতের সুরাহা করা, হাফেজের পিতামাতা কোনভাবেই দোজখে যাবে না, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত: ও প্রধানত: অর্থনৈতিক কারণ। অসহনীয় দারিদ্র্যের কারণেই মাদ্রাসাগামী শিক্ষার্থীর ঢল কমেনি কখনোই।
আশির দশকে সাধারণ শিক্ষার প্রভাব বেশি ছিল। জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের ইংরেজি মাধ্যম একটা ছিল ; সেটা টের পেতাম এসএসসি ও এইচএসসির প্রশ্নপত্র ঘাঁটতে গিয়ে। শুনতাম কাতারে, কুয়েতে বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশে থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসে ইংরেজিতে পরীক্ষা দিচ্ছে এসএসসি বা এইচএসসি। মিরপুরের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মহল্লায় কাউকেই দেখিনি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে। কোন কোন বন্ধুর বড়লোক আত্মীয় যারা গুলশান, বনানী বা ধানমণ্ডি থাকে তাদের কেউ কেউ পড়তো। অবাক ব্যাপার আমাদের বাংলা মিডিয়ামের ছেলেমেয়েদের ওদের ব্যাপারে একটা ঈর্ষামিশ্রিত তাচ্ছিল্য বা উন্নাসিকতা থাকত। কাউকে সামনে পেলে ‘ কী হে আলালের ঘরের দুলাল’ টাইপের একটা চাহনি দিতাম। মেডিক্যালে , বুয়েটে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন বন্ধু জুটে গেল ইংলিশ মিডিয়ামের। আশ্চর্য ! ওদের ব্যাপারে যে উন্নাসিক ধারণা ছিল, চলে গেল। এদের অনেকে বাসায় রবীন্দ্রসংগীত শেখে, সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা চেনে।
ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে আলিয়া মাদ্রাসা থেকে পাশ করা , মেধাতালিকায় জায়গা পাওয়া তুখোড় একজন এসে আমাদের সম্মিলিত মেধাতালিকায় বরাবর দ্বিতীয় স্থান দখল করে বসে রইল। আরো কয়েকজন আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমার। তেমন কোন মানসিক দূরত্ব অনুভব করিনি।
কয়েকমাস আগে বাম রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এক বড়ভাইয়ের বাসায় দাওয়াতে গিয়ে কথা হচ্ছিল। ভাবী আর ভাই দুজনেই তাদের সন্তানদেরকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িয়েছেন।আমি যখন মনে করিয়ে দিলাম, সারাজীবন সাম্যবাদী রাজনীতি করে বাচ্চাগুলোকে তো পশ্চিমের জন্য তৈরি করছেন। তখন তাঁদের কণ্ঠে বিষাদ। নানা বাদানুবাদের পরে আমাকে ইন্টারেস্টিং যে ব্যাপারটা উনি মনে করিয়ে দিলেন বা যেই ব্যাপারটা আলোচিত হল, সেটা হচ্ছে ইংরেজি মিডিয়ামের শিক্ষার্থীরা কোনভাবেই দেশে থাকছে না কেন। ও-লেভেল , এ-লেভেল পাশ করে সাধারণ উচ্চশিক্ষায় এদের জায়গা কোথায় ?
দেশ চালাচ্ছে যারা, সেই প্রশাসন , কাস্টমস সবাইতো সেই কৃষকের ছেলেই। গত কয়েক দশক ধরে ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলেপেলে গুলো কেন সরকার ও প্রশাসন ও পুলিশ সেনাবাহিনীতে নেই। থাকলেও সেটার পারসেন্টেজ এতো কম কেন?
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার এক আলোচনায় বলেছিলেন উনিশ-শতকী প্রজন্মের কথা। প্রথম প্রজন্মের মানুষ শুধু সম্পদ কিনে চলে। পায়ের তলার মাটির জন্য জন্তুসুলভ বর্বর রাক্ষসের মতো গোটা পৃথিবীকে দখল করতে চায়। এদেরকে বলা হয় ‘কেনারাম’। দ্বিতীয় প্রজন্ম বিনাশ্রমে অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে বসে। নতুন করে রাষ্ট্রীয় লুণ্ঠন আর দস্যুবৃত্তিতে না জড়িয়ে শুরু হয় তাদের বাবুগিরি। এই প্রজন্মকে বলে ‘বাবুরাম’। এদের চালচলন কিছুটা রাজকীয় হয়। এরা সবাই বাবার জন্তু প্রকৃতি পেলেও দশভাগ পায় দেবতা-প্রকৃতি। শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি ও সামাজিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে কাজ করে বলে এদের আত্মোৎসর্গ হয় প্রথম প্রজন্মের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।
তৃতীয় প্রজন্মের নাম ‘বেচারাম’। এরা বৈষয়িক ব্যাপারে আগ্রহহীন কিন্তু উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর চেতনার মানুষ।পূর্ব পুরুষের রেখে যাওয়া ধনসম্পদ বিক্রি করে , শ্রেয়তর কাজে চায় আত্মার চরিতার্থতা। যদিও সবাই এটা করেনা, মানুষের একদিকের দশভাগ যেমন দুরারোগ্য দেবতা তেমনি অন্যদিকের দশভাগ দুরারোগ্য জন্তু। স্যারের ধারণা ছিল, আমাদের স্বাধীনতার পরের কয়েক দশক যাবে কেনারামদের। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে বাবুরামদের প্রজন্ম চলে আসবে। যাঁদের ততটা আর্থিক কষ্ট করতে হচ্ছে না, তাদের হাতে থাকছে পৃথিবীকে ভালোবাসার সময় , চারপাশের দুঃখে ব্যথিত হওয়ার অবসর। স্যার তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে রসিকতা করে বলতেন বাবুরামের বাবারা ঘুষ খেয়ে, খুন করে রাষ্ট্রীয় দস্যুবৃত্তি করে করে আরো একবার তাদের উত্তর প্রজন্মকে সেই ঘৃণ্য কাজগুলো করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে গেছেন। স্যারের আশা নদীর প্রথম বর্ষার উন্মত্ত হিংস্রতার পরে জলধারা সুস্থির হয়। সবসময়ই দ্বিতীয় প্রজন্ম প্রথম প্রজন্মের তুলনায় তুলনামূলক ভাবে আর্থিক কষ্ট সম্পর্কহীন নির্লোভ উদার মূল্যবোধ নিয়ে দেখা দেয়। এছাড়া দ্বিতীয় প্রজন্মের অনেকে বিদেশে থাকে সেখান থেকে পাওয়া উচ্চতর মূল্যবোধগুলোকে জাতিতে যুক্ত করে । হা হতোস্মি !
সত্যি কথা বলতে কী, সচ্ছল মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া সন্তানেরা ‘বাবুরাম’ শ্রেণির। উচ্চবিত্ত বাবাদের সম্পদের উপরে বসে সমাজের সবচেয়ে ভালো শিক্ষাটা পায় । সম্পদ তৈরি করার সেই পাশবিক পরিশ্রম করতে হয় না তাদের। অমানুষিক দারিদ্র্য থাকে না বলে একটা সুস্থির নৈতিকতা তৈরি হয় তাদের মাঝে। অথচ এই সুবিধাভোগী যত্নআত্তি করে তৈরি করা প্রজন্মটাকে কোনভাবেই সমাজের মেইন স্ট্রিমে রাখা যায় না।
কেন সচ্ছল ‘কেনারাম’ পিতাদের ‘বাবুরাম’ সন্তান শ্রেণীকে কোনভাবেই দেশের মেইনস্ট্রিমে রাখা যাচ্ছে না। রাখার কোন ব্যবস্থা আমলাতন্ত্র ও রাষ্ট্র আদৌ চায় কীনা সে ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত সন্দেহ আছে।
দুই-যুগ আগে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ভর্তি হওয়ার জন্য এদের সিলেবাস যথোপযুক্ত ছিল না। এদের ‘ও’লেভেল, ‘এ’ লেভেল শেষ হওয়ার আগে ইউরোপ আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাগজপত্র নিয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যেত। অধুনা প্রাইভেট হাসপাতালের মতো যথেচ্ছ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় একশ্রেণীর উচ্চবিত্তদের সন্তানেরা দেশে থেকে যাচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে। পড়া শেষে এরা বাবার তৈরি ব্যবসায় লেগে পড়ছেন অথবা অগতির গতি বড়ো বড়ো মাল্টিপারপাস কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোতে কেরানিগিরি করতে ঢুকে পড়ছেন।
আমাদের সরকারি ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোডাক্টগুলো করুণ অবস্থা দেখলে মনে হয়, চীন যেমন চায়না রেভুলশনের সময় উচ্চশিক্ষা বন্ধ করে কারিগরি শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিল, আমাদেরও তাই করা উচিৎ । নানা তর্ক-বিতর্ক থাকলেও আমার মনে হয়, শত শত বিশ্ববিদ্যালয় আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২টা প্রশ্ন পড়ে ৮টা কমন পড়ে নানাধরনের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করে আমাদের আখেরে লাভ হয়নি কিছুই ; প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ প্রস্তুতি-হীন বেকার তৈরি করা ছাড়া। আর শহর হোক আর গ্রাম হোক, কোনভাবে কেউ গ্রাজুয়েশন করে ফেললে সে আর কোনরকমের কায়িক পরিশ্রমের, কারিগরি, কৃষি, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কোন কিছুতেই আগ্রহ প্রকাশ করে না। সামাজিক ও পারিবারিক চাপে সেই সদ্য গ্রাজুয়েটের একমাত্র মোক্ষ থাকে একটা চাকরির ! একটা ‘বসার চেয়ার’ পেলেই সে বর্তে যায়। ব্রিটিশদের প্রচলিত এই কেরানী তৈরি শিক্ষাব্যবস্থার চক্করে পড়ে না হল আমাদের সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয়; না হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি।
ফিরে আসি ‘বাবুরাম’প্রজন্মের কাছে । উচ্চমাধ্যমিক/এ-লেভেল পাশ করে এদের গুটিকয়েক সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি হলেও এদের লক্ষ্য কিন্তু বিসিএস বা সরকারী চাকরি থাকে না । তাই যুগের পর যুগ সেই মফঃস্বল আর গ্রামের কৃষকের ছেলেরাই এসে শোষক রাষ্ট্রের লোভনীয় চেয়ারগুলোতে বসা শুরু করেন। প্রাথমিক স্বপ্নপূরনের আর স্বপ্নভঙ্গের পরে শুরু করেন নতুন করে পশুসুলভ রাক্ষুসে খাওয়া। রাষ্ট্রীয় প্রতারণার বঞ্চনার মূল ভুক্তভোগী মূলত: নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনরা। রাজনীতির কূটচাল আর সরকারি নেতাদের ও প্রশাসনের দুর্নীতির মোচ্ছব কাছাকাছি থেকে সবচেয়ে বেশি চাক্ষুষ করে উপজেলা ও জেলা শহরের সেই পরিবারের ছেলেগুলোই। অথচ সেই প্রতারিত সন্তানেরা বড় স্বপ্ন নিয়ে দেশের শাসনযন্ত্রে বসছে এবং দুর্নীতি করছে পুর্নোদ্যমে। দুর্নীতি থামছে না কোনভাবেই। প্রতিনিয়ত কেন সেটা হচ্ছে ,তা গবেষণার দাবী রাখে।
সমবয়সী বন্ধুদের মাঝে প্রশাসনে আছে এমন কয়েকজনের সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিকভাবে কথা হয়েছে। কেউ কেউ পরিবারের উচ্চাভিলাষিতার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তাহীনতা সরকারের দলীয় নেতাদের অবৈধ ক্ষমতাচর্চা ও সিস্টেমের দোষ দিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হতে চেয়েছেন। কেউ কেউ আবার মজা করে সরল স্বীকারোক্তি করেছেন যে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের দায়িত্ব যতোখানি না জনগণকে সাহায্য করা তাঁর চেয়েও বেশি হচ্ছে কোন কিছু সহজে করতে না দেওয়া। এক বন্ধুতো বলেই বসল, ‘আমরা না থাকলেই বরং দেশ ভালোভাবে চলবে। আমরা তো কাজের কাজ তেমন কিছু করি না, আমাদের ধান্ধাই থাকে– কে রে, কী হলো রে, কে যায় রে, কেন রে তুই ওইভাবে করলি, আমাকে জানালি না কেন রে! — এইসব করে। মোদ্দাকথা প্রতি পদক্ষেপে কোনকাজ সহজ না করে সেটাতে বাগড়া দেওয়াই মুখ্য। ওদের কথা শুনে কষ্টের হাসি হেসেছি। আসলেই তো যে কাজ পাঁচ মিনিটে হয়ে যায়, সেটা আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় কয়েক বছরে কীভাবে লালফিতায় বেঁধে রাখা হয় সে আমাদের সবার কমবেশি দেখা হয়েছে।
শৈশব থেকেই কয়েকরকম শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের জনগোষ্ঠীর মানসিক বিভেদ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পরিবারের একজন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির মানসিকতা দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে বাকী সদস্যরা । দেশের যে কোন ইস্যুতে প্রত্যেকে যার যার মতো কেউ মধ্যযুগীয় চিন্তা আর কেউ প্রগতিশীল চিন্তার প্রকাশ করছে। মানসিকতার সংঘর্ষ যেখানে অনিবার্য ; মানবিকতার অপমৃত্যু তো সেখানে খুব স্বাভাবিক,প্রাত্যহিক।
একই আলোবাতাসে বেড়ে উঠছে ত্রিমুখী শিক্ষাব্যবস্থার মানুষ। বাংলাদেশ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার চেতনা, ইসলামী শাসনাকাংখা, মদিনা সনদ, পুঁজিবাদ, মুক্তবাজার অর্থনীতি, গণতন্ত্র, সাম্যবাদ , কুসংস্কার , অনিশ্চয়তা, প্রগতিশীল শিক্ষা, অনাধুনিক শিক্ষা, পশ্চিমা শিক্ষা, ধর্মীয় নৈতিকতা, আপোষকামিতা, হিংস্রতা, স্বার্থপরতা—সবকিছুর বাইরে এই তিন শ্রেণির মানুষের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে এক অনতিক্রম্য দূরত্ব তৈরি হচ্ছে।
এতো বিভেদ আর বিদ্বেষ নিয়ে আমাদের দেশের টেকসই উন্নয়ন কবে হবে, কীভাবে হবে ?
প্রকাশকালঃ ৬ই মে,২০২০
by Jahid | Nov 30, 2020 | সমাজ ও রাজনীতি
জমিদার, রাজা মহারাজাদের সব কর্মকাণ্ডকে অবলীলায় মেনে নেওয়ার পক্ষে আমি নই। কিন্তু তাঁদের সম্পদের বাহুল্যের মাঝেও সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য যাঁরা দান করেছেন, স্কুল কলেজ আর হাসপাতাল করেছেন তাঁদের ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধা আছে। একই সঙ্গে বাঙালি মুসলমান সমাজের ধনীদের নিয়ে আছে প্রশ্ন !
নওয়াবি আমলের পরে ইংরেজ শাসনামলে বাঙালি মুসলমান বড় একটা ভুল করে বসেছিল আধুনিক শিক্ষা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে। সেই অধঃপতনের ধারা তারা আজো বয়ে চলছে। সেই ভুলের খেসারতে হিন্দু সমাজের অনেকে জমিদারির পত্তন শুরু করেন। এঁদের মাঝে আমাদের পূর্ববঙ্গে বহু জমিদারকে পেয়েছি যারা সমাজসেবক ছিলেন। এমন না যে সেই সময়ে সমস্ত মুসলমান একেবারে হত দরিদ্র ছিলেন। বহু সম্পদশালী বাঙালী মুসলমান ছিলেন, কিন্তু মনে করার মতো ফিলান্থ্রপিস্ট ( Philanthropist) ছিলেন হাজী মুহাম্মদ মহসীন। নওয়াব আহসানউল্লাহ্, স্যার সলিমুল্লাহ তো বাংলাভাষী ছিলেন না।
তখন থেকেই গড় সম্পদশালী মুসলমানদের সমাজসেবায় দুর্বলতা আমাদের চোখে পড়ে।
ব্রিটিশ আমলের কথা বাদ দিলাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে নব্যধনী বাঙালী মুসলমানেরা শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য সংখ্যা অনুপাতে মোটেও এগিয়ে আসে নি। সারাদেশ জুড়ে আমরা দেখেছি, বড়লোকেরা বাড়ির পাশে একটা করে কওমি মাদ্রাসার সঙ্গে মোজাইক করা মসজিদ স্থাপন করে তাদের ও তাদের পরিবারের আখিরাতের সুরাহা করেছেন। চৌধুরী পরিবারের মসজিদে খোন্দকার সাহেবরা নামাজ পড়লে সওয়াব কম হবে, সেই জাত্যভিমানে ২০০ গজ দূরে একই গ্রামে আরেকটি মসজিদ তৈরি হয়েছে। তৈরি হয়েছে আরেকটা মাদ্রাসা। এরা বছরের পর বছর না করেছেন কোন সাধারণ শিক্ষালয়, না করেছেন কোন হাসপাতাল।
আমি আবারো বলছি বাঙালি মুসলমান ধনীরা যা করেছেন তা তাঁদের সামগ্রিক সামর্থ্যের তুলনায় এতো অনুল্লেখ্য যে তা হাতে গুণে বলে দেওয়া যায়। মাঠ পর্যায়ের ধনীরা আখিরাতের চিন্তায় নিজের ও বাপের নামে মসজিদ আর মায়ের নামে মাদ্রাসা করা ছাড়া তেমন কিছু করেন নাই। এতো এতো মাদ্রাসা দিয়ে দেশের যে তেমন কোন লাভ হয় নি সেটা বোঝার জন্য আইনস্টাইন হওয়ার দরকার নেই।
পূর্ববঙ্গে রণদাপ্রসাদ সাহা, ভারতেশ্বরী হোমস, কুমুদিনী কলেজ, কুমুদিনী হাসপাতাল , কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কী না করেছেন। যদিও তিনি জমিদার ছিলেন না ; ছিলেন সাধারণ থেকে উঠে আসা একজন ব্যবসায়ী। যেদিকে তাকাবেন দেখবেন টাঙ্গাইলের রানী বিন্দুবাসিনী চৌধুরী , বরিশালে ব্রজমোহনের করা বিএম কলেজ ; খুলনায় বাবু ব্রজলাল চ্যাটার্জির বিএল কলেজ। আমার নিজের জেলা কুষ্টিয়াতে কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার একাধারে গ্রামবার্তা প্রকাশিকা থেকে শুরু করে মথুরানাথ প্রেস আর মথুরানাথ স্কুল করে পুরো এলাকার শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এছাড়াও মোহিনী মোহন মিল ও তাদের করা শিক্ষালয়গুলো তো আছেই।
সেই অর্থে নব্যধনী বাঙালি মুসলমানের আর্থিক সামর্থ্য গত কয়েক দশক তুলনারহিত বৃদ্ধি পেয়েছে। কোথায় তাদের সমস্যা ? কেন দেশের যে কোন দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে এঁদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে ! সমাজ ও মানুষের সার্বিক কল্যাণে এঁদের অবদান কোথায় ?
আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম নামের মহতী প্রতিষ্ঠানের কাজ অনেক আগে থেকেই আমার অসম্ভব ভালো লাগে। নাম পরিচয়হীণ মৃতদেহ যে একটা সন্মানজনক সৎকারের দাবি রাখে এবং সেটা আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে, ব্যাপারটা অসাধারণ । আমার ধারণা ছিল এটি ব্রিটিশ পরবর্তী কোন বাঙালি মুসলমানের কেউ করেছেন। পরে দেখলাম এটি তৈরি হয়েছে ১৯০৫ সালে কোলকাতায়।
আচ্ছা, এই লেখার উপরের অংশ লেখা একদিনে। লিখে রেখে দিয়েছিলাম।
আজকে পরের অংশ লিখতে গিয়ে মনে হল, আমার মনে হয় কোথাও একটা ভুল হচ্ছে !
ধনী মুসলমান সমাজ তো এগিয়ে এসেছে, আমাদের চারপাশে অনেক হিন্দু স্কুল ও কলেজের পাশাপাশি নব্যধনী মুসলমান সমাজ গত পাঁচ দশকে তাঁদের স্ত্রী-বাবা-মার নামে অনেক স্কুল-কলেজও করেছেন। তারপরেও সমাজের এই দুরবস্থা কেন ? তখন হিসেব করে দেখলাম ; নব্যধনী মুসলমান সমাজ যদি একটা সাধারণ শিক্ষার স্কুল তৈরি করে থাকে, মাদ্রাসা-মসজিদ করেছে দশটা। সুতরাং সমাজে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পিছিয়েছে বেশি।
মাদ্রাসার মতো একটা অনাধুনিক, অনুৎপাদনশীল, পরিত্যক্ত শিক্ষা সমাজকে এগিয়ে নেবে কী করে ! সেই কুদরতে খুদার সময় থেকে রাষ্ট্র যতোবার মাদ্রাসা শিক্ষায় আধুনিকায়ন করতে গেছেন ততোবারই কওমি সম্প্রদায় হা রে রে করে তেড়ে এসেছে। দেশের সবচেয়ে বড় একটা জনগোষ্ঠী আমৃত্যু অনুৎপাদনশীল থেকে জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধি করে গেলে দেশ এগুবে কী দিয়ে !
প্রকাশকালঃ
by Jahid | Nov 29, 2020 | সমাজ ও রাজনীতি, সাম্প্রতিক
আমি ষড়যন্ত্র তত্ত্বে সহজে বিশ্বাস করতে চাই না । মুসলমানদের সকল দুর্দশার জন্য দায়ী ইহুদি অথবা বাংলাদেশের সকল অস্থিরতা আর অরাজকতার জন্য দায়ী ভারত ; মৌলবাদীদের সকল উত্থানের পিছনে শুধুই পাকিস্তান—এই সব আমার কাছে বড্ডো ক্লিশে মনে হয় !
দিন কয়েক আগে এক সাংবাদিক বন্ধু তাঁর এক দেশি-বিদেশী নগর পরিকল্পনাবিদদের সঙ্গে ঘরোয়া আড্ডার কথা শেয়ার করছিল। তাঁদের আলোচনায় নাকি একটি প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তৃতীয় বিশ্বের সবচেয়ে শিক্ষিত সংবেদনশীল জনগোষ্ঠী বাস করে বড় শহরগুলোতে। হোক সে দিল্লী, ঢাকা অথবা অন্যকোন মহানগরী ! রাষ্ট্রযন্ত্রের অনুষঙ্গ যারা , তারা নাকি চায় , এই শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সকালের ট্রাফিকে ক্লান্ত হয়ে থাকুক সারাদিন ; আর সন্ধ্যার ট্রাফিকে আরো বেশি ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে নির্জীব হয়ে পড়ে থাক পরের দিনের ট্রাফিকের অপেক্ষায়।
তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলোতে ট্রাফিক দূরীকরণ হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বনিম্ন প্রায়োরিটি।
রাষ্ট্রযন্ত্র চায় ট্রাফিক দীর্ঘমেয়াদে থাকুক ! অথবা তারা চায় ট্রাফিক এতো ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হোক, যে তার সময়োপযোগী সুফল জনগণের কাছে থাকুক চির অধরা। শুনেছি ব্রিটিশ রাজের সময়ে জেলখানার কয়েদীদের খাবারে চুলকানির উপাদান মিশিয়ে দেওয়া হত। জেলের পুঁতিগন্ধময় পরিবেশ আর অখাদ্য খেয়ে রাজবন্দী থেকে শুরু করে সকল কয়েদী অসুস্থ হয়ে থাকত, নির্জীব হয়ে পড়ে থাকত। নিজের শরীর যেখানে চলে না, সেখানে একজন কয়েদী আর স্বাধীন ভারতের জন্য কতোখানি চিন্তা করতে পারবে ! বিশ্বাস করতে চাই না, তবু ঐ যে বললাম ষড়যন্ত্র তত্ত্ব– বন্ধুর কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদেরও বোধহয় ব্রিটিশ রাজের কয়েদীদের মতোই অবস্থা !
আমাদের নগর পরিকল্পনাবিদদের নানা ধরণের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ফাইলবন্দী হয়ে উইপোকা খায় ! রাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে আছে স্বল্পমেয়াদের ফ্লাই ওভার নিয়ে। সমন্বয়হীনতা এমন পর্যায়ে যে, একটা রাস্তা দুই বছরের মধ্যে তিনবার পিচঢালাই আর ফুটপাত টাইলস দিয়ে সারা হয় তো আর চারবার খোঁড়াখুঁড়ি করে ফেলে রাখা হয় জনগণের অসহায়ত্বকে একেবারে মাটিতে পিষে থেঁতলে ফেলা দেখার বীভৎস আনন্দে। স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেখানে দীর্ঘমেয়াদের টেকসই ঢালাই রাস্তার কথা বলেছেন কয়েকবার ; অথচ সেই প্রকল্প ফেলে রেখে সবাই মিলে উঠেপড়ে লেগেছে এই বর্ষাপ্রবণ কাদামাটির দেশে পিচের রাস্তার বাইরে কোনকিছু না করতে !
মিরপুরের কালসি থেকে যে নতুন ফ্লাইওভারটি সরাসরি ক্যান্টনমেন্ট ফ্লাইওভারে যোগ দিয়ে হোটেল র্যাডিসনের সামনে গিয়ে অথবা কুড়িল ফ্লাইওভারে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল — সেটা এখন হুট করে মাঝ রাস্তায় নামিয়ে সড়কের জ্যাম চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ! এবং এটা নাকি করা হয়েছে পরিবহন মালিক-শ্রমিকদের চাপে।
এভাবে সরকার প্রধানের সদিচ্ছাকে নিজেদের হীন স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে এতোটুকু দ্বিধা করছে না রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল নিয়ামকরা। যে দেশে নগর পরিকল্পনাবিদদেরই সামান্যতম মূল্যায়ন নেই রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে ; সেই দেশে সাধারণ জনগণের আহাজারি কী করে পৌঁছাবে রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে !
প্রকাশকালঃ ২রা মার্চ,২০২০
by Jahid | Nov 29, 2020 | সমাজ ও রাজনীতি
প্রথমটি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অগ্রজ ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক আমীরুল ইসলাম ভাইয়ের কাছে শোনা বছর তিরিশেক আগে।এর অনেকগুলো ভার্সন আছে। পেয়ারার জায়গায় ডিম, মাছ — বন্ধুর জায়গায় দুই ভাই , ইত্যাদি ইত্যাদি। উপাদানের পরিবর্তনে সমীকরণের মৌলিক কোন তফাৎ হয় না !
দুই ঢাকাইয়া হরিহর আত্মার দোস্ত, পল্টু আর বল্টু। দু’জনে সর্বদা সর্বত্র একসঙ্গে ওঠা-বসা-খাওয়াদাওয়া করে।
একদিন পল্টু একটা পেয়ারা নিয়ে এসে
বলল: দোস্ত এই ল সপরিআমটা ভাগ কর, দুইজন মিল্যা খাই।
বল্টু পেয়ারাটা হাতে নিয়ে ভাগ করে নিজে অর্ধেক রেখে, অর্ধেকটা পল্টুকে বাড়িয়ে
দিলো: এই লে দোস্ত , খা ।
পল্টু পেয়ারার টুকরোখানি হাতে নিয়ে অভিমানের সুরে বলল: দোস্ত, তোর কুনু ইনসাফ নাইক্যা …… ।
বল্টু বলল: ক্যালা দোস্ত, এই কথা কইলি ক্যান ?
পল্টু বলল: এই যে তুই আমটা ভাগ করলি, কমটা আমারে দিলি আর বেশিটা তুই নিলি ।
বল্টু বলল: আচ্ছা দোস্ত, তুই অইলে কি করতি ?
পল্টু বলল: ক্যান আমি কমটা লিতাম, তোরেই বেশিটি দিতাম।
বল্টু বলল: তাইতো করলাম, তয় এতো কথা কচ ক্যান্ ? খা বয়া বয়া !
ধোপার গাধার গপ্পো কবে, কখন , কার কাছে শুনেছিলাম মনে নেই। গল্পে কতো কিছুই তো হয়। “শিলা জলে ভাসি যায় বানরে সঙ্গীত গায় দেখিলেও না হয় প্রত্যয়॥” এই গল্পে গাধাও কথা বলে ; বিচার বিবেচনা আছে আর কী !
বহু বহুযুগ আগের কথা। এই বাংলার কোন এক গ্রামে ধোপা আছে, আছে তার গাধা।
ধোপা সারা গ্রামের কাপড় গাধাকে দিয়ে নদীর ঘাটে নেয়, কাচে শুকায়। নিজে ভাল খায়, কিন্তু গাধাটিকে কম খেতে দেয়। এদিক সেদিক করলে পিঠের উপর দুয়েক ঘা পড়ে।
তো, সেই গ্রামে একবার ডাকাত পড়ল। আর সবার মতো যৎসামান্য যা কিছু আছে তা নিয়ে নিয়ে ধোপা গাধার পিঠে করে পালাচ্ছে।
হাফাতে হাফাতে ক্লান্ত , পরিশ্রান্ত গাধা এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করল: মালিক আমরা দৌড়চ্ছি কেন ?
ধোপা: দৌড়াচ্ছি, কারণ ডাকাত পড়েছে, এরা আমাদের সবকিছু কেড়ে নেবে।
গাধা: আমার কি হবে?
ধোপা: তোকেও ওরা ধরে নিয়ে যাবে।
গাধা: তারপর?
ধোপা: তারপর তোকে দিয়ে সব ভারী ভারী কাজ করাবে। কাপড় কাচার জন্য ব্যবহার করবে। কম কম খেতে দেবে। এদিক সেদিক করলে পিঠের উপর দেবে কয়েক ঘা।
হাফাতে হাফাতে গাধা এক পর্যায়ে ব্রেক কষে বসল।
ধোপা: কি হলো রে , থামলি কেন ?
গাধা: আপনি ডাকাতের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালাচ্ছেন পালান, আমি পালাব না।
আপনি এখন আমাকে দিয়ে যা যা করাচ্ছেন, ডাকাতের হাতে পড়লে তো সেই একই দুরবস্থা, আমার কাছে দুইই সমান !
প্রকাশকালঃ ২রা ফেব্রুয়ারি,২০২০
by Jahid | Nov 29, 2020 | লাইফ স্টাইল, সমাজ ও রাজনীতি
২১। বিবাহ বা ব্রহ্মচর্য, যেটাই মানুষ বেছে নিক না কেন আখেরে তাকে পস্তাতে হবে। সক্রেটিস।।
২২। যে ব্যক্তি স্ত্রীকে বশে রাখতে পারেন, তিনি একটি জাতিকে চালনা করার উপযুক্ত। বালজাক।।
২৩। আমার দুটো বিয়ের একটিও সুখের হয় নি। প্রথম স্ত্রী আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। দ্বিতীয়জন যায় নি ! প্যাট্রিক মুর, ইংরেজ জ্যোতির্বিদ।।
২৪। পুরুষ নারীকে বিয়ে করে এই আশায় যে তারা কখনো বদলাবে না। নারী পুরুষকে বিয়ে করে এই আশায় যে তারা বদলাবে। স্বভাবতই তারা দুজনেই হতাশ হয়। আলবার্ট আইনস্টাইন।।
২৫। বিয়ে হলো মূত্রত্যাগের মতোই প্রাকৃতিক, অযৌক্তিক এবং ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। লিসা হফম্যান, লেখক।।
২৬। মেয়েরা যতো স্বাধীন হতে চেষ্টা করে তত অসুখী হয়। ব্রিজিত বার্দো, ফরাসি মডেল , অভিনেত্রী।।
২৭। নারীর সতীত্ব পুরুষের বৃহত্তম আবিষ্কার। কর্নেলিয়া অটিস স্কিনার, আমেরিকান অভিনেতা।।
২৮। প্রেম হলো ভুতের মতো , ভাবলে আছে না ভাবলে নাই। মিশেল ফুকো। ফরাসী দার্শনিক।।
২৯। একজন বুদ্ধিমতী চুমু দেবে কিন্তু ভালোবাসবে না, শুনবে কিন্তু বিশ্বাস করবে না এবং তাকে ছেড়ে যাওয়ার আগেই সে ছেড়ে চলে যাবে। মেরিলিন মনরো।।
৩০। ভালো মেয়েরা স্বর্গে যায়, খারাপ মেয়েরা সব জায়গায় যেতে পারে। মে ওয়েস্ট, আমেরিকান অভিনেত্রী।।
৩১। যাই ঘটুক না কেন বিয়ে করে ফেল। স্ত্রী ভালো হলে সুখী হবে, না হলে দার্শনিক। সক্রেটিস।।
৩২। আমার সারা শরীর ব্যাথা করছিল, সেই সঙ্গে ছিল বমি বমি ভাব। বুঝতে পারলাম, হয় আমি প্রেমে পড়েছি, নয়তো আমার গুটিবসন্ত হয়েছে। উডি অ্যালেন। আমেরিকান অভিনেতা।।
৩৩। আমার টাকাপয়সার নব্বইভাগ মদ এবং মেয়েমানুষের পেছনে ব্যয় করেছি।বাকী টাকাটা একদম জলে গেছে। জর্জ বেস্ট, ইংলিশ ফুটবলার।।
৩৪। একটি মেয়ের দোষ জানতে হলে বান্ধবীদের কাছে গিয়ে তার প্রশংসা করো। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।।
৩৫। বিয়ের আগে আপনার চোখ খোলা রাখুন। তারপর আধবোজা করে বন্ধ করুন। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।।
৩৬। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন হলো, আমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গে বিয়েতে রাজি করাতে পারা। উইনস্টন চার্চিল।।
৩৭। টাকা দিয়ে ভালোবাসা কেনা যায় না, কিন্তু দরদাম করার মতো একটা শক্ত অবস্থান অর্জন করা যায়। ক্রিস্টোফার মার্লো, ব্রিটিশ নাট্যকার।।
৩৮। প্রেমিক হওয়া সহজ, স্বামী হওয়া শক্ত। মাঝে মাঝে দু’চারটা মজার কথা বলে মন জয় করা যায়, কিন্তু প্রতিদিন রসোক্তি করা সম্ভব নয়। বালজাক।।
৩৯। রমণী খাবার সাজানো টেবিলের মতো, যার দিকে পুরুষ খাবার আগে ও পরে ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকায়। বালজাক।।
৪০। মেয়েদের স্তনকে একই সঙ্গে নান্দনিক ও ব্যবহারযোগ্য বস্তু হিসেবে দেখা উচিত। ম্যুরা পাতিসিয়ে, ফরাসী সেনাধ্যক্ষ।।
৪১। নারী পুরুষের জীবনে এক অসহ্য, অবাধ্য ও অপরিত্যাজ্য সহচারিণী। লেভ তলস্তয়।।
৪২। বলা হয় ঘোড়ার শক্তি তার মুখে ও নিতম্বে। এ সত্য নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জোনাথান সুইফট।।
৪৩। জঞ্জাল ফেলবার সবচেয়ে ভালো ঝুড়ি হচ্ছে বিবাহ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।।
৪৪। মহিলাদের নিয়ে মুশকিল এই যে, এঁরা আলাপ-আলোচনায় অপটু, অথচ কথা বলার শক্তি হারান না । জর্জ বার্নার্ড শ।।
৪৫। আজকের সভ্যতায় পুরুষকে মাপা হয় ব্যাংকের ফিগার দিয়ে আর মেয়েদের মাপা হয় দেহের ফিগার দিয়ে। শঙ্কর, কথাসাহিত্যিক।।
প্রকাশকালঃ১২ই ডিসেম্বর,২০১৯
by Jahid | Nov 29, 2020 | দর্শন, সমাজ ও রাজনীতি
১। মেয়েদেরই বিস্তর অলংকার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।।
২। চমৎকার একটি প্রশ্ন, যার কোন উত্তর নেই।প্রশ্নটি হলো, একজন নারী কি চায় ? সিগমুন্ড ফ্রয়েড।।
৩। একবার পুরুষের সমান হলেই নারী তারচেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় । সক্রেটিস।।
৪। কথা বলার যন্ত্র আসলে আমি নই, স্বয়ং ঈশ্বরই নারী জাতির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। আমি শুধু এমন একটা যন্ত্র তৈরি করেছি যেটাকে ইচ্ছেমত থামিয়ে দেওয়া যায়। টমাস আলভা এডিসন।।
৫। একটি স্থাপত্যকর্ম সম্পর্কেই আমার কোন আপত্তি নেই, তার কোনো সংস্কারও আমি অনুমোদন করি না। স্থাপত্যকর্মটি হচ্ছে নারীদেহ। হুমায়ুন আজাদ।।
৬। সেইসব নারী পুরুষের সমকক্ষ হতে চায়, যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। মেরিলিন মনরো।
৭। মধ্যবিত্ত পতিতাদের নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তারা পতিতার সুখ ও সতীর পুণ্য দুটোই দাবি করে। হুমায়ুন আজাদ।।
৮। মেয়েদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু হলো ডায়মন্ড। মেরিলিন মনরো।।
৯। আমার মনে হয় যেসব পুরুষের কান ফুটো করা, তারা বিয়ের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত। কারণ তারা ব্যাথা সহ্য করেছে এবং অলঙ্কারও কিনেছে। রিটা রুডনার, আমেরিকান অভিনেত্রী।।
১০। অন্ধকারে সব নারীই সুন্দরী। পুতার্ক , রোমান ধর্মযাজক।।
১১। মেয়েছেলেকে লেখাপড়া শেখালে কী আর রক্ষা আছে ? এক ‘আন’ শিখেই তাদের যন্ত্রণায় টেকা দায়। চাল আন, ডাল আন, তেল আন সারাদিন এই করেই অস্থির। রামনারায়ণ তর্করত্ন, নাট্যকার।।
১২। আগে কাননবালারা আসতো পতিতালয় থেকে, এখন আসে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। হুমায়ুন আজাদ।।
১৩। এ সংসারে যৌবনের সমতুল্য আর কি আছে ? কিন্তু এমন জিনিসটিকে বাচ্চাকাচ্চার জন্যে নষ্ট করা সত্যিই অপরাধ। জর্জ বার্নার্ড শ।।
১৪। গত দু’শো বছর গবাদিপশুর যতটা উন্নতি হয়েছে নারীর ততটা উন্নতি ঘটেনি। হুমায়ুন আজাদ।।
১৫। আমি নারী বিদ্বেষী তার প্রথম কারণ তারা নারী, দ্বিতীয় কারণ তারপরেও তারা নারী, তৃতীয় কারণ শেষ পর্যন্ত তারা নারী। বার্টান্ড রাসেল।।
১৬। রমণীর অনর্থক হাসি দেখিয়া অনেক পুরুষ অনর্থক কাঁদে , অনেক পুরুষ ছন্দ মিলাইতে বসে, অনেক পুরুষ গলায় দড়ি দিয়ে মরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।।
১৭। জন্মাবার সময় থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত মেয়েদের দরকার ভালো বাবা-মা, উনিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত সুন্দর মুখ, ছত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন পর্যন্ত নারীর ভূষণ ব্যক্তিত্ব এবং পঞ্চান্নের পর বৃদ্ধার চাই নগদ টাকা। ক্যাথলিন নরিস, আমেরিকান কবি।।
১৮। সবচেয়ে ভালো স্বামী হলো পুরাতাত্ত্বিক । স্ত্রী যতই পুরনো হবে ততই তার আগ্রহ বাড়বে। আগাথা ক্রিস্টি, লেখক।।
১৯। স্বামীরা রুটির ব্যবস্থা করবে এটা আশা করা দোষের নয়। কিন্তু অনেক স্ত্রী চান তাদের স্বামীরা হোক রুটির কারখানা। হামফ্রি বোগার্ট, আমেরিকান অভিনেতা।।
২০। যে পুরুষ স্ত্রীর ড্রেসিং রুমে যান হয় তিনি দার্শনিক , নইলে হাঁদারাম। বালজাক।।
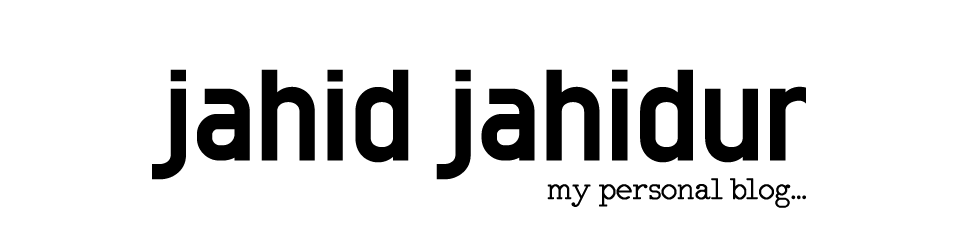
সাম্প্রতিক মন্তব্য