by Jahid | Nov 25, 2020 | শিল্প ও সংস্কৃতি, সাম্প্রতিক
সিনেমা হলে বা সিনেপ্লেক্সে গিয়ে শেষ যে কয়েকটি বাংলা ছবি দেখেছি তা আমি হাতে গুনে বলে দিতে পারি। ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ (গৌতম ঘোষ- ১৯৯৩) ; শ্রাবণ মেঘের দিন( হূমায়ুন আহমেদ -২০০০)। তারপর দীর্ঘ বিরতিতে ‘মনপুরা’ (গিয়াসউদ্দিন সেলিম -২০০৯) সামান্য বিরতিতে ‘মনের মানুষ’ (গৌতম ঘোষ -২০১০) ।
‘মনের মানুষ’-এ চঞ্চল চৌধুরী স্বল্পপরিসরে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের উজ্জ্বলালোকের পাশে থেকেও সবার মন কেড়েছিলেন। আর ‘মনপুরা’-তে তো কেন্দ্রীয় চরিত্রেই ছিলেন।
দেরী করে হলেও এর মাঝে ‘চড়ুইভাতি’, ‘ব্যাচেলর’, ‘পিঁপড়াবিদ্যা’, ‘থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার’, ‘টেলিভিশন’ মোস্তফা সারোয়ার ফারুকীর ঘরনার ছবিগুলো দেখা হয়েছে, হয় টিভি বা কম্পিউটার স্ক্রিনে। পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু ছবিও দেখা হয়েছে এই ফাঁকে ! ‘বেলাশেষে’ , ‘বাইশে শ্রাবণ’, ‘হেমলক সোসাইটি’, ‘অটোগ্রাফ’ ইত্যাদি—কিন্তু সবই ছোট স্ক্রিনে।
বহুদিন পরে বড়পর্দায় যে ছবি দেখে মুগ্ধ, বিস্মিত, গর্বিত, আলোড়িত হলাম সেটা অমিতাভ রেজা চৌধুরীর ‘ আয়নাবাজি’! বিজ্ঞাপন নির্মাতার খোলস থেকে বের হয়ে এসে, প্রথম ছবি দিয়ে অমিতাভ তাঁর জাত চিনিয়ে দিয়েছেন। আমি সিনেমাবোদ্ধা নই। আমি নিতান্তই মধ্যবিত্ত দর্শক। আলোর প্রক্ষেপন, দৃশ্যায়ন, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যকার ভারী শব্দ আমার
জন্য অনধিকার চর্চা।
‘আয়নাবাজি’ আমাদের ধুলোয় মিশে যাওয়া বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে এক অনির্বচনীয় উন্মাদীয় ভালোলাগা এনে দিল । এইছবির প্রণোদনায় উৎসাহী আরো তরুণ নির্মাতারা যদি ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন ; তবে এক বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দর্শক আবার বড়পর্দায় ছবি দেখার সেই দিনগুলোতে ফিরে যাবে, এ আমার গভীর বিশ্বাস।
কয়েকদিন আগেই এক বন্ধুকে বলেছিলাম, আমি ছিলাম ৮৭ সালে হূমায়ুন আহমেদের ‘নন্দিত নরকে’ আর ‘শঙ্খনীল কারাগার’—এর মুগ্ধ কিশোর ! যে কীনা সেই দুর্মূল্যের বাজারেও চল্লিশ টাকা দামের ৪টি বই কিনে কাছের কয়েকজনকে উপহার দিয়েছিল—শুধুমাত্র আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য।
সেই মুগ্ধ কিশোর আজ চল্লিশোর্ধ বয়সে এসে আরেকবার চলচ্চিত্রের আনন্দ ভাগাভাগি করতে চাইছে ! সিনেমা হলে যান, ‘ আয়নাবাজি’ দেখুন। দেখে এসে আমার বক্তব্যের সাথে সহমত বা দ্বিমত পোষণ করুন।
[ প্রকাশকালঃ ১লা অক্টোবর,২০১৬ ]
by Jahid | Nov 25, 2020 | শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহিত্য
ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্বে মৃত্যুকে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মা’র যখন মৃত্যু হয় আমার তখন বয়স অল্প। [{ সারদাদেবীর মৃত্যু, ১২৮১, ২৫ ফাল্গুন, [১৮৭৫, ৮ মার্চ]— র-কথা ]} অনেকদিন হইতে তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন, কখন যে তাঁহার জীবনসংকট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্যন্ত যে-ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই স্বতন্ত্র শয্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গঙ্গায় বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়— তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। যে-রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন ঘুমাইতেছিলাম, তখন কত রাত্রি জানি না, একজন পুরাতন দাসী আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, “ওরে তোদের কী সর্বনাশ হল রে!” তখনই বউঠাকুরানী [{ ↓কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী↓]} তাড়াতাড়ি তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেলেন— পাছে গভীর রাত্রে আচমকা আমাদের মনে গুরুতর আঘাত লাগে এই আশঙ্কা তাঁহার ছিল। স্তিমিত প্রদীপে, অস্পষ্ট আলোকে ক্ষণকালের জন্য জাগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুকটা দমিয়া গেল কিন্তু কী হইয়াছে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া যখন মা’র মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপরে শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ংকর সে-দেহে তাহার কোনো প্রমাণ ছিল না;— সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে-রূপ দেখিলাম তাহা সুখসুপ্তির মতোই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। কেবল যখন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর-দরজার বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মশানে চলিলাম তখনই শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক-দমকায় আসিয়া মনের ভিতরটাতে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ির এই দরজা দিয়া মা আর একদিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকরনার মধ্যে আপনার আসনটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল, শশ্মান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; গলির মোড়ে আসিয়া তেতালায় পিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম— তিনি তখনো তাঁহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন।
বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধূ [{ ↓কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী↓]} ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সর্বদা কাছে টানিয়া, আমাদের যে কোনো অভাব ঘটিয়াছে তাহা ভুলাইয়া রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করিলেন। যে-ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে-বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ;— শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে-মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতোই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। ইহার পরে বড়ো হইলে যখন বসন্তপ্রভাতে একমুঠা অনতিস্ফুট মোটা মোটা বেলফুল চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া খ্যাপার মতো বেড়াইতাম— তখন সেই কোমল চিক্কণ কুঁড়িগুলি ললাটের উপর বুলাইয়া প্রতিদিনই আমার মায়ের শুভ্র আঙুলগুলি মনে পড়িত;— আমি স্পষ্টই দেখিতে পাইতাম যে-স্পর্শ সেই সুন্দর আঙুলের আগায় ছিল সেই স্পর্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির মধ্যে নির্মল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই— তা আমরা ভুলিই আর মনে রাখি।
কিন্তু আমার চব্বিশবছর বয়সের সময় মৃত্যুর [{ ↓কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু, ১২৯১, ৮ বৈশাখ [১৮৮৪, ১৯ এপ্রিল]— রবীন্দ্র-জীবনী ১, পৃ ১৫০↓]} সঙ্গে যে-পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়েসের লঘু জীবন বড়ো বড়ো মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়— কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।
জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর-কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমনসময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল। চারিদিকে গাছপালা মাটিজল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল— এমন-কি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমিষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন! যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেমন করিয়া! [{ ↓তুমি কোথায় (ভারতী, ১২৯১ পৌষ), কড়ি ও কোমল, রচনাবলী ২ ‘পুষ্পাঞ্জলি (ভারতী, ১২৯২ বৈশাখ) এবং ‘প্রথম শোক’ (‘কথিকা’, সবুজপত্র, ১৩২৬ আষাঢ়), লিপিকা↓]}
জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি— যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কী আছে। শূন্যতাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। যাহা নাই তাহাই মিথ্যা, যাহা মিথ্যা তাহা নাই। এইজন্যই যাহা দেখিতেছি না তাহার মধ্যে দেখিবার চেষ্টা, যাহা পাইতেছি না তাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না। চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে— তেমনি, মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা ‘নাই’-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই ‘আছে’-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।
তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না— একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না— এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।
সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগতকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর।
সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য পদার্থের মতো মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে-সমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কী মনে করিবে, কিছুদিন এ-দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধুতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের [{১↓Thacker Spink & Co.↓]} বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে খাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতালায় বাহিরের বারান্দায়; সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হইতে পারিত এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।
এ-সমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা, সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোটো ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই যদি দেখি পৃথিবীর ভারাকর্ষণটা একেবারে অর্ধেক কমিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কি আর সরকারি রাস্তা বাহিয়া সাবধানে চলিতে ইচ্ছা করে। নিশ্চয়ই তাহা হইলে হ্যারিসন রোডের চারতলা-পাঁচতলা বাড়িগুলা বিনা কারণেই লাফ দিয়া ডিঙাইয়া চলি এবং ময়দানে হাওয়া খাইবার সময় যদি সামনে অক্টর্লনি মনুমেণ্ট্টা আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ওইটুকুখানি পাশ কাটাইতেও প্রবৃত্তি হয় না, ধাঁ করিয়া তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া পার হইয়া যাই। আমারও সেই দশা ঘটিয়াছিল— পায়ের নিচে হইতে জীবনের টান কমিয়া যাইতেই আমি বাঁধা রাস্তা একেবারে ছাড়িয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।
বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো-একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক-পাড়া কোনো-একটা অক্ষর কিংবা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকালবেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনলোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।
by Jahid | Nov 25, 2020 | শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহিত্য
আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর কেন ।
আদা জাহাজে করিয়া বিদেশে রপ্তানী হয় না; স্থানীয় হাটে বাজারেই খরিদ বিক্রয় হয়। সেইজন্য আদা ব্যবসায়ীর জাহাজের খবর জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। অনধিকারচর্চাস্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। “ The Cobbler must stick to his last.” Or “ Let the Cobbler(মুচি) stick to his last.”
আহার নিদ্রা ভয়, যত বাড়াও তত হয়।
আহার , নিদ্রা ও ভয় ইহাদিগকে যত বাড়াইবে ততই বাড়িবে।
উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ ।
বাতাসে খৈ উড়িয়ে নিয়ে যাইতেছে, তাহা আর সংগ্রহ করিবার উপায় নাই দেখিয়া সেইগুলি গোবিন্দায় নমঃ বলিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দিল। প্রতিকূল অবস্থায় পড়িইয়া বাধ্য হইয়া কোন সৎ কার্য করা। “ Making a virtue of necessity ”
উসকো মাটিতে বিড়াল হাগে।
নরম লোক পাইলে সকলেই তাহার উপর আধিপত্য প্রকাশ করে।
হিন্দিতে আছে, বিল্লি শাক্তি পার নেহি হাগ্তি।
এক যাত্রার পৃথক ফল।
একসঙ্গে একই কার্য আরম্ভ করিয়া একজনকে যদি পুরস্কৃত এবং অপরজন যদি তিরস্কৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদের এক যাত্রায় পৃথক ফল বলা হয়।
এঙ যায়, ব্যাঙ যায়,
খোল্সে বলে আমিও যাই।
চ্যাং মাছ ও ব্যাঙকে লাফাইতে দেখিয়া খোল্সে মাছও সেইরূপ লাফ দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য হইল না। যে যে কাজ করিতে অক্ষম, সমর্থ অপরের অনুকরণ করিতে গিয়া সে সকলের হাস্যভাজন হয়।
[ প্রকাশকালঃ ৫ই জুন, ২০১৫ ]
by Jahid | Nov 25, 2020 | শিল্প ও সংস্কৃতি, সাহিত্য
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপালের রয়েল লাইব্রেরী থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি আধুনিক লিপিতে প্রকাশিত হয় ‘হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষার বৌদ্ধগান ও দোহা’ নামে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায়।
এর রচনাকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ৬৫০ খ্রীস্টাব্দে আর ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ৯৫০ থেকে ১২৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এর পদগুলো রচিত হয়। সুকুমার সেন সহ বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব পন্ডিতই ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে সমর্থন করেন।
অনেকে বলেন , চর্যাপদের রচনাকাল সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী।তা না থাকলে দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে চর্যাপদের ভাষার নাম – সন্ধ্যা ভাষা বা আলো- আঁধারি ভাষা।
যেহেতু , চর্যাপদের ভাষা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। সেই কারণে চর্যায় ব্যবহৃত ভাষাকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন ‘সন্ধ্যাভাষা ’। তাঁর মতে, “সহজিয়া ধর্মের সকল বই-ই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। সন্ধ্যা ভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিকটা বুঝা যায় না। অর্থাৎ, এই সকল উঁচু অঙ্গের ধর্মকথার ভিতরে একটা অন্য ভাবের কথাও আছে। সেটা খুলিয়া ব্যাখ্যা করিবার নয়। যাঁহারা সাধনভজন করেন তাঁহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুঝিয়া কাজ নাই। ”
সুনীতিকুমার ১৯২৬ সালে ‘Origin and Development of the Bengali Language'(ODBL) গ্রন্থ রচনা করে চর্যাপদকে বাংলা সাহিত্যের বলে প্রমাণ করেন।
৩৩ নং পদে আবহমান বাঙালির চিরায়ত দারিদ্র্যের ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। যেমনঃ
টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।।
আধুনিক বাংলায় : “লোক শূণ্য স্থানে প্রতিবেশীহীন আমার বাড়ি / হাঁড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রেমিক এসে ভিড় করে।”
চর্যার (তেত্রিশ নং) পদটির চরয়িতা মতভেদে ‘ঢেণ্ডণপা’ অথবা ‘ভুসুকুপা’ । ঢেণ্ডণপার জন্মস্থান অবন্তিনগরের উজ্জয়িনীতে। তার জীবৎকাল ৮৪৫ সালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তার আসল নাম হল ঢেণ্ঢস। খ্রিষ্ট্রীয় নবম শতকে তিনি বর্তমান ছিলেন। এক্ষেত্রে বলা যায় তিনি দেবপাল-বিগ্রহপালের সমকালে ছিলেন। ঢেণ্ডণপা মূলত তাঁতি এবং সিদ্ধা ছিলেন। তার পদে বাঙালি জীবনের চিরায়ত দারিদ্রের চিত্র পাওয়া যায়।
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে উপরের পদটির রচয়িতা ছিলেন ‘ভুসুকপা’ । ভুসুকপা ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। তাঁর রচিত ৪৯ নং পদে পদ্মা (পঁউআ) খালের নাম আছে, ‘বাঙ্গাল দেশ’ ও ‘বাঙ্গালী’র কথা আছে। তাঁর রচিত পদসমুহের মাঝে বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। ভুসুকপা রচিত অতিপরিচিত একটি পদঃ অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।।
[ প্রকাশকালঃ ১২ই মে, ২০১৫ ]
by Jahid | Nov 25, 2020 | দর্শন, শিল্প ও সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি
অনেক আগে পড়া একটা সায়েন্স ফিকশন মাথায় ঘুরছে। A Sound of Thunder ( Ray Brudbury; 1952) উল্লেখ্য , একসময় আমি তিনবেলা খাওয়ার মতো প্রায় নিয়মিত বই পড়তাম। এখন তিনবেলার জায়গায় ছয় বেলা খাই, তবে বই পড়ি না। গুগোলকে জিজ্ঞাসা করতেই লিংক দিয়ে দিল। আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন।
http://teacherweb.com/ON/SacredHeartHighSchool/MrStriukas/A_Sound_of_Thunder.pdf
গল্পের দৃশ্যপট আমেরিকা । ১৯৫২ সালের প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের কয়েকদিন পর। মিঃ কিথ জিতেছেন। সবাই খুশী। বিরোধী দলের প্রার্থী মিঃ ডয়েসার মানবতাবিরোধী, প্রগতিবিরোধী। বলা হচ্ছিল, মিঃ ডয়েসার জিতলে আমেরিকাকে প্রাগৈতিহাসিক ১৪৯২ সালের দিকে নিয়ে যেতেন। ভাগ্যিস মিঃ ডয়েসার জেতেন নাই।
ঘটনার নায়ক এক্লিস একটা টাইম মেশিনের অফিসে বসে দেয়ালে ঝুলে থাকা নোটিশ দেখছেনঃ
TIME SAFARI, INC.
SAFARIS TO ANY YEAR IN THE PAST.
YOU NAME THE ANIMAL.
WE TAKE YOU THERE.
YOU SHOOT IT.
৬০ মিলিয়ন বছর আগে যেতে পারবেন, ডাইনোসর শিকার করতে পারবেন। ফিরেও আসতে পারবেন, কিন্ত কঠিন কয়েকটা শর্ত মেনে চলতে হবে। ভবিষ্যতের কোন কিছু আপনি দূর অতীতে ফেলে আসতে পারবেন না, কিছু নিয়েও আসতে পারবেন না। যে প্রানীটি কোন প্রাকৃতিক কারণে মিনিট দু’য়েকের মধ্যে মারা যাবে ( গাছের ডাল ভেঙ্গে বা অন্য কারণে) তাকেই গুলি করতে পারবেন, শিকার করতে পারবেন। বুলেটটাও ফেরত নিয়ে আসতে হবে। ছবি তুলতে পারবেন। নির্দিষ্ট ধাতব পথের বাইরে পা ফেলতে পারবেন না। সোজা কথা ট্যুর গাইডের কথার বাইরে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে কিছুই করা যাবে না।
নানা অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে এক্লিস সবকিছুই ঠিকমতো করে, শুধু অসাবধানে একটা প্রজাপতি তার পায়ের তলায় পড়ে মারা যায়। খুবই সামান্য,কিন্তু ৬০ মিলিয়ন বছরের ব্যবধানে এর দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া টের পাওয়া যায়। অভিযানকারীরা ফিরে আসেন। কিন্তু কোথায় যেন একটু পরিবর্তন সূক্ষ্ণ একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে টের পান । বাতাসের গন্ধে , রিসেপশনে সেই একই লোক, ঘরের রং আসবাব সবই আগের মতোই, তবু কীরকম একটা অস্বস্তি।
প্রবেশমুখের সাইনবোর্ডের দিকে এক্লিসের নজর যায়।
TYME SEFARI INC.
SEFARIS TU ANY YEER EN THE PAST.
YU NAIM THE ANIMALL.
WEE TAEK YU THAIR.
YU SHOOT ITT.
ইংরেজী লেখাগুলোর ধরণ অন্যরকম।
জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন যে ভালো মানুষটিকে প্রেসিডেন্ট পদে আমেরিকায় নির্বাচিত হতে দেখে গিয়েছিলেন তাঁরা , তার যায়গায় সেই প্রগতিবিরোধী অপজিশন প্রার্থী এখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট।
এক্লিস বুঝতে পারে, ৬০ মিলিয়ন বছর আগের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটা প্রজাপতির অবহেলার অসাবধান মৃত্যু তাকে অন্য এক পরিবর্তিত পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে।
এক্লিস হাঁটু গেড়ে বসে পায়ের তলার মৃত সোনালী প্রজাপতিটিকে আঁকড়ে ধরে গুঙিয়ে উঠে প্রার্থনা করে, আমরা কী আবার ফিরে যেতে পারিনা? আমরা কী এই প্রজাপতিটিকে জীবিত করতে পারিনা? আমরা কী আবার শুরু করতে পারিনা ?
ট্যুর গাইড ট্রাভিস এক্লিসের দিকে রাইফেল তাক করে, ঘরের মাঝে বজ্রপাতের মতো একটা গুলির শব্দ শোনা যায়। গল্পের শেষ এইখানেই।
কিন্তু এই থিমের উপরে হলিউডে অসংখ্য ছবি হয়েছে, এখনো হয়ে যাচ্ছে।
Back to The Future; It’s a Wonderful Life ; Frequency ; The Butterfly Effect; হাল আমলের Terminator ; Man In Black এই ধাঁচের ছবি।
পরবর্তীতে Butterfly Effectদারুণ জনপ্রিয় একটা শব্দে পরিণত হয়।
Chaos Theory তে Butterfly Effectকে বলা হয়েছে, প্রাথমিক অবস্থানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে বৃহৎ কোন পরিবর্তন। আমাজানের জঙ্গলে প্রজাপতির ডানার ঝাপটানির দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া প্রভাব ফেলতে পারে প্রশান্ত মহাসাগরের টর্নেডোতে।
কয়েকসপ্তাহ আগে আগে হিন্দি একটা ছবি দেখছিলাম, মাদ্রাজ ক্যাফে( Madras Cafe )
পটভূমি ৮০ দশকে ভারতের শ্রীলংকার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আগ্রাসী হস্তক্ষেপ এবং LTTE (Tamil Tigers) এর সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। একটা জনগোষ্ঠীর জাতিগত লড়াই। রক্তক্ষয়ী ২৭ বছরের যুদ্ধে ( ১৯৮২—২০০৯) প্রায় ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু। উইকি অনুযায়ী, প্রায় ২৭,৬৩৯ জন তামিল টাইগার্স, ২৩,৭৯০ শ্রীলংকান সৈন্য ও পুলিশ, ১১৫৫ জন ভারতীয় সৈন্য, ১০ হাজারেরও বেশী সাধারণ জনগণ। জিঘাংসার রাজনীতির বলি ইন্দিরা পুত্র রাজীব গান্ধীর আত্মঘাতী বোমায় হত্যা। রাজীব গান্ধীর মৃত্যু তামিল টাইগার্সের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করে ফেলে। ভারত হারায় তার প্রধানমন্ত্রীকে, তামিল টাইগার্স হারায় তার ভবিষ্যৎ । এঁরা যে সময়ের সাথে সাথে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সেটা সবাই বুঝে যায়। সন্ত্রাস দিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে কেউ সহানুভূতি পায়নি আজ পর্যন্ত।
নায়কের কথাটা ভালো লাগে , “জো হাম দেখ্তে হ্যাঁয় শুন্তে হ্যাঁয়, সাচ স্রিফ উত্না নেহি হোতা।” আমরা যা দেখি , যা শুনি সত্য শুধু ওইটুকুই নয় ।
আমার মনে হয়, প্রত্যেক রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা থাকে। ভারতের আছে। আমেরিকার আছে, চীনের আছে, সোভিয়েত রাশিয়ার আছে, জার্মানের আছে। পৃথিবী যেমন নিজের অক্ষের উপর ঘুরতে ঘুরতে ৩৬৫ দিনে সূর্য পরিক্রমা করে । প্রতিটি দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাও বাস্তবতা। সেটা সে তার সর্বোচ্চ মঙ্গলের জন্যই করে থাকে। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতায় রাষ্ট্র হওয়াতে ভারতের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক লাভ কি কি, সেইটা ব্যাখ্যা করতে আমার মতো নির্বোধকেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হতে হয় না । বিশাল সেনা খরচ বাঁচিয়ে সামান্য কিছু বিএসএফ দিয়ে সীমান্ত রক্ষায় গত তেতাল্লিশ বছরে ভারতের কত হাজার বিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হয়েছে সেটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় হতে পারে, আমার নয় ।
শোনা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধূলিসাৎ করতে আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ছিল। গর্বাচেভদের একটা জেনারেশনকে পুঁজিবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত করে সময়মতো কাজে লাগানোর জন্য, আমেরিকাকে অনেক অপেক্ষা করতে হয়েছে।
আমাদের দেশের এতোবড় সেনাবাহিনীর দরকার কি ? খুব কমন প্রশ্ন।
আমার পরিচিত এক সেনাবিশেষজ্ঞের মতে, এই সেনাবাহিনী আছে বলে আমাদের সার্বভৌমত্ব টিকে আছে। মায়ানমার আমাদের আক্রমন করার আগে ম্যান অ্যাগেইন্সট ম্যান, বুলেট অ্যাগেইন্সট বুলেট হিসাব করবে। মানে আমাদের সীমান্ত দখল করতে হলে, আমাদের সমস্ত সেনাবাহিনীকে নিঃশেষ করতে হবে, সেটা হবে উভমুখী। সমপরিমাণ সৈন্য তাদেরও ক্ষয় করতে হবে। সুতরাং মায়ানমার চৌদ্দবার ভাববে আমাদের সীমান্ত আক্রমন করার আগে।
এই যে আমাদের আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষানীতি পাশের আরেকটি দেশের স্বৈরশাসক সামরিকজান্তাকে তার নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করছে। এইটা আমাদের আমজনতার বোঝার কথা না। আপনি হয়তো টকশোর পেইড বক্তার কথা রেফারেন্স হিসাবে নিয়ে এসে তর্ক করা শুরু করবেন। তীব্র ভারতবিদ্বেষী হয়ে যাবেন। ঘটনাপ্রবাহ ঘেঁটে দেখার সময় আমাদের নাই। আমরা দুই মিনিটের ম্যাগী নুডলসে তৃপ্ত।
আরেকটা কল্পকাহিনী মনে পড়ছে। কল্পকাহিনীর লেখকের নাম মনে নাই। ধরেন পিঁপড়াদের অসংখ্য প্রজাতির মধ্যে একটা প্রজাতি জ্ঞানবিজ্ঞানে হঠাৎ অসম্ভব উন্নতি করে ফেললো। ধরেন তাদের বসবাস এক বিরাট মাঠের মধ্যে, তাঁরা তাদের চারপাশের এই বিশ্বের রহস্য, সৃষ্টিরহস্য উদঘাটন করতে চাইল। তাঁরা পারবে কি? রানী পিঁপড়া বছর ত্রিশেক বাঁচলেও কর্মী বাঁচে বছর তিনেক। সুতরাং তিন বছর ধরে পায়ে হেঁটে ওই সভ্য জ্ঞানী পিঁপড়ার দল এই মাঠের কতটুকু অতিক্রম করবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কী কী বুঝতে পারবে, সৃষ্টি রহস্যের কী উদ্ধার করতে পারবে ?
আমাদের অবস্থা প্রায়শঃ ওই জ্ঞানী পিঁপড়ার মতোই । এই ক্ষুদ্র জীবনে অনেক রহস্যকে আমীমাংসিত রেখেই আমাদের চলে যেতে হবে।
প্রকাশকালঃ ১২ই জুন, ২০১৫
by Jahid | Nov 25, 2020 | শিল্প ও সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি, সাম্প্রতিক
(পুরনো ও প্রিয় একটি লেখা, যা এই অস্বস্তিকর বাংলাদেশের জন্য সবসময় প্রাসঙ্গিক।)
আজ সকালে কন্যাকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে ভাঙ্গাগাড়ীতে পুরনো সিডি খুঁজছিলাম, কিশোর কুমারের একটা বাংলা সিডিও পেলাম, চালু করতেই সেই ঐশ্বরিক দরাজ গলা বেজে উঠলো।
“তারে আমি চোখে দেখিনি , তার অনেক গল্প শুনেছি,
গল্প শুনে তারে আমি অল্প অল্প ভালোবেসেছি।।
আসতে যেতে ছলকিয়া যায়রে যৌবন,
বইতে পারে না তারও বিবশ মন ;
ভালোবাসার ভালো কথা শুনে নাকি শিহরিয়া যায় শুনেছি।।
চোখেতে তার স্বপ্ন শুনি ভীড় করে থাকে,
মরণ শুনেছি হাতছানি দিয়া ডাকে,
বিষের আবার ভালোমন্দ কীরে যখন আমি মরতে বসেছি !!! ”
কিশোর কুমার , মান্না দে আমাদের দুই প্রজন্ম আগের হলেও এঁদের গান আমাদেরকেও মাতিয়ে রেখেছিল। বাংলাব্যান্ডের উত্থানের সমসাময়িক সময়ে ফিতা ক্যাসেটের যুগে এঁরাই ছিলেন আমাদের সবচেয়ে কাছের।
গানের লাইনটি আবার খেয়াল করুন , ‘আসতে যেতে ছলকিয়া যায়রে যৌবন, বইতে পারে না তারও বিবশ মন !’
দৃশ্যকল্পটি কেমন? যৌবন ছল্কে পড়ছে, উদ্ভিন্ন বাঁকগুলো আপনাকে মুগ্ধ করছে।
যদিও আমি আমার কন্যাকে স্কুলের গেটে নামিয়ে অপেক্ষারত , তারপরেও ভণ্ডামি না করে বলতে পারি, আমার ‘পুরুষ-চোখ’ কিন্তু ঠিক ঠিকই অতিক্রম কারিণী সকলের , যাঁদের যৌবন ছল্কে যাচ্ছিল তাদের দেখছিল।
বর্তমানের একাধারে নারীদের উপর নিরবচ্ছিন্ন যৌন নিপীড়নের হেডলাইন দেখতে দেখতে আমি বিপর্যস্ত ও ক্লান্ত। পুরুষ হিসাবে আমি লজ্জিত। মনোবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানা কুইক রেন্টাল টোটকা দিয়ে এই ভয়াবহ অসুস্থতা থেকে উঠে আসার পথ , উত্তরণের বাৎলাচ্ছেন।
কিন্তু আমার মনে হয়, পুরোপুরি উৎপাটন করা সম্ভব না হলেও এই অসুস্থতার সার্বিক নিরাময় সম্ভব। এবং সেটা শুধুমাত্র শৈশবে সঠিক যৌন শিক্ষার মাধ্যমে।
বালককে বুঝতে হবে, সে শিশ্ন-ধারী মানুষ ঠিক আছে, কিন্তু বালিকা শিশ্ন-হীন দ্বিতীয় লিঙ্গের দুর্বল কেউ না। বালককে নারীর মাহাত্ম্য বোঝাতে, নারীর মর্যাদা শেখাতে খুব বেশী সময় লাগারতো কথা না। বালকের মা আছে, বোন আছে, অন্য শ্রদ্ধেয়া আত্মীয়ারা আছেন। তাঁদের উদাহরণ দিয়ে তাকে নারীর মর্যাদা শেখাতে হবে।
রহস্যময় দৈহিক বাঁক নিয়ে যে নারী সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, সে একজন মানুষ এবং তোমার চেয়েও অধিকতম মানুষ। বংশগতির ধারা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুনরুৎপাদনের বিশাল শারীরিক যন্ত্রণার দায়িত্ব প্রকৃতি তাঁকে দিয়েছে। বালককে বুঝতে হবে , বোঝাতে হবে নারী শুধুমাত্র স্তন ও যোনীর সমষ্টি একটা ভোগের বস্তু নয় !
পরিবারের কাছ থেকে শিক্ষাটা পেলে ভাল। নইলে শিক্ষায়াতনে। পরিবারের একজন পুরুষকে দেখলে প্রথমেই আমরাতো তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি না !
পোশাক, জুতা, আর্থিক-সামাজিক অবস্থা হেন তেনর পরে তার বিশাল বপু বা স্থূলত্ব নিয়ে কথা হয়।
কিন্তু একজন নারীকে দেখলে কেন প্রথমেই তাঁর স্তন ও নিতম্বের দিকে জুলজুলে নজর যাচ্ছে ? সমস্যাটা কোথায় ? তাঁর অন্যসব বৈশিষ্ট্য কেন আলোচিত হয় না ? একজন কিশোরী , তরুণী আমার সামনে এসে প্রথমেই কেন তাঁর বুক আঁচল বা ওড়না দিয়ে ঢাকাঢাকি করা শুরু করে দেয়। কী তাঁকে ভীত করে তোলে, যে সামনের পুরুষটির ( হোক সে কিশোর, তরুণ , মধ্যবয়সী, বৃদ্ধ) সামনে সে ঠিক নিরাপদ বোধ করে না ! কে তাঁর মনে এই অ-নিরাপত্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে?
বাদ দিই, তাত্ত্বিক আলোচনা। সাহস বা দুঃসাহস করে যদি আমার প্রজন্মের যৌন শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করি , তাহলেও কী কিছুটা ধারনা পাওয়া যাবে না !
অন্য সকলের মতোই আমারও কৈশোরের অসহনীয় বয়ঃসন্ধির একাকীত্ব, দেহের অনাকাঙ্ক্ষিত বেড়ে ওঠা ছিল। ছিল মন খারাপ করা বিকেলবেলা। নিজেকে অপাঙতেয় , তুচ্ছ , অবহেলিত ভাবার দুঃসহ দিনরাত্রি। আমি মোটামুটি নজরে পড়ার মতো ভালো ছাত্র ছিলাম। পরিবারের ও শিক্ষকদের আলাদা একটা এক্সপেকটেশনের ভার আমাকে বইতে হতো। কিন্তু আমিও তো একটা কিশোর। আমার যে ছেলে বন্ধুটি , মেয়েদের স্কুলের সামনে যেয়ে সদ্য কিশোরীদের উদ্ভাসিত চাহনি, রহস্যময় বাঁক দেখে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গল্প করতো ,তাতে আমার মনটাও তো হু হু করে উঠতো।
সে ছিল এক কল্পনার রাজ্য। যদিও আমার শারীরিক মানসিক বৃদ্ধির সমানুপাত বৃদ্ধির পরিমাপ নিয়ে আমার পরিবারে দ্বিধা আছে।আমার মানসিক বৃদ্ধি শরীরের তুলনায় শ্লথ। আমি স্তন্যপায়ী ছিলাম ৬ বছর বয়স পর্যন্ত। এবং কেন জানিনা , আম্মাও আমার অত্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন অতোগুলো বছর। বছর পাঁচেক পর্যন্ত আমার বেড়ে ওঠা নানাবাড়ি কুষ্টিয়াতে। অস্পষ্ট আবছা মনে আছে, হয়তো স্মৃতিতেই পুনঃ-নির্মিত হয়ে আছে। গ্রামের বাচ্চারা ছিল যৌনতার ব্যাপারে অকালপক্ব । সহচর-সহচরী খেলার সাথীদের হঠাৎ বাল্যবিবাহ, তাঁদের যৌনতার অভিজ্ঞতার নিষিদ্ধ আলোচনা তাদেরকে পাকিয়ে দেয়। কোনটা শিশ্ন, যোনি, স্তন, কোনটার কী কাজ, সেটা আমাদের সময়ে আমাদের গ্রামের খেলার সাথীরা ভালোই বুঝতো। পুরোপুরি নাগরিক হতে হতে ৭৯ সাল। প্রতি ঈদে পার্বণে নানাবাড়ি যেতে হোত, যৌন জ্ঞানের পার্থক্যটা তখন চোখে পড়ার মতো ছিল । মোরগ-মুরগী বা কুকুরের সংগমে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ না থাকলেও গ্রামের শিশুদের জন্য সেটা ছিল নিষিদ্ধ আনন্দ।
বছর সাতেক থেকে তেরো চৌদ্দ পর্যন্ত সেই অর্থে আমার যৌন চেতনা ছিলনা। অন্তত: আমার কিছুই মনে নেই।ক্লাস ফাইভে আমার সহপাঠিনী মিতু প্রেম করা শুরু করলো বা অধুনা যেটাকে বলে ক্রাশ খেল অপু নামের জনৈক নবম শ্রেণীর উদীয়মান গায়কের সঙ্গে। ওইটা আমার মনে আছে।
ক্লাস সিক্সে স্কুলের পরিবর্তন। স্কুল পরিবর্তনের পরে , নতুন স্কুলের পোলাপানের সঙ্গে এলোমেলো সখ্যতা গড়ে উঠল। ফার্স্ট বয় থেকে লাস্ট বয় সবাই আমার বন্ধু ছিল। সবাই আমাকে আপন করে নিল।
বাসায় মামা চাচা ও গ্রামের আত্মীয়স্বজন অপর্যাপ্ত। দুই বেডরুম,ডাইনিং বাসাতে মাসের বেশীরভাগ দিন আমাকে নিজের বিছানা ছেড়ে দিয়ে ফ্লোরিং করতে হোত। দেশের বাড়ির কেউ না কেউ, হয় চিকিৎসা নয় এয়ারপোর্ট বা চিড়িয়াখানা দেখতে বাড়িতে জিইয়ে থাকত।
বাসায় মামা , চাচা কেউ না কেউ যাওয়া আসার মধ্যে থাকতোই। তাদের ফিসফিসে নারীদেহ নিয়ে কথাবার্তা কানে বাজতো। হ্যাঁ, নারীর নগ্নদেহের ছবি একটা শিরশিরে অনুভূতি এনে দিত। মামা-চাচাদের কারো না কারো অসাবধানে বিছানার তোষকের তলায় ফেলে রাখা নিউজপ্রিন্ট ছাপার পর্ণ পত্রিকা হাতে পড়লো। বেশ কয়েকদিন লুকিয়ে লুকিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলাম। সম্ভবত: অর্ধ-নগ্ন ছবির একসেট প্লেয়িং কার্ডও লুকিয়ে লুকিয়ে কিছুদিন দেখেছিলাম। তো, প নামের এক নতুন স্কুল-বন্ধু স্বমেহনের ব্যাপারটা কেমন করে যেন মাথায় ঢুকিয়ে দিল। আমি জানি না, আমার সব বন্ধুদের সবাই, হয়তো নিজে নিজেই স্বমেহনের আনন্দ পেতে শুরু করেছিল। কিন্তু, এটা কেই আমরা একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করতাম না। এর মাঝে কেউ কেউ স্বমেহন যে খারাপ তা বলে তীব্র অপরাধ-বোধ ঢুকিয়ে দিল। এটা খুব খারাপ, পাপ হবে, শরীর শুকিয়ে খারাপ হয়ে যাবে, স্মৃতিশক্তি নষ্ট হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্লাস সেভেন বা ক্লাস এইট পর্যন্ত যৌনমিলনের ব্যাপারে আমার জ্ঞানের পরিধি ছিল এই যে, শারীরিক মিলনে পুরুষাঙ্গ ও নারীর পায়ুপথ ব্যবহৃত হয়। অবশ্য এইটের শেষের দিকে ক্লাসের অভিজ্ঞ ডেঁপো ছেলেদের জ্ঞান বিতরণে মানব-মানবীর শারীরিক মিলনের সব কিছু সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল !
কিন্তু পড়াশোনার চাপে চিঁড়েচ্যাপটা , কৈশোরের একাকীত্ব স্বমেহনের দিকেই ঠেলে দিয়েছিল আমাকে ও আমাদেরকে।
এসএসসি পরীক্ষার পরপরই আমরা ঘোষণা দিয়ে বড়ো হয়ে গেলাম। এখন আমরা সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরতে পারব। আমরা কলেজ ছাত্র। এবং ‘জ’ নামের এক বন্ধুর বাড়িতে আমাদের প্রথম দলবেঁধে পর্ণ-ছবি দেখা। ঢাকা কলেজে ভয়ঙ্কর মেধাবী মেধাতালিকার বন্ধুদের ছড়াছড়ি। আমরা মিরপুরের ছেলেপেলে ছিলাম নিতান্ত মফস্বলী মফু । গভর্নমেন্ট ল্যাব: বা ধানমণ্ডি বয়েজের পেন্টিয়াম ভার্সনের পোলাপানের কাছে আমরা ছিলাম ডজ মুডের কম্পিউটার। একদিন কেউ একজন আমাদের মিরপুরবাসীকে জিজ্ঞাস করলো আমরা বাংলা পর্ণ বা চটি পড়েছি কীনা। নেতিবাচক উত্তর পেয়ে সে বললো , তোরা তো এখনও শিক্ষিতই হস্ নাই, আয় তোদের শিক্ষিত করি। তো ওই চটি পড়ে আমরা অদ্ভুতুড়ে কিছু পশ্চিমবঙ্গীয় যৌনাঙ্গের ও মিলন পদ্ধতির নাম শিখলাম। বেশীরভাগ পুস্তিকা বটতলায় ছাপানো, নীলক্ষেত উত্তম ভাঁড়ারঘর ছিল সকল কলেজ-গামী ছাত্রদের কাছে।
আমার ধারনা, আমাদের মানসিক গঠনে, ওই সামান্য তথ্য বিকৃতি তেমন দীর্ঘমেয়াদী ছাপ ফেলতে পারে নাই। সমাজ ও পরিবারের এক্সপেকটেশনের চাপ আমাদেরকে অনেকটা একমুখী করে রেখেছিল( স্বমেহনের ব্যাপারটা ছাড়া। পরবর্তীতে আমি পড়াশোনা করে কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারি, স্বমেহন অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। পাপ আর স্বাস্থ্যভঙ্গের ভুল বিকৃত তথ্য যদিও আমার কৈশোরের একটা অংশ বিষময় করে দিয়েছিল। )
বয়েজ স্কুলে পড়লেও নানা কারণে কোচিং ও মহল্লার ভালো ছাত্র হওয়ার বদৌলতে সতীর্থ সমবয়সী বান্ধবী ছিল। কিন্তু ওদের মানসিক পরিপক্বতা ছিল আমার বা আমদের চেয়ে বছর দশেক এগিয়ে। সম্পর্কটা ছিল নিতান্তই বড়বোন-ছোটভাই টাইপের। বিকৃতিহীন স্বাস্থ্যকর।
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির জীবনে নতুন করে কোন তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক জ্ঞানের সম্ভাবনা ছিল না।
যথারীতি কয়েকজন প্লেবয় বন্ধু ছিল, যাদের ব্যবহারিক জ্ঞান ওই পর্ণ-পত্রিকার গল্পের চেয়েও উত্তেজক ছিল। তারা তাদের যৌন অভিজ্ঞতার কথা বলত। আমরা অবদমিত মন নিয়ে তাদের রোমাঞ্চের ও মৈথুনের শীৎকার শুনতাম ও দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম। তারপরে তো বিবাহিত জীবন, ‘দারা পুত্র পরিবার , তুমি কার কে তোমার !’
স্কুলকলেজের ডেঁপো বন্ধুদের কেউ কেউ, ভিড়ের বাসে আরেকজনের সাথে ধাক্কা খেয়েছে বা ধাক্কা না খেয়েই কল্প গল্প বানিয়ে বলেছে এটা বোঝা মুশকিল ছিল । যৌনতার ব্যাপারে ওই বয়সটা ছিল, সবকিছু বিশ্বাস করার, হা করে শোনার।
আমাদের প্রজন্মের মধ্যবিত্ত পরিবারের বেড়ে ওঠা অ্যাভারেজ একটা ছেলের যৌন-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনেকটা আমার মতোই। ছোটখাটো ভুল তথ্য ,স্বমেহন বা পর্ণ ছাড়া আমি কোন বিকৃতি দেখিনা।
কিন্তু এর মাঝে মধ্যবর্তী নতুন একটা বিকৃত প্রজন্ম এসেছে ; যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের শ্লীলতাহানি করছে, বা মাইক্রোবাসে তরুণীকে অপহরণ করে ধর্ষণ করছে, তাদেরকে আমি চিনি না। দুর্ভাগ্য, এই বিকৃতদের সাথেই প্রতিমুহূর্ত বসবাস করতে হচ্ছে আমাকে আমাদেরকে !
[ প্রকাশকালঃ ১৪ই জুন,২০১৫ ]
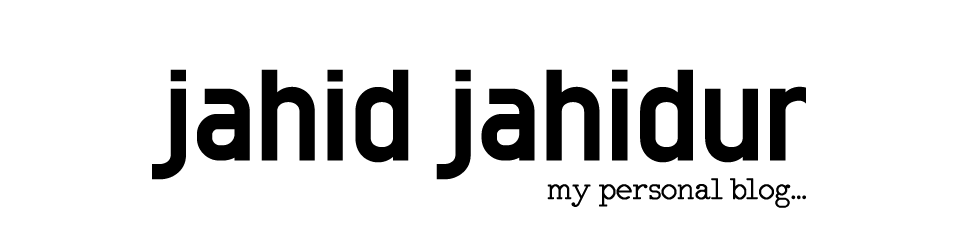
সাম্প্রতিক মন্তব্য