জীবনের উদ্দেশ্য।।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার প্রিয় লেখকদের মধ্যে প্রথমদিকে নেই। যদিও বাংলা সাহিত্যের পুরোধা হিসাবে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য এবং পাঠককুল সেটা অবলীলায় মেনেও নেবেন। সেই বঙ্কিমচন্দ্র যখন কৈশোর পেরিয়ে সদ্য তরুণ ; একটা প্রশ্নের উত্তর হন্যে হয়ে খুঁজেছিলেন। ‘এই জীবন লইয়া আমি কি করিব?’ অনেক অনেকগুলো বছর পেরিয়ে একটি আপাতঃ সন্তোষজনক উত্তর নিজেকেই নিজে দিয়েছিলেন। ‘জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মনুষ্যপ্রজাতির সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা।’
এই এক জীবনে বিভিন্ন বয়সে নানাজনের সঙ্গে ধর্ম-অধর্ম নিয়ে উষ্ণ আলোচনা হয়েছে। দার্শনিক আলোচনায় আমাদের প্রজন্ম কাফকা, ক্যামু, জ্যা পল সার্ত্রে থেকে শুরু করে অধুনা নাসিম তালেব, নোয়াম চমস্কি, স্লাভয় জিজেক, ইউভাল নোয়াহ হারারি-তে এসে পড়েন। আমার মনে হল, আচ্ছা, পশ্চিমাদের তো আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিলই। গত দুইশ বছরের বাংলা সাহিত্যের বাংলা ভাষার বুদ্ধিজীবীরা জীবন , মৃত্যু , জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে কী কী ভেবেছেন, সেটা একটু নেড়েচেড়ে দেখি না কেন।
খুব স্বল্প পরিসরে কিছু প্রবন্ধ পড়েই উপসংহার টানা আমার উদ্দেশ্য নয়। জীবনতো , যতক্ষণ বেঁচে আছি , প্রাণ আছে, ধুকপুক শব্দ আছে চলমান। জীবনের উপসংহার মৃত্যুতেই। আবার এটাও চিন্তা করি , আগের শতকের চিন্তা আমাদের কাছে যেভাবে পৌঁছেছে ; আমাদের চিন্তাশীল মানুষদের চিন্তারাশির গ্রহণযোগ্যতা আগামী শতকে থাকবে, নাকি সেটাও বাতিল হয়ে যাবে।
সংবেদনশীল মানুষমাত্রই জীবন কি, কেন , কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাচ্ছি, জীবনের উদ্দেশ্য কি নিয়ে চিন্তা করে চলেছেন সেই সভ্যতার শুরু থেকে।
নিচের যে আলোচনা অথবা সঙ্কলন ; সেটি, জীবন, জীবনের উদ্দেশ্য ; আমাদের মহাবিশ্ব, ধর্মাচরণ নিয়ে কিছু মনীষীদের প্রাসঙ্গিক চিন্তারাশি। মূলতঃ এখানে আমার কোন নিজস্ব মতামত বা সংযুক্তি নেই বললেই চলে। আমি নতুন কোন দর্শনের কথা বলছি না, পুরনো কোনকিছুকে বাতিল বা তাচ্ছিল্যও করছি না। যেহেতু মনুষ্যসভ্যতার সকল জ্ঞান হচ্ছে সেকেন্ড হ্যান্ড নলেজ। আমি নিজেও বিশ্বাস করি, হোয়াট ইজ অ্যাবসলিউটলি নিউ, ইজ অ্যাবসলিউটলি রাবিশ। সামাজিক যোগাযোগের চলতি হাওয়ায় চলা নানাবিধ মাধ্যমে, বাংলা ভাষার মনিষীদের চিন্তা ও চেতনার একটা সম্মিলিত রূপ পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি মাত্র। আমার সীমাবদ্ধতা ক্ষমার্হ ; সেই কামনা করতেই পারি।
মানুষের স্বরূপ দর্শনের অন্যতম সমস্যা রূপে স্বীকৃত এবং মানুষের স্বরূপ আলোচনা করতে গেলে জীবন কি, জীবনের চেতনা কি, মৃত্যু কি , ইহকাল পরকাল, এই মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থান প্রসঙ্গগুলো চলে আসবেই।
বছর সাতেক আগে ২০১৩ সালে এক দীর্ঘ, ক্লান্তিকর বিমানযাত্রার মাঝে মোহিতলাল মজুমদারের ‘মৃত্যু-দর্শন’ প্রবন্ধটির মুখোমুখি হই। মিটিং তাড়াহুড়ো করে শেষ করে দেশে পথে যাত্রা করেছি। কেননা , আমার বড়মামী যিনি আমাদেরকে মাতৃস্নেহে মানুষ করেছেন , হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন হুট করে। ঐ একই সময়ে আমার নিজের পিতামাতাও শয্যাশায়ী। তাঁদের দুজনেই কিডনি ফেইলে ডায়ালাইসিসের উপরে এক্সটেন্ডেড সময় পার করছেন। বাইরের দেশে অফিসের কাজে যখনি যেতাম, সারাক্ষণ একটা তীব্র আতঙ্ক ও আশঙ্কা বয়ে চলতো মনের গভীরে। এই বুঝি কেউ ফোন করল, এই বুঝি কেউ ফোন করে বলবে আব্বা নেই অথবা আম্মা নেই। আমি শেষ মৃত্যু দেখেছিলাম আমার বড় ফুফার। তাঁর মৃতদেহের পাশে আমাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল। ঐ জলজ্যান্ত মানুষটি সামনে আগরবাতির পাশে সাদা চাদরে কীভাবে পড়েছিল, আমার এখনো চোখে ভাসে। মূলত আমি মৃতদের চেহারা দেখাটা এড়িয়ে চলি। কারণ যখনই সদ্যমৃত সেই আত্মীয় বা আত্মীয়ার চেহারা কাফনের পর্দা সরিয়ে আমার সামনে দেখানো হয়, তাঁকে ঘিরে আমার পূর্বাপর সকল জাগতিক স্মৃতি ম্লান হয়ে যায় , ঐ একটি মাত্র অসহায় চেহারা সারাজীবনের জন্য গেঁথে থাকে, বিঁধে রাখে আমার স্মৃতিকে। বড়ফুফার মৃত্যুর পরে নিজের বাবা-মা। এই আমার মৃতব্যক্তির চেহারা দেখা। এর আগেও আমি দেখিনি, ভবিষ্যতে দেখার দুর্ভাগ্য যেন না হয়।
তো যা বলছিলাম, ‘ মানুষের স্বরূপ’ ( সম্পাদক- আবুল কাশেম ফজলুল হক; মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম)। সঙ্কলনে একসাথে অক্ষয়কুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, কাজী আব্দুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন চৌধুরী, আহমদ শরীফ, আবু সয়ীদ আইয়ুব, মোতাহের হোসেন চৌধুরী —-প্রায় গোটা চল্লিশেক অসাধারণ লেখকের লেখা একসঙ্গে ছিল ! সবগুলো প্রবন্ধ চিন্তা জাগানোর মতো , থমকে দেওয়ার মতো।
মোহিতলাল মজুমদারের একটি প্রবন্ধেই আমি তাঁর ভক্ত হয়ে যাই । একটি প্রবন্ধ আমাকে আমূল বদলে দেয়। এরপরে বিচ্ছিন্নভাবে বইমেলা, আজিজ সুপার, নিউ মার্কেটে সব জায়গায় তাঁর প্রকাশিত বই খুঁজেছি। পাইনি। তিনি বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বিস্মৃতপ্রায় ! তাঁর সম্বন্ধে উইকিপিডিয়ায় কিছু গৎবাঁধা কথা খুঁজে পেলাম। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রকাশিত একটা নির্বাচিত কবিতার বই পেলাম মাত্র। কোলকাতায় একদিনের যাত্রাবিরতিতে বই পাড়ায় ঢুঁ মেরেছিলাম। কয়েকটি নামকরা প্রকাশনীকে তাঁর রচনাসংকলন আছে কিনা জিজ্ঞেস করায় তারা তেমন কোন সদুত্তর দিতে পারলো না।
মোহিতলাল মজুমদারের আরও লেখা পড়ার ইচ্ছায় অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। আমার বেসরকারি চাকরির অবর্ণনীয়, অসহনীয় কাজের চাপে আমার পক্ষে সম্ভব না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগারে অনুসন্ধান চালানো।
আর হ্যাঁ , সেই সময়ের( ৩রা অক্টোবর, ২০১৩) যা লিখেছিলাম, তা তুলে দেওয়াটাও প্রাসঙ্গিক মনে করছি:
বিক্ষিপ্তভাবে ‘ মানুষের স্বরূপ’ বইটা পড়তে পড়তে আসছিলাম ; যেন এক বিপুল সৌন্দর্যের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। মোহিতলাল মজুমদারের ‘ মৃত্যু -দর্শন’ কয়েকবার পড়লাম। অনেকদিন পড়ে কোন প্রবন্ধ আমাকে এইভাবে নাড়া দিলো।
“ মৃত্যুর কথা কেউ ভাবে না, একথা সত্য—ভাবিলে মানুষের পক্ষে বাঁচাই কঠিন হইত।
কিন্তু না ভাবিয়া থাকে কেমন করিয়া ? জীবনের মোহরসে আচ্ছন্ন থাকে—মৃত্যু- বিভীষিকা সে মোহ ভেদ করিতে পারে না। বাঁচিয়া থাকিতে হইবে; সে বাঁচা দিন হইতে দিনে, বা বৎসর হইতে বৎসর নয়-পলে অনুপলে; তাই মৃত্যুকে দেখিলেই সে পাশ কাটায়, বেশিক্ষণ তাহার দিকে তাকাইতে পারে না। ———
মৃত্যুর পরে আর কিছুই নাই—এ কথা যতই সত্য বলিয়া মনে হউক—স্বীকার করিতে সকলেই ভয় পায়। মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবিতে গেলেই মনের মধ্যে একটা অন্ধকার শূন্য মাত্র অনুভব করি—অথচ, শূন্য বা নাস্তিত্বের কল্পনাও আমাদের সংস্কার-বিরোধী; তাই মনে শূন্য বা নাস্তিচেতনাকে নানা কৌশলে আবৃত করার চেষ্টা করে—সেই অন্ধকার গহ্বরকে কোনো কিছু দিয়া ভরাইয়া রাখিতে চায়। মানুষ মৃত্যুশোকে সান্ত্বনা চায়—তাহার অর্থ , মৃত্যুকে সে মানিতে চায় না, অস্তিত্বের ঐকান্তিক বিলোপ তাহার জীবসংস্কারের পক্ষে বিষবৎ মারাত্মক , তাই আত্মপ্রবঞ্চনার দ্বারা সে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।——-
তাই মৃত্যু-দর্শনের কথা যাহা লিখিয়াছি, তাহা মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়; মৃত্যু যত বড় অভিশাপ, মৃত্যু-দর্শন তাহার চেয়ে বেশি। মানুষ ধর্ম বিশ্বাস অথবা দার্শনিক চিন্তা-বিলাস লইয়া থাকুক—মৃত্যুর সত্যকে উপলব্ধি করার মতো দুর্ভাগ্য যেন কাহারও না হয়।”
কিছু লেখা ঘোরের মধ্যে নিয়ে যায় মানুষকে । আমি বহুদিন ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ঘোর কাটেনি এখনো।
সদ্য শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে।
আর্থসামাজিক চাপে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেছি। সারা বাংলাদেশের সরস্বতীর কৃপাধন্য, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত ভর্তি পরীক্ষায় ব্যর্থ, আহত ব্যাঘ্রশাবকদের কিয়দংশ টেক্সটাইল ক্যাম্পাসে জড়ো হয়েছে। বিজেতা ব্যাঘ্রশাবকদের বৃহদাংশ বুয়েটে ও প্রথমসারির কয়েকটি মেডিকেল কলেজ ও নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমার তিন রুমমেটের একজন কুমিল্লা বোর্ডের খোকন দেবনাথ। আর আমার অবস্থা হচ্ছে, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বলে জরুরি কিছু পৃথিবীতে ছিল, সেই ৯০ এর দশকে—সেটা আরেক স্কুলবন্ধুর চাপে ভর্তি পরীক্ষা না দিলে, হয়তো টেরই পেতাম না।
যাই হোক পড়াশোনা নিয়ে একটা গা ছাড়া ভাব আমার ছিল। আমার ভাবলেশহীন উন্নাসিকতা, যাকে অনেকে মননশীলতা বা কদাচিৎ বুদ্ধিবৃত্তিক আধ্যাত্মিকতা বলে ভুল করে বসে ; সেটা দেখে খোকন দেবনাথও ভুল করে বসল। বেচারার ধারণা ছিল এই উন্নাসিক কিশোর হয়তো সেই ‘চিরন্তন প্রশ্ন’ যেটি সকল স্বাভাবিক ও যৎকিঞ্চিত বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যের মনে গত কয়েক হাজার বছর ধরে জেগেছে, ডুবেছে অতঃপর ফিকে হয়ে গেছে, সেটির উত্তর দিতে পারবে। ও জিজ্ঞেস করেছিল:
‘আচ্ছা, জাহিদ আমাদের এই জীবনের অর্থ কি ? এই জীবনের উদ্দেশ্য কি ?’
আমি হুট করে সেই প্রশ্নের গভীরে না গিয়েই বলে ফেললাম, ‘লাইফ ইজ নাথিং বাট পাসিং টাইম!’ ওকে কী বলেছিলাম তা আমি আমি যথারীতি ভুলেও গেলাম। জীবন চলার পথে এরকম কতো মণিমুক্তা চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছি, কে আর রেখেছে খবর!
( হাসির ইমো হবে )।
প্রায় একযুগ পরে, ততোদিনে খোকন দেবনাথ বিয়ে করে ছানাপোনা নিয়ে সুদূর কানাডাতে থিতু হয়েছে।
উল্লেখ্য, এই ছেলের যেমন মেধা, তেমনি ধৈর্য। কানাডাতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর তেমন কর্মক্ষেত্র নেই বলে , সে নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নতুন করে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রী নিয়েছে ! কানাডা সরকারের বিভিন্ন বাঁধ বানানোর প্রজেক্টে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। খোকন দেবনাথ আমার আশেপাশে আমার দেখা একমাত্র লোক, যার দুই বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করা আছে!
তো, খোকনের সঙ্গে ই-মেইলে যোগাযোগ হতো কালেভদ্রে । এবং ২০১০ সালের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আসার পর কথাবার্তা হতো। একদিন জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেমন আছিস রে, জীবন কেমন?’
আমাকে বলল, ‘জাহিদ তোর মনে আছে, শহীদ আজিজ হলের ৩০৩ নাম্বার রুমে বসে আমি তোকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের এই জীবনের অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি?’
আমি বললাম, ‘আমার তো মনে নেইরে, কি উত্তর দিয়েছিলাম।’
ও মনে করিয়ে দিল, আমি কী বলেছিলাম।
ফোনের ওপাশ থেকে বলল, ‘জাহিদ, তোর দেওয়া সেই ব্যাখ্যা থেকে খুব বেশি দূরে যেতে পারিনি আমি। আমি এখন ঠিক তাই করছি, আই অ্যাম পাসিং টাইম ম্যান !’
আচ্ছা ওর কণ্ঠে কি জীবনযাপনের ক্লান্তি ছিল কিংবা বিষণ্ণতা।
কিন্তু মৃত্যুর মতো অনিবার্য একটি ব্যাপারতো আমাদের এই না চাইতেই পাওয়া জীবনকে ম্লান করে দিতে পারে না। কেননা, আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কথাটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।
“ প্রদীপের আলো ক্ষুদ্র, অন্ধকার প্রকাণ্ড। কিন্তু আমার আস্থা ওই প্রদীপের উপরেই ! ” ( রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
জীবন এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা ! কেউ কেউ অনুভব করতে পারে এই মানবজীবন আসলে কতো বড়ো একটা প্রাপ্তি। বৈচিত্র্যময় জীবনের বিশাল , ব্যাপ্ত , বিস্তৃত, অনন্যসাধারণ দীর্ঘ এই পরিক্রমা কতোটাই না উপভোগ্য ! তারপরেও প্রতিমুহূর্তের আলো-অন্ধকারের , ঘৃণা-ভালোবাসার ,অপ্রাপ্তির,আশা-নিরাশার অপর্যাপ্ত আমদের এই বেঁচে থাকা !
আবার একই সঙ্গে কেউ কেউ অনুভব করতে পারে , এই ১৩.৮ বিলিয়ন( ১৩৮০ কোটি) বছরের বিশ্বে , পৃথিবীর জন্ম মাত্র ৪৫৪ কোটি বছর আগে। আদি জীবনের সৃষ্টি মাত্র ৪০০ কোটি বছর আগে আর হাঁটিহাঁটি পা পা করে মানুষ প্রজাতির হামাগুড়ি মাত্র ৪ লাখ বছর আগে থেকে ! সভ্যতার শুরু কম বেশী মাত্র হাজার আটেক বছর ধরে !!!
কয়জন পারে নিজেকে প্রশ্ন করে বুঝতে –এই বিশাল বিস্তৃত কর্মযজ্ঞের মাঝখানে তাঁর অবস্থান আসলে কোথায় ? এতো ক্ষুদ্র, এতো তুচ্ছ, এতো ভঙ্গুর, এতো ক্ষণস্থায়ী , এতো অকিঞ্চিৎ , এতো অসহায়, এতো অনিশ্চিত এই মানব জীবন! একইসঙ্গে জীবনের এই বিশালতা ও ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি পেতে অনেককে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয় !
সেই কৈশোরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ উপন্যাসের নায়ক নিতাই যে বলেছিল, তা সারাক্ষণ আমার কানে বাজে।
‘এই খেদ মোর মনে
ভালবেসে মিটল না আশ- কুলাল না এ জীবনে
হায়, জীবন এত ছোট কেনে ?
এ ভুবনে? ’
আসলেই তো , জীবন এতো ছোট কেন ? আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার এক আড্ডায় বলেছিলেন, ” তবু জীবন শেষ পর্যন্ত অপরিমেয়। কেবলই মনে হয় আজ পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মেছে, যত মানুষ বেঁচে রয়েছে আজকের পৃথিবীতে কিংবা বিশ্বের বিলয় পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেবে, বেঁচে থাকবে—সেইসব মানুষের সমস্ত সম্মিলিত জীবনকে আমাদের এই একটা ছোট্ট জীবন-পরিসরে সজাগভাবে বা অগোচরে আমরা সবাই তো যাপন করেই যাই।
সেদিক থেকে একজন মানুষের জীবন তো আসলে পুরো মানবজাতির জীবন। তা হলে আমরা কাঁদি কেন? আর কেন কাঁদে তারাশঙ্করের নিতাইচরণ?”
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার তাঁর বিস্রস্ত জর্নালে লিখেছেনঃ
আজ এ বয়সে মৃত্যুকে আমার কাছে আর বিস্ময়কর মনে হয় না। মৃত্যুতো চেনাই আমাদের! জন্মমুহূর্ত থেকেই তো আমরা মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত।যাকে আজ আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয় তার নাম জন্ম।
কেবলই মনে হয়, পৃথিবীতে আমার জন্ম নেওয়া—কী অভাবিত এই ব্যাপারটা। কোনো কথা বা প্রতিশ্রুতি ছিল না, কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না, কোনো আবেদনপত্র পাঠানো বা সাক্ষাৎকার দেওয়া হয় নি, কোনো যোগ্যতাও ছিল না এর জন্য, তবু তাই পাওয়া গেছে , সম্পূর্ণ বিনা প্রার্থনায় বিনা এত্তেলায় স্বর্গ থেকে খসে পড়েছে এই অভাবিত মানবজীবন। কী অপরিমেয় আনন্দ আর আলো-আস্বাদময় এই জীবন। গারো পাহাড়ের মতো বড় আর সুবিশাল একটা রাজভোগের ভেতর, তার অফুরন্ত রস আর মাধুর্যের ভেতর যদি ছোট্ট একটা পিঁপড়েকে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে তার কাছে তা যেমন আনন্দ আর উপভোগের এক অন্তহীন জগৎ বলে মনে হবে এ জীবনটাও তো আমাদের কাছে তেমনি।
বিনা মূল্যে বিনা দরখাস্তে পাওয়া এই অমেয় জীবন—অথচ উপেক্ষায় অনাদরে কী অসম্মানই না তাকে আমরা করি।”
আবার প্রিয়তম কবি, বাংলাভাষার শুদ্ধতম কবি, সেই জীবনানন্দ দাশের কথায় স্বস্তি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি। তাঁর কথাগুলো , পড়লেই মনে হয়, আসলেই তো , এই ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের কী মানে হয়।
“ আমি অতো তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে চাই না;
আমার জীবন যা চায় সেখানে হেঁটে হেঁটে পৌঁছুবার সময় আছে,
পৌঁছে অনেকক্ষণ বসে অপেক্ষা করবার অবসর আছে।
জীবনের বিবিধ অত্যাশ্চর্য সফলতার উত্তেজনা
অন্য সবাই বহন করে করুক; আমি প্রয়োজন বোধ করি না :
আমি এক গভীরভাবে অচল মানুষ
হয়তো এই নবীন শতাব্দীতে
নক্ষত্রের নিচে। ”
অথবা সেই কৈশোরেই পড়ে ফেলা , সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন সেইভাবে আমাকে নাড়া দেয় নি। যেভাবে নাড়া দিচ্ছে এই পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে এসে।
লোকটা জানলই না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়।।
বাঁ দিকের বুক পকেটটা সামলাতে সামলাতে
হায়! হায় !
লোকটার ইহকাল পরকাল গেল !
অথচ আর একটু নীচে
হাত দিলেই সে পেত
আলাদ্বীনের আশ্চর্য- প্রদীপ,
তার হৃদয় !
লোকটা জানলোই না !
তার কড়ি গাছে কড়ি হল ।
লক্ষ্মী এলেন
রণ-পায়ে
দেয়াল দিল পাহাড়া
ছোটলোক হাওয়া
যেন ঢুকতে না পারে !
তারপর
একদিন
গোগ্রাসে গিলতে গিলতে
দু-আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে
কখন
খসে পড়ল তার জীবন-
লোকটা জানলই না !
হায় ! জীবন যে কতো অমূল্য ছিল, সে তো বার্ধক্যে এসে, অসুস্থতায় এসে আর মৃত্যুর মুখোমুখি এসে টের পাওয়া যায়।
সেদিন ভাবছিলাম , মানুষে মানুষে তফাৎ কোথায় ? আমিও মানুষ তুমিও মানুষ ! কিসে মানুষের সার্থকতা ? কীসে মানুষ সুখী। জীবনের উদ্দেশ্য কি ? আধ্যাত্মিক চিন্তা কখন আসে, জানেন, যখন ঠিক কাজের চাপ কম থাকে বা অতিরিক্ত থাকে। মানুষ সংসার করে কেন জানেন? আধুনিক মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে থাকে কেন জানেন? মানুষ বিয়ে করে কেন? মানুষ সন্তান উৎপাদন করে কেন? মোটাদাগে মানুষের যৌনতার শারীরিক চাহিদার কথার বাইরে যে কথা থাকে, সেটা তো ডারউইন বলে গেছেন। মানুষ সন্তান রেখে যাওয়ার মাধ্যমে আর সব প্রাণীর মতো , নিজের চিহ্ন রেখে যেতে চায়। আসলে মানুষ চায় ঐহিক অমরত্ব।
সম্পর্কে জড়ায়, বিয়ে করে, সন্তান উৎপন্ন করে কেননা সে চায় তাঁর যাপিত জীবনের একজন হলেও প্রত্যক্ষদর্শী যেন থাকে। পৃথিবীতে হাজার কোটি লোক আছে , এর মাঝে একজন স্বতন্ত্র মানুষের জীবনের কীই বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সমাজে থেকে, বিয়ে করে অন্ততঃ এইটুকু নিশ্চিত করা যায় যে, ব্যক্তির দুঃখ, ব্যক্তির বেদনা, তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর ক্ষুদ্রত্ব, তাঁর সকল প্রাপ্তি, দুর্ঘটনা কেউ একজন দেখছে। সে এই সান্ত্বনা পেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে যে, আমার যাপিত জীবনের প্রত্যক্ষদর্শী একজন তো ছিল !
আলবেয়ার কামু কিন্তু এই যাপিত জীবনের প্রত্যক্ষদর্শনকে একটা আপাতঃ সমাধান বলেছেন। আবার , Existential nihilism বলে একটা ব্যাপার আছে। জীবনের সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে যে সব দার্শনিক মতাদর্শ তৈরি হয়েছে তার মধ্যে যুক্তিবাদীদের কাছে এটিও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে আলবেয়ার কামু এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। Existential nihilism মতে, মানুষের জীবনের কোন অর্থ বা উদ্দেশ্য নেই। মানুষকে পৃথিবীতে ছুড়ে ফেলা হয়েছে প্রাকৃতিকভাবে। মানুষ নিজেই জানে না, সেটা কেন।
এর কিছুটা ভিন্ন মত হল Existentialism। যখন মানুষ নিজের মত করে জীবনের অর্থ খুঁজে নেয়। যেমন: ধর্ম দিয়ে পরকালে বিশ্বাস করে, নিজের কর্মফলে বিশ্বাস করে। পশ্চিমে Christian Existentialism একটা জনপ্রিয় ধারণা।
উল্টোদিকে আলবেয়ার কামুর Absurdism অনেকের কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। মানুষের জীবনের অর্থ জানার আগ্রহ এবং অক্ষমতা দুইটার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সেটাকে Absurdism বলে। Absurd বলতে এখানে ‘লজিক্যালি ইম্পসিবল’ বুঝানো হচ্ছে না, বরং ‘হিউম্যানলি ইম্পসিবল’ বুঝানো হয়েছে। তার মানে জীবনের অর্থ থাকতে পারে। কিন্তু সেটা মানুষ এবং মহাজগত দুটোরই একইসাথে অস্তিত্বগত বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়ত সম্ভব হচ্ছে না।
সরেন এবং কামু এই Absurdity কাটিয়ে ওঠার ৩টি সমাধানও দিয়েছেন।
প্রতমতঃ আত্মহত্যা করা। কেউ যদি জীবনের অর্থ খুঁজে না পায়, সে এই অর্থহীন জীবনকে শেষ করে দিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ পারলৌকিক ধর্মে বিশ্বাস, অলৌকিকতায়। পরকালে বিশ্বাস। জীবনের সমাপ্তি এই ধরাধামেই নয়। জীবন বিস্তৃত হয়ে আছে লক্ষ, কোটি বছর ব্যাপী স্বর্গ ও নরকে। এই অলৌকিকতা মানুষকে স্বস্ত করে। জীবনের সকল বঞ্চনা সইতে সাহায্য করে। ধর্মের বহুল জনপ্রিয়তার কারণ সেটাই। সেখানে মর্তলোকের জীবনই যে সব নয়, পরকালে সুবিস্তীর্ণ , সুদীর্ঘ, অসীম সময়কাল ব্যাপী পরকাল আছে সেই অলৌকিক বিশ্বাস এই জীবনকে মেনে নিতে সাহায্য করে। জীবনের অর্থ খুবই সহজবোধ্য।
তৃতীয়তঃ আধুনিক শিক্ষিতদের আরেকটি মত বহুল প্রচলিত। Absurdity এর মধ্যেই জীবন কাটিয়ে দেয়া। না চাইতেই পাওয়া এই সুবিশাল জীবন, এই উপভোগ্য জীবন ভোগ করে যাওয়াটাই সমীচীন। এর মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে, স্কেপিস্ট, নাস্তিক, সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটা দাগে, পরকালের অলৌকিক রূপকথায় বিশ্বাস করার মতো কোন যুক্তিই তাঁরা খুঁজে পান না।
একটা প্রবন্ধে কলরাডো স্ট্যাট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রখ্যাত প্রফেসর ডোনাল্ড কর্সবির এই উক্তিটি আমার ভালো লেগেছে,“There is no justification for life, but also no reason not to live. Those who claim to find meaning in their lives are either dishonest or deluded. In either case, they fail to face up to the harsh reality of the human situation”. “জীবনের কোন অর্থ বা যৌক্তিকতা নাই। তাই বলে জীবন উপভোগ না করারও কোন কারণ নাই। যারা জীবনের অর্থ পেয়েছে বলে দাবী করে তারা হয় মিথ্যে বলছে অথবা কোন মিথ্যা ভুয়া বিষয়ে বিশ্বাস করছে। দুটো ক্ষেত্রেই তারা মানব জীবনের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে বিফল হয়।”
জীবন, জীবনের উৎপত্তি , ঈশ্বর , ঈশ্বরভাবনা নিয়ে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।
জীবন ও জীবনের উৎপত্তি, ঈশ্বর, ঈশ্বরভাবনা সবগুলো অঙ্গাঙ্গী জড়িত। প্রচলিত ধর্মগুলোর ঈশ্বরভাবনার সঙ্গে অনেকেই ঠিক মানিয়ে নিতে পারেন না। এই অন্তহীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে কী করে জানা সম্ভব। মহাবিশ্বের তুচ্ছ একটা পরমাণুর বা প্রাণকোষের অসীম রহস্যের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক ও নিরুত্তর কম্পমান সেখানে স্রষ্টার এই অপরিমেয় স্বরূপ নির্ধারণ সে কী করে করতে পারে !
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার অনেক আগে গৌতম বুদ্ধের একটা গল্প বলেছিলেন। গৌতম বুদ্ধ নিজেও ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী বা সংশয়বাদী। যা পরিপূর্ণভাবে জানতেন না সে-সম্বন্ধে নীরব থাকাকে তিনি বিজ্ঞসুলভ মনে করতেন। ঈশ্বর-সম্বন্ধে তিনি তাই কখনও কিছু বলেননি। কিন্তু এটাও তো সত্য, যে ইন্দ্রিয় বা বোধের অতীত কোনোকিছু দেখলে পৃথিবীর তুচ্ছতম মানুষটি পর্যন্ত সবসময়ই তাঁর একটা চলন সই ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চায়, না হলে বিশ্বচরাচরের এই নিরবলম্ব নিঃসীম শূন্যতা আর অন্ধকারের মধ্যে সে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।
একবার বুদ্ধের শিষ্যরা তাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করল, ঈশ্বরেরে স্বরূপ তাদেরকে জানাতে। তাঁর বিদায়ের আগে ঈশ্বরের স্বরূপ বুদ্ধের মুখ থেকে তাদের শুনতেই হবে। বুদ্ধ তখন থাকতেন জেতবনে। তিনি তাদের বললেনঃ ‘বেশ , আমি এর উত্তর দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে তোমাদের একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে।’ ‘কী কাজ?’, শিষ্যেরা উৎসুক হয়ে উঠল। তিনি বললেন: ‘ এই বনে যত মৃতপত্র ( মরাপাতা) আছে তোমাদের সেগুলো গণনা করে আসতে হবে,’ এমন বিশাল বনের সমস্ত মরাপাতা সঠিকভাবে গুনে বের করা সহজ নয়। শিষ্যেরা হতোদ্যম হয়ে পড়ল। কিন্তু না-করলে ঈশ্বরের স্বরূপ জানা যাবে না। কাজেই নিরুপায় হয় তারা কাজে নেমে গেল। প্রথমে বহুকষ্টে মাটির ওপরকার সব মরাপাতা ঝাড় দিয়ে একখানে করল তারা। তারপরে এক এক করে প্রতিটা গাছের মরাপাতা সংগ্রহ করে সেগুলোকেও সেইখানে রাখল। তাদের সামনে জমে উঠল এক সুবৃহৎ পাতার পর্বত। তারপর সবাই মিলে বিস্তর পরিশ্রম করে সেই বিপুল পাতাদের গুনে গুনে সঠিক সংখ্যা বের করল। সংখ্যাটা বিরাট। সংখ্যার চেয়েও বিরাট শিষ্যদের শ্রান্তি আর অবসাদ। যখন গণনা শেষ হল, তখন বুদ্ধ তার দ্বিতীয় প্রস্তাবটা উত্থাপন করলেন। বললেন: ‘আমি তোমাদের গণনায় সন্তুষ্ট। কিন্তু তোমাদের আর একটিমাত্র কাজ করতে হবে। সেটি হলেই উত্তর দিয়ে দেব। কাজটি হল, এই বনে যত জীবিত পত্র আছে এবার সেগুলো তোমাদের গণনা করে আসতে হবে।’ আদেশ শুনে তারা প্রায় শুয়ে পড়ল। সামান্য মরাপাতা গুনতেই যাদের শক্তি ফুরিয়ে গেছে, এত জীবিত পাতা তার গুনবে কী করে ? তারা বলে উঠল: ‘এ কী করে সম্ভব প্রভু?’
বুদ্ধ উত্তরে বললেন: ‘এতটুকু একটা অরণ্যের সামনে দাঁড়িয়ে তোমরা ‘অসম্ভব’ শব্দটা উচ্চারণ করতে পারছে অথচ এর চেয়ে অনন্তগুণ ও অসীম যে সর্বব্যাপী ঈশ্বর তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে জানা অসম্ভব বলতে পারছ না ?’
স্যার এই গল্পটি বলার সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ উপনিষদের দর্শন’ বইয়ের আরেকটি গল্প বলেছিলেন। গল্পটি এরকম:
একদিন বুদ্ধ একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিনও এক শিষ্য তাঁকে অনুরোধ করল ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বলতে। বুদ্ধ হাত উঁচু করে গাছ থেকে পরিপূর্ণ একমুষ্টি পাতা আহরণ করে বললেন ঃ আমাকে উপহার দেবার মতো এ বৃক্ষের কি আর কিছু নেই? ( অর্থাৎ আহরণ করার মতো আরও অসংখ্য পাতা কি এ গাছে নেই?)
শিষ্য বলল: আছে ।
বুদ্ধ বললেন : কিন্তু আমার এই ক্ষুদ্র মুষ্টির সে সবে কী প্রয়োজন? ( অর্থাৎ এ মুষ্টি তো ইতিমধ্যেই পাতায় পূর্ণ।)
এর মর্মার্থ হল, ঈশ্বর এই গাছের মতোই অনন্ত। কিন্তু আমার এই ছোট্ট জীবন সেই অসীমতা দিয়ে কী করবে? ঈশ্বরের যেটুকু আমার চারপাশের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ, সেটুকুই তো আমার পক্ষে যথেষ্ট।
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যার তাঁর আরেক আলোচনায় বলেছিলেনঃ
সংস্কৃতশাস্ত্রে কথিত আছেঃ ‘গুরু দ্বিবিধ’। উত্তম গুরু তিনিই যাঁর গৃহে প্রবেশ করার দিন শিষ্যের মনে হবে, ‘এই গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে পদমাত্র ফেলিতে পারিতেছি না।’ কিন্তু যেদিন শিষ্য সেই গুরুগৃহ ত্যাগ করবে সেদিন তার মনে হবে ঃ ‘ এই গুরু এক্ষণে আমার জন্য সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।’ অর্থাৎ এই গুরু শিষ্যকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল, স্বাবলম্বী ও স্বাধীন করে বিদায় দেন। অন্যদিকে নিকৃষ্ট গুরু তিনিই যিনি শিষ্যকে স্বাধীন করার পরিবর্তে প্রতিদিন পরাধীন থেকে পরাধীনতর করতে থাকেন। ফলে একসময় শিষ্য এমন করুণ অবস্থায় পড়ে যে তার মনে হয় ‘ গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পর্যন্ত সুসম্পন্ন করিতে পারিতেছি না।’
জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে গত কয়েক হাজার বছর ধরে লোকে ধর্ম প্রবর্তক, ধর্মগুরু, পুরোহিত, পীর ধরে থাকেন। জীবনকে বোঝার সক্ষমতা নির্ভর করবে তার গুরু প্রথম শ্রেণির নাকি দ্বিতীয় শ্রেণির তার উপর।
ঐহিক অমরতা। কালীপ্রসন্ন ঘোষ।।
মরিয়াও অমর হওয়া যায় কি না , এই আকাঙ্ক্ষা সকলকেই কোনো না কোনো সময়ে আকুল করিয়া তুলে। শত শতাব্দী হইল, গার্গী ও নচিকেতা জ্ঞানে প্রথম অভ্যুদয়েই এই প্রশ্ন লইয়া গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহাদিগের অতি সামান্য চিন্তাশক্তি আছে, তাঁহারা আজিও জীবনের কোনো না কোনো মুহূর্তে চিত্তের ভারে অবনত হইয়া , আকাশে চন্দ্র তারা, বনের বৃক্ষলতা , এবং কীট পতঙ্গ বনের পশুপক্ষী মনুষ্য , সকলের কাছেই এই প্রশ্ন লইয়া উপস্থিত হইতেছেন। কিন্তু কে ইহার উত্তর করিবে ?
বিজ্ঞান এইরূপ অসংখ্য প্রমাণ সহকারে প্রতিপাদন করে যে, বিনাশ একই শব্দটি নিরর্থক ও ভ্রমাত্মক। কিছুরই কোনো দিন বিনাশ হয় নাই, বিশ্বে কিছুরই কোনো দিন বিনাশ হইবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের গতি এই পর্যন্ত যাইয়াই অবরুদ্ধ হয়। বিনাশ না হইলে মনুষ্যের শেষ গতি কি? বিজ্ঞান এখানে নিরুত্তর।
মনুষ্য মনুষ্যকে ভুলে না, এই জন্যই মনুষ্যের ইতিহাস। মনুষ্য মনুষ্যকে ভালবাসে, এই জন্যই মনুষ্যের ইতিহাস। আর যাহাকে ভালবাসে, মনুষ্য সকল সময়েই তাহার গুন-গান ও নাম-কীর্তন করিতে চাহে, এই জন্যই মনুষ্যের ইতিহাস। ইতিহাস এই নিমিত্ত সকলকেই সমান আদরে এই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে যে, — পৃথিবীর যেখানে সে থাক, মানস-কুসুমের সৌরভ ও সৌন্দর্য বিস্তার করিয়া মনুষ্যের মনোমোহনে যত্নশীল হও, ‘আমি ভুলিব না’ ; — পৃথিবীর যেখানে যে থাক, মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শ এবং মানুষী শক্তির শ্রেষ্ঠতর বিকাশ দেখাইয়া মনুষ্যকে উন্নতি হইতে উচ্চতর উন্নতিতে লইয়া যাও, ‘আমি ভুলিব না’ ;–এবং পৃথিবীর যেখানে যে থাক, মনুষ্যকে ভালবাস, মনুষ্যের পরিচর্যা কর, মনুষ্যহিতে ব্রতী হও এবং মনুষ্যের সুখ-বর্দ্ধন ও মঙ্গল-সাধনে স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব দেখাও, এই সৃষ্টি যত কাল রহে, ততকাল ইহা মনে রাখিব,– আমি ভুলিব না। ইহার নাম ঐহিক অমরতা, এবং ইতিহাস যাঁহাদিগকে ভুলে না—যাঁহাদিগের জীবনস্রোতের গতি ঐতিহাসিক স্মৃতির সহিত এইরূপে মিলিত হয়, যাঁহাদিগের হৃদয়-মনের প্রতিকৃতি ইতিহাসের স্মৃতিপটে এইভাবে লিখিত হইয়া রহে, তাঁহারাই সেই অমরতার আশ্রয়পুরুষ।
মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।।
মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কী ?
যখন বৈদিক সময়ে মনুষ্য জীবনের প্রথম অবস্থা, যখন মনুষ্য প্রকৃতির ক্ষমতাদৃষ্টে আশ্চর্যান্বিত হইয়া সর্বত্র দেবতা দেখিত ও সেই দেবতাদিগের আরাধনে করিত, তখন যাগযজ্ঞ, স্তবস্তুতিই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ছিল , ক্রমে যখন চিন্তাশক্তি প্রবল হইতে লাগিল, যখন পৃথিবীর সুখের সঙ্গে জন্মজরামরণকৃত দুঃখ অত্যন্ত ও একান্ত মিশ্রিত বোধ হইতে লাগিল, তখন ইহলোকের সুখে বিসর্জন, পরলোকের শুদ্ধ চৈতন্য ভাবে অবস্থান করাই ( মুক্তিই) জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। যখন অসংখ্য অনার্যগণের মধ্যে আর্যজাতির সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল তখন বংশবৃদ্ধি করিয়া পিতৃপিতামহের নাম রক্ষা করা জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। যখন দারুণ রৌদ্রতপ্ত আরবীয়গণ মহম্মদের মত অবলম্বন করতে প্রথম সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিল—প্রথম চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইল তখন মৃত্যুর পর দিব্যাঙ্গনাসংসর্গে স্বর্গপুরে মদিরা পান করাই বিধেয় স্থির হইল । যখন পুরোহিতপদদলিত ইউরোপ অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন তখন ধর্মের জন্য পুরোহিতদিগকে অকাতরে ধনদান করাই জীবনের উদ্দেশ্যে বলিয়া সংকল্পিত হইল। ইহা অপেক্ষাও আবার যখন ইউরোপের অবস্থা ক্রমশ অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল তখন পোপ মহাশয় ঈশ্বরের নায়েব দেওয়ান হইয়া স্বর্গের একপ্রকার নোট( indulgences) প্রচার করিলেন, সেই নোট ভাঙ্গাইয়া যে টাকা দিবে তাহারই জীবন ধন্য ও সেই “ স্বর্গ লোকে মহীয়তে” স্থিরীকৃত হইল।
এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে কিছু সামাজিক অবস্থায় জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন পরিগণিত হইয়াছে। সমাজ যখন প্রথম উন্নতির মুখে তখন একরূপ উদ্দেশ্য, যখন উন্নতি হইতেছে তখন একরূপ, যখন অতি উন্নতি তখন আর-একরূপ। আবার যখন সমাজ অধঃপাতে যাইতেছে তখন আর-একপ্রকার।
জীবনের উদ্দেশ্য কী, বুঝিতে হইলে আগে জীবন কাহাকে বলিতেছি তাহা জানা চাই।
তাহাই বলিতেছি যে বিদ্যা যশ ধন মান পরোপকার এ-সকল অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ হইলেও ইহার কোনটিই জীবনের উদ্দেশ্য নহে। নিজের শরীর ও মনের উন্নতি হইয়া নিজের কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া তাহার পর বিদ্যা দ্বারা হউক,বুদ্ধি দ্বার হউক, ধন দ্বারা হউক, পরিশ্রম দ্বারা হউক, সমাজকে কিঞ্চিৎ ঋণী করিয়া যাইতে পারিলে জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল। নচেৎ শুদ্ধ বিদ্যা লইয়া ধন লইয়া শক্তি লইয়া স্বাস্থ্য লইয়া ধুইয়া খাইলে কিছুই হইবে না।
আজ কালি লোকে কেবল “সাইন” (Shine ) করিতে চেষ্টা করে। “সাইন” শব্দটির বাংলা তর্জমা হইতে পারে না। বাঙালির –অভিধানে এরূপ উৎকট স্বার্থ-পড়তা-সার-সংগ্রহ- দ্যোতক কথা থাকিতে পারে না।—-
যে সমাজে যথার্থ মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট লোকের আদর নাই এবং গিলটি করা লোকের আদর অধিক, সে সমাজের অবস্থা বাস্তবিকই অতি শোচনীয়। আমাদের এখানে সমাজের অবস্থা সুতরাং বড়ই মন্দ। কিন্তু সে মনুষ্যত্ব কি আর দেখিতে পাইব? আবার কি বাঙালির মনে মনুষ্যত্ব করিবার বাঞ্ছা প্রবল হইবে? এ ছার সাইন করার বাঞ্ছা তিরোহিত হইবে? ভরসা তো দেখি না, সমাজেরও যে বড় মঙ্গল হইবে তাহারো ভরসা নাই।
কে বড়? রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।।
কিছুদিন পূর্বে বিজ্ঞানবিদ্যা স্থির করিয়াছিল, বিশ্বজগৎ মানুষের জন্যই নির্মিত ; যাহাতে মানুষের কোন লাভ নাই, এমন কোন বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে থাকিতে পারে না। এই কথা লইয়া মানুষ আপনার জয়ঢাক আপনি বাজাইয়া তুমুল কোলাহল করিতেছিল; সেই কোলাহলের প্রতিধ্বনি এখনও স্তব্ধ হয় নাই। ইহারই মধ্যে বিজ্ঞানবিদ্যা অন্যরূপ কথা আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তৃণাদপি লঘু, বালুকণা হইতে অধম।
বস্তুতই কি তাই? বস্তুতই কি মানুষ ক্ষুদ্র? বস্তুতই কি অনন্ত জগতের মধ্যে মানুষ অতি ক্ষুদ্র কণিকামাত্র?
না ; ইতিহাসে একই ঘটনা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আইসে ; জ্ঞানের ইতিহাসেও একই সত্য রূপান্তর গ্রহণ করিয়া পুনরাবৃত্ত হয়। মানুষ ক্ষুদ্র নহে।
জগৎ অসীম, আকাশ অনন্ত, কাল অনাদি,– এ সকল মিথ্যা কথা। জগৎ অসীম নহে, আকাশ অনন্ত নহে, কাল অনাদি নহে।মানুষ কল্পনায় পিশাচের সৃষ্টি করিয়া আপনি বিভীষিকা দেখে; মানুষ কাল্পনিক অনন্তের ও কাল্পনিক অনাদির সৃষ্টি করিয়া আপনার সম্মুখে ধরিয়া তাহার কাল্পনিক বৃহত্ত্বের তুলনায় আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া প্রতারিত হয়।
জগৎ কোথায়? জগৎ তোমার বাহিরে নহে ; জ্ঞাননেত্রে চাহিয়া দেখ, জগৎ তোমার অন্তরে। জীবসমাকুলা বসুন্ধরা, সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগৎ, তারকাকীর্ণ নভস্তল তোমারই অন্তরে। তুমি বিশ্বজগতের অন্তর্গত নহে , বিশ্বজগতই তোমার অন্তর্গত। বিশ্বজগতের স্বাধীন অস্তিত্বের প্রমাণ নাই ; তুমি আছো বলিয়াই বিশ্বজগৎ আছে। সূর্য আলোক দিতেছে সেই জন্য তুমি দেখিতেছ ; — ইহা ভ্রান্তি। তুমি দেখিতেছ ও বলিতেছ, সূর্য আলোক দিতেছে ;– ইহাই সত্য। সূর্যের অস্তিত্বের অন্য প্রমাণ কোথায়?
তোমার বন্ধুও হয়তো বলিতেছেন, সূর্য আলোক দিতেছে,– এই সাক্ষ্যে ভুলিও না ; কেননা, তোমার বন্ধুই বা কে ?তুমি দেখিতেছ ও বলিতেছ , উনি আমার বন্ধু ; তুমি দেখিতেছ বলিয়াই তোমার বন্ধু বিদ্যমান।
মানুষের ধর্ম।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
মানুষ আছে তার দুই ভাব কে নিয়ে, একটা তাঁর জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতিকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, সে দিকে বিশ্বমানব।
প্রাণের কথা।। প্রমথ চৌধুরী।।
জীবনটা একটা রহস্য বলেই মানুষের বেঁচে সুখ। কিন্তু তাই বলে এ রহস্যের মর্ম উদঘাটন করার চেষ্টা যে পাগলামি নয় তার প্রমাণ, মানুষ যুগে যুগে এ চেষ্টা করে এসেছে, এবং শতবার বিফল হয়েও অদ্যাবধি সে চেষ্টা থেকে বিরত হয় নি। পৃথিবীর মধ্যে যা সবচেয়ে বড় জিনিস তা জানবার ও বোঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যে দিন চলে যাবে সে দিন মানুষ পশুত্ব লাভ করবে।জীবনের যা-হয়-একটা অর্থ স্থির করে না নিলে মানুষে জীবনযাপন করতেই পারে না। এবং এ পদার্থের কে কি অর্থ করেন তার উপর তাঁর জীবনের মূল্য নির্ভর করে। এ কথা ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। দর্শন-বিজ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বার করতে পারুক আর না পারুক, এ সম্বন্ধে অনেক ভুল বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে। এও বড় কম লাভের কথা নয়। সত্য না জানলেও মানুষের তেমন ক্ষতি নেই—মিথ্যাকে সত্য বলে ভুল করাই সকল সর্বনাশের মূল। সুতরাং প্রবন্ধলেখক এ আলোচনার পুনুরুত্থাপন করে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন।
মানুষের মর্যাদা।। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।।
সভ্য মানুষে একথা বোধহয় ভালো করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছে, মানুষকে পশু করিয়া না লইতে পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না। [ শ্রীকান্ত, ৩ পর্ব পরিচ্ছেদ ১১]
মানুষ জন্মিলেই মরে, কেহ দু-দিন আগে কেহ দু-দিন পরে—- এ আমি সহজ ও অত্যন্ত অনায়াসে বুঝিতে পারি। বরঞ্চ ইহাই ভাবিয়া পাই না, এই মোটা কথা বুঝিবার জন্য এতো শাস্ত্রালোচনা, এতো বৈরাগ্য সাধনা, এত প্রকারের তত্ত্ব বিচারের প্রয়োজন হয় মানুষের কিসের জন্য। সুতরাং মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে। এ যেন আমি সহিতেই পারি না। [ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীকান্ত, ৩ পর্ব, পরিচ্ছেদ ১১ ]
মানব-প্রীতি।। [ছুঁৎমার্গ]। কাজী নজরুল ইসলাম।
মানুষ চিরকাল মানুষের উপর যে অত্যাচার করিয়া আসিতেছে, তাহা পশুদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ মানুষ একটি চিন্তাশীল পশু। তাহার বুদ্ধিবৃত্তি এতো প্রবল যে , ইচ্ছা করিলেই সে তাহার ভিতরকার পশুটিকে দুর্দান্ত এবং নির্মম করিয়া তুলিতে পারে। পশুর সুখের চেয়ে তার সুখ আরামের স্পৃহা একবিন্দু কম নয় এবং এই নিমিত্তে সে পৃথিবী কেন সৌরজগতটাকে ধরিয়া বাঁধিয়া তার আরামের যন্ত্রে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে।তাই রেল স্টিমার, বিদ্যুৎ গাড়ি কলকারখানা একটির পর একটি করিয়া মানুষের আরামের নিমিত্ত সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং এই নিমিত্ত বায়ু , বিদ্যুৎ হইতে আরম্ভ করিয়া কোটি কোটি মনুষ্য পশুপক্ষী, অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য-পশুর দাসখৎ লিখিয়া দিতে বাধ্য হইতে লাগিল। কেহ ধর্মের নামে, কেহ বা সমাজ, শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে কোটি কোটি জীবনকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দী করিতে লাগিল। ফলে আজ সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া ইউরোপীয়গণ এশিয়া ও আফ্রিকার ধর্ম ও সমাজ শাসন করিতেছে, আবার আমাদের সমাজে কতকাল ধরিয়া মুষ্টিমেয় তথাকথিত উচ্চজাতীয় নিম্নজাতির ধর্ম ও সমাজ রক্ষা করিয়া তাহাদের পরলোকে সম্পত্তি করিতেছে।
মানুষকে ঘৃণা করিতে শেখায় যে ধর্ম, তাহা আর যাহাই হউক ধর্ম নয়। ইহা আমরা চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতে পারি। এই ধর্মেই নরকে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কী উদার সুন্দর কথা! মানুষের প্রতি কী মহান পবিত্র পূজা ! আবার এই ধর্মেই সমাজে মানুষকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য মনে করিবার মত হেয় জঘন্য এই ছুঁৎমার্গ বিধি ! কী ভীষণ অসামঞ্জস্য !
কাজী নজরুল ইসলাম। [ প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁকে লেখা চিঠি ]
আমি আজও মানুষের প্রতি আস্থা হারাইনি—তাদের হাতের আঘাত যত বড় এবং যত বেশিই পাই। মানুষের মুখ উল্টে গেলে ভূত হয়, বা ভূত হলে তার মুখ উল্টে যায় ; কিন্তু মানুষের হৃদয় উল্টে গেলে সে-যে ভূতের চেয়েও কত ভীষণ ও প্রতিহিংসাপরায়ন হিংস্র হয়ে ওঠে তাও আমি ভালো করেই জানি। তবু আমি মানুষকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। স্রষ্টাকে আমি দেখিনি , কিন্তু মানুষকে দেখেছি। এই ধূলিমাখা পাপলিপ্ত অসহায় দুঃখী মানুষই একদিন বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করবে, চিররহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করবে, এই ধূলোর নিচে স্বর্গ টেনে আনবে , এ আমি মনে প্রাণ বিশ্বাস করি।
মানুষ ও সভ্যতা। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ।।
আজ মনে পড়িতেছে মহাভারতের সেই যুগের কথা, যখন স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক অসংযত ছিল, যখন ব্যভিচার গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত না, তারপর একদিন মুনিপুত্র সৌনক আপন মায়ের অমর্যাদা দর্শনে মর্মাহত হইয়া মহাসভা আহ্বান করিলেন এবং স্ত্রী-পুরুষের ভিতরকার যৌন-নিষ্ঠার ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেন। এই যে স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তীব্র অনুশাসন—ইহা মানুষকে সভ্যতার দিকে ঠেলিয়া দিল কি অসভ্য করিয়া তুলিল, তাহা বুঝাইবার যোগ্য কোনো বিশ্বজনীন আদর্শ ত লোকের সম্মুখে তখন ছিল না। কেননা প্রকৃতির সর্বত্র তখন ব্যভিচার প্রচলিত। পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকল শ্রেণিতে যে রীতি প্রচলিত, তাহা যে মানুষের অনুষ্ঠেয় নহে প্রকৃতি তখনও এ শিক্ষা দেয় নাই, এবং দেওয়া স্বাভাবিকও ছিল না ; অথচ মানুষ এই অনুশাসনকে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল ; কেননা ইহাতে সমাজের ‘মঙ্গল’ সাধিত হইয়াছিল। একাধিক পুরুষের এক দার গ্রহণ আর্য সমাজেও দেখিতে পাওয়া যাইত। এখনও তিব্বতে এবং নেপাল-দার্জিলিংএ এ-প্রথা প্রচলিত আছে, ইহাতে ত কোনো দৈব অভিসম্পাত তাহাদের প্রতি পতিত হইতে কখনও দেখা যায় নাই। প্রকৃতি ও তাহার বিশাল প্রজাপুঞ্জের ভিতর ইহার বিরুদ্ধে কোনো বিশিষ্ট নিয়ম করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, একটি স্ত্রী-পশু একাধিক পুরুষ-পশুতে উপগতা হইলে কখনও কি তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে? তবে মানুষ দার গ্রহণে স্বাতন্ত্র্যকে এমন করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়াছে কেন? কারণ, ইহাতে সমাজের কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। কল্যাণ অর্থ মানুষের স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধির কথা বলিতেছি না। মানুষ ইহাতে যে সুখী হইয়াছে এই কথাই আমরা বলিতে চাই।
মুসলিম সমাজও এখন অজ্ঞতারূপ শয়তানের দ্বারা আবিষ্ট। অজ্ঞতাই পাপ। পাপই শয়তান। অজ্ঞতায় মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাহার হৃদয়কে এমন আগাছাপূর্ণ করিয়া ফেলে যে , সেখানে কোন সদুপদেশের বীজই শিকড় গড়িতে পারে না, অঙ্কুরিত পল্লবিত হইতে পারে না। সমাজের মানসক্ষেত্রকে আগে আগাছা মুক্ত করিতে হইবে, তার বুকের উপর হইতে সকল কুসংস্কারের চুনা বালি ধুইয়া ফেলিতে হইবে, তারপর তাকে রীতিমত তালীমের কোদালি দ্বারা তৈয়ারি করিতে হইবে, তবে তো সেখানে খাঁটি ইসলামের বীজ বপন করা চলিবে। তবে তো উহাতে সাম্য , প্রীতি ও সাধনার সুরভিত কুসুম মঞ্জরিত হইবে।
মানুষ মরে ,নমাজি মরে, হাজি মরে , গাজি মরে, কে কয়দিন স্মরণ রাখে ? কিন্তু সেবক মরিলে চিরদিন তারজন্য জগৎ কাঁদে, সে ক্রন্দনের শরিক শুধু তার নিজের সমাজ নহে, সকল সমাজ, সকল দেশ, সকল কালে তার জন্য অশ্রু অর্ঘ্য পাঠাইয়া নিজেরা ধন্য হয়। কোন্ কালে কুমারী নাইটিংগেল সেবাধর্মে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সকল জাতির ইতিহাস তাহার গান গাহিতে লালায়িত।
জীবনের শিল্প। এস ওয়াজেদ আলি।।
এক শ্রেণির ভাবুক আছেন, যাঁদের Hedonists বা আনন্দবাদী বলা হয়। তারা বলেন কাজের গুণাগুণ তার আনন্দ-প্রদায়িনী শক্তির উপর নির্ভর করে, অন্য কিছুর উপর করে না। তাদের দুইটি দল আছে, ১. Egoistic Hedonists বা আত্মসুখবাদী এবং ২ Utilitarian বা সাধারণ সুখবাদী , প্রথম দলে মতে ব্যক্তিগত সুখী জীবনে কাম্য, আর দ্বিতীয় দলের মতে , আমাদের পরম কাম্য হচ্ছে ব্যক্তিগত সুখ নয়-সামাজিক সুখ।
তা ছাড়া কেবল সুখই জীবনের পরম কাম্য হতে পারে না। সমুদ্র-সমুদ্রগর্ভ-বিহারী শামুকের বিপদহীন জীবন Socrates কিংবা Luther-এর বিপদসঙ্কুল জীবনের চেয়ে সুখময় হতে পারে, কিন্তু বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। এই জন্য সুখবাদের অন্যতম গুরু দার্শনিক John Stuart Mill বলতে বাধ্য হয়েছেন,’ It is better to be Socrates dissatisfied than Pig satisfied.
তাই যদি হয়, তা হলে, স্বীকার করতে হবে যে, সুখবাদের – তা সে সুখ ব্যক্তিরই হোক আর সমষ্টির হোক—কোনো দার্শনিক ভিত্তি নাই।
এক বাদশাহ নির্দোষ এক বন্দীকে হত্যা করবার আদেশ দিয়েছিলেন। জীবনের আশা যখন রইল না , সেই বন্দী তখন অশ্লীল ভাষায় বাদশাহকে গালি দিতে লাগলো। বাদশাহ অনুচরদের জিজ্ঞাসা করলেন , লোকটি কি বলছে? এক মহামান্য উজির বাদশাহর কথা শুনে বললেন, “ ও বেচারা বলছে , যারা ক্রোধকে দমন করেন , তারাই প্রকৃত মহাশয় লোক।” উজিরের কথা শুনে বাদশাহর মনে দয়ার উদয় হল। তিনি লোকটিকে ক্ষমা করে দিলেন।
বাদশাহর এক দুষ্ট উজির ছিলেন, তিনি আর চুপ থাকতে পারলেন না, বললেন, “ হুজুর, আমাদের মতো লোকের পক্ষে বাদশাহর সামনে মিথ্যা কথা বলা উচিৎ নয়। কয়েদী হুজুরকে গালি দিচ্ছে আর নিন্দাবাদ করছে।” বাদশাহ বিরক্ত হয়ে বললেন, “তোমার সত্যের চেয়ে ওর ( অর্থাৎ প্রথমোক্ত উজিরের) মিথ্যা আমার বেশি প্রিয়। ওর মিথ্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মহৎ আর তোমার সত্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিচ এবং ঘৃণ্য।”
মানুষ মোহাম্মদ। কাজী মোতাহার হোসেন।।
মোহাম্মদের পুত্র সন্তান ইব্রাহিম যেদিন পরলোক গমন করেন, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লোকে বলাবলি করতে লাগল, মহাপুরুষের শোকে সমবেদনা জানাবার জন্য প্রকৃতি মলিন বেশ ধারণ করেছে। মোহাম্মদ এই কথা শুনে বললেন, ‘আমার ছেলের মৃত্যুর সঙ্গে এই সূর্যগ্রহণের কোনো সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতির যে বাঁধা নিয়ম আছে, সেই অনুসারে কাজ হয়ে থাকে।’
মহাপুরুষদের জীবনে অনেকগুলি ঘটনা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ থাকে। মোহাম্মদের শেষ বয়সের বিবাহ ব্যাপারকে সেই শ্রেণির অন্তর্গত বলে মনে করা যেতে পারে।
মানবিকবাদ।। অন্নদাশঙ্কর রায়।
অর্থাৎ মানুষকে জানতে হলে যেমন দেহতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব জানতে হয়, তেমনি তার ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়।
পরিবর্তনই মানুষের ধর্ম, সহস্র পরিবর্তন সত্ত্বেও যদি কিছু অপরিবর্তনীয় থাকে তবে সেই অপরিবর্তনীয় সত্তাও মানুষের ধর্ম। সে যদি ঈশ্বর কি অমৃত হয়ে থাকে তবে তাকে কষ্ট করে রক্ষা করতে হবে না। সে আপনি আপনাকে রক্ষা করবে।‘ গেল ধর্ম, গেল নীতি, গেল সমাজ, গেল রাষ্ট্র’ বলে হৈ চৈ যারা বাধায় তারা পরিবর্তনযোগ্যকে অপরিবর্তনযোগ্য অপরিবর্তনীয় বলে জাহির করে ও পরিবর্তনের স্রোতকে রোধ করে দাঁড়ায়।
মানবিকবাদের বিবর্তন একদিনে হয়নি। প্রাচীন যুগেও এর অস্তিত্ব ছিল, মধ্যযুগেও এর বিলয় ঘটেনি। আধুনিক যুগেও একে বহু বাঁধা বিঘ্নের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। বারবার দীপ নিবে গেছে। তাকে জ্বালিয়ে দিতে হয়েছে। এই তো সেদিন ইটালিতে, জার্মানিতে ও জাপানে গেল নিবে। আবার জ্বলছে। তার পর মানবিকবাদের বীজ ধর্মের মধ্যেও ছিল। বৈদিক, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিস্টান , মুসলমান প্রভৃতি ধর্মের মধ্যে তো নিশ্চয়ই , আরও আগে যেসব ধর্ম উদয় ও অস্ত যায় তাদের মধ্যেও। ধর্মে সঙ্গে এর জাতশত্রুতা নেই। কিন্তু ধর্ম যখনি স্থাণু হয়েছে আর মানবিকবাদ গতিশীল হয়েছে তখন বিরোধ বেধেছে।
খাঁটি মানুষ ও তার কৃত্য। কালিদাস ভট্টাচার্য।
শিল্প ও জ্ঞান , উভয় রাজ্যেই তৃতীয় একদল তথাকথিত সমঝদার দেখা যায় যাঁরা মিত্রম্মন্য হলেও নিজেদের অজ্ঞাতে ভয়ঙ্কর শত্রুতা আচরণ করেন। শিল্পরাজ্যে এঁরা হলেন বাগাড়ম্বরী—কিছুই বোঝেন না, অথচ আপাতমনোরম অনেক কথা বলেন। নিজেদের অজ্ঞাতে এঁরা শিল্পের সমূহ ক্ষতিসাধন করেন। এঁরা প্রকৃত অধিকারী অথচ রসিকজনকে ঈষৎ বিপথে চালিত করেন। তদুপরি এঁরা যখন নিজেদের বিকৃত ধারণা অনুযায়ী ‘শিল্প’ সৃষ্টি শুরু করেন তখন তো একেবারে বিভীষণের পর্যায়ে নেমে আসেন—অজ্ঞাতসারে হলেও অন্তর্ঘাতবৃত্তির পরাকাষ্ঠা দেখান। দর্শনরাজ্যেও এ জাতীয় বিভীষণের উৎপাত চিরকাল হয়ে এসেছে। তার ফলেই দর্শনজগতে এত নৈরাজ্য, এমন-কি, দর্শনশাস্ত্র জিনিসটা কী, সে বিষয়েও। অতি আধুনিককালে এঁরা প্রায় খোলাখুলি অন্তর্ঘাতলিপ্ত। বিরুদ্ধ প্রচারে ততটা ক্ষতি হয় না যতটা হয় বিকৃত দর্শনসৃষ্টিতে। এরা বুদ্ধিমান এই জন্যে ক্ষতিও হয়েছে সর্বাধিক।।
মানবতন্ত্রের ভূমিকা।। শিবনারায়ণ রায়।
হ্যামলেট অথবা ফাউস্ট, খাজুরাহোর মিথুনমূর্তি অথবা মদিলিয়ানির দীর্ঘগ্রীব স্ত্রীপুরুষ, মোৎসার্টের সোনাটা অথবা রবীন্দ্রনাথের গান আহৃত বহুবিধ উপাদানবলীর দ্বারা সুস্পষ্ট বটে, কিন্তু শিল্পীর কল্পনায় সৃজিত ও বিভিন্ন মাধ্যমে বিধৃত হবার আগে এসব শিল্পকৃতির স্থানেকালে কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তারা কোনো পূর্ববর্তী রূপের প্রতিরূপ নয়। অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব রচনার যে শক্তি মানুষের বৈশিষ্ট্য এরা তার বিবিধ প্রকাশ। মানুষী সৃজনীশক্তির বিশুদ্ধতা যন্ত্রসঙ্গীতে স্পষ্টতম, কিন্তু, চিত্রে , ভাস্কর্যে সাহিত্যেও উদ্ভাবনার ক্রিয়া অপ্রকট নয়।
সাধু এবং সজ্জন।। আবু সয়ীদ আইয়ুব।
অপরপক্ষে , বুদ্ধের নির্দেশিত মার্গ হল শীল ও সমাধির পথে প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার ফলে বৈরাগ্য এবং পরিশেষে নির্বাণ। নির্বাণ মানে অবশ্য শূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া নয়, তা ‘ ইহজীবনের মধ্যেই এক বিশেষ মানসিক অবস্থা( অর্হন্তের অবস্থা) যাহাতে পরিপূর্ণ শান্তি অ স্মাহিতি চিত্তে বিরাজ করে।‘ ( হিরীয়ন্ন)
মমতা ও মনন।। অম্লান দত্ত।
মানুষের স্মৃতিশক্তি যেমন দীর্ঘ, সময়ের ব্যবধানে আবেগকে কিছুটা নিরাসক্ত ভাবে দেখবার শক্তিও তেমনই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তা যদি না হত, তবে সঞ্চিত তিক্ততার অন্তর্দাহেই আমাদের দ্রুত মৃত্যু ঘটত। স্মৃতির জাদুর সঙ্গে আমরা সবাই অল্পবেশী পরিচিত।যে-সব ঘটনা একদিন আমাদের অত্যন্ত চঞ্চল ও উত্তেজিত করে তুলেছিল , তারাই আবার ধীরে ধীরে স্মৃতির পটে ঈষৎ সহাস্য, ঈষৎ বিষণ্ণ মুখচ্ছবির মতো সারিবদ্ধ হয়। এরই সঙ্গে , সাহিত্যের জাদুরও মিল আছে।
ধর্ম একটি ভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ায়। আমাদের ‘অহং’- কে নিয়েই ধর্মের প্রশ্ন, যাতে বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে টান পড়ে। যে –অস্বস্তির মূলে ধর্মজিজ্ঞাসা, শুধু শিল্পে তা আশ্বস্ত হয় না।
বিজ্ঞানীর ধর্ম।। দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়।
ধর্মের কাছে মানুষ কেন যায় এবং কী ধরণের চাহিদার নিরসন তার কাছে আশা করে।
এ-প্রশ্নের সদুত্তর কপিলের সংখ্যাদর্শনে দেওয়া হয়েছে। কপিল অবশ্য ঠিক ধর্মের কথা বলেননি, বলেছেন মানুষের মনের জিজ্ঞাসার কথা। তাঁর মতে, আধিভৌতিক, , আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক, এই তিন রকমের দুঃখের নিবৃত্তিই হচ্ছে জিজ্ঞাসার বিষয়।
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনের প্রথম পৃষ্ঠাতেই বলেছেন:
Even when I was a fairly precocious young man the nothingness of the hope and strivings which chase most men restlessly through life came to consciousness with considerable vitality. Moreover, I soon discovered the cruelty of the chase, which in those years was much more carefully covered by hypocrisy and glittering words than in the case today. By the mere existence of the stomach everyone was condemned to participate in that chase. Moreover, it was possible to satisfy the stomach by such participation, but not man in so far as he is a thinking and feeling being.
১৬ই জুলাই ১৯৪৫ সালে হিরোশিমার ঠিক একমাস আগে লস অ্যালামস গবেষণাগারের কাছে নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে পরমাণু বোমার প্রথম পরীক্ষাটা করা হয়। — সেই বহুধাবিকীর্ণ পাপ এখন একটা সংস্কৃতি হয়ে গেছে। পরিণাম যাই হোক, উক্ত সংস্কৃতির নাম দেওয়া হয়েছে আত্মরক্ষার গবেষণা ( defense research )
কিন্তু এর অনৈতিকতাটা কোথায়?—
পুরো লড়াইটা হয়ে যায় অঙ্কের ব্যাপার। হাজার হাজার রক্তমাংসের মানুষকে এই যে সংখ্যা বানিয়ে দেওয়া, অবিশেষ ( abstract) করে দেওয়া, আধুনিক সমরপদ্ধতির অনৈতিকতাটা এখানেই। ……
মানুষ আজ জেনেছে, সে মূলতঃ অযোনিসম্ভূত । তার জন্ম এই পৃথিবীর ধুলো থেকে। সেই ধুলো একদিন এককোষী প্রাণী হল। তারপর অভিব্যক্তির দীর্ঘ জটিল পথ বেয়ে একদিন মানুষ আত্মপ্রকাশ করল। দুর্বল দিশেহারা মানুষ। যার আত্মীয়তা কীটানুকীটের সঙ্গে, প্রতিটি প্রাণীর সঙ্গে , সর্বোপরি, উচ্চতর বানরের সঙ্গে। সেই বানর , যারা আজও বৃক্ষচারী।……
এই জ্ঞান কি মানুষকে রিক্ত করবে, পথভ্রষ্ট করবে? কই এর আগে তো তেমনটি ঘটেনি। দেড় কোটি বছর আগে যখন তার দুর্বল বানর-পূর্বপুরুষ বুঝল, শত অসুবিধা সত্ত্বেও বাঁচতে হলে তাকে বৃক্ষ শাখা থেকে নামতে হবে, তখন তো সে হার মানেনি। তার নখদন্ত ছিল না, পাথর ভেঙ্গে সে অস্ত্র বানিয়েছে। একা বেঁচে থাকা সম্ভব নয় বলে সে সমাজ গড়েছে। শিকারকে আকৃষ্ট করতে সে গুহার গায়ে ছবি এঁকেছে। গান গেয়েছে। তার ধর্মানুষ্ঠানের পিছনেও নিছক বাঁচার তাগিদ কম ছিল না একদিন।………..
এই স্বনির্মান, এই বারবার নিজেকে অতিক্রম করাটাই মনুষ্যত্ব। এই বিপদকেই সম্পদ করে তোলাতেই মানুষের যথার্থ পরিচয়। আজ সেই পরিচয় ছড়িয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর সীমানার বাইরে। মহাকাশে এবং মহাকালে।……..
অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের একটি উক্তি এই সূত্রে মনে পড়ে। গভীর অসুখে যখন তাঁর প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়েছে, সেই রকম সময়ে প্রিয় বন্ধু ম্যাক্স বর্ন -এর স্ত্রী হেডিকে আইনস্টাইন বলেছিলেন, ‘ প্রতিটি প্রাণীর সঙ্গেই আমি এমন একটা একাত্মতা অনুভব করি যে, ব্যক্তির শুরু কোথায় আর শেষই বা কোথায়, তাতে আমার কিছু আসে যায় না ।’
প্রগতি ও ধর্ম।। আবদুল হক।।
মানুষ ক্রমাগত বস্তুমুখিন হওয়ার ফলে, এবং তার নীতিবোধ—অন্য কথায় বিবেক—ধর্মনিরপেক্ষ বিচারবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে জীবনযাত্রা ধর্মের সঙ্গে ক্রমাগত সম্পর্কহীন হয়ে আসছে। জন্মহেতু ধর্মবিশেষের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্বীকার করলেও দৈনন্দিন ধর্মাচরণগুলো ক্রমেই পরিত্যক্ত হচ্ছে। যে-কোনো ধর্মাবলম্বীর দিকে তাকালেই ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ হয়। অনেকে ধর্মকে প্রগতির বিরোধী বলেও মনে করেন। ধর্মের ভবিষ্যৎ তাহলে কি ?
মনে হতে পারে, ভবিষ্যতে ধর্ম হয়তো লুপ্ত হয়ে যাবে। ধর্মের মধ্যে চিরন্তনতা যদি না থাকে, ধর্ম যদি সমাজের কোনো অবস্থাবিশেষের পরিবর্তন সাধনের মাত্র যন্ত্রস্বরূপ হয়, তবে বলতে হবে যেটুকু কাজ শেষ হয়ে গেলেই আর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে ! ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না।
কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, ধর্মের অনেক উত্থানপতন অতীতে হয়ে গেছে। কোনো ধর্ম যখন অকার্যকর হয়ে গেছে, অথবা সকল প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ হয়েছে, তখনই নতুন কোনো ধর্মের উদ্ভব হয়েছে।
আজও প্রায় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই এমন কিছু লোক আছে যারা তাদের ধর্মকে ভিতরে বাইরে পুরোপুরি মেনে চলে। তাদের ধর্মাচরণে কোনো বিচ্যুতি নেই। কোনো স্খলন নেই, তাদের ধর্মবিশ্বাসে কোনো ভাঙন আসেনি, ভাঙন আসে না।
এই শ্রেণির মানুষ আগামী যুগে একেবারেই থাকবে না এরূপ মনে করার বোধহয় কোনো কারণ নেই। মানুষের প্রকৃতিগত পার্থক্য ও বৈচিত্র্যে যখন সত্য, পৃথিবীতে সবরকম লোকের জন্মই যখন সম্ভব, তখন মনে হয় ধার্মিক লোকেরও অভাব হয়তো কোনো দিন হবে না। প্রকৃতি, জীবনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের জন্য এক-একজন এক-একদিকে আকৃষ্ট হয়, ( যেমন শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্মপ্রাণতা, নিরীশ্বরবাদিতা ইত্যাদি বিভিন্নদিকে), এবং সেদিকেই সে শান্তি ; তৃপ্তি ও জীবনের সার্থকতা খোঁজে। কোনো অলৌকিক কারণে নয়, মানব প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের জন্যই ধর্ম মনে হয় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা স্বল্প।
মেরুদণ্ড । মোতাহের হোসেন চৌধুরী।।
If the wicked flourish and the fittest survive , Nature must be the Gob or rascals.— G.B.S.
যেদিন ‘সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট’—এই সাধারণ সত্যটি দার্শনিকের কণ্ঠে প্রথম ঘোষিত হল, সেদিন থেকেই পৃথিবীর সর্বনাশের সূত্রপাত। কেননা মূল্যবোধ বিস্মৃত হয়ে সেদিন থেকেই মানুষ তার শ্রেষ্ঠ গুণরাজিকে অবহেলা করে নিকৃষ্ট শক্তিসমূহের পূজার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে, আর শুধু বাঁচার কথাটা বড় হয়ে উঠল বলে, সৌন্দর্য , প্রেম ও আনন্দ মানুষের দৃষ্টিসীমা থেকে অনেক দূরে সরে গেল। সে বুঝতে পারলে, এ-সব গৌণ ব্যাপার, বাঁচার জন্য এ-সবের কোনো প্রয়োজন নেই, যদি পাওয়া যায় ভালো। অধিকন্তু ন দোষায়- না পাওয়া গেলেও তেমন দুঃখ নেই।
দার্শনিকের চেষ্টা হয় অনেক সময় ‘মাচ এডো এবাউট নাথিং’, অথবা পর্বতের মূষিক প্রসবের মত। অনেক মাল-মসলা সংগ্রহ ও গবেষণার ফলে তাঁরা যে সত্যে এসে পৌঁছান, অনেক সময় তা মামুলি সত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দর্শনের সমর্থনে তাই হয়ে ওঠে সকলে শ্রদ্ধেয়—সাধারণ ব্যাপারটাও অসাধারণ হয়ে দেখা দেয়। ‘ফিট’ লোকেরাই সবসময় বেঁচেছে ও বাঁচবে এ-কথাটা বলার জন্য দার্শনিকের গবেষণার প্রয়োজন হয় না, সামান্য পর্যবেক্ষনশীলেরাও তা বলতে পারে।
বাঁচার সাধনা আর ঐশ্বর্যের সাধনা এক নয়, ঐশ্বর্যের জন্য ত্যাগের প্রয়োজন। ছোট জিনিসের দাবিকে না দমালে বড় জিনিসের দাবি বড় হয়ে উঠতে পারে না। বাঁচার সাধনার আধিক্যের ফলে মানুষের ভিতরের ছোট মানুষটিই প্রাধান্য লাভ করে, বড় মানুষটি নষ্ট হয়ে যায়। সেবার অভাবে দেবতা অন্তর্হিত হন, মন্দির খালি পড়ে থাকে। …….
সৃষ্টির গোড়ায় বুভুক্ষা বা বেদনা। বেদনার ফলেই অসম্ভব সম্ভব হয়।
দার্শনিকের শিক্ষার ফলে কী করে এই বেদনার মৃত্যু হয় ; ইদানীং তার একটা প্রমাণ পেয়েছি।
আমার তরুণ বয়সে জনৈক কিশোর বয়স্ক ছাত্রকে আমার খুব ভালো লাগত। তিনি মাঝে মাঝে মুসলমান সমাজের মানসিক দীনতা সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করতেন, আর যাঁরা সেকালে এই দৈন্য দূর করার আন্তরিক চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের প্রশংসা করতেন। তাঁর মুখে কবি-সাহিত্যিকদের কথাই ছিল, রাজনীতিকদের কথা নয়। তিনি বলতেন, রাজনীতিকরা অধিকার আদায় করেন বটে , কিন্তু সুন্দর আনন্দিত জীবনের প্রেরণা দেন কবি-সাহিত্যিকরা ; তাই তাঁরা সমাজের প্রকৃত স্রষ্টা, মানুষের অন্তরে তাঁদেরই সিংহাসন।
তবে মাঝে মাঝে রাজনীতিকরা বড় হয়ে ওঠেন, তার কারণ সমাজের রুগ্ন অবস্থা ; পীড়িতদের কাছে ডাক্তারই বড়, বন্ধু নয়। কিন্তু সুস্থ অবস্থায় এর বিপরীতটাই ঠিক। আধুনিক কালে যে রাজনীতিকরা পৃথিবীতে বড় স্থান লাভ করেছেন, তার কারণ পৃথিবীর পীড়িত অবস্থা। এক হিসাবে দেখতে গেলে সমাজের আভ্যন্তরীণ বিকাশের বাহ্যিক প্রকাশ বলে রাজনৈতিক আন্দোলন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার—সমাজ যে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ নয়, তারই লক্ষণ। কিন্তু বন্ধুদের ছেড়ে যে রোগী ডাক্তারকেই বড় করে তোলেন, বুঝতে হবে তিনি চিররোগী। তার মুক্তির উপায় স্বল্পই।
চিররোগ প্রায়ই মানসিক ব্যাধি। অতএব বন্ধু-বান্ধবের প্রীতিকর সঙ্গই তা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়—বোতল বোতল ঔষধ সেবনে ফায়দা পাওয়া কঠিন। যে জাতি বা সমাজ কবি-সাহিত্যিক ও সৌন্দর্য-শিল্পীদের অবজ্ঞা করে কেবল রাজনীতিকদের বড় করে দেখে, চিররোগীর ন্যায় তারও মুক্তি সুদূরপরাহত। ( রুগ্ন অবস্থায় মানুষের কুপথ্যে রুচি হয় ; প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলনের যুগেও কুপ্রবৃত্তি বড় হয়ে ওঠে । তাই সামাজিক সমর্থন লাভ করে নিষ্ঠুরতাকে নগ্নমূর্তিতে রাজপথে বের হতে দেখা যায়। ) ……..
জাতি যদি কেবল রাজনীতির সাধনা করে তো তার মেরুদণ্ড ষাঁড়ের মতো শক্ত হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারাটিও ষাঁড়ের মতোই কদর্য হয়ে ওঠে। রাজনীতিসর্বস্ব ষণ্ডামার্কা জাতিরা মৌতাতের জন্য মানুষের মতো কোলাকুলি বা করকম্পন না করে ষাঁড়ের মতো গুঁতোগুঁতি করে। ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা লাভ হয়ে পৃথিবীর সর্বনাশ হয়—মানুষের জীবনের মূল্যবান বলে আর কিছু থাকে না। প্রতিকার স্বরূপ মনে রাখা দরকার , মেরুদণ্ড বাঁচার লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র ; রাজনীতিও জাতির লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্য—লক্ষ্য সৌন্দর্যধ্যান ও আনন্দ সাধনা। লক্ষ্যের স্থান উপলক্ষ্য তথা দেবতার স্থানে বাহনকে বসিয়ে পূজা করলে কালের হাতে শাস্তি পেতে হয়, আর যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভিতর দিয়ে আমরা সেই শাস্তিই পেয়ে থাকি।
প্রতিভা। আবুল ফজল।।
প্রতিভা থাকা ভালো কি মন্দ এই নিয়ে রীতিমত তর্ক চলতে পারে। মাঝারি অর্থাৎ যারা কিঞ্চিৎ মোটা বুদ্ধির মানুষ, দেখা গেছে জীবনে তারাই বেশির ভাগ হয় সফল, ও পায় শিরোপা। মোটা বুদ্ধির লোকের চামড়াও হয় কিছুটা স্থূল—প্রায় গণ্ডারের চামড়ার সমতুল্য। কাজেই মারামারি কাড়াকাড়িতে ওরাই হয়ে থাকে দক্ষ—জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হলে যা একান্তই অপরিহার্য। অপরকে ঠেলে, কনুই মেরে সরিয়ে , পা-মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে তাঁরা যারা দেহে বেশ মোটা, আর বুদ্ধিতে বেশ ভোঁতা। বলাই বাহুল্য, সাফল্যের খাতায় এরাই প্রায় পহেলা স্থান। এমন ছেলেকে নিয়ে মা বাপের বুক ফুলে ওঠে গর্বে—বাস্তুভিটা বিক্রি করেও এমন ছেলেকে জামাই করতে চান যে কোনো কন্যার বাবা।
প্রতিভাবানকে লোকে মনে করে অকেজো , নিষ্কর্মা, বুদ্ধির ঢেঁকি—যার ভবিষ্যৎ নির্ঘাত অমাবস্যার তিমির রাত্রি। এমন ছেলেকে মা-বাপও ভালো চোখে দেখে না। জানে এই ছেলে কোনোদিন রোজগেরে হবে না, জীবনে কোনো দুঃখই ঘুচবে না এই ছেলেকে দিয়ে, শুধু শুধু বিড়ম্বনার বোঝা বইতে হবে এই ছেলেকে নিয়ে। কন্যার পিতাও এমন ছেলেকে জামাই করা আর আজরাইলকে ঘরে ডেকে আনা সমান মনে করে।
প্রতিভাবানের বুদ্ধিতে আছে যেমন তীক্ষ্ণতা, চামড়ায় আছে তেমনি সূক্ষ্ণতা—লজ্জা-শরম ও সম্ভ্রমবোধ তাঁর এত টনটনে যে কাড়াকাড়ি ধাক্কা-ধাক্কি করা বা অপরের পা মাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার কল্পনাই তাঁর কাছে ‘ ধরণী দ্বিধা হও’। তাই সরজমিন থেকে শূন্য হাতে সরে পড়া বা শূন্য উদরে পড়ে থাকা প্রতিভাবানের পক্ষে এমন কিছু অসম্ভব কাজ নয়। তাই বলে প্রতিভাবান কি পলাতক ? কাড়াকাড়ির পণ্য-শালা থেকে তিনি পলাতক হতে পারেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভার হাত থেকে পালাবেন কেমন করে ? প্রতিভা যে অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনিব। সে মনিব যে তাকে ঘুমুতে দেয় না, বিশ্রাম করতে দেয় না, খেতে পরতে দেয় না—দিন রাত ঘাড়ে ধরিয়ে নেয় খাটিয়ে। তাই, অনেক মনীষীই এক খাটবার শক্তির নাম দিয়েছেন— প্রতিভা। প্রতিভা আছে অথচ খাটে না, এটা কখনো সত্য হতে পারে না। যেখানে ওটা সত্য সেখানে মনে করতে হবে ওটা প্রতিভা নয়—প্রতিভার ভান মাত্র। বৃদ্ধ বয়সেও রবীন্দ্রনাথ দিনে শুতেন না, নিজের হাতেই নকল করতেন নিজের সব লেখা। শেষ বয়সে লেখা ‘ যোগাযোগ’ এর মতো বিরাট উপন্যাসও নাকি তিনি তিনবার কেটে তিনবার লিখেছেন। এইটি প্রতিভার ধর্ম ও প্রতিভার দায়িত্ব। প্রতিভা ঠাকুরণের দিলে দয়ামায়ার লেশ মাত্রও নাই। বুড়োর ঘাড়ে হাত দিতেও তাঁর বাধে না—খাটিয়ে নেয় বুড়োকেও শেষ নিঃশ্বাস শেষ বারের মতো না পড়া পর্যন্ত। এমনিভাবে খাটুনির খাটিয়া বয়ে বয়েই প্রতিভা পায় সার্থকতা। যদিও প্রতিভার মালিকের জীবনে আসে বারে বারেই ব্যর্থতা। জীবনের ঘোড়দৌড়ে বাজিমাৎ করে তো যত সব মাঝারিরাই। প্রতিভাকে অপেক্ষা করতে হয় দূর ইতিহাসের মুখ চেয়ে। আর মাঝারির ভাগ্যে জোটে নগদ বিদায়। বলাই বাহুল্য মানুষ খুশি হয় নগদ বিদায়ে। তাই , দুনিয়া মাঝারিকেই দেয় জয় ও বরমাল্য দুই-ই। গণতান্ত্রিক নিয়মে ভোট নিলেও নিঃসন্দেহে মাঝারিরই হবে জয় জয়কার। সৃষ্টি বলতে যা বুঝায়—কি সাহিত্যে , কি জীবনে তার ষোল আনাই নির্ভর করে ধৈর্য ধরে খাটবার শক্তির উপর—যার চলতি নাম প্রতিভা। আমাদের তরুণরা যদি প্রতিভার এ অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করেন, তার মূল্য দিতে প্রস্তুত হন, তা হলেই তাঁরা সাহিত্যে, শিল্পে ও জীবনে সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন—যে সৃষ্টি ছাড়া কোনো জাতি , কোনো দেশ কোনো দিন বড় হতে পারেনি। আমরাও পারব না।
মাঝারি সেয়ানা বুদ্ধি জীবনে অবশ্যই নিয়ে আসে সুযোগ-সুবিধা, চলার পথকে করে মসৃণ—তাঁরা সুবিধাসন্ধানী ও সহজপন্থী। প্রতিভাবান কঠিনের সাধক—তিনি নিয়ে আসেন অশেষ দুঃখ শুধু নিজের নয়, অপরের জীবনেও। তাই মাঝারির ভাগ্যেই জোটে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা। প্রতিভাবানদের জন্য তোলা থাকে কাঁটার মালা। তবুও দুনিয়ায় কাঁটার মালা গলায় পরার লোকের অভাব কোনদিন হয়নি। যে জাতির মধ্যে ঐ রকম লোকের সংখ্যা যত বেশি সেই জাতি তত বড় , মহৎ ও তত বেশি সভ্য।
মানুষ প্রবাহপতিত হয় কেন? রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।
বেশির ভাগ লোকই প্রবাহপতিত হয়ে চলেন বা পড়েন—অনেকে আগাগোড়াই, কেউ কেউ এক বয়েসের পর—এ তো আর অস্বীকার করা যাবে না। একথা জেনে-বুঝেই সিদ্ধান্ত করতে হয় ; আমি কী করব? আর দশজন যে-ভাবে জীবন কাটাচ্ছে তা-ই করে কাটাব, নাকি বাঁচার অন্য কোনো লক্ষ্য থাকবে, আর নিজের জীবনযাত্রার ধরণ সেই অনুযায়ী ঠিক করব?
যে-দল ভারী সেই দলে থাকতে চাইলে অবশ্য এতসব ভাবার কোন দরকার নেই। নিজের থেকে কিছুই করতে হবে না। পরিবার , সমাজ ও রাষ্ট্রই পর-পর সব ধাপ বাতলে দেবে। ‘ আগে সবাই ঘুষ খাওয়া বন্ধ করুক, তবে আমি করব’ , বলেছিল এক ঘুষখোর । তেমনি , সবাই নিজে ভাবতে শিখলে তারপর আমি ভাবব—এ হলো ভীতু লোকের মনের কথা। প্রবাহপতিত হওয়ার জন্যেই সে হাত-পা, এলিয়ে তৈরি হয়ে আছে।
মানুষে ভয় , মানুষেই ভরসা। হাবিব রহমান।।
মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটি মানব-প্রবৃত্তির কথা বলেছেন। এর একটি সৃজনীবৃত্তি (Eros ) , অন্যটি মারণীবৃত্তি (Thanatos), মানুষ একদিকে সৃষ্টি করে , আবার অন্যদিকে ধ্বংস করে। ঐতিহাসিক যুগ থেকে অদ্যাবধি এই সত্যেরই পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। কিন্তু ফ্রয়েডেই এই সত্যের প্রথম উপলব্ধি নয় ; বহু প্রাচীন কাল থেকে মানুষের চেতনার এই ধারণার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তবে তা ভিন্নরূপে। প্রাচীন পারস্যে জরথ্রুস্ত্রের আমলে ভালো ঈশ্বর ( আহুরা মাজদা) ও মন্দ ঈশ্বর ( আহরিমান) এই দুই ঈশ্বরের ধারণা প্রচলিত ছিল। পারসিয়ানরা এও বিশ্বাস করতো যে এই দুই ঈশ্বরের মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলেছে। এরও আগে ইহুদিদের মনে জিজ্ঞাসা জেগেছিল যে ঈশ্বর তো সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় ; তাহলে মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত করায় কে ? আর এতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই বা ঘটে কার দ্বারা ? তবে কি এই মঙ্গলকারী দেবতার বিরুদ্ধে কোনো দুষ্টুশক্তি তার পরিকল্পনা সফল করে চলেছে? এ প্রশ্নে তাঁরা সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত হতে পারেনি। সে দ্বিধার অবসান তাদের হয় প্রভাবশালী পারসিয়ান চিন্তাচেতনার সংস্পর্শে, সে অন্তত খ্রি. পূ. ৪০০ অব্দের কথা।
ইহুদি –ধারণার প্রভাব পড়ে খ্রিস্ট-ধারনায়ও । ইসলাম ধর্মও এ থেকে বাদ পড়েনি। অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ স্বীকারও করেছেন ইসলাম ধর্ম ইহুদি ও খ্রিস্ট ধর্মেরই বিবর্তিত রূপ। কিন্তু যেহেতু বিবর্তিত সেহেতু ইষ্ট-অনিষ্টকারী সম্পর্কে পারসিয়ান-ইহুদি-খ্রিস্ট ধারণার সঙ্গে ইসলামের ধারণা সম্পূর্ণ মিলবে না। ইসলামে আল্লাহ্ হচ্ছেন দয়াময় প্রভু, আর শয়তান হচ্ছে মানুষের অনিষ্টকারী। উল্লেখ্য যে মানুষকে অনিষ্ট করার ক্ষমতা শয়তানকে আল্লাহ্ নিজেই দিয়েছেন এবং তার ফলেই সে হয়েছে আল্লাহ্ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, যদিও তার নিজের সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। এসব ধারণার বাইরের রূপে গরমিল থাকলেও স্বরূপত কি এক নয়? অর্থাৎ দুটি বিপরীতধর্মী শক্তির কথা সব ধারণায় স্বীকৃতি পেয়েছে।
মানুষের স্বরূপ।। আবুল কাসেম ফজলুল হক।
মানুষের স্বরূপ ( the nature of man, the concept of man, human nature) দর্শনের অন্যতম সমস্যারূপে স্বীকৃত। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় দর্শনের জটিল বিতর্কে প্রবেশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা চাইছি আমাদের কালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।
সভ্যতার ধারায় কারণ- কার্য সূত্র ও উত্থান পতন লক্ষ্য করা যায়। যারা শক্তিশালী তারা একসময় দুর্বল হয়ে পড়ে, আর যারা দুর্বল তারা এক সময়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ……….
কৌটিল্য ও ম্যাকিয়াভ্যালিকে যারা মানবজাতির কুসন্তান বলে গণ্য করেন , তারা ভুল করেন। এই মনীষীরা তৎকালীন শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানবজাতির কল্যাণ কামনা করেছেন ; তাঁদের দেশকালে তাঁরা শাসক শ্রেণির বাইরে গিয়ে মানবীয় সমস্যাবলীর সমাধানের উপায় ভাবতে পারেননি— যেমন প্লেটো, এরিস্টটল দাসবিহীন কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা ভাবতে পারেননি। মানবস্বভাব সম্পর্কে কৌটিল্য ও ম্যাকিয়াভ্যালির গভীর জ্ঞান ছিল। নীতির সঙ্গে যে নমনীয়তার কথা তাঁরা বলেছেন হিংসামুক্ত শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের অনন্ত প্রয়াসের প্রতিস্তরে তাকে কাজে লাগানোর সুযোগ আছে, প্রয়োজন আছে।
মানুষের স্বরূপ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে হব্স এবং রুশো বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছেন। তাঁদের দেশকালও ভিন্ন। দুজনই মানবজাতির পরম কল্যাণ চিন্তা করেছেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করেছেন। আমরা মানুষকে কোন দৃষ্টিতে দেখব? রুশোর না হব্র্সের ?
যাঁরা ‘মানবচরিত্র’ বলে কোনো কিছু স্বীকার করেন না, কেবল ‘শ্রেণিচরিত্র’ আছে বলে মনে করেন, তাঁরা কেউ কি নিজেকে নিজে কখনও প্রশ্ন করে দেখেছেন ঃ যে-কারণে মানবচরিত্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়, সেই কারণেই কি শ্রেণিচরিত্রের অস্তিত্বও অস্বীকার্য নয় ? শ্রমিকদের মধ্যেও তো মালিকের দালাল, সরকারের দালাল, চৌর্যপ্রবণতা ইত্যাদি থাকে। মালিকদের মধ্যেও সার্বিক কল্যাণবোধ ও মানবপ্রেম খুঁজে পাওয়া যায়। শ্রেণিচরিত্র স্বীকার করলে মানবচরিত্রও স্বীকার করতে হয়। আমাদের দেশে যারা শ্রেণিচরিত্র, শ্রেণিচ্যুতি, শ্রেণিসংগ্রাম ইত্যাদি কথা বলে আসছেন, সাধারণভাবে মানুষ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ভুল। ……..
বার্ট্রান্ড রাসেল ১৯৫০ সনে নোবেল পুরস্কার গ্রহণকালে নোবেল ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে What Desires Are Politically Important? শিরোনামে যে বক্তৃতা দেন, তাতে উল্লেখ করেন : “ বিপুল জনসাধারণকে যখন আপনারা কোন মহৎ অনুপ্রেরণার নামে আন্দোলিত হতে দেখেন, তখন আপনাদের কর্তব্য , একটু গভীরে দৃষ্টি দিয়ে নিজেদের অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা : এই অনুপ্রেরণার পেছনে ক্রিয়াশীল প্রকৃত কারণ কি? মহত্ত্বের এতোই আকর্ষণ যে ,তাঁর মুখো দেখলেই মানুষ তার প্রতি ধাবিত হয়।”
রাজনীতি-ক্ষেত্রে মানুষ-যে মহত্ত্বের মুখোশকেও মহত্ত্ব ভেবে তার পেছনে ধাবিত হয়, তাঁর ফলে মানবীয় সমস্যা জটিলতর রূপ নেয়। উক্ত বক্তৃতায় রাসেল মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে ইতিহাসের দিকে তাকিয়েছেন, এবং ক্ষুধা, যৌনতাড়না, ক্ষমতালিপ্সা, খ্যাতিলিপ্সা, প্রতিদ্বন্দ্বিতাস্পৃহা, মালিকানালিপ্সা, উত্তেজনাপ্রীতি, ভয়, ঘৃণা, সমাজবোধ, লোকহিতৈষণা, সহানুভূতি ইত্যাদি মানবীয় বৃত্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে রাজনীতিতে এসবের ভূমিকা চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।
খ্যাতিলিপ্সা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন:
“খ্যাতিলিপ্সা তথা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার আকাঙ্ক্ষা হল একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা। শিশুদের নিয়ে যাঁদের ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁরা জানেন, কেমন করে শিশুরা সব সময় অদ্ভুত কিছু করতে থাকে এবং বলতে থাকে, ‘আমার দিকে তাকাও।‘ নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রবৃত্তি হচ্ছে মানবচিত্তের একটি অত্যন্ত মৌলিক প্রবৃত্তি। ভাঁড়ামো থেকে আরম্ভ করে মরণোত্তর খ্যাতি অর্জনের প্রয়াস পর্যন্ত অসংখ্য রূপে এই প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি ঘটতে পারে। রেনেসাঁস কালের ইতালির এক ক্ষুদ্র নৃপতিকে মৃত্যুশয্যায় যাজক জিজ্ঞেস করেছিলেন, অনুশোচনা করার মতো তাঁর কিছু আছে কী না। নৃপতি বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, একটি বিষয় আছে। একবার এক অনুষ্ঠানে আমি একসঙ্গে সম্রাট এবং পোপ উভয়েরই সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। তখন আমি তাঁদেরকে নিয়ে দৃশ্য দেখার উদ্দেশ্যে আমার সুউচ্চ দুর্গের শীর্ষে উঠেছিলাম ; তাঁদের উভয়কে নীচে ফেলে দেওয়ার সুযোগ তখন আমি হেলায় হারিয়েছিলাম। তখন যদি আমি তাঁদেরকে নিচে ফেলে দিতাম, তাহলে আমি অমর খ্যাতির অধিকারী হতাম।” ইতিহাসে বর্ণিত নেই, যাজক তাঁর পাপমুক্তির অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন কিনা। নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রবৃত্তি নিয়ে একটা অসুবিধা এই যে, যে কোন দিক থেকে প্রশংসার ইন্ধন পেলেই তা আরো বেশি করে জ্বলে উঠতে থাকে ……
ঘৃণ্য হত্যাকারীকে যদি তাঁর বিচারের বিবরণ খবরের কাগজে দেখতে দেওয়া হয়, তাহলে কোনো কাগজে তার বিবরণ কম উঠেছে দেখলে সে রাগান্বিত হয়, আর অন্যান্য কাগজে নিজের সম্পর্কে যতোই সে বেশি উল্লেখ দেখতে পায়, ততই ঐ কম-বিবরণ দানকারী কাগজের প্রতি তার রাগ বাড়তে থাকে। রাজনীতিবিদদের আর কবি-সাহিত্যিক-লেখকদের বেলায়ও এই রকমই ঘটে থাকে। যতই তাঁরা বিখ্যাত হতে থাকেন, প্রেস-কাটিং সংস্থাগুলো তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে ততই বেশি করে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তিন বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে, যার ভ্রুকুটিতে দুনিয়া প্রকম্পিত হয় সেই ক্ষমতাবান পর্যন্ত, সকলের জীবনেই নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের বাসনা তথা খ্যাতিলিপ্সা এত প্রবল যে, তার কোনো প্রকার অতিরঞ্জন সম্ভব নয়। মানবজাতি এমনকি এমন ধর্মবিগর্হিত কাজও করেছে যে, বিধাতাকে পর্যন্ত এই প্রবৃত্তির শিকার বানিয়েছে ; বিধাতাকে মানুষ কল্পনা করেছে সর্ব মুহূর্তে প্রশংসালোলুপ রূপে। ”
জীবন, মৃত্যু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাদের অবস্থান, কি, কেন, কোথা থেকে , আবার কোথায়, জীবনের উদ্দেশ্য কি – এই অনুসন্ধিৎসা সভ্যতার উন্মেষ থেকেই চলে আসছে। আমাদের বাঙালি মনিষীদের চিন্তারাশির একটা সঙ্কলন করে রাখলাম। এই লেখা ভবিষ্যতে আরো সংযোজিত, মার্জিত, পরিবর্ধিত, সংশোধিত করার আশা রাখছি।
পাঠ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
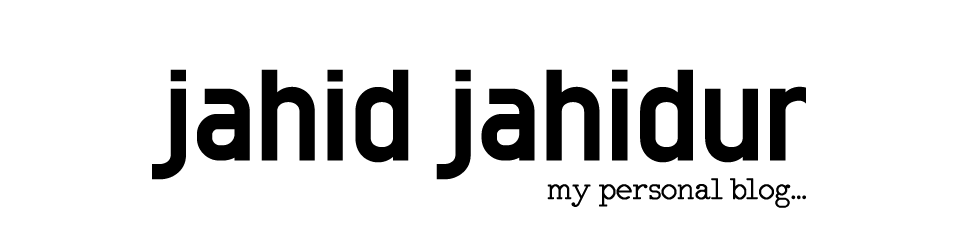
খুবই ডিটেইল লেখা । খুবই সুন্দর ও ইনফরমেটিক ।
ধন্যবাদ রিয়াজ আনোয়ার ভাই। আমার ব্লগে প্রথম কমেন্টটি করার জন্য। পাঠ করার জন্য শুভেচ্ছা রইল
লিখতে না পারলেও পড়তে আমি বরাবরই ভালোবাসি।
আগ্রহ নিয়ে পড়েছি, খুবই চমৎকার এবং তথ্যবহুল বলে মনে হয়েছে আমার কাছে।
জাহিদের সুন্দর ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।
বিপুল আমি ভীষণ অবাক হয়েছি, আমার ধারণা ছিল, তুই ফেসবুকে অনেক নিস্ক্রিয় থাকিস, ব্লগে আবার কী করতে ঢুকবি। যাই হোক, কাকা তোমার কমেন্ট পড়ে ভালো লেগেছে। নিজেকে প্রকাশ করার আনন্দেই লিখে চলি, বকবক করি অনবরত। সঙ্গেই থাকিস। দেখা হবে কোন একদিন
ধন্যবাদ রিয়াজ আনোয়ার ভাই। আমার ব্লগে প্রথম কমেন্টটি করার জন্য। পাঠ করার জন্য শুভেচ্ছা রইল
দোস্ত পড়ছি ভাল লাগছে। পড়া শেষে আবার জানাবো ।
পড়া শেষ হইছে ? হা হা হা !
মাথা ঝিমঝিম করা-বুকের ভিতরটা শূন্য লাগা-এমনই এক লেখা। জীবনের ‘গভীরতম’ খাদে নেমে সেই হাহাকার করা প্রশ্ন ‘জীবনে উদ্দেশ্য কী?’ অথবা প্রশ্ন নয়, প্রতিধ্বনি।
শুভেচ্ছা রইল…
তোর কমেন্টস পড়ে অনেক ভালো লেগেছে, কিন্তু কয়েকদিন ধরে ফেসবুক ও অন্য জায়গার লেখা গুলো সব নিজের ওয়েবে নিয়ে আসা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তাছাড়া অফিসের হুজ্জত তো আছেই।অনেক ধন্যবাদ তোর সেরা কমেন্ট-টির জন্য। কমেন্ট করার জন্য নোবেল দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে তোকে নোবেল দিতাম।
দোস্ত পড়ছি , ভাল লাগছে ,
থ্যাংকস দোস্ত।