බаІГපаІНඃ඙а¶Я аІІ:
а¶Жපගа¶∞ බපа¶ХаІЗ ඥඌа¶Ха¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІВа¶∞аІНа¶ђа¶ђа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЬаІЗа¶≤а¶Ња¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Єа¶єа¶Ьа¶≤а¶≠аІНа¶ѓ а¶∞аІБа¶Я а¶Ыа¶ња¶≤ ඥඌа¶Ха¶Њ-а¶Жа¶∞а¶ња¶Ъа¶Њ-а¶ЧаІЛаІЯа¶Ња¶≤ථаІНබ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња•§ а¶Жа¶ђаІНа¶ђа¶Њ-а¶Жа¶ЃаІНа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ ථඌථඌඐඌаІЬа¶њ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶њ–පаІИපඐаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶Ѓа¶ІаІБа¶∞ а¶ЄаІНа¶ЃаІГටගа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња•§ а¶≤а¶ЮаІНа¶ЪаІЗа¶∞ а¶≠аІЗа¶Б඙аІБ, а¶Ша¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶єаІЛа¶ЯаІЗа¶≤аІЗ а¶Жа¶ђаІНа¶ђа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ђаІЬа¶Ѓа¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ ඙аІЗа¶Яа¶њ බගаІЯаІЗ а¶≠ඌට а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Ња•§ а¶єаІЛа¶ЯаІЗа¶≤аІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ ඐගපඌа¶≤ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІБඁගථගаІЯа¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඕඌа¶≤а¶ЊаІЯ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶Яа¶Ха¶Яа¶ХаІЗ а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞ ටа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶ња•§ а¶Ша¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶єаІЛа¶ЯаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЃаІЗа¶Єа¶њаІЯа¶Ња¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶У а¶ХаІА ඃටаІНථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඐඪටаІЗ බගට, ඙аІНа¶≤аІЗа¶Я а¶Па¶Ча¶њаІЯаІЗ බගට; පගපаІБ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗප а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ ඁථаІЗ а¶єа¶§а•§
а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ පаІЗа¶ЈаІЗ а¶ЧаІЛаІЯа¶Ња¶≤ථаІНබ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗපථаІЗ а¶ХаІБа¶ЈаІНа¶Яа¶њаІЯа¶Њ-а¶Ча¶Ња¶ЃаІА а¶ЯаІНа¶∞аІЗථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Е඙аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶Ња•§ а¶ЯаІНа¶∞аІЗථ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶≤аІЗа¶З а¶ЄаІЗа¶З а¶Жа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤а¶ња¶Х а¶ЯඌථаІЗа¶∞ යඌටග-а¶ШаІЛаІЬа¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Ъа¶њаІОа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶Ба¶Ъа¶Ња¶ЃаІЗа¶Ъа¶ња•§ а¶Па¶Цථ а¶ЪаІАථඌඐඌබඌඁ ටаІЛ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ ඙а¶∞аІЗа¶З а¶Эа¶Ња¶≤а¶ЃаІБаІЬа¶њ, ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗ ඪගබаІНа¶І а¶°а¶ња¶Ѓа•§ вАШа¶Па¶З а¶Ъඌථඌа¶ЪаІНа¶ЪаІБа¶∞вА٠පаІБථаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶ЊаІЯа•§ а¶∞а¶Ња¶ЬаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶єа¶ња¶Ьа¶ња¶ђа¶ња¶Ьа¶њ а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Еа¶ђа¶Ња¶І а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌ а¶Р а¶Єа¶ЃаІЯа¶ЯගටаІЗа•§
බаІГපаІНඃ඙а¶Я аІ®:
ථබаІАа¶∞ а¶Чටග඙ඕаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථаІЗ а¶ЂаІЗа¶∞а¶ња¶Ша¶Ња¶Я а¶Жа¶∞а¶ња¶Ъа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶∞ටаІЗ а¶Єа¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶ЯаІБа¶∞а¶њаІЯඌටаІЗ а¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶Чට ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටගට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶єаІЯථග පаІБа¶ІаІБ බа¶∞ගබаІНа¶∞ а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ ඀ගථ඀ගථаІЗ බඌа¶БаІЬа¶ња¶∞ а¶ХගපаІЛа¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Єа¶Ьගබ а¶ђа¶Њ ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Ъа¶Ња¶Бබඌ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶Яа¶Ња•§ а¶Ша¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶ЃаІЛаІЬаІЗа¶∞ а¶ЬаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІЗ а¶Ча¶ЊаІЬаІА ඕඌඁа¶≤аІЗа¶З , а¶Ъа¶Ња¶Бබඌа¶∞ а¶∞පගබ а¶ђа¶З යඌටаІЗ а¶Па¶Х а¶ђа¶Њ а¶Еа¶Іа¶ња¶Х බа¶∞ගබаІНа¶∞ а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤аІНа¶≤а¶њ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ යඌට а¶ђа¶ЊаІЬа¶њаІЯаІЗ බаІЗаІЯа•§
а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට: а¶Жа¶∞а¶ња¶Ъа¶Њ а¶Ша¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶ЃаІЛаІЬаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђа¶Ыа¶∞ ඐගපаІЗа¶Х а¶Іа¶∞аІЗ а¶ЫаІЛа¶Я а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶За¶Х බගаІЯаІЗ а¶Ѓа¶Єа¶ЬගබаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Бබඌ ටаІБа¶≤ටаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ЖබаІМ а¶Ѓа¶Єа¶Ьගබ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ХаІАථඌ а¶Ьа¶Ња¶®а¶ња¶®а¶Ња•§ а¶єаІЯටаІЛ а¶ђа¶Ња¶БපаІЗа¶∞ а¶Ыඌ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶Єа¶Ьගබ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ , а¶єаІЯටаІЛ а¶єаІЯථග ; а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ьඌථග, а¶Ъа¶Ња¶Бබඌа¶∞ а¶ђаІЬ а¶Еа¶Вපа¶Яа¶Ња¶З а¶ђаІНа¶ѓаІЯගට а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ඙ඌа¶∞аІНඕගඐ а¶ХаІНа¶ЈаІБථаІНථගඐаІГටаІНටගа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа•§
බаІГපаІНඃ඙а¶Я аІ©:
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶Ѓ а¶У а¶ђаІЗаІЬаІЗ а¶Уආඌ ඥඌа¶Ха¶Њ පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Х඙аІНа¶∞ඌථаІНටаІЗ , а¶Ѓа¶ња¶∞඙аІБа¶∞аІЗ а•§ а¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶≠බаІНа¶∞аІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ ථඌථඌа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬаІАа•§ ඀ගථ඀ගථаІЗ බඌа¶БаІЬа¶ња¶∞ а¶ХගපаІЛа¶∞ а¶ђа¶Њ а¶ђаІЬ බඌа¶БаІЬа¶ња¶∞ а¶ѓаІБа¶ђа¶ХබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඌබаІБа¶∞аІНа¶≠а¶Ња¶ђ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶З а¶ђаІЗපаІА а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ථටаІБථ а¶ѓаІЗ а¶єаІБа¶ЬаІБа¶∞а¶Яа¶њ а¶Єа¶ЃаІНඁඌථаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ђаІИආа¶Ха¶ЦඌථඌаІЯ а¶Ж඙аІНа¶ѓа¶ЊаІЯගට а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗථ , а¶ЄаІЗ а¶єаІЯටаІЛ а¶ђа¶Ыа¶∞ බපаІЗа¶Х а¶Жа¶ЧаІЗа¶У а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЫаІЛа¶Яа¶Ѓа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ ඪටаІАа¶∞аІНඕ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Па¶Цථ а¶ЄаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ца¶ња¶∞ඌටаІЗа¶∞ а¶єаІЗа¶Ђа¶Ња¶ЬටаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶Ња¶Ѓа¶∞аІНප බගаІЯаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Р බගа¶ХаІЗ ඥඌа¶Ха¶ЊаІЯ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶Ња¶∞ ඙ඌපаІЗа¶З а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ѓа¶Єа¶Ьගබ а¶У а¶≤а¶Ња¶ЧаІЛаІЯа¶Њ а¶Ха¶Уа¶Ѓа¶њ ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶Ња•§ а¶ђаІЗප а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Ѓа¶єа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶Ња¶ЧаІБа¶≤аІЛ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶∞аІЛа¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ ඙බаІН඲ටගටаІЗ ඪ඙аІНටඌයаІЗа¶∞ а¶Па¶Хබගථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Єа¶ЬගබаІЗа¶∞ а¶За¶Ѓа¶Ња¶Ѓа¶ХаІЗ а¶Ца¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ බඌඐඌа¶∞ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶∞аІЗа¶УаІЯа¶Ња¶Ь а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ථගа¶ЬаІЗа¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶З а¶Ца¶Ња¶З ථඌ а¶ХаІЗථ, а¶За¶Ѓа¶Ња¶Ѓ-а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ආගа¶Ха¶З а¶Жа¶ЃаІНа¶Ѓа¶Њ а¶Жа¶Ба¶Ъа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ба¶Ъа¶њаІЯаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЃаІБа¶∞а¶ЧаІАа¶∞ а¶ЭаІЛа¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ца¶Ња¶УаІЯඌටаІЗа¶®а•§ вАШа¶Іа¶∞аІНඁ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථвАЩ а¶Жа¶∞ вАШа¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа¶≠аІАа¶∞аІБ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථвАЩа•§ а¶Па¶З බаІБа¶З පаІНа¶∞аІЗа¶£аІАа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ђаІЬ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ ට඀ඌаІО а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶Ча¶∞а¶ња¶ЈаІНආ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗථ вАШа¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа¶≠аІАа¶∞аІБ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථвАЩ !
඙ඐගටаІНа¶∞ а¶Жа¶∞а¶ђаІА а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗа¶У а¶Ѓа¶єа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶∞ ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶ЊаІЯ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ! а¶ХගථаІНටаІБ ඁඌඕඌ බаІБа¶≤а¶њаІЯаІЗ බаІБа¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶≤а¶ња¶Ђ а¶Ьа¶ђа¶∞ а¶Ж, а¶ђаІЗ а¶Ьа¶ђа¶∞ а¶ђа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жඁ඙ඌа¶∞а¶Њ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ЖඪටаІЗ а¶ЖඪටаІЗа¶З а¶ђаІЛа¶∞аІНа¶°аІЗа¶∞ а¶ђаІГටаІНටග ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶≤а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙ඐගටаІНа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶Уа¶За¶ЦඌථаІЗа¶З ඪඁඌ඙аІНа¶§а¶ња•§ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶ђа¶ЄаІЗ а¶Жа¶∞а¶ђаІА ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁඌඕඌаІЯ а¶ѓа¶Цථ а¶Яа¶Ѓ а¶ЕаІНඃඌථаІНа¶° а¶ЬаІЗа¶∞аІА, ඕඌථаІНа¶°а¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶Яа¶Є а¶ШаІБа¶∞ටаІЛ ; а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙ඌපаІЗ а¶ђа¶Єа¶Њ ථගඁаІНථඐගටаІНට а¶Е඙аІБа¶ЈаІНа¶Я а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶Ња¶∞ ඁඌඕඌаІЯ а¶єаІЯටаІЛ ටа¶Цථ а¶ШаІБа¶∞ටаІЛ බаІБ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ца¶Ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЪගථаІНටඌ ,ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶Ња¶∞ а¶∞ඌථаІНථඌа¶Ша¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≠аІЗа¶ЄаІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶Ча¶∞а¶Ѓа¶Ѓа¶Єа¶≤а¶Њ ටа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶ња¶∞ а¶ЧථаІНа¶Іа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Еථටගа¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х-а¶Жа¶∞аІНඕගа¶Х-ඁඌථඪගа¶Х බаІВа¶∞ටаІНа¶ђаІЗ а¶ђаІЗаІЬаІЗ а¶Уආඌ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а•§
а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъ-а¶Ѓа¶ІаІНඃඐගටаІНට а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶Па¶Х ඐථаІНа¶ІаІБа¶∞ බаІБа¶За¶≠а¶Ња¶З-බаІБа¶За¶ђаІЛථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ЫаІЛа¶Яа¶≠а¶Ња¶За¶Яа¶ња¶ХаІЗ ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶ЊаІЯ බаІЗаІЯа¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඃඕඌа¶∞аІАටග а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶ЊаІЯаІА ඐඌ඙-බඌබඌа¶∞ а¶Жа¶Ца¶ња¶∞ඌටаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶∞а¶Ња¶єа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЖපඌаІЯа•§ а¶Ша¶∞аІЛаІЯа¶Њ ථඌථඌ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗ а¶ЫаІЛа¶Яа¶≠а¶Ња¶За¶Яа¶њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ђ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ ටඌа¶≤ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Ъа¶≤а¶≤аІЗа¶У а¶Уа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З ඪඌබඌ а¶ЬаІЛа¶ђаІНа¶ђа¶Њ а¶Жа¶∞ බඌа¶БаІЬа¶њ ථගаІЯаІЗ а¶ХаІЛඕඌаІЯ а¶ѓаІЗථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ බаІВа¶∞ටаІНа¶ђ ඕඌа¶Хට ! බගථаІЗ බගථаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ђаІЗаІЬаІЗа¶З а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶ЃаІЗථග !
а¶ЃаІВа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жа¶Єа¶ња•§
ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶Ња¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථ ඐගබаІНа¶ђаІЗа¶Ј а¶Ыа¶ња¶≤ථඌ а¶ђа¶Њ ථаІЗа¶За•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІИаІЯබ а¶УаІЯа¶Ња¶≤аІАа¶Йа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶єаІНвАМа¶∞ вАШа¶≤а¶Ња¶≤а¶Єа¶Ња¶≤аІБвАЩ а¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶ХаІЗථ а¶Ьඌථග ඁථаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Жа¶ІаІНඃඌටаІНа¶Ѓа¶ња¶Хටඌ а¶ђа¶Њ а¶ЄаІН඙ගа¶∞а¶ња¶ЪаІБаІЯа¶Ња¶≤а¶ња¶Яа¶ња¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶Па¶∞ а¶≠а¶ња¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶ђаІГටаІНටගа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Ња¶Яа¶Њ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ђаІЗපаІА පа¶ХаІНටගපඌа¶≤аІА а•§ а¶Ча¶∞аІАа¶ђ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶њ ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶ЊаІЯ ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч ඙аІЗа¶≤аІЗ а¶ЕථаІНටට ටඌа¶Ба¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶ЪගථаІНටඌ ඕඌа¶ХаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Пඁථа¶Ха¶њ а¶Ѓа¶ІаІНඃඐගටаІНටаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶њ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ ඙аІЬඌපаІЛථඌаІЯ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ බаІБа¶∞аІНа¶ђа¶≤ ටඌа¶ХаІЗа¶У а¶Жа¶∞ а¶Жа¶Ца¶ња¶∞ඌටаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶≠аІЗ ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶ЊаІЯ බගаІЯаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶∞аІЗа¶УаІЯа¶Ња¶Ь а¶Ыа¶ња¶≤а•§
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඁථаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶З ඀ගථ඀ගථаІЗ බඌа¶БаІЬа¶ња¶∞ а¶єаІБа¶ЬаІБа¶∞බаІЗа¶∞а¶ХаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Ха¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ца¶Ња¶ЗаІЯаІЗ බඌа¶ЗаІЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≠а¶ња¶ХаІНа¶ЈаІБа¶ХපаІНа¶∞аІЗа¶£а¶ња¶З ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ХаІЛථа¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Ха¶ЊаІЯа¶ња¶Х ඙а¶∞ගපаІНа¶∞а¶Ѓ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ පаІБа¶ІаІБ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶ЕථаІБපඌඪථ- а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ъа¶∞аІНа¶Ъа¶Њ а¶ђа¶Ьа¶ЊаІЯ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ , а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ПටаІЛ а¶ђаІЬ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓ а¶Еа¶Вපа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Еа¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶£аІНа¶ѓ ඙а¶ЩаІНа¶ЧаІБ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Па¶З а¶≠а¶ња¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶ђаІГටаІНටග а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶≤а¶Ња¶ЧаІЗථග а¶Ха¶ЦථаІЛа¶За•§
а¶Па¶З а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓ а¶ѓаІМඐථаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶Ьа¶ЩаІНа¶ЧගඐඌබаІЗа¶∞ а¶ЙටаІНඕඌථ а¶ђа¶Њ а¶єаІЗа¶Ђа¶Ња¶ЬටаІЗа¶∞ а¶ЙටаІНඕඌථаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ѓа¶∞аІНඁඌයට а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶≠ගටа¶∞аІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ ඐගටаІГа¶ЈаІНа¶£а¶Њ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ බаІНа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ ථаІЗа¶З а•§ а¶ђа¶єаІБа¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶ХаІЛа¶∞ඐඌථගа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶ЃаІЬа¶Ња¶∞ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶Ѓа¶єа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶∞ ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶ЊаІЯ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єа¶§а•§а¶Чට а¶ђа¶Ыа¶∞ ඙ඌа¶Ба¶ЪаІЗа¶Х а¶Жа¶ЧаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶ђаІНа¶ђа¶Њ-а¶Жа¶ЃаІНа¶Ѓа¶Њ а¶ђаІЗа¶Ба¶ЪаІЗ ඕඌа¶ХටаІЗа¶З ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЕථаІБඁටගа¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Па¶Цථ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯ බа¶∞ගබаІНа¶∞ а¶ЖටаІНа¶ЃаІАаІЯබаІЗа¶∞а•§
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶єа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІАа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ђа¶єаІБබගථ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Хඕඌ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶ЕථаІБаІО඙ඌබථපаІАа¶≤ а¶Ха¶Уа¶Ѓа¶њ ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶Њ-පගа¶ХаІНඣගටබаІЗа¶∞ а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА ථගаІЯаІЗа•§ а¶Єа¶єа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІА ටඌа¶Ба¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х ඙ගටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Хඕඌ а¶Йආа¶≤аІЗ а¶Ъа¶ЃаІОа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, ඁථаІЗ а¶ЧаІЗа¶БඕаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶єа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІАа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ බаІАа¶∞аІНа¶ШබගථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ђа¶Га¶ЄаІНа¶ђа¶≤аІЗа¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Хටඌ а¶У ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶Њ-පගа¶ХаІНඣගට а¶ЃаІМа¶≤а¶≠ගබаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞පаІАа¶≤ටඌ а¶Ха¶Ѓа¶њаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ බඌа¶∞аІБа¶£ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඪඁඌ඲ඌථ а¶ђа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶≤аІЗа¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ьඌථග ටඌа¶Ба¶∞ а¶Па¶З ඁටаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗ බаІНඐගඁට ඙аІЛа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶П а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶Й඙ඌаІЯ ථаІЗа¶За•§ а¶ђа¶єаІБа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶У а¶Ха¶Уа¶Ѓа¶њ ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶ЊаІЯ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶ња¶ХаІБа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ХаІЛථ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶ђаІНа¶≤ගප а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ ථඌа¶За•§ а¶Ъа¶Ња¶∞ගබගа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶Жа¶ђа¶єа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶ђаІЗаІЬаІЗ а¶Йආа¶ЫаІЗ а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНඃටаІЗа¶У а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඌඐථඌ බаІЗа¶Ца¶Ыа¶ња¶®а¶Ња•§
а¶Єа¶єа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІАа¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶∞а¶ња¶≠а¶Ња¶∞аІНа¶Є а¶ЪගථаІНටඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ а•§
а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶Па¶З ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶Ња¶∞ а¶єаІБа¶ЬаІБа¶∞ а¶У а¶ЗඁඌඁබаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ-а¶ЬаІАඐථ а¶Хටа¶Цඌථග ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞පаІАа¶≤, а¶ХаІЛඕඌаІЯ а¶ХаІЛඕඌаІЯ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ъа¶≤аІЗа¶З ථඌ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ටගථග а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Ъа¶ња¶єаІНථගට а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§
а¶ЃаІГටඐаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶∞ බඌ඀ථ а¶У а¶Ьඌථඌа¶Ьа¶Ња•§
а¶Ж඙ථග а¶Ха¶Ѓ а¶ђа¶Њ а¶ђаІЗපаІА а¶Іа¶Ња¶∞аІНа¶Ѓа¶ња¶Х а¶ѓа¶Ња¶З а¶єаІЛථ ථඌ а¶ХаІЗථ , а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБ а¶Ж඙ථඌа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶ІаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶єаІЗа¶Ђа¶Ња¶Ьටа¶Ха¶Ња¶∞аІАබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ а¶°аІЗа¶ХаІЗ а¶ЖථටаІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Ж඙ථග а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶ХаІЛථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶ња¶Х а¶ЬаІНа¶Юඌථ ථаІЗа¶З බඌ඀ථ-а¶Хඌ඀ථаІЗа¶∞а•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶∞ а¶Па¶З ඐගඣඌබඁаІЯ а¶ЙаІОа¶Єа¶ђаІЗ а¶Па¶БබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶Ха¶≤аІН඙ ථаІЗа¶За•§ ඙аІБа¶∞аІЛ ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶ЯගටаІЗ, а¶ЧаІЛа¶Єа¶≤ а¶Ха¶∞ඌථаІЛ, а¶Хඌ඀ථ ඙аІЬඌථаІЛ, а¶Ха¶ђа¶∞аІЗ ථඌඁඌථаІЛ, а¶ХаІБа¶≤а¶Цඌථගа¶∞ බගථаІЗа¶∞ බඌа¶УаІЯа¶Ња¶§а•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ а¶ХаІЛа¶∞а¶Жථ а¶Цටඁ, а¶Ђа¶Ха¶ња¶∞-а¶Ѓа¶ња¶Єа¶Хගථ а¶ЖටаІНа¶ЃаІАаІЯබаІЗа¶∞ а¶Ца¶Ња¶УаІЯඌථаІЛ, බаІЛаІЯа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶Њ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗа¶З а¶Па¶БබаІЗа¶∞ а¶Єа¶∞а¶ђ а¶Й඙ඪаІНඕගටග, а¶ЕඐපаІНа¶ѓа¶З а¶Еа¶∞аІНඕаІЗа¶∞ ඐගථගඁаІЯаІЗа•§ а¶Ж඙ථඌа¶ХаІЗ ථට යටаІЗ а¶єаІЯ, а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶Ъа¶ња¶∞඙аІНа¶∞а¶ЄаІНඕඌථа¶Ха¶Ња¶∞аІА ඙ගටඌ ඁඌටඌа¶∞ а¶Жа¶Ца¶ња¶∞ඌටаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶∞а¶Ња¶єа¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єаІЯа•§
а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ж඙ථග ඃබග а¶Па¶З ඙аІНа¶∞а¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶Яа¶њ ථඌඁඌа¶Ь පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ ඁටаІЛ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶З පගа¶ЦаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗථ?
а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Єа¶єа¶Ь යට ථඌ ? а¶Ж඙ථග ටඌඪඐаІАа¶є а¶∞аІБа¶ХаІБ ඙аІЬаІЗ ඙ඌа¶Ба¶Ъ а¶УаІЯа¶Ња¶ХаІНට ථඌඁඌа¶Ь ඙аІЬටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ЫаІЗථ а¶Жа¶∞ а¶Па¶За¶Яа¶Њ පගа¶ЦටаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ха¶њ? а¶Па¶Яа¶Њ ටаІЛ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඁඌථඐа¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶У а¶Е඙а¶∞а¶ња¶єа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඪඁඌ඙аІНа¶§а¶ња•§
а¶Жа¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶ХаІЛа¶∞ඐඌථග බаІЗа¶УаІЯа¶Њ, ථඌඁඌа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Зඁඌඁටග а¶Ха¶∞а¶Њ , а¶Ѓа¶ња¶≤ඌබ ඙аІЬඌථаІЛ, а¶ЃаІГටඐаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶∞ а¶ЖටаІНа¶Ѓа¶Ња¶∞ පඌථаІНටගටаІЗ а¶ЃаІЛථඌа¶Ьඌට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§
а¶Па¶Цථ , а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ а¶ђа¶Ња¶ІаІНඃටඌඁаІВа¶≤а¶Х а¶За¶Єа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ බපඁ පаІНа¶∞аІЗа¶£аІА ඙а¶∞аІНඃථаІНа¶§а•§
а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ, аІІаІ¶аІ¶ ථඌඁаІНа¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙аІБа¶∞аІЛа¶Яа¶Ња¶З а¶≤а¶ња¶Цගට ථඌ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа•§ аІЂаІ¶ ථඁаІНа¶ђа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶ња¶Х а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶єаІЛа¶Ха•§
а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЃаІГටඐаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶ХаІЗ а¶ЧаІЛа¶Єа¶≤ а¶Ха¶∞ඌටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ, а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ьඌථඌа¶Ьа¶Ња¶∞ ථඌඁඌа¶Ь ඙аІЬඌටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ, а¶ХаІЛа¶∞ඐඌථග а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ, ථඌඁඌа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Зඁඌඁටග а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶ња¶Х ඙аІНа¶∞පගа¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶ња¶Х ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌ ඕඌа¶ХаІБа¶Ха•§
а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Іа¶∞аІНඁ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ѓа¶Цථ а¶Па¶З а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞а¶ња¶Х а¶ЕථаІБපඌඪථ а¶У а¶Жа¶Ъа¶Ња¶∞а¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛඁටаІЛ ඙аІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Яа¶ња¶Є а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ, ටа¶Цථ а¶Па¶З а¶ЕථаІБаІО඙ඌබථපаІАа¶≤ ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶Њ පගа¶ХаІНඣගටබаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ටඌ а¶Ха¶ЃаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа•§ а¶≠а¶ња¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶ђаІГටаІНටග ටаІНа¶ѓа¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ЃаІБа¶ЦаІА පගа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ පගа¶ХаІНඣගට а¶єаІЛа¶Х а¶Па¶З а¶Ьа¶Ња¶§а¶ња•§
а¶ХаІЗථථඌ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඕ !
[ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපа¶Ха¶Ња¶≤а¶Г ಩ಲපаІЗ а¶Жа¶Ча¶ЄаІНа¶Я,аІ®аІ¶аІІаІђ ]
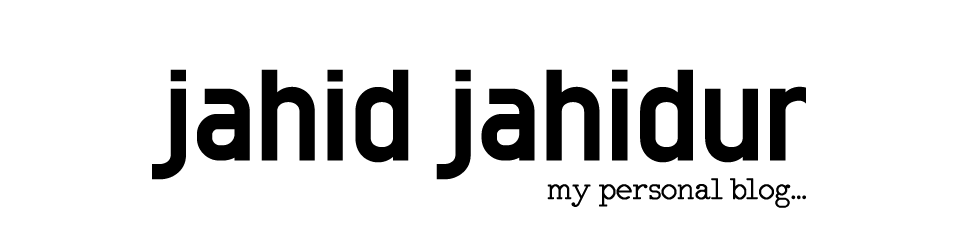
а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞ටගа¶Х ඁථаІНටඐаІНа¶ѓ