আমার পড়াশোনা শুরু থেকেই বিজ্ঞানবিভাগে। ম্যানেজমেন্টের উপর নামকা ওয়াস্তে একটা অখ্যাত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের খুবই ‘হালকার উপর ঝাপসা’মানের একটা MBA ডিগ্রী আছে। তাও সেটার সার্টিফিকেট গত একযুগ ধরে পড়ে আছে সেই ইউনিভার্সিটির কোন এক জং ধরা ক্যাবিনেটে ; আমার সুবিখ্যাত আলস্যের কারণে ওটা আর তুলতেও যাই নি
তো ‘Trial and Error’ , সেই বিখ্যাত মৌলিক পদ্ধতিতে আমার ম্যানেজমেন্ট শেখার হাতেখড়ি । প্রতিমুহূর্তেই শেখার আবশ্যকতা আছে এবং জীবন্ত মানুষদের সঙ্গে কাজ করতে গেলে যা হয়–একজনের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, আরেকজনের ক্ষেত্রে সেটা ভীষণভাবে ব্যর্থ ! সবকিছু বিবেচনা করে এখন পর্যন্ত ‘Situational Leadership’ বা ‘Situational Management’ সবগুলোর একটা সম্মিলিত রূপ মনে হয়েছে।
আরেকটা ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি খুব কার্যকর, বহুল প্রচলিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় আমাদের দেশে । ম্যানেজমেন্টের ভাষায় এটাকে Autocratic Management বলা হলেও বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমি এটার নাম দিয়েছি Spider Management বা ‘মাকড়শা ম্যানেজমেন্ট’।
ধরুন , একজন মেধাবী লোক একটা কোম্পানির মালিক অথবা একজন সিইও বা ম্যানেজার। তার দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করার কিছু নেই। এই ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকেই আছেন এবং ছোট্ট প্রতিষ্ঠানে বাকী লোকেরা তার চেয়ে কম মেধাবী। এবং যে কোন পরিপ্রেক্ষিতে অন্যকেউ যেই সিদ্ধান্তই দিক না কেন, ঐ মেধাবী মালিকের বা ম্যানেজারের সিদ্ধান্ত পরীক্ষিতভাবে সবচেয়ে কার্যকর !
তো, হয় কী , ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানের সবধরনের সিদ্ধান্তের একচ্ছত্র অধিকারী হয়ে বসেন তিনি ! এক পর্যায়ে দেখা যায় রিসিপশনের চেয়ার টেবিলের রং , কার্পেট , কাপ-পিরিচ থেকে টয়লেটের কমোড কেনার সিদ্ধান্তও তাকে দিতে হয়। সকলেই ব্যাপারটাকে মেনে নেয়। সবাই তার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। কোম্পানির সর্বোচ্চ মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিটিকে এককভাবে সাধুবাদ দেওয়া হয়। আর ঐ ব্যক্তি নিজেকে ধীরে ধীরে কোম্পানির অন্যান্য আসবাবপত্রের মতো নিজেকে অপরিহার্য করে ফেলে।
ব্যাপারটা মাকড়শার মতো অনেকটা। একটা মাকড়শা তার জালের ঠিক কেন্দ্রে থেকে মুখ দিয়ে , পেট দিয়ে , হাত দিয়ে পা দিয়ে চারপাশ আঁকড়ে থাকে। অনেক সময় সেই স্কুলপাঠ্যের লোভী স্বার্থপর মাকড়শার মতো হয়, চারদিকের টানে নিজেকে একসময় ছিঁড়েখুঁড়ে ধ্বংস করে ফেলে সে। কর্মজীবনে এই মাকড়শা মালিক বা ম্যানেজারদের মুখোমুখি হতেই হবে আপনাকে। আমাদের চারপাশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ম্যানেজাররাই এই পদ্ধতিতে চলতে চান। কেন চান , সে গল্প আরেকদিন হবে।
দীর্ঘমেয়াদি মুশকিল হয় অন্যখানে। একজন মানুষ যতো দক্ষ বা সিদ্ধান্তগ্রহণে পারঙ্গম হন না কেন; সিদ্ধান্তগ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার গুণগত মান কমতে থাকে। একজন দক্ষ ডাক্তার দিনে একটা অপারেশন করলে যে গুণগত মান পাওয়া যাবে ; ১০টা করলে সেক্ষেত্রে ছোটখাটো বা বড় ধরণের ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ! যে মালিক বা ম্যানেজার সপ্তাহে ১০টি বড় ধরণের সিদ্ধান্ত দিচ্ছে, ধরে নিচ্ছি তার এফিসিয়েন্সির মান শতকরা ৯৫ ভাগ। কিন্তু সেই একই ব্যক্তি যখন ১০০ টা সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন বা দিতে বাধ্য হচ্ছেন, তার এফিসিয়েন্সি কমে যাচ্ছে । ধরুন, তা নেমে হয়ে গেল ৯০ ভাগে। এখন ২০০টি সিদ্ধান্ত হলে, ২০টি দুর্বল সিদ্ধান্ত বা ভুল সিদ্ধান্ত অনেকাংশে প্রতিষ্ঠানের জন্য বা কর্মচারীদের জন্য নিদারুণ ক্ষতিকর হতে পারে।
কিন্তু এই দুষ্টচক্র থেকে ঐ ব্যক্তি বের হয়ে আসতে পারেন না কোনভাবেই। নিজের জালে নিজে এমনভাবে আটকে যান যে– না পারেন ছিঁড়তে, না পারেন বের হতে, না পারেন কাউকে বলতে। নিজের পরিবারপরিজন থেকে ধীরে ধীরে সরে যান ; পরিবারও তাকে ছাড়া দিব্যি চলতে শিখে যায়।
আমার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে, ‘মাকড়শা ম্যানেজমেন্ট’ ছোট প্রতিষ্ঠানের উত্থানের জন্য দারুণ কার্যকর একটা পদ্ধতি। কিন্তু একই প্রতিষ্ঠান যখন ২০ জন থেকে ২০০ বা ২০০০ জনের হয়ে যায় ; তখন তা থেকে বের হয়ে না আসতে পারলে, সেটা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, দুইজনের জন্য চরম অমঙ্গলকর !
[ প্রকাশকালঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর , ২০১৬ ]
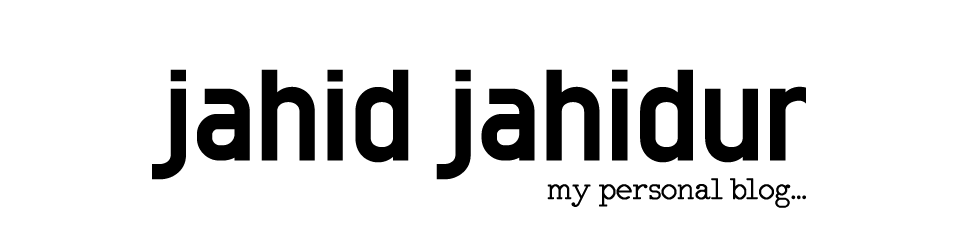
সাম্প্রতিক মন্তব্য