а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶У а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Є а¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶°аІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБබගථ а¶Ха¶Ња¶Яа¶њаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶Ыа¶њ а¶ђа¶≤аІЗ , ථඐаІАථ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗ а¶ЂаІЛථаІЗ а¶ђа¶Њ а¶Єа¶∞а¶Ња¶Єа¶∞а¶њ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶∞ ථගаІЯаІЗ а¶Єа¶Ња¶ЬаІЗපථ а¶Ъа¶ЊаІЯа•§ а¶ХаІЛඕඌаІЯ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶єаІЯ а¶≠а¶Ња¶ЗаІЯа¶Њ ; а¶Уа¶З а¶ЦඌථаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ч බගටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶њ , а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ЬаІЗපථ а¶Ха¶њ а¶ЗටаІНඃඌබග а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛа¶ХаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ђа¶≤а¶њ– а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ а¶Єа¶Ђа¶≤ ඪගථගаІЯа¶∞ аІ™ а¶Ьථ а¶≠а¶Ња¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶∞ ථගаІЯаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗ ඙ඌа¶Ба¶Ъ а¶∞а¶Ха¶ЃаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ЬаІЗපථ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ! а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶У ටаІЗඁථа¶Яа¶Ња¶З ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶њ, ටаІЛඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶У ඙ඌඐаІЗ а•§ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶ЬаІАඐථ ටаІЛඁඌබаІЗа¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞, а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌа¶З පаІЛථ, а¶ХගථаІНටаІБ ඪගබаІН඲ඌථаІНටа¶Яа¶Њ ථගа¶ЬаІЗа¶З ථඌа¶Уа•§
а¶ХаІЗ ථඌ а¶ЬඌථаІЗ , а¶Па¶Ха¶З а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶∞аІНඕ ඁථаІЛа¶∞ඕ а¶єаІЯаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ХаІЗа¶Й а¶ХаІЗа¶Й а¶ЄаІЗа¶З а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЪаІМබаІНබ-а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶ЙබаІНа¶Іа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Уа¶З а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶Ъа¶ња¶Ха¶њаІОа¶Єа¶ЊаІЯ а¶ХаІЗа¶Й а¶≠а¶Ња¶≤ а¶єаІЯаІЗ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ බаІЗඐටඌටаІВа¶≤аІНа¶ѓ а¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶Ха¶∞аІЗ ඙а¶ЮаІНа¶Ъа¶ЃаІБа¶Ц а¶єаІЯа•§ а¶ѓа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Хඕඌ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌ බගаІЯаІЗ ටගථග а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗ ඕඌа¶ХаІЗа¶®а•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа¶Ха¶Ња¶≤, ඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНඣගට ටаІЛ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа¶Ха¶Ња¶≤ а¶У ඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНඣගට ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Жа¶≤а¶Ња¶¶а¶Ња•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌа¶∞ а¶ЄаІЗа¶За¶ЯаІБа¶ХаІБа¶З ථඌа¶У, а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶ЬථаІАаІЯ ඁථаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§
а¶Еටа¶Па¶ђ ථаІАа¶ЪаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶ња¶У а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ථගටඌථаІНටа¶З а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞ඌථаІНටගа¶∞ а¶ЄаІНа¶ЃаІГටගа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඪටаІАа¶∞аІНඕ , а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶Ь а¶ЕථаІБа¶ЬаІЗа¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗ а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶∞ට а¶Жа¶ЫаІЗථ; ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ඙а¶∞ගපаІНа¶∞ඌථаІНට а¶ЙබаІНа¶ѓа¶ЃаІА а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ьа¶Ња¶®а¶ња•§ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Па¶ХаІЗа¶Ха¶Ьථ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤, а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Є а¶ЗථаІНа¶°а¶Ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶∞ а¶Па¶ХаІЗа¶Х а¶ЄаІН඙аІЗපඌа¶≤а¶Ња¶За¶Ьа¶° а¶ЄаІЗа¶ХаІНа¶Яа¶∞аІЗ а¶Пඁථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ බаІЗපаІЗа¶∞ ථඌඁ а¶Йа¶ЬаІНа¶ЬаІНа¶ђа¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗථ ; а¶ѓаІЗ а¶Па¶БබаІЗа¶∞ ඪඌඁථඌඪඌඁථග а¶єа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ථගа¶ЬаІЗа¶З а¶ЦаІБа¶ђ ථаІБа¶ЗаІЯаІЗ ඙аІЬа¶ња•§ а¶ЖඁගටаІЛ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶За¶ЮаІНа¶ЬගථගаІЯа¶Ња¶∞а¶ња¶В а¶ђа¶Њ а¶ЯаІЗа¶Хථගа¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶°а¶ња¶ЧаІНа¶∞аІАа¶∞ ටаІЗඁථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З යඌටаІЗ а¶Ха¶≤а¶ЃаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ња¶®а¶ња•§ ථටаІБථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Жа¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞а¶У а¶Ха¶∞а¶ња¶®а¶ња•§ а¶Ха¶ња¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ха¶ња¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶Ыа¶њ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІЗථаІНа¶°а¶Ња¶За¶Ьа¶ња¶В, а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ХаІЗа¶Яа¶ња¶В а¶Жа¶∞ а¶ЕаІНඃඌධඁගථගඪаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Яа¶ња¶≠ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථаІЗа•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶Єа¶Ња¶∞ඌබගථ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЧаІБа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ѓа¶Ња¶∞аІНපගаІЯа¶Ња¶≤ а¶Жа¶∞ а¶єа¶ња¶Ьа¶ња¶ђа¶ња¶Ьа¶њ а¶Ха¶Ња¶Ь ථගаІЯаІЗ ඕඌа¶ХටаІЗ а¶єаІЯа•§ а¶ЯаІЗа¶Хථගа¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ ධගඪගපථ а¶ЃаІЗа¶Ха¶ња¶Ва¶Па¶∞ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ ටаІЗඁථ а¶Ыа¶ња¶ЯаІЗа¶ЂаІЛа¶Ба¶Яа¶Ња¶У ථаІЗа¶За•§
а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓа¶Цථ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ба¶Ха¶Ња¶ђа¶Ња¶Ба¶Ха¶Њ ඙ඕ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶За¶ЮаІНа¶ЬගථගаІЯа¶Ња¶∞а¶ња¶В а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗ а¶≠а¶∞аІНටග а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶њ, ටа¶Цථ ටаІЗа¶Ьа¶Ча¶Ња¶Ба¶У а¶Па¶∞ а¶ђаІЗа¶ЧаІБථඐඌаІЬа¶ња¶∞ а¶ђаІГа¶ХаІНඣපаІЛа¶≠ගට а¶Цඌථගа¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІНа¶ѓ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ඌඪ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ђаІЗප а¶Жපඌයට а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටа¶ЦථаІЛ а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට а¶≤аІЗа¶Ца¶Х а¶°а¶Г а¶єаІБа¶Ѓа¶ЊаІЯаІВථ а¶Жа¶єа¶ЃаІЗබ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Єа¶ЊаІЯථ а¶ђа¶ња¶≠а¶Ња¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЫඌටаІНа¶∞, ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ ඙බаІЛථаІНථටග а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ђа¶≤ගට а¶∞а¶Єа¶ЊаІЯථаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶њ ථඌ а¶ѓа¶Ња¶З а¶ХаІЗа¶Ѓа¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶∞ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ЄаІЗ , ථඌ а¶ѓа¶Ња¶З ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ђа¶≤ගට а¶∞а¶Єа¶ЊаІЯථаІЗ а¶≠а¶∞аІНටග යටаІЗа•§ а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞ඌථаІНට а¶У а¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶ђа¶Ња¶ЪаІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Њ а¶ЦаІЗаІЯаІЗ а¶Пබගа¶Х а¶ЄаІЗබගа¶Х а¶ШаІЛа¶∞а¶Ња¶ЂаІЗа¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞а¶ња•§ ටаІЛ , ථඌථඌ ඙ඌа¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞а¶ња¶Х а¶Ъඌ඙аІЗ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤аІЗ а¶≠а¶∞аІНටග а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶Ѓа¶ња¶∞඙аІБа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶ЄаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ђа¶Ња¶∞аІНа¶Ѓа¶ЧаІЗа¶ЯаІЗ а¶®а¶Ња¶Ѓа¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶∞а¶ња¶Хපඌа¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶Ња¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶За¶ЮаІНа¶ЬගථගаІЯа¶Ња¶∞а¶ња¶В а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь а¶ЪаІЗථаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶єаІЯ ටඌа¶БබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶єаІЯ ඙а¶≤а¶ња¶ЯаІЗа¶Хථගа¶Х а¶ѓа¶Ња¶ђ а¶Еඕඐඌ а¶ђа¶ња¶Ьа¶њ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ЄаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђа•§ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗ а¶єа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶З а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Ха•§ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤аІЗ а¶≠а¶∞аІНටග а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ථගа¶ЬаІЗа¶З а¶Ха¶њ а¶Ъගථටඌඁ а¶ѓаІЗ а¶Хඌ඙аІЬа¶ЪаІЛ඙аІЬаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗа¶У а¶За¶ЮаІНа¶ЬගථගаІЯа¶Ња¶∞а¶ња¶В යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ! а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤-а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗа¶∞ ඐථаІНа¶ІаІБа¶∞а¶Њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ЦаІНඃඌටථඌඁඌ а¶Єа¶ђ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථаІЗ , а¶ХаІЗа¶Й ඥඌа¶Ха¶Њ а¶ЃаІЗа¶°а¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь, а¶ХаІЗа¶Й а¶ђаІБаІЯаІЗа¶ЯаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටа¶Цථ а¶ђаІБаІЯаІЗа¶ЯаІЗ බаІНඐගටаІАаІЯа¶ђа¶Ња¶∞ а¶≠а¶∞аІНටග ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶єаІЗа¶≤аІЗ බаІБа¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞ග඙ඌа¶∞аІЗපථ ථගа¶ЪаІНа¶Ыа¶њ ; а¶ЄаІЗа¶У а¶Жа¶∞аІЗа¶Х а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞ඌථаІНටග ! а¶Жа¶∞ ඙аІНа¶∞ග඙ඌа¶∞аІЗපථаІЗа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶ХаІЗ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶ХаІЗ, ඁථ а¶Ъа¶Ња¶За¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶ђаІЗа¶≤а¶Њ ඥඌа¶Ха¶Њ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Ьථ а¶єа¶≤аІЗа¶∞ а¶ХаІНඃඌථаІНа¶ЯගථаІЗ аІІаІ® а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ъа¶ња¶ХаІЗථ а¶ђа¶ња¶∞а¶њаІЯඌථග а¶Ца¶Ња¶З, ටаІЛ а¶Жа¶∞аІЗа¶Х а¶ђаІЗа¶≤а¶Њ а¶ђаІБаІЯаІЗа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶єа¶≤аІЗ ඪගථගаІЯа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Ѓа¶°аІЗа¶≤ а¶ЯаІЗа¶ЄаІНа¶Я බගа¶За•§а¶™а¶∞аІЗа¶∞ ටගථබගථ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶єа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Па¶Х ඐථаІНа¶ІаІБа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬаІАටаІЗ ටඌඪ ඙ගа¶Яа¶Ња¶За•§
а¶ѓа¶Ња¶З а¶єаІЛа¶Х а¶≠а¶∞аІНටග а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІН඙ඌඪаІЗ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶Є පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶≤а•§ ඁථඁа¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ѓа¶ња¶∞඙аІБа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶∞аІЛа¶Ь а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ЄаІЗ а¶ѓа¶Ња¶З а¶Жа¶∞ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Жа¶Єа¶ња•§ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ ඪටаІАа¶∞аІНඕ а¶єаІБа¶Ѓа¶ЊаІЯаІБථ а¶Ха¶ђа¶ња¶∞ а¶Уа¶∞а¶ЂаІЗ а¶≤а¶Ња¶ђаІБ а¶ЙආаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶≤аІЗа¶ЧаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶Ђа¶Ња¶∞аІНа¶Ѓа¶ЧаІЗа¶Я а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Ња¶∞( а¶ЃаІВа¶≤ට: а¶єа¶≤а¶ња¶ХаІНа¶∞а¶Є а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЃаІЛаІЬаІЗа¶∞) а¶∞а¶ња¶Хපඌа¶УаІЯа¶Ња¶≤ඌබаІЗа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶За¶ЮаІНа¶ЬගථගаІЯа¶Ња¶∞а¶ња¶В а¶Ха¶≤аІЗа¶Ь а¶ЪаІЗථඌථаІЛа¶∞ а¶Е඙а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶ЊаІЯа•§ ටඌа¶З а¶Ха¶њ а¶єаІЯ, а¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶Х-а¶ЄаІНа¶ЯаІНඃඌථаІНа¶° ඙ඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗа¶З , а¶∞а¶ња¶Хපඌа¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞а¶Њ а¶Ша¶ЊаІЬ а¶ШаІБа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞ට, вАШа¶Ѓа¶Ња¶Ѓа¶Њ а¶Па¶За¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶З ථඌඁඐаІЗථ ඙а¶≤а¶ња¶ЯаІЗа¶Хථගа¶ХаІЗ ?вАЩ
඙а¶∞аІЗ а¶Ха¶њ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ පයаІАබ а¶Жа¶Ьа¶ња¶Ь а¶єа¶≤аІЗ аІІаІІаІ® ථඌඁаІНа¶ђа¶Ња¶∞ а¶∞аІБа¶ЃаІЗ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Ьථ а¶ђаІБа¶ЬаІБа¶∞аІНа¶Ч а¶єаІБа¶ЬаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЙආаІЗ ඙аІЬа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§
а¶∞ඌටаІЗ а¶ШаІБඁඌථаІЛа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ඐඌබ බගаІЯаІЗ а¶ђа¶Ња¶ХаІА-а¶Єа¶ЃаІЯ ඥඌа¶Ха¶Њ а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІБа¶∞ථаІЛ ඪටаІАа¶∞аІНඕබаІЗа¶∞ а¶∞аІБа¶ЃаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶°аІНа¶°а¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶њ а•§ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ЃаІЯ ඙а¶≤а¶ња¶ЯаІЗа¶Хථගа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶∞а¶Ња¶ЬථаІАටගа¶∞ බаІБа¶∞аІНа¶ђа¶ња¶Ја¶є а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Ъа¶≤а¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶Ња¶∞ඌබගථ а¶ХаІЛථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඙ඌа¶∞ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶∞ඌටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓаІЗට а¶єаІБа¶ЯаІЛ඙аІБа¶Яа¶ња•§ а¶ЫඌටаІНа¶∞බа¶≤ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ බаІМаІЬ බගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶≤аІАа¶Ча¶ХаІЗ ටаІЛ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£ ඙а¶∞аІЗ ටඌа¶∞ ඐග඙а¶∞аІАට а¶ЪගටаІНа¶∞а•§ а¶Еа¶ЄаІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Эථа¶Эථඌථග а¶Жа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъа¶Њ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶∞аІЛටаІЗ а¶Ѓа¶Ђа¶Га¶ЄаІНа¶ђа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ ඙а¶≤а¶ња¶ЯаІЗа¶Хථගа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ѓ а¶ђаІЯа¶ЄаІА а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶∞а¶Њ а¶ЬаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬа¶Ыа¶ња¶≤ ථаІЛа¶Ва¶∞а¶Њ а¶ЯаІЗථаІНа¶°а¶Ња¶∞-а¶ђа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІАටගටаІЗа•§ а¶Па¶Ба¶∞а¶Њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ ටаІЗа¶Ьа¶Ча¶Ња¶Ба¶УаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶Ча¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶†а•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶Х а¶ђа¶∞аІНа¶ЈаІЗ а¶Жඪථ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЧаІЛа¶Яа¶Њ ඙а¶ЮаІНа¶ЪඌපаІЗа¶Х а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ШаІБа¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓаІЗට а¶Жа¶ЫаІЗ аІ©аІЂ/аІ™аІ¶ а¶Ьа¶®а•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ђа¶∞аІНа¶Ј а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶ѓаІЗ а¶ЫඌටаІНа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ, ඙а¶≤а¶ња¶ЯаІЗа¶Хථගа¶ХаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ධග඙ඌа¶∞аІНа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶ЯаІЗа¶∞ ථටаІБථ а¶ЫඌටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶У ටඌа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ђаІЗපаІА а•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶ѓа¶Њ а¶єаІЯ, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЃаІЗа¶Іа¶Ња¶ђаІА а¶У ඪගථගаІЯа¶∞ а¶Єа¶ња¶Яа¶ња¶ЬаІЗථ а¶єаІЯаІЗа¶У а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІМа¶≤аІАථаІНа¶ѓ а¶ђа¶Ьа¶ЊаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶∞ටඌඁ а¶®а¶Ња•§ а¶УබаІЗа¶∞ ථаІЛа¶Ва¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ња¶∞ а¶Жа¶ђа¶∞аІНа¶Ьථඌ а¶Па¶ЄаІЗ ඙аІЬට පයаІАබ а¶Жа¶Ьа¶ња¶Ь а¶Жа¶ђа¶Ња¶Єа¶ња¶Х а¶єа¶≤аІЗа•§ а¶ЃаІБа¶Ц а¶ђаІБа¶ЬаІЗ а¶Єа¶єаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Й඙ඌаІЯа¶У а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Яа¶ња¶≠а¶њ а¶∞аІБа¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ , а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІНඃඌථаІНа¶ЯගථаІЗа¶У බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓаІЗට а¶УබаІЗа¶∞ а¶Еථඌа¶Ха¶Ња¶ЩаІНа¶ХаІНඣගට а¶Ъа¶≤а¶Ња¶ЂаІЗа¶∞а¶Ња•§
а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Жа¶Єа¶њ а¶ЃаІВа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ; а¶Хඕඌ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЯаІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶Х а¶ђа¶Њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞ඌථаІНටග ථගаІЯаІЗа•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤аІЗа¶∞ ඙аІЬඌපаІЛථඌ а¶Жа¶∞ а¶Еа¶ЃаІНа¶≤а¶Ѓа¶ІаІБа¶∞ а¶ЄаІНа¶ЃаІГටගа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Жа¶∞аІЗа¶Хබගථ а¶ђа¶≤а¶ђа•§ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌ а¶ђаІБа¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ѓа¶Ња¶Ба¶∞а¶Њ а¶Па¶З а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ ඙аІЬа¶ЫаІЗථ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ѓа¶ђаІЗපග а¶Жа¶ЫаІЗа•§
ටаІГටаІАаІЯ а¶ђа¶∞аІНа¶Ј ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Єа¶ђа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ ( а¶ЗаІЯа¶Ња¶∞аІНථ, а¶ЂаІЗа¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Х, а¶УаІЯаІЗа¶Я ඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶ња¶В, а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Є) а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶ња¶≤аІЗа¶ђа¶Ња¶Є а¶Ыа¶ња¶≤ ටඌ а¶Па¶Ха¶Ьථ ඙аІНа¶∞а¶ХаІМපа¶≤аІАа¶∞ а¶ЗථаІНа¶°а¶Ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶≤ а¶ЂаІНа¶≤аІЛа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶≤ඌථаІЛа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඃඕаІЗа¶ЈаІНа¶Я а•§ ඪඁඌ඙ථаІА а¶ђа¶∞аІНа¶ЈаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђаІЗа¶ЫаІЗ ථගටаІЗ යට а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶°а¶≠ඌථаІНа¶Є а¶ђа¶Њ а¶ЄаІН඙аІЗපඌа¶≤а¶Ња¶За¶Ьа¶° а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Яа¶ња•§ а¶ЗබඌථаІАа¶В а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ђа¶ња¶≠а¶Ња¶Ч а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ьа¶Ња¶®а¶ња•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Ьථ ටа¶Цථ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙а¶Х а¶Ѓа¶Ња¶Єа¶Йබ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞( ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАටаІЗ ටගථග а¶ђаІБа¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶≠а¶ња¶Єа¶њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ) а¶ЕථаІНа¶Іа¶≠а¶ХаІНට а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Ѓа¶Ња¶Єа¶Йබ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Еа¶ІаІБථඌ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶Й඙ඌа¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ѓа•§ а¶УаІЯаІЗа¶Я ඙аІНа¶∞а¶ЄаІЗа¶Єа¶ња¶В а¶Па¶Х ථඌඁаІНа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶ђа¶ЬаІЗа¶ХаІНа¶Я а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Ьථ а¶ђаІЗа¶ЫаІЗ ථගа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Ѓа¶Ња¶Єа¶Йබ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЂаІЗа¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Х а¶ЃаІНඃඌථаІБа¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Ъа¶Ња¶∞а¶ња¶В а¶ЯаІЗа¶ХථаІЛа¶≤а¶Ьа¶ња¶ХаІЗа•§ ඪටаІНа¶ѓа¶њ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Ха¶њ , පаІЗа¶Ј а¶ђа¶∞аІНа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Єа¶Йබ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Уа¶З а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶°а¶≠ඌථаІНа¶Є а¶ЄаІН඙аІЗපඌа¶≤а¶Ња¶За¶Ьа¶° а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶Єа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶ЯаІЗа¶Хථගа¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ටඌ а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶Ха¶њ බගаІЯаІЗ а¶ђаІЗаІЬඌථаІЛ , а¶Еа¶ђа¶єаІЗа¶≤ගට а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶ђаІЗබථඌ а¶≠аІБа¶≤а¶њаІЯаІЗ බගටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඁථаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Б, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Па¶За¶ђа¶Ња¶∞ ඪටаІНа¶ѓа¶ња¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХථаІЛа¶≤а¶Ьа¶њ පගа¶Ца¶Ыа¶ња•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶Є ථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ටඕаІНа¶ѓаІЗа¶∞ බа¶ХаІНඣටඌ , а¶ЃаІБа¶ЧаІНа¶І а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња¶∞ а¶У а¶ЃаІЛа¶Яа¶ња¶≠аІЗа¶Я а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ බඌа¶∞аІБа¶£ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඪඁථаІНа¶ђаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඁථаІНටаІНа¶∞а¶ЃаІБа¶ЧаІНа¶ІаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Ча¶ња¶≤а¶§а¶Ња¶Ѓа•§
а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶∞ ථගаІЯаІЗ а¶ХඌයගථаІА පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶≤, а¶Ђа¶Ња¶Зථඌа¶≤ ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶За•§ ටа¶Цථа¶Ха¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ථ а¶ђа¶Њ а¶ЯаІНа¶∞аІЗථаІНа¶° а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ХаІЗ а¶ХаІЛඕඌаІЯ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶Ђа¶Ња¶Зථඌа¶≤ ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З ආගа¶Хආඌа¶Х а¶єаІЯаІЗ а¶ѓаІЗа¶§а•§ а¶Ѓа¶ња¶≤ а¶ЯаІНа¶∞аІЗථගа¶В а¶Па¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ђаІЬа¶≠а¶Ња¶З, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Йа¶ХаІЗ ඙а¶ЫථаІНබ а¶єа¶≤аІЗ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶≠а¶Ња¶ЧаІЗа¶З ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗථ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤аІЗ а¶ѓаІЛа¶Чබඌථ а¶Ха¶∞ටаІЗа•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶ЖඁබаІЗа¶∞ аІђаІ¶ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶ХаІЗ а¶ХаІЛඕඌаІЯ а¶ѓаІЛа¶Ч බගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶∞аІЗа¶Ьа¶Ња¶≤аІНа¶Я ඙ඌඐа¶≤ගප а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З ආගа¶Х а¶єаІЯаІЗ а¶ѓаІЗа¶§а•§ а¶ђа¶Ња¶ХаІА а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඁටаІЛ аІ™аІ¶ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ ඙аІБа¶∞аІЛ඙аІБа¶∞а¶њ а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞ඌථаІНа¶§а•§ а¶Па¶З а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞ඌථаІНටа¶∞а¶Њ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ ථඌථඌ ඪගථගаІЯа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ЗබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞ටඌඁ а¶ХаІЛඕඌаІЯ ඙аІНа¶∞ඪ඙аІЗа¶ХаІНа¶Я а¶ђаІЗපаІАа•§ а¶ЃаІБපа¶Ха¶ња¶≤ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Єа¶Ђа¶≤ а¶ђаІЬа¶≠а¶Ња¶ЗබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞ඌථаІНටග а¶ѓаІЗට а¶ђаІЗаІЬаІЗа•§ вАШа¶Жа¶∞аІЗ а¶Ѓа¶њаІЯа¶Њ а¶єаІБබඌа¶З а¶ђа¶ЗаІЯа¶Њ а¶∞а¶За¶Ы а¶ХаІНа¶ѓа¶Њ , а¶ѓа¶Ња¶У а¶ѓа¶Ња¶У ! ථගа¶Яа¶ња¶В- а¶П а¶ЬаІЯаІЗථ а¶Ха¶∞ !а¶Уа¶За¶ЦඌථаІЗ ටаІЛ а¶ХаІЗа¶Й ථඌа¶З а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤аІЗа¶∞а•§ а¶Ђа¶ња¶≤аІНа¶° а¶Па¶ХаІНа¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶Ха¶Ња•§вАЩ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Ьථ а¶ђа¶≤ට, вАШа¶Жа¶∞аІЗ а¶ІаІНඃඌට ! а¶Йа¶За¶≠а¶ња¶В а¶П а¶ѓа¶Ња¶Уа•§ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථග а¶ЃаІВа¶∞аІНа¶Ц а¶Ђа¶ња¶Яа¶Ња¶∞а¶∞а¶Њ а¶ђаІЬ а¶ђаІЬ а¶ЄаІБа¶≤а¶Ьа¶Ња¶∞ а¶∞аІЛа¶Яа¶њ, а¶∞аІЗ඙ගаІЯа¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЬаІЗа¶ХаІНа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶≤аІБа¶Ѓ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶ЦථටаІЛ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ПаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬаІЗа¶Я а¶УаІЯа¶Ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЬаІЗа¶ЯаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶ЕටаІНа¶ѓа¶Ња¶ІаІБථගа¶Х а¶≤аІБа¶Ѓа¶У а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗа•§ පаІАටටඌ඙ ථගаІЯථаІНටаІНа¶∞ගට а¶ђаІЬа¶ђаІЬ а¶ЂаІНа¶≤аІЛа¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ьа¶Ња¶З а¶Жа¶≤ඌබඌ!вАЩ вАШ а¶Жа¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶В а¶П а¶ЬаІЯаІЗථ а¶Ха¶∞а•§ පаІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓа¶≤බඌа¶∞аІЗ බаІЗа¶Ц а¶Ха¶З а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ча¶њаІЯа¶Њ!вАЩ вАШ а¶ЖපаІНа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓ, ටаІЛа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶°аІЗථගඁ ඙аІНа¶≤аІНඃඌථаІНа¶ЯаІЗ а¶ЬаІЯаІЗථ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶Ы ථඌ а¶ХаІЗථ ? а¶ЬඌථаІЛ а¶°аІЗථගඁаІЗа¶∞ а¶≠а¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶ѓаІО а¶ХටаІЛ а¶Йа¶ЬаІНа¶ЬаІНа¶ђа¶≤ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗ !вАЩ вАШ а¶ЄаІЛаІЯаІЗа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђа¶Њ а¶ЂаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Я ථගа¶Яа¶ња¶В а¶П а¶ЯаІЗа¶Хථගа¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶≤аІЛа¶Х ථඌа¶З, а¶ЧаІБа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа¶∞ а¶Еපගа¶ХаІНඣගටබаІЗа¶∞ බගаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞аІЛа¶°а¶Ња¶Хපථ а¶Ъа¶≤а¶ЫаІЗ , а¶Уа¶З а¶ЦඌථаІЗ а¶ѓа¶Ња¶У!вАЩ а¶°а¶ЊаІЯа¶ња¶В ඀ගථගපගа¶В а¶Па¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤ටаІЗ යට ථඌ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶∞аІНа¶ђаІЛа¶ЪаІНа¶Ъ а¶Ъඌයගබඌа¶∞а•§ аІѓаІ¶ а¶Па¶∞ බපа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථගа¶Я а¶Ха¶ЃаІН඙аІЛа¶Ьа¶ња¶Я а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶ђа¶Ыа¶∞ බаІБаІЯаІЗа¶ХаІЗа¶∞ ඪගථගаІЯа¶∞ а¶ђаІЬ а¶≠а¶Ња¶ЗаІЯаІЗа¶∞а¶Њ а¶Эа¶Ха¶Эа¶ХаІЗ а¶ЯаІЯаІЛа¶Яа¶Њ а¶Ча¶ЊаІЬаІАටаІЗ ඃඌටඌаІЯඌට а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Ѓа¶Ња¶Є පаІЗа¶ЈаІЗ аІ©аІ¶-аІ™аІ¶ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶ђаІЗටථ ඙ඌаІЯа•§ а¶ЄаІЛ, ඙аІНа¶∞ටග а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЪаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ЃаІЗа¶Іа¶Ња¶ђаІА а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ථගа¶Я а¶Ха¶ЃаІН඙аІЛа¶Ьа¶ња¶ЯаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ч බගа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ а¶Еа¶ђа¶єаІЗа¶≤ගට а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІН඙ගථගа¶В а¶ђа¶Њ а¶ЗаІЯа¶Ња¶∞аІНථ а¶ЃаІНඃඌථаІБа¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Ъа¶Ња¶∞а¶ња¶В а¶ЄаІЗа¶ХаІНа¶Яа¶∞а¶Яа¶Ња•§ а¶ЄаІН඙ගථගа¶В а¶Ха¶Ња¶∞а¶Цඌථඌа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЕථаІЗа¶Х බаІВа¶∞аІЗ බаІВа¶∞аІЗа•§ ටаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶°а¶Ња¶ЄаІНа¶Я а¶Жа¶∞ а¶ЃаІЗපගථаІЗа¶∞ а¶Жа¶УаІЯа¶Ња¶Ь а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗප а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Хගට а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞а•§
ටаІЛ а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞ඌථаІНට а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Па¶З а¶Жа¶Ѓа¶њ, а¶Пබගа¶Х а¶ЄаІЗබගа¶Х а¶ШаІЛа¶∞а¶Ња¶ЂаІЗа¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶Х а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶Па¶За¶ЦඌථаІЗ බаІБа¶За¶Ѓа¶Ња¶Є а¶Уа¶За¶ЦඌථаІЗ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЕඐපаІЗа¶ЈаІЗ а¶ђаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶ња¶Ѓа¶ХаІЛ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤аІЗ а¶Па¶ЄаІЗ ඕගටаІБ а¶єа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶ХඌයගථаІА පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶≤а•§ ඙аІНа¶∞а¶њ-а¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Я ථඌඁаІЗа¶∞ а¶Па¶Х ධග඙ඌа¶∞аІНа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶ЯаІЗ ඐගපඌа¶≤ а¶Жа¶Ьබඌයඌ а¶Яа¶Ња¶З඙аІЗа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶≠аІЯа¶Ва¶Ха¶∞ а¶ЃаІЗපගථаІЗа¶∞ а¶≠аІЯа¶Ва¶Ха¶∞ ටඌ඙ඁඌටаІНа¶∞а¶Ња¶∞ а¶У යඌට а¶ХаІНа¶ЈаІЯ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶≤а¶ња¶ХаІБа¶За¶° а¶Ха¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶ХаІЗа¶∞ а¶ЂаІНа¶≤аІЛа¶∞аІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶≤ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЬаІАа¶ђа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Є а¶Ыа¶ња¶≤ බаІБа¶За¶Ьа¶®а•§ а¶ЫаІЛа¶Яа¶Ьථ а¶Ьа¶Ња¶≠аІЗබ а¶Жа¶∞ а¶ђаІЬа¶Ьථ а¶Ца¶ЊаІЯаІЗа¶∞а•§ බаІБа¶За¶ЬථаІЗа¶З ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ а¶За¶ЃаІН඙аІЛа¶∞аІНа¶ЯаІЗа¶°а•§ а¶Па¶Ба¶∞а¶Њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶≠а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ а¶У යගථаІНබග- а¶Йа¶∞аІНබаІБ а¶ЃаІЗපඌථаІЛ а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶§а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඃබගа¶У а¶Еа¶ђа¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶≤аІА а¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІА а¶Еа¶ІаІНа¶ѓаІБඣගට а¶Ѓа¶ња¶∞඙аІБа¶∞аІЗ а¶ђаІЬ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶њ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Йа¶∞аІНබаІБ а¶У යගථаІНබග а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤ ; а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථ ඐගබаІНа¶ђаІЗа¶Ј а¶Ыа¶ња¶≤! а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Пඁථ а¶≠а¶Ња¶ђ බаІЗа¶Цඌටඌඁ а¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Йа¶∞аІНබаІБ вАУයගථаІНබග а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶ђаІБа¶Эа¶ња¶®а¶Ња•§ а¶Уа¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට а¶Ша¶ЊаІЬටаІНа¶ѓа¶ЊаІЬа¶Ња¶Ѓа¶ња•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ша¶ЊаІЬටаІНа¶ѓа¶ЊаІЬа¶Ња¶Ѓа¶ња¶∞ ඁඌපаІБа¶≤ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ බගටаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ බаІБа¶Га¶Ца¶Ьථа¶Х-а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ша¶ЊаІЬටаІНа¶ѓа¶ЊаІЬа¶Ња¶Ѓа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶ЦථаІЛ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶Єа¶єа¶Ь, а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶Ы ; а¶єаІЯ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶ЊаІЯ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤ ථа¶За¶≤аІЗ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶ЬගටаІЗ а•§ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶ђа¶∞аІНටаІА а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶ХаІЗථ а¶ђа¶≤а¶Ы а¶ђа¶Њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ බගаІЯаІЗ а¶ђа¶≤ඌටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶ЪаІНа¶Ы?
බගථ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶∞ඌට а¶Жа¶ЄаІЗа•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Є а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ පග඀а¶Яа¶ња¶В а¶°а¶ња¶Йа¶Яа¶ња¶∞ ඙аІНа¶ѓа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Жа¶ЪаІНа¶ЫථаІНථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗа•§ а¶∞ඌටаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ѓа¶Цථ а¶єаІБа¶Ѓа¶ЊаІЯаІВථ а¶ЖයඁබаІЗа¶∞ ථඌа¶Яа¶Х බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ , а¶Жа¶Ѓа¶њ ටа¶Цථ а¶ЧаІЛа¶Ыа¶Ча¶Ња¶Ы а¶Ха¶∞аІЗ а¶Єа¶∞а¶Ња¶ђаІЛ,а¶Ча¶Ња¶ЬаІА඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶ња¶Ѓа¶ХаІЛ а¶ЗථаІНа¶°а¶Ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶≤ ඙ඌа¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶ѓа¶Ња¶З ‘а¶Єа¶њ’ පග඀а¶ЯаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Йа¶Яа¶њ බගටаІЗа•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ вАШа¶ПвА٠පග඀а¶ЯаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Йа¶Яа¶њ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤ аІђа¶Яа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІБ඙аІБа¶∞ аІ®а¶Яа¶Њ а•§ а¶Р පග඀а¶ЯаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶Йа¶Яа¶њ а¶Іа¶∞ටаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶∞ඌටаІЗ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶Ха¶Ъа¶≤ඌටаІЗ а¶Ха¶Ъа¶≤ඌටаІЗ а¶ШаІБа¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Йආග а¶Ха¶њ а¶Йආග ථඌ а•§ а¶Жа¶ЃаІНа¶Ѓа¶Њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ථඌ а¶ЦаІЗаІЯаІЗ а¶ђа¶Ња¶Єа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ යටаІЗ බගටаІЗථ ථඌ ! а¶ЕටаІЛ а¶≠аІЛа¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъඌ඙аІЗа¶ЯаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЦаІЗටаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶≤а¶Ња¶ЧаІЗ ? ටඐаІЗ а¶ђаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶ња¶Ѓа¶ХаІЛ ටаІЗ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Єа¶Ња¶∞ а¶ХаІНඃඌථаІНа¶ЯගථаІЗа¶∞ а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ බඌа¶УаІЯа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ බаІБа¶∞аІНබඌථаІНට ! а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Й඙а¶≠аІЛа¶Ч а¶Ха¶∞ටඌඁ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯප:
පග඀а¶Яа¶ња¶В а¶°а¶ња¶Йа¶Яа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ЃаІЛа¶ЯаІЗа¶У а¶≠а¶Ња¶≤ а¶≤а¶Ња¶ЧටаІЛ а¶®а¶Ња•§ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ඌට а¶ЬаІЗа¶ЧаІЗ බගථаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛටаІЗ а¶ШаІБа¶Ѓ а¶ЖඪටаІЛ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Эа¶ња¶Ѓа¶Эа¶ња¶Ѓ а¶ШаІБа¶Ѓ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶єа¶≤аІЗа¶З බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓаІЗට පග඀а¶Яа¶ња¶В а¶°а¶ња¶Йа¶Яа¶ња¶∞ а¶ђаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶ња¶Ѓа¶ХаІЛа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶За¶ХаІНа¶∞аІЛ-а¶ђа¶Ња¶Є а¶Іа¶∞ටаІЗ а¶єаІБаІЬаІЛа¶єаІБаІЬа¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶Єа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња•§ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Єа¶ЃаІЯ ඪගථගаІЯа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ЗබаІЗа¶∞ а¶ЬаІЗථඌа¶∞аІЗа¶≤ පග඀а¶Я а¶Ча¶ЊаІЬаІАටаІЗ а¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Па¶Х а¶ђаІЬа¶≠а¶Ња¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЃаІЛа¶єа¶Ња¶ЃаІНඁබ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗа•§ а¶Ча¶ЊаІЬаІА ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶≠ගටаІНටගටаІЗ ථඌඁගаІЯаІЗ බගаІЯаІЗ а¶Ѓа¶ња¶∞඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Жа¶Єа¶§а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЕථаІЗа¶Хබගථ а¶ЪථаІНබаІНа¶∞а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶ЙබаІНඃඌථаІЗ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶ѓаІЗа¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶≤аІЗа¶ХаІЗа¶∞ ඙ඌපаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђ а¶ЃаІЗа¶≤ඌටаІЗ ඙ඌа¶∞ටඌඁ а¶®а¶Ња•§ а¶П а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ха¶њ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶њ ? а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶∞ඌටаІЗ а¶Хටа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ඐගපඌа¶≤ ඃථаІНටаІНа¶∞аІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯ ඙ඌа¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња•§ а¶∞аІЗඪග඙ග බගа¶ЪаІНа¶Ыа¶њ, а¶ШථටаІНа¶ђ ඁඌ඙а¶Ыа¶ња•§ а¶Хඌ඙аІЬаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ а¶єа¶≤аІЗ а¶Е඙ඌа¶∞аІЗа¶Яа¶∞а¶ХаІЗ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ а¶єаІЯа¶∞ඌථ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඐබ а¶Е඙ඌа¶∞аІЗа¶Яа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤, ථඌඁ а¶≠аІБа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶ња•§ ආගа¶Х ආගа¶Х а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶Па¶ХаІЗ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓаІЗට а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ථටаІБථ ඙аІНа¶∞аІЛа¶°а¶Ња¶Хපථ а¶За¶ЮаІНа¶ЬගථගаІЯа¶Ња¶∞а¶∞а¶Њ а¶Па¶З а¶Єа¶ђ ඐබ а¶У ඙аІБа¶∞ථаІЛ а¶Е඙ඌа¶∞аІЗа¶Яа¶∞аІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶ЪаІЛа¶Я඙ඌа¶Яа¶У а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞ටඌඁ а¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Уа¶З ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶ЃаІЗපගථ а¶ЄаІЗ а¶єаІЯටаІЛ а¶Чට аІ™/аІЂ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ; а¶ЄаІЗ а¶ЬඌථаІЗ а¶ХаІЛථ а¶∞аІЛа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ а¶ђа¶Њ а¶ХаІЛථ а¶ЪаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටаІЛ а¶ШаІЛаІЬа¶Ња¶∞ а¶°а¶ња¶Ѓа¶У а¶Ьඌථග а¶®а¶Ња•§ ටаІЛ а¶ЄаІЗа¶З ඐබ а¶Е඙ඌа¶∞аІЗа¶Яа¶∞а¶ХаІЗ а¶ђа¶єаІБබගථ а¶≤аІЛа¶Х ඙ඌආගаІЯаІЗ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ЖථටаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶°аІЗථගඁ ඙аІНа¶≤аІНඃඌථаІНа¶Я ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶Уа¶ЦඌථаІЗ а¶ХаІЛථ а¶ЖබගඐඌඪаІА а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ථඌа¶Ха¶њ ටඌа¶Ба¶∞ а¶≠а¶Ња¶ђ-а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа¶ђа¶Ња¶Єа¶Ња•§
а¶Па¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ШаІБа¶∞ටаІЗ ථඌ а¶ШаІБа¶∞ටаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶њ යටаІЛබаІНа¶ѓа¶Ѓ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ЪථаІНබаІНа¶∞а¶ња¶Ѓа¶Њ а¶ЙබаІНඃඌථаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ ඐඌබඌඁ а¶Ца¶Ња¶З, а¶Ъа¶Њ а¶Єа¶ња¶Ча¶Ња¶∞аІЗа¶Я а¶Ца¶Ња¶З а¶Жа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ђа¶ња•§ ඐථаІНа¶ІаІБа¶∞а¶Њ а¶Єа¶ђ а¶ХаІЗ а¶ХаІЛඕඌаІЯа•§ а¶ЃаІЛа¶ђа¶Ња¶За¶≤аІЗа¶∞ а¶ѓаІБа¶Ч ථඌ , а¶ѓаІЗ а¶ЄаІБа¶Ц බаІБа¶Га¶ЦаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђ ! а¶ХаІЗа¶Й а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶≠а¶Ња¶≤аІБа¶Ха¶Њ а¶ЃаІЯඁථඪගа¶Ва¶є, а¶ХаІЗа¶Й ථа¶∞а¶Єа¶ња¶ВබаІА, а¶ХаІЗа¶Й а¶Ъа¶ЯаІНа¶Яа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ, а¶ХаІЗа¶Й а¶Ча¶Ња¶ЬаІА඙аІБа¶∞аІЗ а¶ХаІЗа¶Й ථඌа¶∞а¶ЊаІЯа¶£а¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗ !
а¶Па¶Х ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗ ඪගබаІН඲ඌථаІНට ථගаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ ථඌа¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶°а¶ЊаІЯа¶ња¶В ඀ගථගඪගа¶В а¶Па¶∞ а¶ЃаІЛа¶Яа¶Њ а¶ђаІЗටථаІЗа¶∞а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЬаІЗථඌа¶∞аІЗа¶≤ පග඀а¶Я а¶°а¶ња¶Йа¶Яа¶њ а¶єа¶≤аІЗа¶З а¶ђа¶∞аІНටаІЗ а¶ѓа¶Ња¶За•§ а¶∞ඌටаІЗ а¶ШаІБа¶Ѓа¶њаІЯаІЗ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Є а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ња¶Яа¶Ња¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞඲ඌථටඁ а¶ЃаІЛа¶ХаІНа¶Ј а¶єаІЯаІЗ බඌа¶БаІЬа¶Ња¶≤аІЛа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶ЗаІЯа¶Ња¶∞ а¶≤а¶Є а¶Ыа¶ња¶≤, а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඥඌа¶Ха¶Њ а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗа¶∞ ඪටаІАа¶∞аІНඕ аІІаІѓ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЪаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ьа¶≤ а¶Ыа¶ња¶≤ ඐථаІНа¶ІаІБа•§ а¶Уа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ХаІБа¶Ѓа¶ња¶≤аІНа¶≤а¶Њ а¶≠а¶ња¶ХаІНа¶ЯаІЛа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ьа¶Ња¶≤а¶Ња¶≤а¶У а¶ШථගඣаІНආ а¶єаІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ьඌථටඌඁ а¶Ьа¶Ња¶≤а¶Ња¶≤, а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІВ඙බඌ, а¶У а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ಮಶටඁ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЪаІЗа¶∞ а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Є а¶ЯаІЗа¶ХථаІЛа¶≤а¶Ьа¶ња¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Ьථ а¶У඙аІЗа¶ХаІНа¶Є а¶ЧаІНа¶∞аІБ඙аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІЗථаІНа¶°а¶Ња¶За¶Ьа¶ња¶В а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІЗථаІНа¶°а¶Ња¶За¶Ьа¶ња¶В а¶Єа¶ЃаІНඐථаІНа¶ІаІЗ ඐගථаІНබаІБа¶ђа¶ња¶Єа¶∞аІНа¶Ч а¶Ьඌථග а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶БබаІЗа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЬаІЗථඌа¶∞аІЗа¶≤ පග඀а¶Я а¶°а¶ња¶Йа¶Яа¶ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ЃаІНඃඌථаІЗа¶Ь а¶Ха¶∞аІЗ බගටаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ЬаІЗථඌа¶∞аІЗа¶≤ පග඀а¶Я а¶°а¶ња¶Йа¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶єаІЯ а¶°а¶Ња¶За¶Ь-а¶ХаІЗа¶Ѓа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶Є (а¶∞а¶В а¶ЗටаІНඃඌබග) а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ХаІЗа¶Яа¶ња¶В а¶Еඕඐඌ а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Я а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІЗථаІНа¶°а¶Ња¶За¶Ьа¶ња¶Ва•§
а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Цඌථග а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞ඌථаІНටග ථගаІЯаІЗ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶Ха¶њ බගаІЯаІЗ а¶Па¶Хබගථ а¶ЧаІЗа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶У඙аІЗа¶ХаІНа¶Є а¶ЧаІНа¶∞аІБ඙аІЗа¶∞ а¶єаІЗа¶° а¶Еа¶Ђа¶ња¶ЄаІЗа•§ а¶Ха¶∞аІНථаІЗа¶≤ (а¶Еа¶ђа¶Г) а¶Ђа¶∞ගබ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶Ха¶∞а¶ђа•§ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶єаІЗа¶° а¶Еа¶Ђа¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶∞ගපග඙ඪථаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶Жа¶ЫගටаІЛ, а¶ђа¶ЄаІЗа¶З а¶Жа¶Ыа¶ња•§ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤ а¶ЧаІЬа¶њаІЯаІЗ බаІБ඙аІБа¶∞ , а¶ХаІНа¶ЈаІБа¶Іа¶ЊаІЯ ඙аІЗа¶Я а¶ЬаІНа¶ђа¶≤а¶ЫаІЗ, а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ца¶Ња¶ђ ටඌа¶У а¶ѓаІЗටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ыа¶њ ථඌ; а¶Ха¶Цථ а¶Ђа¶∞ගබ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶°аІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗа¶®а•§ ටаІЛ , а¶ђа¶ЄаІЗ ඕඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶Х ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗ а¶ЧаІНа¶∞аІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶ЮаІНа¶Ь а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъඌ඙ඌа¶Ха¶Њ а¶ЪаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶≠බаІНа¶∞а¶≤аІЛа¶Х а¶∞ගපග඙පථаІЗ ඥаІБа¶Ха¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ђаІЗප а¶Єа¶ЃаІНа¶≠аІНа¶∞а¶ЃаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬа¶≤а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶Ъගථගථඌ ; а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЄаІЛа¶Ђа¶Ња¶ЄаІЗа¶ЯаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗа¶З ඕඌа¶Ха¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ඙а¶∞аІЗ а¶∞ගපග඙පථаІЗа¶∞ а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶Яа¶њ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ЂаІЛථаІЗ а¶Іа¶∞а¶њаІЯаІЗ බගа¶≤аІЗථ ඪගථයඌ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤аІЗа¶∞ ටа¶Цථа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Єа¶∞аІНа¶ђаІЗа¶Єа¶∞аІНа¶ђа¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶єа¶њ а¶Жа¶≤а¶Ѓ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ѓа¶Ња¶єа¶њ а¶Жа¶≤а¶Ѓ ථඌඁа¶Яа¶њ а¶Ъගථග а¶≠а¶Ња¶≤аІЛඁටаІЛа¶З, а¶ХаІЗථථඌ ටගථග а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁබගа¶ХаІЗа¶∞ ඪගථගаІЯа¶∞ а¶За¶ЮаІНа¶ЬගථගаІЯа¶Ња¶∞ а¶ђаІЬа¶≠а¶Ња¶За•§ а¶Ша¶Яථඌ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶Уа¶З а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъඌ඙ඌа¶Ха¶Њ а¶ЪаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶≠බаІНа¶∞а¶≤аІЛа¶Х а¶ЂаІЛථ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶єа¶њ а¶Жа¶≤а¶Ѓ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђа¶ХаІЗ ‘ටаІБа¶Ѓа¶њ’ а¶Єа¶ЃаІНа¶ђаІЛ඲ථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶Я а¶°а¶Ња¶За¶В а¶Па¶∞ а¶Й඙а¶Ха¶Ња¶∞ගටඌ а¶У а¶Е඙а¶Ха¶Ња¶∞ගටඌ а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶У඙аІЗа¶ХаІНа¶Є ඐගපඌа¶≤ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶Ѓа¶њ ථඐаІАථ ඙аІНа¶∞а¶ХаІМපа¶≤аІА ; а¶Єа¶Ха¶≤ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ ඪගථගаІЯа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ЗබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ъගථගа¶У а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Уа¶З а¶≠බаІНа¶∞а¶≤аІЛа¶Х а¶У а¶Ѓа¶Ња¶єа¶њ а¶Жа¶≤а¶Ѓ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶ХඕаІЛ඙а¶Хඕථ පаІБථаІЗ а¶Іа¶∞аІЗа¶З ථගа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Йථගа¶У а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ьඌටග а¶ХаІЛථ ඪගථගаІЯа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶За¶ЮаІНа¶ЬගථගаІЯа¶Ња¶∞ а¶єа¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Йථග а¶Й඙а¶∞аІЗа¶∞ ටа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶∞ගපග඙පථගඪаІНа¶Яа¶ХаІЗ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Йථග а¶ХаІЗ ? а¶∞ගපග඙පථගඪаІНа¶Я а¶ђаІЗප а¶ђа¶ња¶∞а¶ХаІНට а¶єаІЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ ටඌа¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤, а¶Йථගа¶З ඪගථයඌ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞; а¶Жа¶Ѓа¶њ ඥаІЛа¶Х а¶Ча¶ња¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ටඌයа¶≤аІЗ а¶Зථගа¶З а¶ЄаІЗа¶З а¶Ха¶ња¶ВඐබථаІНටග а¶ХаІНඃඌ඙аІНа¶ЯаІЗථ а¶ЖථගඪаІБа¶∞ а¶∞යඁඌථ ඪගථයඌ ?
පаІЗа¶Ј а¶ђа¶ња¶ХаІЗа¶≤аІЗ а¶ЦаІБа¶ђ а¶єаІЗа¶≤а¶Ња¶ЂаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ а¶°а¶Ња¶Х ඙аІЬа¶≤ а¶Ха¶∞аІНථаІЗа¶≤ а¶Ђа¶∞ගබ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶∞аІБа¶ЃаІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь඙ටаІНа¶∞аІЗ а¶Єа¶Ња¶Зථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Йථග а¶Ъපඁඌа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶Х බගаІЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ඙а¶∞ගඁඌ඙ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶ЫаІБа¶БаІЬаІЗ බගа¶≤аІЗථ а¶ХаІЗථ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඙аІНа¶∞аІЛа¶°а¶Ња¶Хපථ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІЗථаІНа¶°а¶Ња¶За¶Ьа¶ња¶В а¶П а¶ЖඪටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶Хඌප඙ඌටඌа¶≤ а¶ЪගථаІНටඌ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶≠а¶Ња¶ђа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Ха¶њ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶Йථග а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Еа¶Ђа¶Ња¶∞ බගа¶≤аІЗථ, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓаІЗථ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඪගථයඌ а¶Уа¶≠аІЗථ а¶°а¶Ња¶За¶В а¶П а¶ѓаІЛа¶Ч බගа¶З, а¶Уа¶ЦඌථаІЗ а¶≤аІЛа¶Х а¶≤а¶Ња¶Ча¶ђаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЗටඪаІНටට а¶Ха¶∞а¶Ыа¶њ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶Йථග а¶Єа¶Ња¶єа¶Є බගа¶≤аІЗථ, ඪටаІНа¶ѓа¶њ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤ටаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ѓаІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЃаІВа¶≤ට: а¶ЬථаІНа¶Ѓа¶ЄаІВටаІНа¶∞аІЗ ඥඌа¶Ха¶Ња¶∞а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ බаІАа¶∞аІНа¶Шබගථ ඙аІНа¶∞аІЛа¶°а¶Ња¶ХපථаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶У а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ බаІВа¶∞ටаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶У а¶ђаІЬ а¶ѓаІЗ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ඙аІАаІЬа¶Њ බගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ පග඀а¶Яа¶ња¶В а¶°а¶ња¶Йа¶Яа¶њ а¶Па¶ђа¶В а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗа¶ґа•§ а¶Йථග а¶ЪаІЛа¶Ц බගаІЯаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ, ඁඌථаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓаІЗථ а¶Жа¶∞а¶У а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞ගට а¶ђа¶≤а¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඁථаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Ъа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ъа¶Ња¶З а¶ЬаІЗථඌа¶∞аІЗа¶≤ පග඀а¶Я а¶°а¶ња¶Йа¶Яа¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ъа¶Ња¶З, а¶Ха¶ња¶ЫаІБ පගа¶ХаІНඣගට а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Є-а¶Яа¶Ња¶За¶Ѓ а¶ђаІНа¶ѓаІЯ а¶Ха¶∞ටаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඁථаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶њ ඙аІНа¶∞аІЛа¶°а¶Ња¶ХපථаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ ඙ග඙а¶≤ а¶ЃаІНඃඌථаІЗа¶Ьа¶ЃаІЗථаІНа¶Я а¶У а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ХаІЗа¶Яа¶ња¶В а¶П а¶≠а¶Ња¶≤ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђа•§ а¶Жа¶∞а¶У а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶єа¶ња¶Ьа¶ња¶ђа¶ња¶Ьа¶њ а¶ІаІБථаІБа¶ЂаІБථаІБ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶Єа¶ђ а¶Хඕඌ ඁථаІЗа¶У ථඌа¶За•§
а¶Йථග а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶≤аІЗථ, а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Б а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІЗථаІНа¶°а¶Ња¶За¶Ьа¶ња¶В а¶П а¶ЬаІЗථඌа¶∞аІЗа¶≤ පග඀а¶Я а¶°а¶ња¶Йа¶Яа¶њ , а¶ХගථаІНටаІБ ඥаІЛа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ආගа¶Х ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶У а¶ђаІЗа¶∞ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶ХගථаІНටаІБ ආගа¶Х ථаІЗа¶З ! а¶Єа¶ђ а¶Хඕඌ පаІЛථඌа¶∞ ඙а¶∞, а¶Йථග а¶ЂаІЛථаІЗ а¶ЃаІЗа¶Ьа¶∞( а¶Еа¶ђа¶Г) а¶ЄаІБථаІАа¶≤ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶ХаІЗ а¶°аІЗа¶ХаІЗ ඙ඌආඌа¶≤аІЗථ ටඌа¶Ба¶∞ а¶∞аІБа¶ЃаІЗа•§ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ , а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶ЃаІМа¶Ца¶ња¶Х а¶≤а¶ња¶Цගට ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ ථගටаІЗа•§ а¶Ђа¶∞ගබ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІЬ а¶Хථ඀ඌа¶∞аІЗථаІНа¶Є а¶∞аІБа¶ЃаІЗ а¶ЄаІБථаІАа¶≤ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ ඪඌබඌ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь а¶Іа¶∞а¶њаІЯаІЗ බගаІЯаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶∞аІЗа¶ЃаІЗа¶°а¶ња¶Є а¶Еа¶Ђ а¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶Ђа¶ња¶Х а¶Зථ ඥඌа¶Ха¶Њ( Remedies of Traffic in Dhaka) вАФа¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІНඐථаІНа¶ІаІЗ а¶≤а¶ња¶ЦටаІЗа•§ а¶ѓа¶Ња¶єаІН ඐඌ඙ඪаІН ! а¶Жа¶Єа¶Ыа¶њ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІЗථаІНа¶°а¶Ња¶За¶Ьа¶ња¶В а¶Па¶∞ ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ බගටаІЗ , а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ ඙аІНа¶∞а¶ХаІМපа¶≤аІАа•§ а¶Па¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඥඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶Ђа¶ња¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶њ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶≠аІЗа¶ђаІЗ ටඐаІНබඌ а¶ЦаІЗаІЯаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶ђа¶ЄаІЗ ඕඌа¶Ха¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶∞ ඥඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶Ђа¶ња¶ХаІЗа¶∞ а¶Еа¶Ъа¶≤а¶Ња¶ђа¶ЄаІНඕඌ ථගаІЯаІЗ а¶Хට а¶∞ඕаІАа¶Ѓа¶єа¶Ња¶∞ඕаІА а¶ЪගථаІНටඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶єа¶ња¶Ѓа¶Єа¶ња¶Ѓ а¶Ца¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ХаІЛථ а¶єа¶∞ගබඌඪ ඙ඌа¶≤ ? а¶ѓа¶Ња¶З а¶єаІЛа¶Х ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Ха¶•а¶Ња•§ а¶ЧаІЛа¶Яа¶Њ а¶ЧаІЛа¶Яа¶Њ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞аІЗ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶ЬගටаІЗ а¶ХаІА а¶ѓаІЗ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ බаІБа¶З ඙ඌටඌ а¶≠а¶∞аІЗ а¶ЄаІЗ а¶Жа¶∞ ඁථаІЗ ථаІЗа¶З а•§
а¶≤а¶ња¶ЦаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶Жа¶Ыа¶њ ටаІЛ, а¶Жа¶Ыа¶ња¶За•§ а¶ЄаІБථаІАа¶≤ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙ඌටаІНටඌ ථаІЗа¶За•§ а¶Йථග а¶Ша¶£аІНа¶Яа¶Њ බаІБаІЯаІЗа¶Х ඙а¶∞аІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶Цඌටඌ ථගаІЯаІЗ а¶Ђа¶∞ගබ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶∞аІБа¶ЃаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶®а•§ ඁගථගа¶Я බаІБаІЯаІЗа¶Х ඙а¶∞аІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶Ха¶ђаІЗ а¶ЬаІЯаІЗථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђ ? а¶Жа¶Ѓа¶њ ඪ඙аІНටඌය බаІБаІЯаІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ ථගа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЖථඌаІЬа¶њ ථටаІБථ ඙аІНа¶∞аІЛа¶°а¶Ња¶Хපථ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Єа¶Ња¶∞ ; а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЂаІНа¶≤аІЛа¶∞аІЗ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶З а¶Ха¶њ а¶Жа¶∞ ථඌ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶З а¶ђа¶Њ а¶Ха¶њ! а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶ђаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶ња¶Ѓа¶ХаІЛ а¶Пටබගථ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ, а¶Жа¶Ча¶Ња¶ЃаІАටаІЗа¶У а¶Ъа¶≤а¶ђаІЗа•§ ථඌථඌ а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞ඌථаІНටග а¶Ха¶Ња¶Яа¶њаІЯаІЗ බගа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶За¶ЄаІНට඀ඌ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞ගටаІЗа•§ ටаІЛ а¶ђаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶ња¶Ѓа¶ХаІЛа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶Па¶Ба¶∞а¶Њ ටගථ а¶Ѓа¶Ња¶Є ඙а¶∞аІЗ а¶ђаІЗටථ а¶¶а¶ња¶§а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙ඌа¶Уථඌ ටගථ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶ђаІЗටථ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඃඕඌа¶∞аІАටග а¶ЫаІЯа¶Ѓа¶Ња¶Є ඙а¶∞аІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶ХаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ යඌටаІЗ ඙аІЗа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ ඙аІНа¶∞аІЛа¶°а¶Ња¶Хපථ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Уа¶За¶ЦඌථаІЗа¶З вАШа¶Ѓа¶ІаІБа¶∞аІЗа¶£ ඪඁඌ඙ඃඊаІЗаІОвАЩ а¶Ша¶ЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІМපа¶≤аІА а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶єа¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶Ња¶ХаІА а¶ЬаІАඐථ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІЗථаІНа¶°а¶Ња¶За¶Ьа¶ња¶В, а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ХаІЗа¶Яа¶ња¶В а¶Жа¶∞ а¶ЕаІНඃඌධඁගථගඪаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗපථ ථගаІЯаІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶Яа¶њаІЯаІЗ බගа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња•§
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Па¶Цථа¶У а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ба¶ЭаІЗ а¶ЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞а¶≠а¶ња¶Й а¶ђаІЛа¶∞аІНа¶°аІЗ ඐඪටаІЗ а¶єаІЯа•§ ථඐаІАථ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІМපа¶≤аІАබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ѓа¶Цථ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЬаІБаІЯа¶Ња¶≤ а¶ЃаІБа¶°аІЗ ඕඌа¶Ха¶њ, а¶ђа¶≤а¶њ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ ටаІЛඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ХаІНа¶Ја¶£ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓ ; а¶ЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞а¶≠а¶ња¶Й පаІЗа¶ЈаІЗ ටаІЛඁඌබаІЗа¶∞ ඁථаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථаІЗ а¶Жа¶Ыа¶њ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶ХаІЛථ ඙аІНа¶∞පаІНථ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а•§ а¶Йа¶≠аІЯ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗа¶∞ ඪඁඌථඌ඲ගа¶Ха¶Ња¶∞! а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶§: а¶Па¶Ба¶∞а¶Њ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ ථගаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Ха¶њ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІЗа¶Ь , а¶ХаІЯබගථаІЗа¶∞ а¶ЫаІБа¶Яа¶њ, ඙аІНа¶∞а¶Ђа¶ња¶Я පаІЗаІЯа¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Хගථඌ а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§
а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶Хබගථ а¶Па¶Х а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞аІА඙аІНа¶∞а¶Ња¶∞аІНඕаІА а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ЄаІН඙а¶∞аІНපа¶Хඌටа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶Єа¶≤а•§ а¶ЄаІЗ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞а¶≤, вАШа¶Ж඙ථග а¶ХаІЗථ а¶Па¶З ටаІАа¶ђаІНа¶∞ පඌа¶∞аІАа¶∞а¶ња¶Х а¶У ඁඌථඪගа¶Х පаІНа¶∞а¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІЗථаІНа¶°а¶Ња¶За¶Ьа¶ња¶В ඙аІЗපඌаІЯ а¶Жа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶Ха¶њ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Па¶З ඙аІЗපඌ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ බගටаІЗ а¶За¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ ථඌ?вАЩ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶єа¶Ња¶Єа¶њ а¶єа¶Ња¶Єа¶њ а¶ЃаІБа¶Ц а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Х а¶ЯаІЛаІЯа¶Ња¶Зථ а¶ђа¶Њ а¶Жа¶∞аІНථаІЗа¶ЄаІНа¶Я а¶єаІЗа¶Ѓа¶ња¶В а¶УаІЯаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Е඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට ඁථаІНටඐаІНа¶ѓ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ පаІЛථඌа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Єа¶Ња¶Вඐඌබගа¶ХаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞පаІНථаІЛටаІНටа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Х ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗ ටගථග ථඌа¶Ха¶њ а¶ЄаІНа¶ђа¶ЧටаІЛа¶ХаІНටග а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, вАШа¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Па¶Х ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶Ьඌථග ථඌ!вАЩ а¶Єа¶Ња¶Вඐඌබගа¶Х ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶Йа¶≤аІНа¶ЯаІЛ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ, вАШ а¶§а¶Ња¶єа¶≤аІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶њ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ බගа¶≤аІЗථ ථඌ а¶ХаІЗථ?вА٠ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞а¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටගථග а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, вАШа¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶њ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶≠аІЗа¶ђаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ ; а¶ХගථаІНටаІБ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓ ටටබගථаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ђаІЗප а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶ња•§ ටඌа¶З а¶Жа¶∞ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗථග !вАЩ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶Яа¶Ња¶У а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Ња¶Ха¶Ња¶Ыа¶њ а•§ а¶Па¶З а¶єаІГаІОа¶™а¶ња¶£аІНа¶° а¶Ха¶Ња¶Б඙ඌථаІЛ ඙аІЗපඌа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЪගථаІНටඌ а¶Ха¶∞ගථග а¶ѓаІЗ , ටඌ а¶®а¶Ња•§ ටඐаІЗ, බаІЗаІЬа¶ѓаІБа¶Ч а¶Па¶З ඙аІЗපඌаІЯ а¶Ха¶Ња¶Яа¶њаІЯаІЗ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓ , а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЗа¶Ыа¶њ! а¶ЫаІЗаІЬаІЗ а¶Жа¶∞ а¶ХаІА а¶єа¶ђаІЗ !
а¶Жа¶∞аІЗа¶Хබගථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶Х а¶ЕථаІБа¶Ь а¶Ха¶≤а¶ња¶ЧаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЧаІЗ а¶Хඕඌ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЄаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІЗපඌа¶Чට а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ђа¶≤аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЕථаІНටට: ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌපа¶ЧаІБа¶£ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶З, а¶Ѓа¶Ња¶∞ඌටаІНа¶Ѓа¶Х ඙аІНа¶∞аІЗපඌа¶∞ ථගаІЯаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єаІЯ ටඌа¶Ба¶ХаІЗа•§ ඁඌටаІНа¶∞ඌටගа¶∞а¶ња¶ХаІНට а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ъඌ඙аІЗ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ђаІЗප а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞а¶У පа¶∞а¶£а¶Ња¶™а¶®аІНථ යටаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓ , вАШа¶ПටаІЛ ඙аІНа¶∞аІЗපඌа¶∞ ථගаІЯаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶Ы а¶ХаІЗථ? ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶њ а¶Па¶З ඙аІЗපඌ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ බගටаІЗ а¶За¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶За¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ ථඌа¶Ха¶њ?вАЩ а¶ЄаІЗ а¶ЄаІНඁගට а¶єаІЗа¶ЄаІЗ බඌа¶∞аІБа¶£ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЙටаІНටа¶∞ බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤, вАШа¶Ьඌයගබ а¶≠а¶Ња¶З, а¶Па¶З ඙аІЗපඌ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶∞а¶ХаІНටаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඥаІБа¶ХаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З ඙аІЗපඌа¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЬаІАඐථ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓаІЗඁථ а¶ЬаІАඐථ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙ඌа¶≤ඌටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Па¶Яа¶Њ ඁඌඕඌ а¶Йа¶Ба¶ЪаІБ а¶Ха¶∞аІЗ ඪඌඁථඌඪඌඁථග බඌа¶БаІЬඌටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ, а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Я ඙аІЗපඌа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗа¶У ටඌа¶За•§ I canвАЩt quit my life !вАЩ
а¶ђа¶єаІБබගථ а¶Жа¶ЧаІЗ, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථගа¶∞ පаІНа¶∞බаІНа¶ІаІЗаІЯ а¶Єа¶ња¶За¶У¬† а¶Ѓа¶Ња¶За¶ХаІЗа¶≤ а¶ХаІЛа¶єаІНвАМ¬† а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶∞аІЗа¶ЄаІНටа¶∞а¶Ња¶БаІЯ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЬаІБаІЯа¶Ња¶≤ а¶ЃаІБа¶°аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Ьථ ඪගථගаІЯа¶∞ а¶ЃаІНඃඌථаІЗа¶Ьа¶Ња¶∞බаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ІаІНа¶ђа¶ЄаІНට а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Њ බаІЗа¶ЦаІЗ ඙ඌපаІЗа¶∞ а¶Ьථа¶ХаІЗ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ, вАШа¶Ха¶њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ?вА٠ඃඕඌа¶∞аІАටග а¶Уа¶З а¶ЃаІНඃඌථаІЗа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶У а¶Еа¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЗපඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶®а•§а¶§а¶Ња¶Ба¶∞ පඌа¶∞аІАа¶∞а¶ња¶Х а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ, а¶ђаІНа¶≤а¶Ња¶° ඙аІНа¶∞аІЗපඌа¶∞, а¶ХаІЛа¶≤аІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶∞аІЗа¶≤ а¶ЗටаІНඃඌබගа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶ђа¶Њ а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Є а¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶°аІЗ а¶ѓаІЗ ඁඌථඪගа¶Х а¶Ъඌ඙ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯප: а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶≤ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶ЃаІБපа¶Ха¶ња¶≤ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶Яගපථ, а¶Еа¶∞аІНа¶°а¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Хඁටග, а¶Еටගа¶∞а¶ња¶ХаІНට а¶Еа¶∞аІНа¶°а¶Ња¶∞, а¶ђа¶ЊаІЯа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Еа¶ѓа¶Ња¶Ъගට а¶°а¶ња¶Єа¶Ха¶Ња¶ЙථаІНа¶Я, а¶ПаІЯа¶Ња¶∞ පග඙ඁаІЗථаІНа¶Я, ඪඌ඙аІНа¶≤а¶Ња¶З-а¶ЪаІЗථаІЗа¶∞ ථඌථඌ а¶≤аІЗа¶≠аІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶Еබа¶ХаІНඣටඌ а¶У а¶Еа¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶Чගටඌ а¶ЗටаІНඃඌබග а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶Єа¶ња¶За¶У ඁථ බගаІЯаІЗ පаІБථаІЗ а¶ѓа¶Њ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ- ටගථගа¶У аІ©аІЂ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Њ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶ЊаІЯ а¶ѓа¶Цථ а¶Жа¶ЄаІЗථ, а¶Ха¶ња¶ЫаІБබගථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶Йථග а¶ЯаІЗа¶∞ ඙аІЗа¶≤аІЗථ а¶Па¶З ඙аІЗපඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ъඌ඙аІЗа¶∞а•§ а¶Йථග යටаІЛබаІНа¶ѓа¶Ѓ а¶єа¶≤аІЗථ а¶®а¶Ња•§ ථඌථඌ а¶Шඌට඙аІНа¶∞ටගа¶ШඌටаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶Цඌථ බගаІЯаІЗ а¶Йථග а¶Па¶Цථ ඐගපඌа¶≤ а¶Па¶Х ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІНа¶£а¶Іа¶Ња¶∞а•§ а¶Йථග а¶Жа¶∞а¶У а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, аІ©аІЂ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶У а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤аІЗ а¶ѓаІЗ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ъඌ඙ а¶Ыа¶ња¶≤ , ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Ыа¶ња¶≤, ටඌ а¶Па¶ЦථаІЛ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶∞а¶У аІ©аІЂ а¶ђа¶Ыа¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶Ѓ а¶Жа¶Єа¶ђаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞а¶У а¶Па¶З а¶Па¶Ха¶З а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч ඕඌа¶Ха¶ђаІЗ ! а¶ЃаІЛබаІНබඌ-а¶Хඕඌ , а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Є а¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶°аІЗа¶∞ а¶Па¶Яа¶Ња¶З а¶Еа¶ХаІГටаІНа¶∞а¶ња¶Ѓ а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња•§ а¶ѓаІБа¶Ч ඐබа¶≤а¶Ња¶≤аІЗа¶У а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ ටаІЗඁථ а¶ХаІЛථ а¶єаІЗа¶∞а¶ЂаІЗа¶∞ а¶єа¶ђаІЗ ථඌ ! ටඌа¶З а¶Па¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЃаІЗථаІЗ ථගаІЯаІЗа¶З а¶Па¶З ඙аІЗපඌаІЯ ඕඌа¶ХටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§
а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ , а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗ а¶ЖපඌඐඌබаІА යටаІЗ а¶ђа¶≤а¶ња•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙ඌප а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶З පගа¶≤аІН඙ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЪගථаІНටඌа¶У а¶Ха¶∞ට ථඌ а¶ХаІЗа¶Йа•§ а¶Еа¶ІаІБථඌ ථඐаІАථ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞ගටаІЗ ඥаІБа¶Ха¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ђа¶ња¶Єа¶ња¶Па¶Є බගаІЯаІЗ ඙аІБа¶≤ගප, ඙аІНа¶∞පඌඪථаІЗ ඥаІБа¶Ха¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ХаІЗа¶Й а¶ХаІЗа¶Й а¶Єа¶Ђа¶Яа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶ЊаІЯ а¶Єа¶Ђа¶≤ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ а¶ѓа¶Цථ а¶ЃаІЗа¶Іа¶Ња¶ђаІА а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЬаІБаІЯаІЗа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶ђаІЗаІЬаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Єа¶Ва¶ЄаІНඕඌථаІЗа¶∞ ටаІБа¶≤ථඌаІЯ, ටа¶Цථ ටඌа¶БබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬටаІЗ а¶єаІЯ а¶Жа¶∞а¶У ථඌථඌ а¶ђа¶єаІБа¶ЃаІБа¶ЦаІА а¶ЄаІЗа¶ХаІНа¶Яа¶∞аІЗа•§ а¶ХаІГа¶Ја¶њ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ХගථаІНටаІБ а¶ХаІГа¶Ја¶њ а¶Еа¶Ђа¶ња¶Єа¶Ња¶∞ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗථ а¶®а¶Ња•§ ඥඌа¶Ха¶Њ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ХගථаІНටаІБ ඙බඌа¶∞аІНඕඐගබ, а¶∞а¶Єа¶ЊаІЯථඐගබ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ , а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶≠ගටаІНටගа¶Х а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Єа¶Ва¶ЄаІНඕඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ХаІБа¶≤ඌථаІЗ а¶Ъඌ඙ а¶Жа¶ЫаІЗ ; ථඐаІАථ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЬаІБаІЯаІЗа¶ЯබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ а¶Жа¶З а¶З ( а¶ЗථаІНа¶°а¶Ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶≤ а¶За¶ЮаІНа¶ЬගථගаІЯа¶Ња¶∞а¶ња¶В) ; а¶ХаІЛаІЯа¶Ња¶≤а¶ња¶Яа¶њ а¶ХථаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЛа¶≤ а¶Єа¶є ථඌථඌ а¶ђа¶єаІБа¶ЃаІБа¶ЦаІА а¶ЄаІЗа¶ХаІНа¶Яа¶∞аІЗ ඥаІБа¶ХටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ а¶°а¶Ња¶За¶В ඀ගථගඪගа¶В а¶ђа¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ЪаІЗථаІНа¶°а¶Ња¶За¶Ьа¶ња¶В а¶Па¶∞ а¶Хඕඌ а¶ЪගථаІНටඌ ථඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ЄаІЗа¶ХаІНа¶Яа¶∞аІЗ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶ѓаІЛа¶ЧаІНඃටඌ බаІЗа¶ЦඌටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§
а¶ІаІИа¶∞аІНа¶ѓ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≠аІНа¶∞ඌථаІНටග ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඲ථаІНа¶ѓа¶ђа¶Ња¶¶а•§
඙аІНа¶∞а¶Хඌපа¶Ха¶Ња¶≤а¶Г аІІа¶≤а¶Њ а¶°а¶ња¶ЄаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞,аІ®аІ¶аІІаІђ
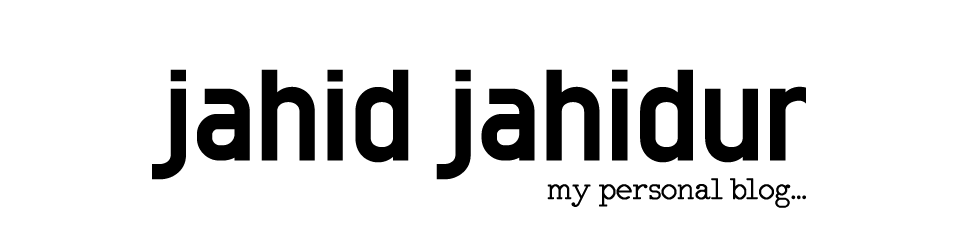
а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞ටගа¶Х ඁථаІНටඐаІНа¶ѓ