а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶ња¶ВඐබථаІНටаІА а¶Еа¶∞аІНඕථаІАටගඐගබබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ вАШа¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶њ ථаІЯ, а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌ а¶єа¶У!вАЩ вАШ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶ЊвАЩ а¶ЗටаІНඃඌබග පаІБථаІЗ පаІБථаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁටаІЛ а¶ХаІБа¶≤а¶њ а¶Ѓа¶ЬаІБа¶∞බаІЗа¶∞а¶У а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ба¶ЭаІЗ а¶ЬඌථටаІЗ а¶За¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶ПටаІЛ а¶ђаІЬ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ѓаІБа¶ХаІНටගථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶Ѓ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙ඕаІЗ а¶Ха¶њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ ! ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЃаІМа¶≤а¶ња¶Х а¶ђа¶Ња¶Іа¶Њ а¶Ха¶њ а¶Ха¶њ ; ථඐаІАථ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶њ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ ? а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ථටаІБථ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඌඐථඌ а¶Ха¶њ ?
а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට: аІ®аІ¶аІ¶аІ≠/аІЃ а¶Па¶∞ ඙а¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ පගа¶≤аІН඙ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌබаІЗа¶∞ а¶ЧаІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ѓаІЛа¶Ч බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Еа¶ІаІБථඌ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ђа¶Ыа¶∞ ඃඌඐට ටඌ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІЗа¶З а¶ЧаІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶≤а¶Ња¶Зථ ථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶њ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶£ вАШ а¶ЄаІН඙ගධ ඁඌථගвАЩ а¶Ца¶∞а¶Ъ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ; а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ පаІБථа¶≤аІЗ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶Х඙ඌа¶≤аІЗ а¶ЙආඐаІЗ ! ඐගපаІНа¶ђ а¶Еа¶∞аІНඕථаІИටගа¶Х ඁථаІНබඌ, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЬаІНа¶ђа¶Ња¶≤ඌථаІА а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я, а¶∞ඌථඌ ඙аІНа¶≤а¶Ња¶Ьа¶Њ, ටඌа¶Ьа¶∞аІАථ а¶ЂаІНඃඌපථ а¶ЯаІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶°а¶њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЄаІНටаІНа¶∞පගа¶≤аІН඙а¶ХаІЗ а¶ЦаІЛа¶≤ථа¶≤а¶ЪаІЗ ඐබа¶≤аІЗ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ђа¶≤පаІНа¶∞аІБටගටаІЗ а¶ЕථаІНඃටඁ а¶∞඙аІНටඌථаІАа¶ЃаІБа¶Ца¶њ පගа¶≤аІН඙аІЗ ථටаІБථ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶£ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ха¶ЃаІЗ а•§ ථටаІБථ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤аІЗ ථටаІБථ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌබаІЗа¶∞ ඙බа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£ ථаІЗа¶З а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶З а¶Ъа¶≤аІЗ а•§ а¶ѓа¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶ђаІЬ පගа¶≤аІН඙ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞а¶Єа¶Ња¶∞а¶£ ! а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ аІђ а¶≤а¶Ња¶Ц а¶Ча¶Ь а¶ЙаІО඙ඌබථ а¶ХаІНඣඁටඌ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ЄаІЗ а¶Па¶Х а¶Іа¶Ња¶ХаІНа¶Ха¶ЊаІЯ аІІаІ® а¶≤а¶Ња¶Ц а¶Ча¶Ь а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶ЫаІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ аІ©аІ¶ а¶≤а¶Ња¶ЗථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶Цඌථඌ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ЄаІЗ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ђа¶Ыа¶∞аІЗ аІђаІ¶ а¶≤а¶Ња¶Зථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶ЫаІЗа•§ а¶Еа¶Єа¶Ѓ а¶ЃаІВа¶≤аІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞ටගඃаІЛа¶ЧගටඌаІЯ а¶Яа¶ња¶ХටаІЗ ථඌ ඙аІЗа¶∞аІЗ а¶Еа¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓ а¶ЫаІЛа¶Я ඁඌ඙аІЗа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶У а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Є පගа¶≤аІН඙ а¶Ха¶Ња¶∞а¶Цඌථඌ ඐථаІНа¶І а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶Ња¶∞а¶њ ඁඌ඙аІЗа¶∞ а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Єа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Хඌථඌ а¶ђаІЬ а¶ЧаІНа¶∞аІБ඙а¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ђаІЬ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ඙аІНа¶∞ටගඐа¶Ыа¶∞ а¶Жа¶∞а¶У а¶ђаІГයබඌаІЯටථ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§
බаІЗаІЬ а¶ѓаІБа¶Ч а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ පаІБа¶∞аІБටаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶њ , а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Є-а¶Па¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ХබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶ЙаІО඙ඌබථ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ටඌ а¶Ыа¶ња¶≤ , а¶Хඌ඙аІЬ а¶ЙаІО඙ඌබථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶У а¶ЄаІЗа¶≤а¶Ња¶З а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЄаІАඁඌඐබаІНа¶Іа•§ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Х-а¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶° а¶≤а¶ња¶Ва¶ХаІЗа¶Ь а¶ђа¶Њ а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ а¶ЦаІБа¶Ъа¶∞а¶Њ а¶™а¶£аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Єа¶∞а¶ђа¶∞а¶Ња¶є а¶Ыа¶ња¶≤ ඙аІБа¶∞аІЛа¶Яа¶Ња¶З а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа•§ а¶ђаІЛටඌඁ, а¶ЯаІБа¶За¶≤ а¶ЯаІЗ඙, а¶≤аІЗа¶ђаІЗа¶≤, а¶ЄаІБටඌ, а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Яථ, ඙а¶≤а¶њ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ч, а¶ЄаІНа¶ХаІНа¶∞ගථ ඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Я , а¶Па¶Ѓа¶ђаІНа¶∞аІЯа¶°а¶Ња¶∞а¶њ ඃඌඐටаІАаІЯ а¶Єа¶∞а¶ђа¶∞а¶Ња¶є а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЫаІЛа¶Я ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථа¶ЧаІБа¶≤аІЛටаІЗа¶У а¶ЕථаІЗа¶Х а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Єа¶Ва¶ЄаІНඕඌථ а¶єа¶§а•§а¶Па¶Цථ а¶ђаІЬ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶ЦඌථඌаІЯ а¶Єа¶ђ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶≠а¶ња¶Є а¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Х-а¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶° а¶≤а¶ња¶Ва¶ХаІЗа¶Ь а¶За¶Йථගа¶Я а¶ЦаІБа¶≤аІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗа¶®а•§
ටඌයа¶≤аІЗ а¶Р а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞- а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶Ња¶∞а¶њ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶њ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ ? ඙аІНа¶∞ටගඃаІЛа¶ЧගටඌаІЯ а¶Яа¶ња¶ХටаІЗ ථඌ ඙аІЗа¶∞аІЗ, ඙аІБа¶∞ථаІЛа¶∞а¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Њ а¶ЧаІБа¶Яа¶њаІЯаІЗ ථගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗථ а•§ а¶Па¶ђа¶В а¶Эа¶ЮаІНа¶Эа¶Ња¶ђа¶ња¶ХаІНа¶ЈаІБа¶ђаІНа¶І а¶Жа¶ђа¶єа¶Ња¶УаІЯа¶ЊаІЯ ථටаІБථ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌа¶∞а¶Њ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ ථаІМа¶Ха¶Ња¶∞ ඙ඌа¶≤ ථඌ ටаІБа¶≤аІЗ вАШ а¶Жа¶∞ඌඁබඌаІЯа¶ХвАЩ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶ња¶∞ а¶ђа¶≤аІЯаІЗ а¶ШаІБа¶∞඙ඌа¶Х а¶Ца¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа¶®а•§
а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶У а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Є а¶ЄаІЗа¶ХаІНа¶Яа¶∞ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ а¶Жа¶Єа¶ња•§ а¶ЄаІНа¶ХаІЯа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£-а¶Жа¶∞а¶Па¶Ђа¶Па¶≤ а¶Па¶∞ ඁටаІЛ а¶ђаІЬ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථа¶ХаІЗ а¶Йබඌයа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶∞аІНඕаІЗ а¶Йබඌයа¶∞а¶£ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ а¶Іа¶∞а¶Ыа¶ња•§ а¶ЄаІНа¶ХаІЯа¶Ња¶∞-а¶Па¶∞ а¶Ђа¶Ња¶∞аІНа¶Ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶Йа¶Яа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶Є බගаІЯаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Њ පаІБа¶∞аІБа•§ ඙а¶∞аІЗ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤, ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗ а¶ЂаІБа¶° а¶У а¶ђаІЗа¶≠а¶Ња¶∞аІЗа¶Ь, а¶Ха¶Єа¶ЃаІЗа¶Яа¶ња¶ХаІНа¶Є, а¶ЯаІЯа¶≤аІЗа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Ь, යඌඪ඙ඌටඌа¶≤ а¶Єа¶ђа•§ බаІАа¶∞аІНа¶ШබගථаІЗа¶∞ а¶Па¶ХථගඣаІНආටඌаІЯ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤ а¶™а¶£аІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶∞аІНඃඌථаІНа¶° а¶≤аІЗа¶ђаІЗа¶≤ ඙аІЗаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶ѓаІЛа¶ЧаІНඃටඌ а¶Пඁථ ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶™а¶£аІНа¶ѓ а¶ЪаІЛа¶Ц а¶ђаІБа¶ЬаІЗ а¶≠аІЛа¶ХаІНටඌа¶∞а¶Њ а¶ХගථаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Пඁථ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶™а¶£аІНа¶ѓ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ѓаІЗа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌа¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђаІЗа¶Ба¶ЪаІЗ ඕඌа¶Ха¶§а•§ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶У а¶ІаІАа¶∞аІЗ а¶ІаІАа¶∞аІЗ а¶ЄаІНа¶ХаІЯа¶Ња¶∞ බа¶Ца¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ ථගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶Эа¶Ња¶≤ а¶ЃаІБаІЬа¶њ а¶ђа¶Њ а¶ЪаІАථඌඐඌබඌඁа¶У ඃබග а¶ЄаІНа¶ХаІЯа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶ђаІГа¶єаІО ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞а¶Ьඌට а¶Ха¶∞аІЗ, ටඌයа¶≤аІЗ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶≠аІЛа¶ХаІНටඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІЗа¶Й а¶Ха¶њ а¶Жа¶∞ а¶Ъа¶≤ටග а¶Эа¶Ња¶≤ а¶ЃаІБаІЬа¶ња¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ХගථඐаІЗ ?
а¶Рබගа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£-а¶Жа¶∞а¶Па¶Ђа¶Па¶≤ а¶Па¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶™а¶£аІНа¶ѓ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට: а¶Ыа¶ња¶≤, а¶Па¶Хබගа¶ХаІЗ ටа¶∞а¶≤ ඙ඌථаІАаІЯ а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ а¶єаІЗа¶≠а¶њ-а¶≤а¶Ња¶За¶Я а¶ЃаІЗපගථඌа¶∞а¶ња¶Ь, ථа¶≤а¶ХаІВ඙ а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶Па¶Цථ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ඙аІНа¶≤а¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶ХаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶ђа¶Ња¶≤ටග,ඐබථඌ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ЙаІО඙ඌබථ а¶У а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞а¶Ьඌට а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶єа¶Ња¶ЄаІНа¶ѓа¶Ха¶∞ а¶єа¶≤аІЗа¶У ඪටаІНа¶ѓ, ඙аІНа¶≤а¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶ХаІЗа¶∞ ඐබථඌ а¶ЦаІБа¶ђа¶З а¶ЫаІЛа¶Я ඁඌ඙аІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌа¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ඕඌа¶ХටаІЗа¶®а•§ а¶ѓаІЗ а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌ ඙аІНа¶≤а¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶ХаІЗа¶∞ ඐබථඌ, а¶ђа¶Ња¶≤ටග ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞ට ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Њ а¶ЧаІБа¶Яа¶њаІЯаІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Па¶Цථ а¶ЧටаІНඃථаІНටа¶∞ ථаІЗа¶З а•§ а¶ђаІНа¶∞аІНඃඌථаІНа¶° а¶За¶ЃаІЗа¶ЬаІЗ а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌа¶∞а¶Њ а¶ЕථаІЗа¶Х ඙ගа¶Ыа¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ ඙аІЗ඙ඌа¶∞ а¶У а¶За¶≤аІЗа¶Ха¶ЯаІНа¶∞ථගа¶Х а¶Ѓа¶ња¶°а¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ѓа¶∞а¶Ѓа¶Њ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌ඙ථаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶ђаІНа¶∞аІНඃඌථаІНа¶°а¶ња¶В а¶У а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђа•§
а¶ђаІЬ а¶ђаІЬ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶™а¶£аІНа¶ѓ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶У а¶ЫаІЛа¶Яа¶Ца¶Ња¶ЯаІЛ а¶Єа¶ђа¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶™а¶£аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ѓаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ බа¶Ца¶≤ а¶Ха¶∞а¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ; බаІЗа¶ЦаІЗ පаІБථаІЗ ඁථаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ , а¶ЄаІЗа¶З බගථ а¶Жа¶∞ а¶ђаІЗපග බаІБа¶∞аІЗ ථаІЗа¶З, а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶њ а¶ђаІЬ а¶Ха¶∞аІН඙аІЛа¶∞аІЗපථ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ ටඌඐаІО а¶™а¶£аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЙаІО඙ඌබථ а¶У а¶Єа¶∞а¶ђа¶∞а¶Ња¶єаІЗа¶∞ බඌаІЯගටаІНа¶ђ ථගаІЯаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗа¶®а•§ ඙аІБа¶Ба¶Ьа¶њ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶У а¶ЃаІБа¶ХаІНටඐඌа¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕථаІАටගа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЬаІНа¶Юඌ඙ථаІЗ ථаІИටගа¶Хටඌ ඙а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ ඙аІБа¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶ЫаІЗථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђаІЬ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌа¶∞а¶Ња•§
а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Жа¶Єа¶њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Ња¶За¶≤ а¶У а¶ђа¶ЄаІНටаІНа¶∞ а¶ЦඌටаІЗа•§ а¶ХаІЗථ ථටаІБථ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌබаІЗа¶∞ බаІЗа¶Ца¶Њ ථаІЗа¶З ?а¶ХаІЗථ а¶Па¶Ба¶∞а¶Њ ථටаІБථ පගа¶≤аІН඙ а¶ЄаІНඕඌ඙ථаІЗ а¶ЙаІОа¶Єа¶Ња¶єаІА а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗථ ථඌ ?
඙аІНа¶∞ඕඁට: а¶ђаІЬ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌа¶∞а¶Њ а¶ЫаІЛа¶ЯබаІЗа¶∞ а¶°а¶њ-а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ХаІЗа¶Яа¶ња¶В а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ђаІЬ а¶Ѓа¶Ња¶Ы, ඙аІБа¶ХаІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ђ а¶ЫаІЛа¶Яа¶Ѓа¶Ња¶Ыа¶ХаІЗ а¶ЦаІЗаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶ЫаІЗа•§
බаІНඐගටаІАаІЯට: а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶Х ථටаІБථ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌබаІЗа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Єа¶єа¶ЊаІЯටඌ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶Х ථගа¶∞ඌ඙බ ඐගථගаІЯаІЛа¶ЧаІЗ а¶ђаІЬ а¶Ла¶£-а¶ЦаІЗа¶≤ඌ඙ග ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථа¶ХаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ла¶£ බගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶∞ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Еа¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓ а¶ЃаІЗа¶Іа¶Ња¶ђаІА ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯ а¶ЄаІНථඌටа¶ХаІЗа¶∞а¶Њ ආගа¶Х а¶ђаІБа¶ЭаІЗ а¶ЙආටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ЫаІЗථ ථඌ , ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶њ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶У а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЄаІНඐ඙аІНථ а¶ЖබаІМ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶ХаІАථඌ, а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ! ටаІГටаІАаІЯට: (а¶Па¶Яа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට ඁටа¶У а¶ђа¶ЯаІЗ)вАФа¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Яගප а¶ХаІЗа¶∞ඌථග-ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЧаІБථටග а¶ХаІЗа¶∞ඌථаІА ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§ පට පට а¶ђаІЗа¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶њ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђаІЗපග බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ – а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶ња¶Ча¶∞а¶њ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ ථගа¶∞аІНа¶≠а¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶≤аІЯа•§ а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ, а¶Па¶Ха¶Ьථ ටа¶∞аІБа¶£а¶ХаІЗ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌ යටаІЗ а¶ЙаІОа¶Єа¶Ња¶є බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єа¶ђаІЗа•§ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶°а¶ња¶ЧаІНа¶∞аІА ,а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ ඁඌථඪගа¶Х ඙аІНа¶∞ටගඐථаІНа¶ІаІА а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЪаІЗаІЯа¶Ња¶∞ а¶У а¶ЯаІЗа¶ђа¶ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶Єа¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඌඐථඌ а¶Ьа¶≤а¶Ња¶ЮаІНа¶Ьа¶≤а¶њ බගටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටаІБට а•§
а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗප а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶У а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІАаІЯ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶≤аІНඃඌථ а¶єаІЯටаІЛ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ьඌථග ථඌ а•§ ථඌථඌ а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ ඀ඌථаІНа¶° ඕඌа¶ХаІЗ , а¶Па¶Єа¶Па¶Ѓа¶З ( Small Medium Entrepreneur) а¶Ла¶£ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Хටа¶Цඌථග ඪආගа¶Х а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ ඙аІМа¶Ба¶Ыа¶ЊаІЯ , а¶ЄаІЗ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඪථаІНබаІЗа¶є а¶Еа¶ЃаІВа¶≤а¶Х ථаІЯа•§ а¶Па¶ђа¶В ඙аІНа¶∞ටගඐа¶Ыа¶∞аІЗ а¶Уа¶З ඀ඌථаІНа¶°аІЗа¶∞ ඃඕаІЛ඙ඃаІБа¶ХаІНට а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶єаІЯ а¶Хගථඌ , а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ХаІЛථ ටඕаІНа¶ѓ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ а¶Ьඌථඌ ථаІЗа¶За•§
а¶Ха¶ња¶ЫаІБබගථ а¶Жа¶ЧаІЗ , ඐගපඌа¶≤ පගа¶≤аІН඙а¶Ха¶Ња¶∞а¶Цඌථඌа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Х а¶Па¶Х а¶ђаІЬа¶≠а¶Ња¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Хඕඌ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටගථග ථගа¶ЬаІЗа¶У а¶Ъа¶Ња¶ЗටаІЗථ, а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЄаІНа¶ХаІНа¶∞ගථ ඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Яа¶ња¶В а¶Ха¶Ња¶∞а¶Цඌථඌ , а¶≤аІЗа¶ђаІЗа¶≤, ඙а¶≤а¶њ , а¶ЯаІБа¶За¶≤ а¶ЯаІЗ඙, а¶ђа¶Ња¶Яථ , а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Яථ а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Яа¶∞а¶њ а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Яа¶∞а¶њ а¶Ъа¶Ња¶≤аІБ ඕඌа¶Ха•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ьථ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌ а¶єаІЛа¶Ха•§ а¶ЃаІБපа¶Ха¶ња¶≤ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, ටඌа¶Ба¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌ а¶Па¶З а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ЦаІБа¶ђа¶З ටගа¶ХаІНට ! ටගථග а¶єаІЯටаІЛ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ ඁඌථаІЗа¶∞ а¶ЄаІБටඌ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЯаІБа¶За¶≤ а¶ЯаІЗ඙ а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓа•§ а¶ХගථаІНටаІБ , а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌ а¶Еටග а¶≤аІЛа¶≠аІЗ , а¶Ѓа¶Ња¶Э඙ඕаІЗа¶З а¶Ча¶ЊаІЬаІАа¶Єа¶є а¶ЄаІЗа¶З а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ ඁඌථаІЗа¶∞ а¶ЄаІБටඌ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ ඙а¶∞аІЗ, බаІБථගаІЯа¶Ња¶∞ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶ЈаІНа¶Я а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЄаІБටඌ а¶ХගථаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЯаІБа¶За¶≤ а¶ЯаІЗ඙ ඐඌථගаІЯаІЗ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Ђа¶≤පаІНа¶∞аІБටගටаІЗ а¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶ђа¶∞аІЗа¶Яа¶∞а¶ња¶∞ ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ а¶ЧаІБа¶£а¶Чට ඁඌථаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Є а¶ЂаІЗа¶≤ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶Па¶Ха¶З а¶Хඕඌ а¶ЕථаІНа¶ѓа¶Єа¶ђ а¶ђаІЬ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ, а¶Па¶Ба¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗ බඌඁаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶ЫаІЛа¶ЯබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ බаІЗаІЯа•§ ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ඃබග ඪආගа¶Х а¶Й඙ඌබඌථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞ට ටඌයа¶≤аІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶®а¶Ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ, а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Еටගа¶≤аІЛа¶≠аІА බаІНа¶∞аІБට а¶ЃаІБථඌ඀ඌ а¶Ха¶Ња¶ЃаІА а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІГටа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ බඌаІЯ ථගටаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯපа¶З а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌа¶∞а¶Њ а¶≠аІЗа¶Ьа¶Ња¶≤ а¶У ථගඁаІНථඁඌථаІЗа¶∞ а¶Й඙ඌබඌථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђаІЬ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථа¶ХаІЗ ඐග඙බаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶њ, ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶ЄаІБටඌ, а¶ђаІЛටඌඁ, а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶Яථ, а¶ЯаІБа¶За¶≤ а¶ЯаІЗ඙, а¶ЄаІНа¶ХаІНа¶∞ගථ ඙аІНа¶∞ගථаІНа¶Я а¶ЂаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНа¶Яа¶∞а¶ња¶∞ а¶ЧаІБа¶£а¶Чට ඁඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ а¶Еඕඐඌ а¶Єа¶∞а¶ђа¶∞а¶Ња¶єаІЗ බаІЗа¶∞аІА а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Є а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Ха¶ХаІЗ а¶°а¶ња¶Єа¶Ха¶Ња¶ЙථаІНа¶Я а¶У а¶ПаІЯа¶Ња¶∞ පග඙ඁаІЗථаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ьа¶∞ගඁඌථඌ а¶ЧаІБථටаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§
බаІНа¶∞аІБට а¶ђаІЬа¶≤аІЛа¶Х а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶У а¶Еටගа¶∞а¶ња¶ХаІНට а¶ЃаІБථඌ඀ඌа¶∞ а¶≤аІЛа¶≠аІЗ ඙аІЬаІЗ а¶ІаІАа¶∞аІЗ а¶ІаІАа¶∞аІЗ а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞ а¶ЙබаІНа¶ѓаІЛа¶ХаІНටඌа¶∞а¶Њ а¶ђаІЬ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථаІЗа¶∞ а¶≠а¶∞а¶Єа¶Њ а¶єа¶Ња¶∞а¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Па¶Цථ а¶ђаІЬ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶Цඌථඌа¶∞ а¶Еа¶≠аІНඃථаІНටа¶∞аІЗа¶З а¶Єа¶ђ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Х а¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶° а¶≤а¶ња¶Ва¶ХаІЗа¶Ь а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ХаІЗථථඌ, ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њаІЯථ а¶°а¶≤а¶Ња¶∞аІЗа¶∞ පග඙ඁаІЗථаІНа¶Я ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶ХаІЯаІЗа¶Х ඙аІЯа¶Єа¶Ња¶∞ а¶ЕаІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶ЄаІЗа¶Єа¶∞а¶ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶єаІБа¶Ѓа¶Ха¶ња¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗ а¶Ъඌථ а¶®а¶Ња•§
а¶Па¶З බаІБа¶ЈаІНа¶Яа¶Ъа¶ХаІНа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ , а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶ХаІА а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Ча¶ђаІЗа¶Ја¶£а¶Њ а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶Йа¶Ъа¶њаІО а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Ьඌථඌа¶∞ а¶Жа¶Ха¶Ња¶ЩаІНа¶ХаІНа¶Ја¶Њ ථගаІЯаІЗа¶З පаІЗа¶Ј а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъа¶®а¶Ња•§
඙аІНа¶∞а¶Хඌපа¶Ха¶Ња¶≤а¶Г аІІаІ¶а¶З а¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Ъ, аІ®аІ¶аІІаІ≠
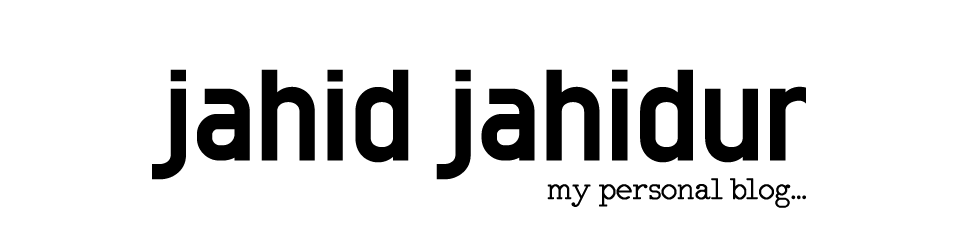
а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞ටගа¶Х ඁථаІНටඐаІНа¶ѓ