ЯдЋЯд┐ЯдЏЯДЂЯддЯд┐Яде ЯдєЯдЌЯДЄ ЯдфЯДЇЯд░ЯдЦЯд« ЯдХЯДЇЯд░ЯДЄЯдБЯДђЯд░ ЯдфЯдЙЯдаЯДЇЯд»ЯдфЯДЂЯдИЯДЇЯдцЯдЋЯДЄ ЯдЁЯдЋЯДЇЯдиЯд░ ЯдфЯд░Яд┐ЯдџЯДЪЯДЄ РђўЯдЊРђЎ ЯдЁЯдЋЯДЇЯдиЯд░ЯДЄЯд░ ЯдюЯдеЯДЇЯд» РђўЯдЊЯДюЯдеЯдЙ ЯдџЯдЙЯдЄ ЯдгЯдЙЯдЋЯДЇЯд» ЯдгЯДЇЯд»ЯдгЯд╣ЯдЙЯд░ ЯдЋЯд░ЯдЙ Яд╣ЯДЪЯДЄЯдЏЯДЄЯЦц ЯдгЯдЏЯд░ЯДЄЯд░ ЯдХЯДЂЯд░ЯДЂЯдцЯДЄ ЯдфЯДЇЯд░ЯдЙЯдџЯДђЯде ЯдЊ ЯдфЯДЇЯд░ЯдЌЯдцЯд┐ЯдХЯДђЯд▓ЯддЯДЄЯд░ Яд«ЯдДЯДЇЯд»ЯДЄ ЯдХЯДЂЯд░ЯДЂ Яд╣ЯДЪЯДЄЯдЏЯДЄ ЯдгЯдЙЯддЯдЙЯдеЯДЂЯдгЯдЙЯддЯЦц ЯдИЯдЙЯд«ЯдЙЯдюЯд┐ЯдЋ Яд»ЯДІЯдЌЯдЙЯд»ЯДІЯдЌ Яд«ЯдЙЯдДЯДЇЯд»Яд«ЯдЌЯДЂЯд▓ЯДІЯдцЯДЄ Яд»ЯДЄ ЯдЋЯДІЯде ЯдЄЯдИЯДЇЯд»ЯДЂ ЯдеЯд┐ЯДЪЯДЄ Яд╣ЯДѕЯдџЯДѕ ЯддЯДЂЯдЄ-ЯдЈЯдЋЯддЯд┐ЯдеЯДЄЯд░ ЯдгЯДЄЯдХЯДђ ЯдЦЯдЙЯдЋЯДЄ ЯдеЯдЙЯЦц ЯдЈЯдќЯде Яд»ЯДЄЯд╣ЯДЄЯдцЯДЂ ЯдгЯДЇЯд»ЯдЙЯдфЯдЙЯд░ЯдЪЯдЙ ЯдИЯдгЯдЙЯдЄ ЯдГЯДЂЯд▓ЯДЄ Яд»ЯДЄЯдцЯДЄ ЯдгЯдИЯДЄЯдЏЯДЄ , ЯдєЯд«Яд┐ ЯдєЯд«ЯдЙЯд░ ЯдЋЯд░ЯДЇЯдфЯДІЯд░ЯДЄЯдЪ ЯдЁЯдгЯдюЯдЙЯд░ЯДЇЯдГЯДЄЯдХЯдеЯДЄ ЯдЊЯДюЯдеЯдЙ ЯдЊ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђЯддЯДЄЯд░ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд« ЯдфЯд░Яд┐ЯдгЯДЄЯдХ ЯдеЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯддЯДЂЯДЪЯДЄЯдЋ ЯдЋЯдЦЯдЙ ЯдгЯд▓ЯдцЯДЄЯдЄ ЯдфЯдЙЯд░Яд┐ЯЦц
ЯдфЯдЙЯд░Яд┐ЯдгЯдЙЯд░Яд┐ЯдЋ Яд«ЯДѓЯд▓ЯДЇЯд»ЯдгЯДІЯдД ЯдЦЯДЄЯдЋЯДЄЯдЄ ЯдЋЯдеЯДЇЯд»ЯдЙ-ЯдХЯд┐ЯдХЯДЂЯддЯДЄЯд░ЯдЋЯДЄ ЯдЊЯДюЯдеЯдЙ ЯдЊ ЯдЊЯДюЯдеЯдЙ ЯддЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдгЯДЂЯдЋ ЯдбЯДЄЯдЋЯДЄ Яд░ЯдЙЯдќЯдЙЯд░ ЯдгЯДЇЯд»ЯдЙЯдфЯдЙЯд░ЯдЪЯдЙ ЯдХЯДЄЯдќЯдЙЯдеЯДІ Яд╣ЯДЪЯЦц ЯдфЯДЂЯд░ЯДІ ЯдгЯДЇЯд»ЯдЙЯдфЯдЙЯд░ЯдЪЯд┐ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђЯд░ ЯддЯДЇЯдгЯд┐ЯдцЯДђЯДЪ ЯдХЯДЇЯд░ЯДЄЯдБЯд┐Яд░ ЯдеЯдЙЯдЌЯд░Яд┐ЯдЋЯдцЯДЇЯдг, ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдеЯд┐Яд░ЯдЙЯдфЯдцЯДЇЯдцЯдЙЯд╣ЯДђЯдеЯдцЯдЙ, ЯдДЯд░ЯДЇЯд«ЯДђЯДЪ ЯдЁЯдеЯДЂЯдХЯдЙЯдИЯде ЯдЊ Яд«ЯдЙ-ЯдќЯдЙЯд▓ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдЁЯдцЯДђЯдц ЯдцЯд┐ЯдЋЯДЇЯдц ЯдЁЯдГЯд┐ЯдюЯДЇЯдъЯдцЯдЙЯд░ ЯдИЯдѓЯд«Яд┐ЯдХЯДЇЯд░ЯдБЯДЄ Яд╣ЯДЪЯДЄ ЯдЦЯдЙЯдЋЯДЄЯЦц ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдЁЯдгЯддЯд«ЯдеЯДЄЯд░ ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди ЯдХЯдЙЯдИЯд┐Ядц ЯдИЯд«ЯдЙЯдюЯДЄ ЯдЈЯдЋЯдюЯде ЯдгЯд┐ЯдфЯд░ЯДђЯдц Яд▓Яд┐ЯдЎЯДЇЯдЌЯДЄЯд░ Яд«ЯдЙЯдеЯДЂЯдиЯдЋЯДЄ ЯддЯДЄЯдќЯдЙЯд░ ЯддЯДЃЯдиЯДЇЯдЪЯд┐ЯдГЯдЎЯДЇЯдЌЯд┐ ЯдгЯДЄЯдХ ЯдЈЯдЋЯдЪЯдЙ ЯдЁЯддЯДЇЯдГЯДЂЯдцЯДЂЯДюЯДЄ ЯдЅЯдфЯдЙЯДЪЯДЄ ЯдцЯДѕЯд░Яд┐ Яд╣ЯДЪ ЯЦц ЯдфЯДЇЯд░ЯдЦЯд«Ядц: Яд»ЯДїЯдеЯдцЯдЙ ЯдЊ ЯдцЯдЙЯд░ Яд»ЯДЄ ЯдЋЯДІЯде ЯдєЯд▓ЯДІЯдџЯдеЯдЙ ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдИЯд«ЯдЙЯдюЯДЄ ЯдеЯд┐ЯдиЯд┐ЯддЯДЇЯдД ЯдЊ ЯдЪЯДЇЯд»ЯдЙЯдгЯДЂЯЦц ЯдєЯдЌЯДЄЯдЊ ЯдЏЯд┐Яд▓ , ЯдЈЯдќЯдеЯДІ ЯдЈЯдЄ Яд«ЯДЂЯдЋЯДЇЯдц ЯдЁЯдеЯДЇЯдцЯд░ЯДЇЯдюЯдЙЯд▓ЯДЄЯд░ ЯдИЯд«ЯДЪЯДЄЯдЊ ЯдєЯдЏЯДЄЯЦц ЯддЯДЇЯдгЯд┐ЯдцЯДђЯДЪЯдц: ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ-ЯдХЯд┐ЯдХЯДЂЯдЪЯд┐ Яд»ЯДЄ ЯдеЯд┐ЯдюЯДЄЯд░ ЯдфЯд░Яд┐ЯдгЯдЙЯд░ЯДЄЯд░ ЯдфЯд┐ЯдцЯдЙ ЯдЊ ЯдГЯдЙЯдЄ ЯдЏЯдЙЯДюЯдЙ ЯдфЯДЃЯдЦЯд┐ЯдгЯДђЯд░ ЯдЁЯдеЯДЇЯд» ЯдИЯдЋЯд▓ ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯдиЯДЄЯд░ ЯдЋЯдЙЯдЏЯДЄ ЯдЁЯдеЯд┐Яд░ЯдЙЯдфЯдд ЯдИЯДЄЯдЪЯдЙ Яд«ЯдЙ, ЯдќЯдЙЯд▓ЯдЙЯд░ЯдЙ ЯдЌЯДЇЯд░ЯдЙЯд«ЯДЄЯд░ ЯдЈЯдЋЯдЪЯд┐ ЯдХЯд┐ЯдХЯДЂЯдЋЯДЄ ЯдХЯд┐ЯдќЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдфЯДюЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯддЯд┐ЯдцЯДЄ ЯдЈЯдЋЯддЯд« ЯддЯДЄЯд░ЯДђ ЯдЋЯд░ЯДЄЯде ЯдеЯдЙЯЦц
ЯдЈЯдЋЯдЄ ЯдИЯдЎЯДЇЯдЌЯДЄ ЯдЌЯДЇЯд░ЯдЙЯд«ЯДЄЯд░ ЯдЈЯдЋЯдЪЯд┐ ЯдЏЯДЄЯд▓ЯДЄ ЯдЋЯДђЯдГЯдЙЯдгЯДЄ Яд»ЯДЄЯде ЯдюЯДЄЯдеЯДЄ ЯдФЯДЄЯд▓ЯДЄ– ЯдЁЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдБЯДЇЯд» , ЯдЁЯдфЯддЯдЙЯд░ЯДЇЯдЦ ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди Яд╣Яд▓ЯДЄЯдЊ, ЯдХЯДЂЯдДЯДЂЯд«ЯдЙЯдцЯДЇЯд░ ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди Яд╣ЯдЊЯДЪЯдЙЯдЊ ЯдЈЯдЋЯдЪЯдЙ ЯдгЯд┐ЯдХЯдЙЯд▓ ЯдИЯДїЯдГЯдЙЯдЌЯДЇЯд» ЯдЊ ЯдЌЯДЂЯдБЯЦц ЯдЈЯдгЯдѓ Яд«ЯДЄЯДЪЯДЄЯдЪЯд┐Яд░ ЯдЋЯДЇЯдиЯДЄЯдцЯДЇЯд░ЯДЄ ЯдаЯд┐ЯдЋ ЯдЅЯд▓ЯДЇЯдЪЯДІЯЦц ЯдфЯДЂЯдцЯДЇЯд░ЯдИЯдеЯДЇЯдцЯдЙЯде ЯдфЯДЇЯд░ЯдИЯдгЯдЋЯдЙЯд░ЯДђ ЯдюЯдеЯдеЯДђЯддЯДЄЯд░ ЯддЯдЙЯд« ЯдгЯДЄЯдХЯДђЯЦц ЯДЕ/ЯДф ЯдЪЯд┐ ЯдЋЯдеЯДЇЯд»ЯдЙ ЯдИЯдеЯДЇЯдцЯдЙЯдеЯДЄЯд░ ЯдфЯд░ ЯдЈЯдЋЯдЪЯд┐ ЯдфЯДЂЯдцЯДЇЯд░ЯдИЯдеЯДЇЯдцЯдЙЯдеЯДЄЯд░ ЯдюЯдеЯДЇЯд« ЯдЁЯдЦЯдгЯдЙ ЯдєЯд░ЯДЄЯдЋЯдюЯде ЯдцЯд░ЯДЂЯдБЯДђЯдЋЯДЄ ЯдИЯд«ЯДЇЯдГЯДІЯдЌ ЯдЋЯд░ЯДЄ ЯдфЯДЂЯдцЯДЇЯд░Яд▓ЯдЙЯдГЯДЄЯд░ ЯдўЯдЪЯдеЯдЙ Яд╣Яд░Яд╣ЯдЙЯд«ЯДЄЯдХЯдЙЯдЄ ЯдўЯдЪЯдЏЯДЄЯЦц ЯдЌЯДЇЯд░ЯдЙЯд«ЯДЄ ЯдгЯд┐ЯДЪЯДЄЯд░ ЯдЋЯДЇЯдиЯДЄЯдцЯДЇЯд░ЯДЄ ЯдфЯдБЯДЇЯд»ЯДЄЯд░ ЯдгЯд┐ЯдџЯдЙЯд░-Яд«ЯДѓЯд▓ЯДЇЯд»ЯДЄ ЯдИЯдгЯдџЯДЄЯДЪЯДЄ ЯдеЯд┐Яд░ЯДЇЯдгЯДІЯдД, ЯдЅЯдеЯДЇЯд«ЯдЙЯдд Яд»ЯдЙЯдЄ Яд╣ЯДІЯдЋ ЯдеЯдЙ ЯдЋЯДЄЯде, ЯдЈЯдЋЯдюЯде Яд»ЯДЂЯдгЯдЋЯДЄЯд░ ЯдюЯдеЯДЇЯд» ЯдфЯдЙЯдцЯДЇЯд░ЯДђ ЯдаЯд┐ЯдЋЯдЄ ЯдюЯДЂЯдЪЯДЄ Яд»ЯдЙЯДЪЯЦц ЯдЁЯдЦЯдџ, ЯдИЯдџЯДЇЯдЏЯд▓ ЯдфЯд░Яд┐ЯдгЯдЙЯд░ЯДЄЯд░ Яд«ЯдЙЯдЮЯдЙЯд░Яд┐ ЯдџЯДЄЯд╣ЯдЙЯд░ЯдЙЯд░ ЯдгЯдЙ ЯдХЯДЇЯд»ЯдЙЯд«Яд▓ЯдЙ Яд«ЯДЄЯДЪЯДЄЯддЯДЄЯд░ ЯдфЯдЙЯдцЯДЇЯд░ЯдИЯДЇЯдЦ ЯдЋЯд░ЯдцЯДЄЯдЊ Яд╣Яд┐Яд«ЯдИЯд┐Яд« ЯдќЯДЄЯдцЯДЄ Яд╣ЯДЪ ЯдфЯДЂЯд░ЯДІ ЯдфЯд░Яд┐ЯдгЯдЙЯд░ЯдЋЯДЄЯЦц
ЯдЋЯДЪЯДЄЯдЋЯдЪЯд┐ ЯдХЯд┐ЯдЋЯДЇЯдиЯд┐Ядц ЯдИЯдѓЯдИЯДЇЯдЋЯДЃЯдцЯд«ЯдеЯдЙ ЯдюЯДЄЯд▓ЯдЙ ЯдЏЯдЙЯДюЯдЙ ЯдгЯДЄЯдХЯд┐Яд░ЯдГЯдЙЯдЌ ЯдюЯДЄЯд▓ЯдЙ ЯдХЯд╣Яд░ЯдЌЯДЂЯд▓ЯДІЯд░ ЯдИЯдЙЯд«ЯдЙЯдюЯд┐ЯдЋ Яд«ЯДѓЯд▓ЯДЇЯд»ЯдгЯДІЯдД ЯдЌЯДюЯДЄ ЯдцЯДІЯд▓ЯдЙЯд░ ЯдюЯдЙЯДЪЯдЌЯдЙЯдЪЯдЙ ЯдГЯДђЯдиЯдБЯдГЯдЙЯдгЯДЄЯдЄ ЯддЯДЂЯд░ЯДЇЯдгЯд▓ЯЦц ЯдеЯдЙ ЯдєЯдЏЯДЄ ЯдГЯдЙЯд▓ЯДІ ЯдЋЯДІЯде ЯдЋЯДЇЯд▓ЯдЙЯдг, ЯдеЯдЙ ЯдєЯдЏЯДЄ Яд▓ЯдЙЯдЄЯдгЯДЇЯд░ЯДЄЯд░Яд┐ ЯдеЯдЙ ЯдєЯдЏЯДЄ ЯдИЯДЂЯдИЯДЇЯдЦ ЯдИЯдѓЯдИЯДЇЯдЋЯДЃЯдцЯд┐Яд░ ЯдџЯд░ЯДЇЯдџЯдЙЯЦц ЯдгЯдЙЯдѓЯд▓ЯдЙЯддЯДЄЯдХЯДЄЯд░ ЯдеЯдЙЯдеЯдЙ ЯдфЯДЇЯд░ЯдЙЯдеЯДЇЯдц ЯдЦЯДЄЯдЋЯДЄ ЯдєЯдИЯдЙ ЯдЏЯДЄЯд▓ЯДЄЯд░ЯдЙ ЯдЋЯд▓ЯДЄЯдюЯДЄ ЯдЊ ЯдгЯд┐ЯдХЯДЇЯдгЯдгЯд┐ЯддЯДЇЯд»ЯдЙЯд▓ЯДЪЯДЄ ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдИЯд╣ЯдфЯдЙЯдаЯДђ ЯдЏЯд┐Яд▓ЯЦц ЯдЈЯдЂЯддЯДЄЯд░ ЯдИЯдЎЯДЇЯдЌЯДЄ ЯдџЯд▓ЯДЄ ЯдгЯДЂЯдЮЯдцЯДЄ ЯдфЯдЙЯд░Яд┐ ЯдЊЯдЂЯддЯДЄЯд░ ЯдЋЯДѕЯдХЯДІЯд░ ЯдєЯд░ ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдбЯдЙЯдЋЯдЙ ЯдХЯд╣Яд░ЯДЄЯд░ ЯдгЯДЄЯДюЯДЄ ЯдЊЯдаЯдЙ ЯдЋЯДѕЯдХЯДІЯд░ЯДЄ ЯдгЯДю ЯдЋЯДІЯде ЯдфЯдЙЯд░ЯДЇЯдЦЯдЋЯДЇЯд» ЯдеЯДЄЯдЄЯЦц ЯдцЯдгЯДЄ ЯдЋЯд┐ЯдЏЯДЂ ЯдюЯДЄЯд▓ЯдЙ ЯдХЯд╣Яд░ЯДЄ ЯдДЯд░ЯДЇЯд«ЯДЄЯд░ ЯдфЯДЇЯд░ЯдЋЯДІЯдф ЯдгЯДЄЯдХЯДђ, ЯдфЯд░ЯДЇЯддЯдЙЯдфЯДЇЯд░ЯдЦЯдЙ ЯдгЯДЄЯдХЯДђЯЦц ЯдИЯДЄЯдќЯдЙЯдеЯДЄ ЯдЁЯдеЯДЄЯдЋЯдЋЯДЄ ЯдХЯДѕЯдХЯдг ЯдЋЯДѕЯдХЯДІЯд░ЯДЄ ЯдгЯДю ЯдЈЯдЋЯдЪЯдЙ ЯдЁЯдѓЯдХЯДЄ ЯдгЯДЄЯДюЯДЄ ЯдЅЯдаЯдцЯДЄ Яд╣ЯДЪЯДЄ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ-ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯдиЯДЄЯд░ ЯдИЯДЇЯдгЯдЙЯдГЯдЙЯдгЯд┐ЯдЋ ЯдИЯд«ЯДЇЯдфЯд░ЯДЇЯдЋЯДЄ ЯдЈЯдЋЯд«ЯДЂЯдќЯДђ ЯдЁЯдюЯДЇЯдъЯдЙЯдеЯдцЯдЙ ЯдеЯд┐ЯДЪЯДЄЯЦц Яд«ЯдФЯдЃЯдИЯДЇЯдгЯд▓ЯДЄ ЯдгЯДЄЯДюЯДЄ ЯдЊЯдаЯдЙ ЯдєЯд«ЯдЙЯд░ ЯдЈЯдЋ ЯддЯДЂЯдЃЯдИЯд«ЯДЇЯдфЯд░ЯДЇЯдЋЯДЄЯд░ Яд«ЯдЙЯд«ЯдЙЯд░ ЯдЋЯдЦЯдЙ Яд«ЯдеЯДЄ ЯдфЯДюЯдЏЯДЄЯЦц ЯдцЯд┐ЯдеЯд┐ ЯдИЯдЙЯд░ЯдЙЯдюЯДђЯдгЯде ЯдгЯДЪЯДЄЯдю ЯдИЯДЇЯдЋЯДЂЯд▓, ЯдгЯДЪЯДЄЯдю ЯдЋЯд▓ЯДЄЯдю ЯдЋЯд░ЯДЄ ЯдфЯДЇЯд░ЯдЙЯДЪ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдгЯд┐ЯдгЯд░ЯДЇЯдюЯд┐Ядц ЯдюЯДђЯдгЯде Яд»ЯдЙЯдфЯде ЯдЋЯд░ЯДЄЯдЏЯд┐Яд▓ЯДЄЯдеЯЦц ЯдгЯд┐ЯДЪЯДЄЯд░ ЯдфЯд░ЯДЄ ЯдеЯдцЯДЂЯде Яд«ЯдЙЯд«ЯДђЯд░ ЯдфЯДЇЯд░ЯдцЯд┐ЯдЪЯдЙ ЯдџЯдЙЯд▓ЯдџЯд▓Яде ЯдЊ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдЋЯдЙЯдБЯДЇЯдА ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдЋЯдЙЯдЏЯДЄ ЯдгЯд┐ЯдИЯДЇЯд«ЯДЪЯдЋЯд░ Яд«ЯдеЯДЄ Яд╣ЯдцЯЦц ЯдЈЯдЋЯдюЯде ЯдЁЯдДЯд░ЯдЙ ЯдєЯдЋЯдЙЯдЎЯДЇЯдЋЯДЇЯдиЯд┐Ядц ЯдеЯдЙЯд░ЯДђЯдЊ Яд»ЯДЄ ЯдќЯдЙЯдЊЯДЪЯдЙ ЯддЯдЙЯдЊЯДЪЯдЙЯд░ ЯдфЯдЙЯдХЯдЙЯдфЯдЙЯдХЯд┐ ЯдєЯд░ ЯдИЯдгЯдЙЯд░ Яд«ЯдцЯДІ Яд«Яд▓-Яд«ЯДѓЯдцЯДЇЯд░ ЯдцЯДЇЯд»ЯдЙЯдЌ ЯдЋЯд░ЯДЄ, ЯдгЯдЙЯДЪЯДЂ ЯдцЯДЇЯд»ЯдЙЯдЌ ЯдЋЯд░ЯДЄ ЯдИЯДЄЯдЪЯдЙ ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдДЯдЙЯд░ЯдБЯдЙЯд░ ЯдгЯдЙЯдЄЯд░ЯДЄ ЯдЏЯд┐Яд▓ ! ЯдеЯдцЯДЂЯде Яд«ЯдЙЯд«ЯДђЯдЋЯДЄ ЯдеЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдєЯддЯд┐ЯдќЯДЇЯд»ЯДЄЯдцЯдЙ ЯдЏЯд┐Яд▓ ЯддЯДЄЯдќЯдЙЯд░ Яд«ЯдцЯДІЯЦц ЯдфЯДЇЯд░ЯдЙЯДЪЯдХ: ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдХЯДЂЯдеЯдцЯДЄ Яд╣ЯДІЯдцЯДІ, ЯдюЯдЙЯдеЯд┐ЯдИ ЯдєЯдю ЯдцЯДІЯд░ Яд«ЯдЙЯд«ЯДђ ЯдЈЯдЄЯдЪЯдЙ ЯдЋЯд░ЯДЄЯдЏЯДЄ ! ЯдюЯдЙЯдеЯд┐ЯдИ, ЯдєЯдю ЯдцЯДІЯд░ Яд«ЯдЙЯд«ЯДђ ЯдИЯДЄЯдЄЯдЪЯдЙ ЯдЋЯд░ЯДЄЯдЏЯДЄЯЦц ЯдєЯд«Яд░ЯдЙ ЯдЋЯд┐ЯдХЯДІЯд░ ЯдгЯДЪЯдИЯДЄЯдЄ ЯдгЯд┐Яд░ЯдЋЯДЇЯдц ЯдгЯДІЯдД ЯдЋЯд░ЯдцЯдЙЯд«ЯЦц
ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдХЯд╣ЯДЂЯд░ЯДЄ ЯдЏЯДЄЯд▓ЯДЄЯддЯДЄЯд░ ЯдЋЯДѕЯдХЯДІЯд░ЯДЄЯд░ ЯддЯДЂЯдЃЯдИЯд╣ЯдцЯдЙ ЯдЏЯд┐Яд▓ЯЦц ЯдцЯдгЯДЂЯдЊ ЯдИЯдѓЯдќЯДЇЯд»ЯдЙ ЯдЌЯд░Яд┐ЯдиЯДЇЯдаЯд░ЯдЙ ЯдЈЯдЋЯдЪЯдЙ Яд«ЯдЙЯдеЯдИЯд┐ЯдЋ ЯдИЯДЇЯдЦЯд┐ЯдцЯд┐Яд░ Яд«ЯдДЯДЇЯд» ЯддЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдгЯДЄЯДюЯДЄ ЯдЅЯдаЯДЄЯдЏЯд┐ЯЦц Яд«ЯдДЯДЇЯд»ЯдгЯд┐ЯдцЯДЇЯдц ЯдгЯдЙЯдгЯдЙ-Яд«ЯдЙЯДЪЯДЄЯд░ЯдЙ, Яд«Яд╣Яд▓ЯДЇЯд▓ЯдЙЯд░ Яд«ЯДЂЯд░ЯдгЯДЇЯдгЯДђЯд░ЯдЙ, ЯдЋЯДІ-ЯдЈЯдАЯДЂЯдЋЯДЄЯдХЯде ЯдЁЯдЦЯдгЯдЙ ЯдЋЯДІЯдџЯд┐Ядѓ Яд▓ЯДЄЯдГЯДЄЯд▓ЯДЄЯдЄ Яд«ЯДЄЯДЪЯДЄЯддЯДЄЯд░ ЯдИЯдѓЯдЌЯДЄ ЯдџЯд▓ЯдЙЯдФЯДЄЯд░ЯдЙ ЯдЈЯдЋЯдЪЯдЙ ЯдИЯДЇЯдгЯдЙЯдГЯдЙЯдгЯд┐ЯдЋ ЯддЯДЃЯдиЯДЇЯдЪЯд┐ЯдГЯдЎЯДЇЯдЌЯд┐ ЯдЌЯДюЯДЄ ЯдЅЯдаЯдцЯДЄ ЯдИЯдЙЯд╣ЯдЙЯд»ЯДЇЯд» ЯдЋЯд░ЯДЄЯдЏЯд┐Яд▓ЯЦц ЯдЁЯд▓ЯДЇЯдфЯдгЯд┐ЯдИЯДЇЯдцЯд░ ЯдгЯд┐ЯдЋЯДЃЯдцЯд┐ Яд»ЯДЄ ЯдЏЯд┐Яд▓ ЯдеЯдЙ , ЯдцЯдЙЯдЊ ЯдгЯд▓Ядг ЯдеЯдЙЯЦц
ЯдЋЯд┐ЯдЏЯДЂЯддЯд┐Яде ЯдєЯдЌЯДЄ ЯдєЯд«Яд┐, ЯдєЯд«ЯдЙЯд░ ЯдИЯДЇЯдцЯДЇЯд░ЯДђ, ЯдєЯд░ ЯддЯдХ ЯдгЯдЏЯд░ЯДЄЯд░ ЯдЋЯдеЯДЇЯд»ЯдЙ ЯдгЯдЙЯдИ ЯдИЯДЇЯдЪЯДЇЯд»ЯдЙЯдеЯДЇЯдАЯДЄ ЯддЯдЙЯдЂЯДюЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдЏЯд┐Яд▓ЯдЙЯд«ЯЦц ЯдєЯд«ЯдЙЯд░ ЯдИЯДЇЯдцЯДЇЯд░ЯДђ Яд╣ЯдаЯдЙЯДј ЯдЋЯд░ЯДЄ Яд«ЯДЄЯДЪЯДЄЯдЋЯДЄ ЯдєЯд░ЯДІ ЯдЋЯдЙЯдЏЯДЄ ЯдЪЯДЄЯдеЯДЄ ЯдеЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдЊЯд░ ЯдфЯд░Яд┐ЯдДЯДЄЯДЪ ЯдЋЯдЙЯдфЯДю ЯдаЯд┐ЯдЋ ЯдЋЯд░ЯДЄ ЯддЯд┐Яд▓ ЯдєЯд░ ЯдєЯд«ЯдЙЯдЋЯДЄ ЯдеЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдЈЯдЋЯдЪЯДЂ ЯддЯДЂЯд░ЯДЄ ЯдЌЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯддЯдЙЯдЂЯДюЯдЙЯд▓ЯЦц ЯдєЯд«Яд┐ ЯдЈЯдЋЯдЪЯДЂ ЯдЁЯдгЯдЙЯдЋ ЯдџЯДІЯдќЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЋЯдЙЯд▓ЯДЄ ЯдцЯДјЯдЋЯДЇЯдиЯдБЯдЙЯДј ЯдЋЯДІЯде ЯдЅЯдцЯДЇЯдцЯд░ ЯдфЯдЙЯдЊЯДЪЯдЙ ЯдЌЯДЄЯд▓ ЯдеЯдЙЯЦц ЯдФЯДЄЯд░ЯдЙЯд░ ЯдфЯдЦЯДЄ ЯдюЯдЙЯдеЯдЙЯд▓ЯДІ, ЯдєЯд«ЯдЙЯд░ ЯдаЯд┐ЯдЋ ЯдфЯд┐ЯдЏЯде ЯдЦЯДЄЯдЋЯДЄ ЯдЈЯдЋ Яд«ЯдЙЯдЮЯдгЯДЪЯдИЯДђ ЯдгЯд┐ЯдЋЯДЃЯдц ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди ЯдеЯдЙЯдЋЯд┐ ЯдюЯДЂЯд▓ЯдюЯДЂЯд▓ ЯдЋЯд░ЯДЄ ЯдЋЯдеЯДЇЯд»ЯдЙЯд░ ЯддЯд┐ЯдЋЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЋЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдЏЯд┐Яд▓! ЯдЋЯДЄЯдЅ ЯдцЯдЙЯдЋЯдЙЯд▓ЯДЄ ЯдЋЯДђ ЯдЋЯд░ЯдгЯДЄЯде ? ЯдєЯд«ЯдЙЯд░ ЯдИЯд╣ЯдфЯдЙЯдаЯд┐ЯдеЯДђЯд░ЯдЙ ЯдИЯДЄЯдЄ ЯдИЯд«ЯДЪЯДЄ ЯдфЯдЙЯдгЯд▓Яд┐ЯдЋ ЯдгЯдЙЯдИЯДЄ ЯдЋЯд░ЯДЄ Яд«Яд┐Яд░ЯдфЯДЂЯд░ ЯдЦЯДЄЯдЋЯДЄ ЯдЄЯдАЯДЄЯде , Яд╣ЯДІЯд« ЯдЄЯдЋЯДІЯдеЯд«Яд┐ЯдЋЯдИЯДЇ , ЯдИЯд┐ЯдЪЯд┐ ЯдЋЯд▓ЯДЄЯдюЯДЄ Яд»ЯдЙЯдЊЯДЪЯдЙЯд░ ЯдИЯд«ЯДЪ ЯдцЯдЙЯдЂЯддЯДЄЯд░ЯдЋЯДЄ ЯдЋЯд┐ ЯдфЯд░Яд┐Яд«ЯдЙЯдБЯДЄ ЯдгЯд┐ЯдгЯДЇЯд░Ядц Яд╣ЯдцЯДЄ Яд╣Ядц ЯдюЯдЙЯдеЯд┐ЯЦц ЯдгЯдЙЯдИЯДЄ ЯдЋЯдеЯДЇЯдАЯдЙЯдЋЯдЪЯд░ ЯдЦЯДЄЯдЋЯДЄ ЯдХЯДЂЯд░ЯДЂ ЯдЋЯд░ЯДЄ ЯдфЯДЇЯд░ЯДїЯДЮ , Яд»ЯДЂЯдгЯдЋ, ЯдЋЯд┐ЯдХЯДІЯд░ ЯдИЯдгЯдЙЯд░ ЯдџЯДЄЯдиЯДЇЯдЪЯдЙ ЯдЦЯдЙЯдЋЯдц ЯдцЯдЙЯдЂЯддЯДЄЯд░ ЯдЌЯдЙ ЯдўЯДЄЯдЂЯдиЯДЄ ЯддЯдЙЯдЂЯДюЯдЙЯдеЯДІЯд░ЯЦц ЯдЁЯдеЯДЄЯдЋ ЯдИЯд╣ЯдфЯдЙЯдаЯд┐ЯдеЯДђЯдЄ ЯдгЯДЇЯд»ЯдЙЯдЌ ЯдЊ ЯдгЯдЄ ЯддЯДЂЯдЄ Яд╣ЯдЙЯдцЯДЄ ЯдгЯДЂЯдЋЯДЄЯд░ ЯдИЯдЙЯд«ЯдеЯДЄ ЯдџЯДЄЯдфЯДЄ ЯдДЯд░ЯДЄ Яд░ЯдЙЯдќЯдцЯЦц ЯдЋЯд┐ЯдеЯДЇЯдцЯДЂ ЯдХЯд░ЯДђЯд░ЯДЄЯд░ ЯдЁЯдеЯДЇЯд» ЯдИЯДЇЯдфЯд░ЯДЇЯдХЯдЋЯдЙЯдцЯд░ ЯдЁЯдѓЯдХЯдЌЯДЂЯд▓ЯДІЯдцЯДЄ ЯдЋЯдЙЯд░ЯДІ ЯдеЯдЙ ЯдЋЯдЙЯд░ЯДІ ЯдЁЯдгЯдЙЯдъЯДЇЯдЏЯд┐Ядц ,ЯдЁЯдеЯд┐ЯдџЯДЇЯдЏЯдЙЯдЋЯДЃЯдц(!) ЯдХЯдЙЯд░ЯДђЯд░Яд┐ЯдЋ ЯдџЯдЙЯдф ЯдфЯДюЯдцЯдЄЯЦц ЯдєЯдгЯдЙЯд░ ЯдЈЯдЪЯдЙЯдЊ ЯдаЯд┐ЯдЋ , ЯдИЯДЄЯдЄ ЯдИЯд«ЯДЪЯДЄЯдЊ ЯдЁЯдеЯДЄЯдЋ ЯдИЯдџЯДЄЯдцЯде ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди ЯдЈЯдЄ ЯдгЯДЇЯд»ЯдЙЯдфЯдЙЯд░ЯдЪЯдЙЯдЋЯДЄ ЯдгЯДЂЯдЮЯДЄ ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдИЯд╣ЯдфЯдЙЯдаЯд┐ЯдеЯДђЯддЯДЄЯд░ЯдЋЯДЄ ЯдеЯд┐Яд░ЯдЙЯдфЯдд ЯдюЯдЙЯДЪЯдЌЯдЙЯДЪ , Яд«ЯдЙЯдеЯДЄ ЯдАЯДЇЯд░ЯдЙЯдЄЯдГЯдЙЯд░ЯДЄЯд░ ЯдгЯдЙЯдЂ ЯдфЯдЙЯдХЯДЄЯд░ ЯдИЯд┐ЯдЪЯДЄ ЯдгЯдИЯдЙЯд░ ЯдгЯДЇЯд»ЯдгЯдИЯДЇЯдЦЯдЙ ЯдЋЯд░ЯдцЯДЄЯдеЯЦц
ЯдЈЯдќЯде ЯдцЯДІ ЯдЁЯдгЯдИЯДЇЯдЦЯдЙ ЯдєЯд░ЯДІ ЯдќЯдЙЯд░ЯдЙЯдф Яд╣ЯДЪЯДЄЯдЏЯДЄЯЦц ЯдЅЯдеЯДЇЯд«ЯДЂЯдЋЯДЇЯдц-ЯдИЯДЇЯдЦЯдЙЯдеЯДЄ ЯдгЯдЙ ЯдфЯдЙЯдгЯд▓Яд┐ЯдЋ ЯдгЯдЙЯдИЯДЄ ЯдЈЯдЋЯдюЯде ЯдИЯДЇЯдгЯдЙЯдГЯдЙЯдгЯд┐ЯдЋ ЯдфЯДІЯдХЯдЙЯдЋЯДЄЯд░ ЯдцЯд░ЯДЂЯдБЯДђЯдЋЯДЄЯдЊ ЯдюЯДЂЯд▓ЯдюЯДЂЯд▓ ЯдЋЯд░ЯДЄ, ЯдЁЯдХЯДЇЯд▓ЯДђЯд▓ ЯдгЯдЙЯдЂЯдЋЯдЙ ЯдџЯДІЯдќЯДЄ ЯдфЯДЂЯд░ЯДІ ЯдгЯдЙЯдИЯДЄЯд░ ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯдиЯдЌЯДЂЯд▓ЯДІ ЯдцЯдЙЯдЋЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЋЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯддЯДЄЯдќЯДЄЯЦц ЯдЋЯДЪЯдюЯдеЯдЋЯДЄ ЯдгЯд▓ЯдгЯДЄЯде ЯддЯДЃЯдиЯДЇЯдЪЯд┐ ЯдгЯддЯд▓ЯдЙЯдцЯДЄ ? ЯдДЯдЙЯд░ЯДЇЯд«Яд┐ЯдЋЯд░ЯдЙ ЯдДЯд░ЯДЄЯдЄ ЯдеЯд┐ЯДЪЯДЄЯдЏЯДЄЯде , ЯдЈЯд░ ЯдИЯд«ЯдЙЯдДЯдЙЯде ЯдгЯДЄЯдХЯДђ ЯдЋЯд░ЯДЄ ЯдгЯДІЯд░ЯдќЯдЙ ЯдЊ Яд╣Яд┐ЯдюЯдЙЯдг ЯдфЯДюЯдЙЯЦц ЯдИЯДЄЯдЪЯд┐ ЯдЋЯд░ЯДЄЯдЊ Яд»ЯДЄ Яд░ЯДЄЯд╣ЯдЙЯдЄ ЯдфЯдЙЯдЊЯДЪЯдЙ Яд»ЯдЙЯдџЯДЇЯдЏЯДЄ ЯдеЯдЙ ЯдИЯДЄ ЯдЅЯддЯдЙЯд╣Яд░ЯдБ ЯдГЯДЂЯд░Яд┐ЯдГЯДЂЯд░Яд┐ЯЦц
ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдгЯдЙЯдЎЯдЙЯд▓ЯДђ ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯдиЯДЄЯд░ ЯдИЯдЙЯд«ЯдЌЯДЇЯд░Яд┐ЯдЋ ЯдєЯдџЯд░ЯдБ ЯдЋЯдцЯдќЯдЙЯдеЯд┐ ЯдИЯдГЯДЇЯд» ЯдЊ ЯдХЯДЇЯд▓ЯДђЯд▓ Яд╣ЯдЊЯДЪЯдЙ ЯдЅЯдџЯд┐ЯДј ЯдИЯДЄЯдЪЯдЙ ЯдфЯд░Яд┐ЯдгЯдЙЯд░ ЯдЦЯДЄЯдЋЯДЄ, ЯдгЯд┐ЯддЯДЇЯд»ЯдЙЯд▓ЯДЪ ЯдЦЯДЄЯдЋЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЋЯДЄ ЯдХЯд┐ЯдќЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯддЯДЄЯдЊЯДЪЯдЙ Яд╣ЯДЪ ЯдеЯд┐ЯЦц ЯдЄЯдЂЯдџЯДюЯДЄЯдфЯдЙЯдЋЯдЙ ЯдгЯдеЯДЇЯдДЯДЂ, ЯдЋЯдЙЯдюЯДЄЯд░ ЯдЏЯДЄЯд▓ЯДЄ ЯдєЯд░ ЯдфЯдЙЯДюЯдЙЯд░ ЯдАЯДЄЯдЂЯдфЯДІ ЯдЏЯДЄЯд▓ЯДЄ ЯдЋЯдЙЯдЏ ЯдЦЯДЄЯдЋЯДЄ ЯдцЯдЙЯд░ ЯдЋЯДЂЯдХЯд┐ЯдЋЯДЇЯдиЯдЙ ЯдХЯДЂЯд░ЯДЂ Яд╣ЯДЪЯЦц ЯдЈЯдЋ ЯдфЯд░ЯДЇЯд»ЯдЙЯДЪЯДЄ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђЯдЋЯДЄ Яд»ЯДІЯдеЯд┐ ЯдЊ ЯдИЯДЇЯдцЯдеЯДЄЯд░ ЯдИЯд«ЯдеЯДЇЯдгЯд┐Ядц ЯдЈЯдЋЯдЪЯд┐ ЯдГЯДІЯдЌЯДЇЯд»ЯдфЯдБЯДЇЯд»ЯДЄЯд░ ЯдгЯдЙЯдЄЯд░ЯДЄ ЯдЋЯд┐ЯдЏЯДЂЯдЄ ЯдИЯДЄ ЯдГЯдЙЯдгЯдцЯДЄ ЯдфЯдЙЯд░ЯДЄ ЯдеЯдЙ ! ЯдфЯДЇЯд░ЯдцЯд┐ЯдЪЯд┐ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ , ЯдИЯДЄ Яд»ЯДЄ ЯдгЯДЪЯдИЯДЄЯд░ЯдЄ Яд╣ЯДІЯдЋ ЯдеЯдЙ ЯдЋЯДЄЯде ЯдцЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдЋЯдЙЯдЏЯДЄ ЯдГЯДІЯдЌЯДЇЯд» ЯдЊ Яд░Яд«ЯдеЯд»ЯДІЯдЌЯДЇЯд» Яд«ЯдеЯДЄ Яд╣ЯДЪЯЦц
ЯдєЯдю ЯдЈЯдЋЯдгЯд┐ЯдѓЯдХ ЯдХЯдцЯдЙЯдгЯДЇЯддЯДђЯдцЯДЄ ЯдЈЯдИЯДЄ ЯдєЯд«ЯдЙЯд░ ЯддЯдХ ЯдгЯдЏЯд░ЯДЄ ЯдЋЯдеЯДЇЯд»ЯдЙ ЯдХЯд┐ЯдХЯДЂЯдЋЯДЄ ЯдгЯДІЯдЮЯдЙЯдцЯДЄ Яд╣ЯдџЯДЇЯдЏЯДЄ ЯдИЯДЄ ЯдЈЯдЄ ЯдИЯд«ЯдЙЯдюЯДЄ ЯдЋЯДІЯдЦЯдЙЯдЊ ЯдеЯд┐Яд░ЯдЙЯдфЯдд ЯдеЯДЪЯЦц ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдџЯдЙЯд░ЯддЯд┐ЯдЋЯДЄ ЯдгЯдИЯдгЯдЙЯдИ ЯдЋЯд░ЯдЏЯДЄ ЯдЋЯДЂЯДјЯдИЯд┐Ядц, ЯдгЯд┐ЯдЋЯДЃЯдц ЯдЊ Яд«ЯДЂЯдќЯДІЯдХ-ЯдДЯдЙЯд░ЯДђ ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди ЯдфЯдХЯДЂ ; ЯдЈЯд░ ЯдџЯДЄЯДЪЯДЄ ЯдєЯдФЯдИЯДІЯдИЯДЄЯд░ ЯдєЯд░ ЯдЋЯд┐ Яд╣ЯдцЯДЄ ЯдфЯдЙЯд░ЯДЄЯЦц
ЯдЈЯдгЯдЙЯд░ ЯддЯДЄЯдќЯд┐ ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдЋЯд░ЯДЇЯдфЯДІЯд░ЯДЄЯдЪ ЯдфЯДЇЯд░ЯдцЯд┐ЯдиЯДЇЯдаЯдЙЯдеЯДЄ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђЯддЯДЄЯд░ ЯдИЯдЙЯд«ЯдЙЯдюЯд┐ЯдЋ ЯдЁЯдгЯдИЯДЇЯдЦЯдЙ ЯдЋЯд┐Яд░ЯдЋЯд« ЯЦц ЯдЈЯдЋЯд»ЯДЂЯдЌ ЯдєЯдЌЯДЄЯдЊ ЯдЋЯДЇЯд»ЯдЙЯд░Яд┐ЯДЪЯдЙЯд░ ЯдИЯдџЯДЄЯдцЯде Яд«ЯДЄЯДЪЯДЄЯдЪЯд┐ЯдЋЯДЄ ЯдИЯДЇЯдЋЯДЂЯд▓, ЯдЋЯд▓ЯДЄЯдю , ЯдгЯДЇЯд»ЯдЙЯдѓЯдЋ ЯдЏЯдЙЯДюЯдЙ ЯдЁЯдеЯДЇЯд» ЯдЋЯДІЯдЦЯдЙЯдЊ ЯдџЯдЙЯдЋЯд░Яд┐ ЯдЋЯд░ЯдцЯДЄ ЯддЯд┐ЯдцЯДЄ ЯдфЯдЙЯд░Яд┐ЯдгЯдЙЯд░Яд┐ЯдЋ ЯдгЯдЙЯдЂЯдДЯдЙ ЯдєЯдИЯдцЯЦц ЯдЈЯдќЯде ЯдЋЯд░ЯДЇЯдфЯДІЯд░ЯДЄЯдЪ ЯдфЯд░Яд┐ЯдгЯДЄЯдХ ЯдЁЯдеЯДЄЯдЋ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђЯдгЯдЙЯдеЯДЇЯдДЯдг Яд╣ЯДЪЯДЄЯдЏЯДЄЯЦц ЯдеЯдЙЯдеЯдЙ ЯдДЯд░ЯдБЯДЄЯд░ ЯдфЯДЇЯд░Яд»ЯДЂЯдЋЯДЇЯдцЯд┐Яд░( Яд«ЯДІЯдгЯдЙЯдЄЯд▓ ЯдФЯДІЯде ) ЯдЅЯДјЯдЋЯд░ЯДЇЯдиЯдцЯдЙЯДЪ ЯдцЯдЙЯдЂЯддЯДЄЯд░ ЯдюЯДђЯдгЯде ЯдеЯд┐Яд░ЯдЙЯдфЯддЯЦц ЯдЋЯд┐ЯдеЯДЇЯдцЯДЂ ЯдаЯд┐ЯдЋ ЯдЅЯд▓ЯДЇЯдЪЯДІ ЯдЁЯдгЯдИЯДЇЯдЦЯдЙ Яд╣ЯДЪЯДЄЯдЏЯДЄ ЯдгЯдЙЯдЄЯд░ЯДЄЯд░ Яд░ЯдЙЯдИЯДЇЯдцЯдЙЯДЪ ЯЦц ЯдЁЯдФЯд┐ЯдИЯДЄ ЯдЈЯдЋЯдЪЯдЙ ЯдХЯДЃЯдЎЯДЇЯдќЯд▓Яд┐Ядц ЯдеЯд┐ЯДЪЯд«ЯдеЯДђЯдцЯд┐Яд░ ЯдГЯд┐ЯдцЯд░ЯДЄ ЯдЈЯдЋЯдюЯде ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ Яд»ЯдцЯДІЯдќЯдЙЯдеЯд┐ ЯдеЯд┐Яд░ЯдЙЯдфЯдд ; Яд░ЯдЙЯдИЯДЇЯдцЯдЙ-ЯдўЯдЙЯдЪЯДЄ ЯдИЯДЄ ЯдцЯдцЯДІЯдќЯдЙЯдеЯд┐ ЯдЁЯдеЯд┐Яд░ЯдЙЯдфЯддЯЦц
ЯдєЯд«ЯдЙЯд░ Яд»ЯДЄ ЯдЋЯдЙЯдюЯДЄЯд░ ЯдЋЯДЇЯдиЯДЄЯдцЯДЇЯд░–Яд«ЯдЙЯд░ЯДЇЯдЋЯДЄЯдЪЯд┐Ядѓ Яд«ЯдЙЯд░ЯДЇЯдџЯДЄЯдеЯДЇЯдАЯдЙЯдЄЯдюЯд┐Ядѓ , ЯдИЯДЄЯдќЯдЙЯдеЯДЄ ЯдєЯд«Яд░ЯдЙ ЯдгЯд╣ЯДЂЯдгЯдЙЯд░ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдИЯд╣ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯДђЯддЯДЄЯд░ ЯдЅЯДјЯдИЯдЙЯд╣Яд┐Ядц ЯдЋЯд░ЯДЄЯдЏЯд┐ ЯддЯДђЯд░ЯДЇЯдўЯд«ЯДЄЯДЪЯдЙЯддЯДђ ЯдЋЯДЇЯд»ЯдЙЯд░Яд┐ЯДЪЯдЙЯд░ ЯдфЯд░Яд┐ЯдЋЯд▓ЯДЇЯдфЯдеЯдЙЯд░ ЯдЋЯдЦЯдЙ ЯдГЯдЙЯдгЯдцЯДЄ ЯЦц ЯдЋЯд┐ЯдеЯДЇЯдцЯДЂ ЯдЈЯдќЯдЙЯдеЯДЄЯдЊ ЯдИЯДЄЯдЄ ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди ЯдєЯдДЯд┐ЯдфЯдцЯДЇЯд»ЯДЄЯд░ ЯдфЯДЇЯд░ЯдџЯДЇЯдЏЯдеЯДЇЯде ЯдгЯдЙЯдЂЯдДЯдЙЯЦц
ЯдфЯДЇЯд░ЯдЦЯд«Ядц: ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдЋЯд░ЯДЇЯдцЯдЙЯд░ЯдЙ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђЯддЯДЄЯд░ЯдЋЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЂЯддЯДЄЯд░ ЯдеЯд┐ЯдюЯДЄЯддЯДЄЯд░ ЯдгЯд┐ЯдГЯдЙЯдЌЯДЄ ЯдеЯд┐ЯдцЯдЙЯдеЯДЇЯдц ЯдаЯДЄЯдЋЯдЙЯДЪ ЯдеЯдЙ ЯдфЯДюЯд▓ЯДЄ ЯдеЯд┐ЯдцЯДЄ ЯдџЯдЙЯде ЯдеЯдЙЯЦц Яд»ЯДЂЯдЋЯДЇЯдцЯд┐ Яд╣Яд┐ЯдИЯдЙЯдгЯДЄ ЯдцЯдЙЯд░ЯдЙ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдџЯдЙЯд░ЯДђЯддЯДЄЯд░ ЯдЁЯдФЯд┐ЯдИ ЯдЪЯдЙЯдЄЯд«ЯДЄЯд░ ЯдХЯДЄЯдиЯДЄЯдЄ ЯдцЯдЙЯДюЯдЙЯдцЯдЙЯДюЯд┐ ЯдгЯдЙЯдИЯдЙЯДЪ Яд»ЯдЙЯдЊЯДЪЯдЙЯд░ ЯдфЯДЇЯд░ЯдгЯдБЯдцЯдЙЯдЋЯДЄ ЯдцЯДЂЯд▓ЯДЄ ЯдДЯд░ЯДЄЯдеЯЦц ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдџЯдЙЯд░ЯДђ Яд╣ЯДЪЯдцЯДІ ЯдЋЯдЙЯдюЯДЄЯд░ ЯдџЯдЙЯдфЯДЄ ЯдЄЯдџЯДЇЯдЏЯДЄ ЯдЋЯд░Яд▓ЯДЄЯдЄ ЯдєЯд░ЯДІ ЯдўЯдеЯДЇЯдЪЯдЙЯдќЯдЙЯдеЯДЄЯдЋ ЯдЦЯДЄЯдЋЯДЄ Яд»ЯДЄЯдцЯДЄ ЯдфЯдЙЯд░ЯДЄЯде ЯдЁЯдФЯд┐ЯдИЯДЄ, ЯдЋЯд┐ЯдеЯДЇЯдцЯДЂ ЯдгЯдЙЯдЄЯд░ЯДЄЯд░ Яд░ЯдЙЯдИЯДЇЯдцЯдЙЯд░ ЯдфЯд░Яд┐ЯдгЯДЄЯдХ ЯдЊ ЯдИЯДЇЯдгЯдЙЯд«ЯДђ-ЯдИЯдеЯДЇЯдцЯдЙЯдеЯДЄЯд░ ЯдџЯдЙЯдф , ЯдцЯдЙЯдЂЯдЋЯДЄ ЯдгЯдЙЯДюЯдцЯд┐ ЯдИЯд«ЯДЪЯддЯдЙЯдеЯДЄ ЯдеЯд┐Яд░ЯДЂЯДјЯдИЯдЙЯд╣Яд┐Ядц ЯдЋЯд░ЯДЄЯЦц
ЯддЯДЇЯдгЯд┐ЯдцЯДђЯДЪЯдц: ЯдфЯдХЯДЇЯдџЯд┐Яд«ЯдЙ ЯддЯДЄЯдХЯДЄЯд░ ЯдИЯд«ЯДЪЯДЄЯд░ ЯдИЯдЙЯдЦЯДЄ ЯдцЯдЙЯд▓ Яд«Яд┐Яд▓Яд┐ЯДЪЯДЄ ЯдЁЯдеЯДЄЯдЋЯдИЯд«ЯДЪ ЯдИЯдеЯДЇЯдДЯДЇЯд»ЯдЙЯд░ ЯдфЯд░ЯдЊ ЯдЁЯдФЯд┐ЯдИЯДЄ ЯдЦЯдЙЯдЋЯдЙЯд░ ЯдфЯДЇЯд░ЯДЪЯДІЯдюЯдеЯДђЯДЪЯдцЯдЙ ЯддЯДЄЯдќЯдЙ ЯддЯДЄЯДЪЯЦц ЯдЁЯдЦЯдгЯдЙ ЯдЋЯДЇЯд░ЯДЄЯдцЯдЙ ЯдєЯдИЯд▓ЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЂЯддЯДЄЯд░ ЯдИЯдЎЯДЇЯдЌЯДЄ Яд░ЯдЙЯдцЯДЄЯд░ ЯдќЯдЙЯдгЯдЙЯд░ЯДЄ ЯдЅЯдфЯдИЯДЇЯдЦЯд┐Ядц ЯдЦЯдЙЯдЋЯдЙЯд░ ЯдИЯДїЯдюЯдеЯДЇЯд»ЯдцЯдЙ ЯдЦЯдЙЯдЋЯДЄЯЦц ЯдгЯдЙЯдѓЯд▓ЯдЙЯддЯДЄЯдХ ЯдЏЯдЙЯДюЯдЙ ЯдЁЯдеЯДЇЯд» ЯдИЯдг ЯдЌЯдЙЯд░ЯДЇЯд«ЯДЄЯдеЯДЇЯдЪЯдИ ЯдЅЯДјЯдфЯдЙЯддЯдеЯдЋЯдЙЯд░ЯДђ ЯддЯДЄЯдХЯДЄ ЯдИЯдЙЯд«ЯдЙЯдюЯд┐ЯдЋ ЯдЁЯдгЯдИЯДЇЯдЦЯдЙЯде ЯдГЯДЄЯддЯДЄ Яд«ЯдЙЯд░ЯДЇЯдџЯДЄЯдеЯДЇЯдАЯдЙЯдЄЯдюЯд┐Ядѓ ЯдЈЯд░ ЯдфЯДЂЯд░ЯДІ ЯддЯдќЯд▓ ЯдеЯд┐ЯДЪЯДЄ Яд░ЯДЄЯдќЯДЄЯдЏЯДЄЯде ЯдеЯдЙЯд░ЯДђЯд░ЯдЙЯЦцЯдгЯДЇЯд»ЯдцЯд┐ЯдЋЯДЇЯд░Яд« ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯддЯДЄЯдХЯДЄЯЦц ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди-ЯдХЯдЙЯдИЯд┐Ядц ЯдгЯд▓ЯДЄЯдЄ ЯдцЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдфЯДЇЯд░ЯдЙЯдДЯдЙЯдеЯДЇЯд» ЯдгЯДЄЯдХЯДђЯЦц Яд»ЯддЯд┐ЯдЊ ЯдЌЯдЙЯд░ЯДЇЯд«ЯДЄЯдеЯДЇЯдЪЯдИ ЯдЋЯдЙЯд░ЯдќЯдЙЯдеЯдЙЯДЪ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдХЯДЇЯд░Яд«Яд┐ЯдЋЯДЄЯд░ ЯдюЯДЪЯдюЯДЪЯдЋЯдЙЯд░ЯЦц
ЯдцЯДЃЯдцЯДђЯДЪЯдц: ЯдЈЯдЋЯдюЯде ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди ЯдИЯд╣ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯДђЯдЋЯДЄ ЯддЯд┐ЯдеЯДЄЯд░ Яд»ЯДЄ ЯдЋЯДІЯде ЯдИЯд«ЯДЪЯДЄ Яд»ЯДЄ ЯдЋЯДІЯде ЯдЋЯдЙЯд░ЯдќЯдЙЯдеЯдЙЯДЪ ЯдфЯДЇЯд░ЯДІЯдАЯдЙЯдЋЯдХЯде ЯдФЯд▓ЯДІ ЯдєЯдфЯДЄЯд░ ЯдюЯдеЯДЇЯд» ЯдфЯдЙЯдаЯдЙЯдеЯДІ Яд»ЯдЙЯДЪЯЦц ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдИЯд╣ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯДђЯд░ ЯдюЯдеЯДЇЯд» ЯдфЯДЇЯд░ЯдцЯд┐ЯдиЯДЇЯдаЯдЙЯдеЯДЄЯд░ ЯдеЯд┐ЯдюЯдИЯДЇЯдг Яд»ЯдЙЯдеЯдгЯдЙЯд╣Яде ЯдЏЯдЙЯДюЯдЙ ЯдЊ ЯддЯд┐ЯдеЯДЄЯд░ ЯдеЯд┐Яд░ЯДЇЯддЯд┐ЯдиЯДЇЯдЪ ЯдИЯд«ЯДЪ ЯдЏЯдЙЯДюЯдЙ ЯдЋЯдЙЯд░ЯдќЯдЙЯдеЯдЙЯДЪ Яд»ЯдЙЯдцЯдЙЯДЪЯдЙЯдцЯДЄЯд░ ЯдфЯДЇЯд░ЯдХЯДЇЯдеЯдЄ ЯдЊЯдаЯДЄ ЯдеЯдЙЯЦц
ЯдЈЯдЏЯдЙЯДюЯдЙ ЯдєЯд░ЯДЄЯдЋЯдЪЯд┐ ЯдГЯДЪЯдѓЯдЋЯд░ ЯдЁЯд«ЯдЙЯдеЯдгЯд┐ЯдЋ ЯддЯд┐ЯдЋ ЯдєЯдЏЯДЄ, Яд»ЯДЄЯдЪЯдЙ ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдЋЯд░ЯДЇЯдфЯДІЯд░ЯДЄЯдЪ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдЋЯд░ЯДЇЯдцЯдЙЯд░ЯдЙ Яд«ЯДЂЯдќЯДЄ ЯдЅЯдџЯДЇЯдџЯдЙЯд░ЯдБ ЯдЋЯд░ЯДЄЯде ЯдеЯдЙЯЦц ЯдЋЯд┐ЯдеЯДЇЯдцЯДЂ ЯдгЯДЇЯд»ЯдЋЯДЇЯдцЯд┐ЯдЌЯдц ЯдєЯд▓ЯдЙЯдфЯдџЯдЙЯд░Яд┐ЯдцЯдЙЯДЪ ЯдаЯд┐ЯдЋЯдЄ ЯдгЯДЄЯд░ Яд╣ЯДЪЯДЄ ЯдєЯдИЯДЄЯЦц ЯдИЯДЄЯдЪЯдЙ Яд╣ЯдџЯДЇЯдЏЯДЄ, ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдџЯдЙЯд░ЯДђЯддЯДЄЯд░ ЯдЁЯдеЯДЇЯдцЯдЃЯдИЯдцЯДЇЯдцЯДЇЯдгЯдЙ ЯдЋЯдЙЯд▓ЯДђЯде ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдгЯд┐Яд░ЯдцЯд┐Яд░ ЯдИЯд«ЯДЪЯдЪЯд┐ЯЦц ЯдЈЯдЪЯдЙ ЯдЋЯДЄЯдЅ ЯдгЯд┐ЯдгЯДЄЯдџЯдеЯдЙ ЯдЋЯд░ЯдцЯДЄ Яд░ЯдЙЯдюЯДђ ЯдеЯДЪ Яд»ЯДЄ Яд«ЯдЙЯдцЯДЃЯдцЯДЇЯдгЯДЄЯд░ Яд«ЯдцЯДІ ЯдЈЯдЋЯдЪЯдЙ Яд«Яд╣ЯДј ЯдгЯд┐ЯдХЯдЙЯд▓ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«Яд»ЯдюЯДЇЯдъЯДЄ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдХЯд░ЯДђЯд░ ЯдЋЯДЇЯдиЯДЪ ЯдЋЯд░ЯДЄ ЯдгЯдѓЯдХЯд░ЯдЋЯДЇЯдиЯдЙЯд░ ЯддЯдЙЯДЪЯд┐ЯдцЯДЇЯдг ЯдфЯдЙЯд▓Яде ЯдЋЯд░ЯДЄ ЯдџЯд▓ЯДЄЯдЏЯДЄЯдеЯЦц ЯдфЯдХЯДЇЯдџЯд┐Яд«ЯдЙ ЯддЯДЄЯдХЯДЄ ЯдфЯДЇЯд░ЯдЙЯДЪ ЯдгЯдЏЯд░ ЯдќЯдЙЯдеЯДЄЯдЋЯДЄЯд░ ЯдгЯДЄЯдцЯдеЯдИЯд╣ Яд«ЯдЙЯдцЯДЃЯдцЯДЇЯдг ЯдЋЯдЙЯд▓ЯДђЯде ЯдЏЯДЂЯдЪЯд┐ ЯдЏЯдЙЯДюЯдЙЯдЊ ЯдЄЯдџЯДЇЯдЏЯДЄЯд«ЯдцЯДІ ЯдгЯДЄЯдцЯде-ЯдгЯд┐Яд╣ЯДђЯде ЯдЏЯДЂЯдЪЯд┐ ЯдфЯДЇЯд░Яд»ЯДІЯдюЯДЇЯд»ЯЦц ЯдєЯдгЯдЙЯд░ ЯдфЯДЇЯд░ЯдцЯд┐ЯдиЯДЇЯдаЯдЙЯдеЯдЌЯДЂЯд▓ЯДІЯдЊ ЯдЏЯДЂЯдЪЯд┐Яд░ ЯдгЯд┐Яд░ЯдцЯд┐Яд░ ЯдфЯд░ЯДЄ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдџЯдЙЯд░ЯДђЯдЋЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдєЯдЌЯДЄЯд░ ЯдЁЯдгЯдИЯДЇЯдЦЯдЙЯдеЯДЄ ЯдеЯд┐ЯДЪЯДІЯдЌ ЯддЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдЦЯдЙЯдЋЯДЄЯдеЯЦц ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯддЯДЄЯдХЯДЄ ЯдЋЯд░ЯДЇЯдфЯДІЯд░ЯДЄЯдЪ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђЯддЯДЄЯд░ ЯдЁЯдгЯдИЯДЇЯдЦЯдЙЯде ЯдаЯд┐ЯдЋ ЯдцЯдЙЯд░ ЯдгЯд┐ЯдфЯд░ЯДђЯдцЯДЄЯЦц ЯдЈЯдЋЯдюЯде ЯддЯдЋЯДЇЯди ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдџЯдЙЯд░ЯДђЯд░ ЯдгЯд┐ЯДЪЯДЄ Яд╣ЯДЪЯДЄ Яд»ЯдЙЯдЊЯДЪЯдЙ Яд«ЯдЙЯдеЯДЄЯдЄ, ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдеЯдцЯДЂЯде ЯдЁЯдГЯд┐ЯдГЯдЙЯдгЯдЋ ЯдИЯДЇЯдгЯдЙЯд«ЯДђ РђЊЯдХЯДЇЯдгЯдХЯДЂЯд░ЯдЋЯДЂЯд▓ЯДЄЯд░ ЯдеЯд┐ЯдцЯДЇЯд»ЯдеЯдцЯДЂЯде ЯдИЯдѓЯдгЯд┐ЯдДЯд┐ЯдгЯддЯДЇЯдД ЯдИЯдцЯд░ЯДЇЯдЋЯДђЯдЋЯд░ЯдБЯЦц ЯдєЯд░ ЯдцЯдЙЯд░ЯдфЯд░ЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдЋЯДЇЯд»ЯдЙЯд░Яд┐ЯДЪЯдЙЯд░ЯДЄЯд░ ЯдгЯДю ЯдДЯд░ЯдБЯДЄЯд░ ЯдДЯдЙЯдЋЯДЇЯдЋЯдЙ ЯдєЯдИЯДЄ Яд«ЯдЙЯдцЯДЃЯдцЯДЇЯдг ЯдЋЯдЙЯд▓ЯДђЯде ЯдИЯд«ЯДЪЯдЪЯд┐ЯдцЯДЄЯЦц Яд«ЯдЙЯдцЯДЃЯдцЯДЇЯдг ЯдЋЯдЙЯд▓ЯДђЯде ЯдЏЯДЂЯдЪЯд┐ЯдцЯДЄ Яд»ЯдЙЯдЊЯДЪЯдЙ Яд«ЯдЙЯдеЯДЄЯдЄ ЯдДЯд░ЯДЄ ЯдеЯДЄЯдЊЯДЪЯдЙ Яд»ЯдЙЯДЪ ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдЋЯДЇЯд»ЯдЙЯд░Яд┐ЯДЪЯдЙЯд░ЯДЄЯд░ ЯдгЯд┐ЯддЯдЙЯДЪ ЯдўЯдБЯДЇЯдЪЯдЙ ЯдгЯДЄЯдюЯДЄ ЯдЌЯДЄЯд▓ЯЦц ЯдЈЯдЋЯдЪЯдЙ ЯдгЯд┐Яд░ЯдцЯд┐ ЯддЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдФЯд┐Яд░ЯДЄ ЯдЈЯдИЯДЄ, ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдџЯдЙЯд░ЯДђ ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдєЯдЌЯДЄЯд░ ЯдЁЯдгЯдИЯДЇЯдЦЯдЙЯде ЯдФЯд┐Яд░ЯДЄ ЯдфЯдЙЯде ЯдеЯдЙ ЯЦц ЯдцЯдЙЯдЂЯдЋЯДЄ ЯдХЯДѓЯдеЯДЇЯд» ЯдЦЯДЄЯдЋЯДЄ ЯдХЯДЂЯд░ЯДЂ ЯдЋЯд░ЯдцЯДЄ Яд╣ЯДЪЯЦц ЯдцЯдЙ ЯдЏЯдЙЯДюЯдЙ ЯдфЯдЙЯд░Яд┐ЯдфЯдЙЯд░ЯДЇЯдХЯДЇЯдгЯд┐ЯдЋ ЯдџЯдЙЯдфЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдДЯДЇЯд»ЯдЙЯде ЯдЊ ЯдюЯДЇЯдъЯдЙЯде Яд╣ЯДЪЯДЄ ЯдфЯДюЯДЄ ЯдеЯдцЯДЂЯде ЯдХЯд┐ЯдХЯДЂЯдЪЯд┐ЯЦц ЯдЈЯдЄЯдИЯдг ЯдгЯд╣ЯДЂЯд«ЯДЂЯдќЯДђ ЯдИЯДђЯд«ЯдЙЯдгЯддЯДЇЯдДЯдцЯдЙ ЯддЯДЄЯдќЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдЋЯд░ЯДЇЯдфЯДІЯд░ЯДЄЯдЪ ЯдЅЯдџЯДЇЯдџЯдфЯддЯдИЯДЇЯдЦЯд░ЯдЙ Яд»ЯдцЯДІЯдЄ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђЯдгЯдЙЯдеЯДЇЯдДЯдг ЯдЋЯдЦЯдЙЯдгЯдЙЯд░ЯДЇЯдцЯдЙ ЯдгЯд▓ЯДЄЯде ЯдеЯдЙ ЯдЋЯДЄЯде ; ЯдеЯд┐ЯДЪЯДІЯдЌЯддЯдЙЯдеЯДЄЯд░ ЯдЋЯДЇЯдиЯДЄЯдцЯДЇЯд░ЯДЄ ЯдцЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдфЯДЇЯд░ЯдЙЯдДЯдЙЯдеЯДЇЯд» ЯдЦЯдЙЯдЋЯДЄ ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдџЯдЙЯд░ЯДђЯд░ ЯддЯд┐ЯдЋЯДЄЯЦц
ЯдЋЯд░ЯДЇЯдфЯДІЯд░ЯДЄЯдЪ ЯдфЯд░Яд┐ЯдгЯДЄЯдХ ЯдеЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдєЯд«ЯдЙЯд░ Яд«ЯдцЯдЙЯд«ЯдцЯДЄЯд░ ЯдИЯдЎЯДЇЯдЌЯДЄ ЯдЁЯдеЯДЄЯдЋЯДЄЯд░ Яд«Яд┐Яд▓ЯдгЯДЄ ЯдеЯдЙ ; ЯдЋЯдЙЯд░ЯдБ ЯдєЯд«ЯдЙЯд░ ЯддЯДЄЯдќЯдЙ ЯдфЯд░Яд┐ЯдИЯДЇЯдЦЯд┐ЯдцЯд┐Яд░ ЯдџЯДЄЯДЪЯДЄ ЯдЁЯдеЯДЄЯдЋ ЯдГЯдЙЯд▓ЯДІ ЯдфЯд░Яд┐ЯдгЯДЄЯдХ Яд»ЯДЄЯд«Яде ЯдгЯд┐ЯдГЯд┐ЯдеЯДЇЯде ЯдфЯДЇЯд░ЯдцЯд┐ЯдиЯДЇЯдаЯдЙЯдеЯДЄ ЯдєЯдЏЯДЄ ; ЯдаЯд┐ЯдЋ ЯдцЯДЄЯд«ЯдеЯд┐ ЯдЁЯдеЯДЄЯдЋ ЯдќЯдЙЯд░ЯдЙЯдф ЯдфЯд░Яд┐ЯдгЯДЄЯдХЯдЊ ЯдєЯдЏЯДЄЯЦц Яд«ЯДІЯдЪЯдЙ-ЯддЯдЙЯдЌЯДЄ, ЯдЈЯдЋЯдЪЯдЙ ЯдИЯд«ЯДЪ ЯдЏЯд┐Яд▓ ЯдЋЯд░ЯДЇЯдфЯДІЯд░ЯДЄЯдЪ ЯдюЯдЌЯдцЯДЄЯд░ Яд«ЯДЄЯДЪЯДЄЯддЯДЄЯд░ЯдЋЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЂЯддЯДЄЯд░ ЯдіЯд░ЯДЇЯдДЯДЇЯдгЯдцЯдеЯд░ЯдЙ ЯдЊ ЯдИЯд╣ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯДђЯд░ЯдЙ ЯдИЯд╣ЯдюЯд▓ЯдГЯДЇЯд» ЯдГЯдЙЯдгЯдцЯДЄЯдеЯЦц Яд«ЯДЄЯдДЯдЙЯдгЯДђ ЯдЏЯдЙЯдцЯДЇЯд░ЯДђЯд░ЯдЙ ЯдХЯд┐ЯдЋЯДЇЯдиЯдЋЯдцЯдЙ ЯдЋЯд░ЯдгЯДЄ ; ЯдеЯд┐Яд░ЯдЙЯдфЯдд ЯдфЯДЄЯдХЯдЙЯЦц ЯдєЯд░ Яд«ЯДІЯдЪЯдЙЯд«ЯДЂЯдЪЯд┐ ЯдИЯДЂЯдеЯДЇЯддЯд░ЯДђ Яд«ЯДЄЯДЪЯДЄЯд░ЯдЙ ЯдИЯДЂЯдфЯдЙЯдцЯДЇЯд░ЯДЄЯд░ ЯдЌЯд▓ЯдЙЯДЪ ЯдЮЯДЂЯд▓ЯДЄ ЯдфЯДюЯдгЯДЄЯЦц ЯдеЯд┐ЯдюЯДЄЯд░ ЯдєЯдцЯДЇЯд«ЯдИЯд«ЯДЇЯд«ЯдЙЯдеЯдгЯДІЯдД ЯдеЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдЁЯдеЯДЄЯдЋ Яд«ЯДЄЯдДЯдЙЯдгЯДђ Яд«ЯДЄЯДЪЯДЄЯд░ЯдЙ ЯдгЯДЄЯдИЯд░ЯдЋЯдЙЯд░Яд┐ ЯдЁЯдФЯд┐ЯдИЯДЄ ЯдЋЯдЙЯдю ЯдЋЯд░ЯдЙ ЯдХЯДЂЯд░ЯДЂ ЯдЋЯд░ЯДЄЯдЏЯДЄЯде ЯдЌЯдц ЯдцЯд┐Яде ЯддЯдХЯдЋЯДЄЯЦц ЯдЋЯд┐ЯдеЯДЇЯдцЯДЂ, ЯдЈЯдќЯдеЯДІ ЯдеЯд┐ЯдюЯДЄЯд░ ЯдфЯдЙЯДЪЯДЄ ЯдеЯдЙ ЯддЯдЙЯдЂЯДюЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдеЯд┐ЯдюЯДЄЯд░ ЯдИЯДЇЯдгЯдЙЯд«ЯДђЯд░ ЯдфЯдЙЯДЪЯДЄ ЯддЯдЙЯдЂЯДюЯдЙЯдеЯДІЯдЋЯДЄ ЯдфЯд░Яд┐ЯдгЯдЙЯд░ ЯдЦЯДЄЯдЋЯДЄ ЯдЅЯДјЯдИЯдЙЯд╣ ЯддЯДЄЯдЊЯДЪЯдЙ Яд╣ЯДЪЯДЄ ЯдЦЯдЙЯдЋЯДЄЯЦц
ЯдбЯдЙЯдЋЯдЙЯДЪ ЯдгЯДЄЯДюЯДЄ ЯдЊЯдаЯдЙ ЯдЏЯДЄЯд▓ЯДЄЯддЯДЄЯд░ ЯдЈЯдЋЯдЪЯдЙ ЯдИЯДЂЯдгЯд┐ЯдДЯдЙ ЯдЏЯд┐Яд▓, ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдИЯд╣ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯДђ Яд╣ЯДЄЯдИЯДЄ ЯдЋЯдЦЯдЙ ЯдгЯд▓Яд▓ЯДЄ ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ Яд╣ЯдЙЯдИЯд┐Яд«ЯдЙЯдќЯдЙ ЯдфЯДЇЯд░ЯдцЯДЇЯд»ЯДЂЯдцЯДЇЯдцЯд░ ЯдЏЯд┐Яд▓ЯЦц ЯдЋЯд┐ЯдеЯДЇЯдцЯДЂ Яд«ЯдФЯдИЯДЇЯдгЯд▓ ЯдЦЯДЄЯдЋЯДЄ ЯдєЯдИЯдЙ ЯдЁЯдеЯДЄЯдЋЯДЄ Яд╣ЯдЙЯдИЯд┐ Яд«ЯДЂЯдќЯДЄ ЯдЋЯдЦЯдЙ ЯдгЯд▓ЯдЙЯдЋЯДЄ ЯдфЯДЇЯд░ЯДЄЯд«ЯДЄЯд░ ЯдфЯДЇЯд░ЯдЙЯдЦЯд«Яд┐ЯдЋ ЯдфЯДЇЯд░ЯдХЯДЇЯд░ЯДЪ ЯдгЯд▓ЯДЄ ЯдДЯд░ЯДЄ ЯдеЯд┐ЯдцЯДЄЯдеЯЦц ЯдЈЯдЄ ЯдИЯд«ЯдИЯДЇЯд»ЯдЙЯд░ ЯдфЯдЙЯдХЯдЙЯдфЯдЙЯдХЯд┐ ЯдЏЯд┐Яд▓, ЯдіЯд░ЯДЇЯдДЯДЇЯдгЯдцЯде ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдЋЯд░ЯДЇЯдцЯдЙЯд░ЯдЙЯдЊ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдџЯдЙЯд░ЯДђЯддЯДЄЯд░ЯдЋЯДЄ ЯдИЯд╣ЯдюЯд▓ЯдГЯДЇЯд» ЯдДЯд░ЯДЄ ЯдеЯд┐ЯдцЯДЄЯдеЯЦц ЯдЁЯдеЯДЄЯдЋ Яд▓ЯДІЯдГЯДђ ЯдіЯд░ЯДЇЯдДЯДЇЯдгЯдцЯдеЯдЋЯДЄ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдџЯдЙЯд░ЯДђЯдЋЯДЄ ЯддЯДѕЯд╣Яд┐ЯдЋЯдГЯдЙЯдгЯДЄ ЯдеЯдЙ Яд╣Яд▓ЯДЄЯдЊ Яд«ЯдЙЯдеЯдИЯд┐ЯдЋЯдГЯдЙЯдгЯДЄ ЯдЁЯдфЯддЯдИЯДЇЯдЦ ЯдЋЯд░ЯдцЯДЄ ЯддЯДЄЯдќЯДЄЯдЏЯд┐ЯЦц ЯдєЯд«ЯдЙЯд░ ЯдЈЯдЋ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдИЯд╣ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯДђ ЯдЈЯдЋЯдгЯдЙЯд░ ЯдЈЯдЋ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдЋЯд░ЯДЇЯдцЯдЙЯд░ Яд░ЯДЂЯд« ЯдЦЯДЄЯдЋЯДЄ ЯдгЯДЄЯд░ Яд╣ЯДЪЯДЄ Яд»ЯдЙ ЯдгЯд▓Яд▓ЯДЄЯде, ЯдцЯдЙЯд░ ЯдИЯдЙЯддЯдЙ ЯдгЯдЙЯдѓЯд▓ЯдЙ ЯддЯдЙЯдЂЯДюЯдЙЯДЪ –ЯдЋЯдЦЯдЙ ЯдгЯд▓ЯдЙЯд░ ЯдџЯДЄЯДЪЯДЄЯдЊ ЯдИЯДЄЯдЄ ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдЋЯд░ЯДЇЯдцЯдЙЯд░ ЯдџЯДІЯдќ ЯдИЯдЙЯд░ЯдЙЯдЋЯДЇЯдиЯдБ ЯдўЯДЂЯд░ЯДЄ ЯдгЯДЄЯДюЯд┐ЯДЪЯДЄЯдЏЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдгЯДЂЯдЋЯДЄЯд░ ЯддЯд┐ЯдЋЯДЄ ЯдеЯДЪЯдцЯДІ ЯдЁЯдеЯДЇЯд» ЯдЋЯДІЯде ЯдгЯдЙЯдЂЯдЋЯДЄЯЦц
ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдИЯдџЯДЄЯдцЯде ЯдИЯдЙЯдгЯдДЯдЙЯдеЯДђ ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯдЋЯд░ЯДЇЯдцЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдИЯд╣ЯдЋЯд░ЯДЇЯд«ЯДђЯд░ ЯдИЯдЎЯДЇЯдЌЯДЄ Яд»ЯДЄ ЯдЋЯДІЯде ЯдєЯд▓ЯдЙЯдф ЯдєЯд▓ЯДІЯдџЯдеЯдЙЯДЪ ЯдИЯдџЯДЄЯдцЯдеЯдГЯдЙЯдгЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЂЯддЯДЄЯд░ ЯдџЯДІЯдќЯДЄЯд░ ЯддЯд┐ЯдЋЯДЄ ЯдцЯдЙЯдЋЯд┐ЯДЪЯДЄ ЯдЋЯдЦЯдЙ ЯдгЯд▓ЯдцЯДЄ Яд╣ЯДЪЯЦц Яд«ЯДЂЯдХЯдЋЯд┐Яд▓ Яд╣ЯдџЯДЇЯдЏЯДЄ, ЯдИЯдг ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯдиЯдЋЯДЄЯдЄ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђ ЯдЈЯдЋ ЯдџЯДІЯдќЯДЄ ЯддЯДЄЯдќЯдЙ ЯдХЯДЂЯд░ЯДЂ ЯдЋЯд░ЯДЄ ЯдгЯд▓ЯДЄ Яд»ЯДЄ ЯдЋЯДІЯде ЯдИЯдЙЯдЋЯДЇЯдиЯдЙЯдцЯДЄЯдЄ ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯдфЯДЇЯд░ЯдЦЯд« ЯдЋЯдЙЯдюЯдЪЯд┐ Яд╣ЯДЪ ЯдЊЯДюЯдеЯдЙ ЯдаЯд┐ЯдЋ ЯдЋЯд░ЯдЙЯЦц
ЯдфЯДЇЯд░ЯдЙЯдЦЯд«Яд┐ЯдЋЯдГЯдЙЯдгЯДЄ ЯдЊЯДюЯдеЯдЙ Яд«ЯдЙЯдЦЯдЙЯДЪ ЯддЯДЄЯдЊЯДЪЯдЙЯд░ ЯдгЯДЇЯд»ЯдЙЯдфЯдЙЯд░ЯдЪЯд┐ Яд╣ЯдџЯДЇЯдЏЯДЄ, Яд«ЯДЂЯд░ЯдгЯДЇЯдгЯДђ ЯдХЯДЇЯд░ЯДЄЯдБЯд┐Яд░ ЯдЋЯдЙЯдЅЯдЋЯДЄ ЯддЯДЄЯдќЯДЄ ЯдИЯд«ЯДЇЯд«ЯдЙЯде ЯддЯДЄЯдќЯдЙЯдеЯДІЯЦц ЯдЈЯдЪЯд┐ ЯдЋЯд░ЯДЇЯдфЯДІЯд░ЯДЄЯдЪ ЯдюЯдЌЯдцЯДЄ ЯдеЯДЄЯдЄЯЦц ЯддЯДЇЯдгЯд┐ЯдцЯДђЯДЪЯдЪЯд┐ ЯдєЯдЏЯДЄЯЦц ЯдЌЯд▓ЯдЙЯДЪ ЯдЊЯДюЯдеЯдЙ ЯдЦЯдЙЯдЋЯдЙЯдЪЯдЙ ЯдЋЯДЇЯд»ЯдЙЯдюЯДЂЯДЪЯдЙЯд▓ Яд«ЯДЂЯдАЯДЄЯд░ ЯдгЯДЇЯд»ЯдЙЯдфЯдЙЯд░ЯЦц ЯдЋЯд┐ЯдеЯДЇЯдцЯДЂ ЯдИЯдЙЯд«ЯдеЯДЄ ЯдЋЯДІЯде ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди ЯдфЯДюЯд▓ЯДЄЯдЄ ЯдЁЯдгЯдџЯДЄЯдцЯде Яд«ЯдеЯДЄЯдЄ ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ Яд╣ЯдЙЯдц ЯдгЯДЂЯдЋЯДЄЯд░ ЯдЁЯдѓЯдХЯДЄЯд░ ЯдЊЯДюЯдеЯдЙЯдЪЯДЂЯдЋЯДЂ ЯдаЯд┐ЯдЋЯдаЯдЙЯдЋ ЯдЋЯд░ЯДЄ ЯдеЯДЄЯДЪЯЦц ЯдеЯдЙЯд░ЯДђЯд░ЯдЙ ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯди ЯддЯДЄЯдќЯд▓ЯДЄЯдЄ ЯдгЯдЙЯд░ ЯдгЯдЙЯд░ ЯдЊЯДюЯдеЯдЙ ЯдаЯд┐ЯдЋ ЯдЋЯДЄЯде ЯдЋЯд░ЯДЄ ЯдцЯдЙ ЯдЈЯдЋ ЯдЋЯдЦЯдЙЯДЪ ЯдгЯд▓ЯдЙ ЯдЅЯдџЯд┐ЯДј Яд╣ЯдгЯДЄ ЯдеЯдЙЯЦц ЯдЈЯдгЯдѓ ЯдИЯдг ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯдиЯДЄЯд░ ЯдИЯдЙЯд«ЯдеЯДЄЯдЄ ЯдИЯдгЯдЙЯдЄ ЯдЈЯд«ЯдеЯдЪЯдЙ ЯдЋЯд░ЯДЄ , ЯдцЯдЙЯдЊ ЯдеЯдЙЯЦц ЯдџЯд░Яд┐ЯдцЯДЇЯд░ ЯдГЯДЄЯддЯДЄ ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯдиЯдЪЯд┐Яд░ ЯдєЯдџЯд░ЯдБ ЯдЊ ЯдџЯДІЯдќЯДЄЯд░ ЯдєЯдгЯд░ЯДЇЯдцЯде ЯддЯДЄЯдќЯДЄ ЯдеЯдЙЯд░ЯДђЯдЪЯд┐ ЯдгЯДЂЯдЮЯДЄ ЯдеЯДЄЯДЪ ЯдцЯдЙЯдЂЯдЋЯДЄ ЯдЋЯд┐ ЯдЋЯд░ЯдцЯДЄ Яд╣ЯдгЯДЄЯЦц ЯдЈЯдЪЯдЙ Яд«ЯдЙЯдЮЯДЄ Яд«ЯдЙЯдЮЯДЄ ЯдгЯдЙЯДюЯдЙЯдгЯдЙЯДюЯд┐Яд░ ЯдфЯд░ЯДЇЯд»ЯдЙЯДЪЯДЄ ЯдџЯд▓ЯДЄ Яд»ЯдЙЯДЪЯЦц ЯдфЯдЙЯдЂЯдџ Яд«Яд┐ЯдеЯд┐ЯдЪЯДЄЯд░ ЯдЋЯдЦЯДІЯдфЯдЋЯдЦЯдеЯДЄ ЯдЋЯДЄЯдЅ Яд»ЯддЯд┐ ЯдфЯдеЯДЄЯд░ ЯдЋЯДЂЯДюЯд┐ЯдгЯдЙЯд░ ЯдЊЯДюЯдеЯдЙ ЯдаЯд┐ЯдЋ ЯдЋЯд░ЯДЄ ; ЯдцЯдЙЯдЂЯд░ ЯддЯДЂРђЎЯд░ЯдЋЯд« ЯдЁЯд░ЯДЇЯдЦ Яд╣ЯдцЯДЄ ЯдфЯдЙЯд░ЯДЄЯЦц Яд╣ЯДЪ, ЯдеЯдЙЯд░ЯДђЯдЪЯд┐ ЯдЁЯдгЯдџЯДЄЯдцЯдеЯДЄ ЯдфЯДЂЯд░ЯдеЯДІ ЯддЯДђЯд░ЯДЇЯдў ЯдЁЯдГЯДЇЯд»ЯдЙЯдИЯДЄЯд░ ЯдЋЯдЙЯд░ЯдБЯДЄ ЯдЁЯдИЯДЇЯдгЯдИЯДЇЯдцЯд┐ ЯдгЯДІЯдД ЯдЋЯд░ЯдЏЯДЄ ЯдфЯДЂЯд░ЯДЂЯдиЯдЪЯд┐Яд░ ЯдИЯдЙЯд«ЯдеЯДЄЯЦц ЯдЁЯдЦЯдгЯдЙ , ЯдєЯдИЯд▓ЯДЄ ЯдИЯДЄ ЯдЋЯд┐ ЯдЋЯд░ЯдгЯДЄ ЯдгЯДЂЯдЮЯдцЯДЄ ЯдеЯдЙ ЯдфЯДЄЯд░ЯДЄ ЯдгЯдЙ ЯдЁЯдИЯДЇЯдЦЯд┐Яд░ЯдцЯдЙ ЯдбЯдЙЯдЋЯдцЯДЄ ЯдЊЯДюЯдеЯдЙ ЯдаЯд┐ЯдЋ ЯдЋЯд░ЯДЄ ЯдџЯд▓ЯДЄЯдЏЯДЄЯЦц ЯдфЯдЙЯдХЯДЇЯдџЯдЙЯдцЯДЇЯд» ЯдцЯДІ ЯдЁЯдгЯдХЯДЇЯд»ЯдЄ ; ЯдЈЯдХЯд┐ЯДЪЯдЙ ЯдЊ ЯддЯдЋЯДЇЯдиЯд┐ЯдБ ЯдЈЯдХЯд┐ЯДЪЯдЙЯд░ ЯдЁЯдеЯДЄЯдЋЯдЌЯДЂЯд▓ЯДІ ЯддЯДЄЯдХЯДЄЯдЊ ЯдЊЯДюЯдеЯдЙ ЯдгЯдЙЯд╣ЯДЂЯд▓ЯДЇЯд»ЯдфЯДЇЯд░ЯдЙЯДЪЯЦц ЯдєЯд«ЯдЙЯддЯДЄЯд░ ЯдюЯДђЯдгЯддЯДЇЯддЯдХЯдЙЯДЪ ЯдгЯдЙЯдѓЯд▓ЯдЙЯддЯДЄЯдХЯДЄ ЯдЊЯДюЯдеЯдЙ ЯдгЯд┐Яд▓ЯДЂЯдфЯДЇЯдцЯд┐Яд░ ЯдЋЯДІЯде ЯдИЯд«ЯДЇЯдГЯдЙЯдгЯдеЯдЙ ЯддЯДЄЯдќЯдЏЯд┐ ЯдеЯдЙЯЦц ЯдєЯд░ЯДІ ЯдЋЯДЪЯДЄЯдЋ ЯдюЯДЄЯдеЯдЙЯд░ЯДЄЯдХЯде ЯдЊЯДюЯдеЯдЙ ЯдгЯДЇЯд»ЯдЙЯдфЯдЋ ЯдЊ ЯдгЯд╣ЯДЂЯд▓ЯдГЯдЙЯдгЯДЄЯдЄ ЯдЦЯдЙЯдЋЯдгЯДЄЯЦц
ЯдфЯДЇЯд░ЯдЋЯдЙЯдХЯдЋЯдЙЯд▓ЯдЃ ЯдюЯдЙЯдеЯДЂЯДЪЯдЙЯд░Яд┐ ЯДеЯДдЯДДЯДГ
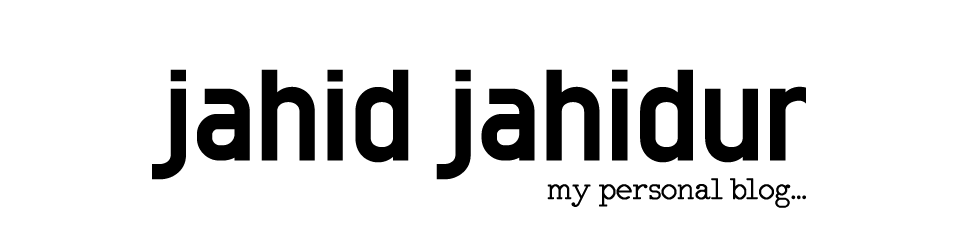
ЯдИЯдЙЯд«ЯДЇЯдфЯДЇЯд░ЯдцЯд┐ЯдЋ Яд«ЯдеЯДЇЯдцЯдгЯДЇЯд»