а¶Па¶З а¶°а¶ња¶ЄаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞аІЗ а¶ХаІЯаІЗа¶ХබගථаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඐ඲ඌථаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶ЄаІА ඐථаІНа¶ІаІБබаІЗа¶∞ а¶Ха¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶£аІЗ а¶ЖඐබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶є а¶Жа¶ђаІБ а¶Єа¶ЊаІЯаІАබ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ аІѓаІ¶ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЪаІЗа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ ඙а¶∞඙а¶∞ බаІБвАЩа¶Яа¶њ а¶Ша¶∞аІЛаІЯа¶Њ а¶Жа¶°аІНа¶°а¶Њ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Ха¶Ња¶ЯඌථаІЛа¶∞ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶∞аІНа¶Ш а¶ЄаІНа¶ЃаІГටග а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ а¶Іа¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤аІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чටа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ බаІБвАЩа¶ЯаІЛ а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Ња•§ ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІНа¶∞ටග а¶ХаІГටа¶ЬаІНа¶Юටඌ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප ; а¶Жа¶∞ а¶ђа¶єаІБබගථ ඙а¶∞аІЗ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶Па¶З а¶ЄаІНа¶ЃаІГටගа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ථаІЗаІЬаІЗ බаІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ча•§
පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х-а¶ЫඌටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ша¶∞аІЛаІЯа¶Њ а¶ЕථаІНටа¶∞а¶ЩаІНа¶Ч а¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНටа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ПටаІЛ а¶ђаІЗපаІА а¶ЕථඌаІЬа¶Ња¶ЃаІНа¶ђа¶∞а¶ЃаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓаІЗ, а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶ња¶∞ а¶Жа¶≤а¶ЄаІНа¶ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶Іа¶ХаІНа¶ѓ, а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБ-а¶ђаІЗබථඌ ථගаІЯаІЗа¶У а¶Хඕඌ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х-а¶ЫඌටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ша¶∞аІЛаІЯа¶Њ а¶Жа¶°аІНа¶°а¶Њ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ ඐගථаІЛබථаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶єа¶≤аІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ђа¶ЊаІЬටග ඙ඌа¶Уа¶®а¶Ња•§
а¶Жа¶°аІНа¶°а¶Ња¶∞ පаІБа¶∞аІБටаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶ЄаІА ඪටаІАа¶∞аІНඕ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶њаІЯаІЗ බගа¶≤, вАШа¶ЬඌයගබаІЗа¶∞ ටаІЛ ථගаІЯඁගට а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶У а¶Ха¶њ а¶Па¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ?вАЩ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІНඁටගඪаІВа¶Ъа¶Х ඁඌඕඌ ථаІЗаІЬаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ЙаІОа¶Єа¶Ња¶є ථගаІЯаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАШа¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Б а¶У ටаІЛ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ බප а¶ђа¶Ња¶∞аІЛ а¶ђа¶Ња¶∞ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗ!вАЩ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ а¶≠а¶ЩаІНа¶ЧаІАටаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ЯаІЗа¶∞ ඙аІЗаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Чටඐа¶Ыа¶∞ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶Па¶З ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£ යඌඪගආඌа¶ЯаІНа¶Яа¶Њ а¶Ъа¶≤а¶≤а•§
а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ඐගපаІНඐඪඌයගටаІНа¶ѓ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ ථගаІЯаІЗ ථටаІБථ а¶ЄаІНඐ඙аІНථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ පаІЛථඌа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ЬඁගටаІЗ а¶ХаІЗа¶∞ඌථаІАа¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Уа¶ЦඌථаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ аІ® а¶ђа¶ња¶Ша¶Ња¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶њ ඐගපаІНа¶ђ ඪඌයගටаІНа¶ѓа¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ ථаІАа¶ЪаІЗ а¶Ха¶Ѓа¶ња¶Йථගа¶Яа¶њ а¶ЄаІЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗа•§ а¶ѓаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Й඙ඌа¶∞аІНа¶Ьථ ඕаІЗа¶ХаІЗ, а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ а¶єа¶≤аІЗа¶У а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶≤ඌථаІЛа¶∞ ඪඌපаІНа¶∞аІЯ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ аІ®аІђ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ ඙ඌආа¶Х-а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞аІЗа•§ а¶Па¶Цථ පаІБа¶ІаІБඁඌටаІНа¶∞ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗа¶З аІ®аІЂ а¶≤а¶ХаІНа¶Ј а¶ЫඌටаІНа¶∞-а¶ЫඌටаІНа¶∞аІА а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶З ඙а¶∞аІЗа•§ аІ®аІ¶аІІаІѓ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЄаІНඐ඙аІНථ аІ™аІ¶ а¶≤а¶ХаІНа¶Ј а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶ХаІЗ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶З඙аІЬа¶Њ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ЄаІВа¶ЪගටаІЗ а¶Жථඌа¶∞а•§
а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІЗථ а¶ХаІЛථ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ ථаІЗа¶З , а¶Па¶З ඙аІНа¶∞පаІНථаІЗа¶∞ а¶ЙටаІНටа¶∞аІЗ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЄаІЛа¶Ьа¶Њ а¶Ьа¶ђа¶Ња¶ђ, ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ ටඌа¶Ба¶∞ ඙а¶ЫථаІНබаІЗа¶∞ ථаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞а¶У ටඌа¶З ඁථаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ බаІАа¶∞аІНа¶Шබගථ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ІаІАа¶∞аІЗ а¶ІаІАа¶∞аІЗ а¶ђа¶З ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗ а¶ђа¶Њ а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶∞ а¶ЄаІЗ ඁඌථඪа¶Ьа¶ЧаІО а¶ЧаІЬаІЗ а¶УආаІЗ ; а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞а¶З ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞а¶£а¶ЊаІЯ а¶Еа¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓ а¶Еථඌа¶Ха¶Ња¶ЩаІНа¶ХаІНඣගට а¶ђа¶Ња¶єаІБа¶≤аІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЯаІЛа¶Яа¶Ха¶Њ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Еа¶∞аІНඕයаІАа¶®а•§ ඙а¶∞ගපаІАа¶≤ගට ඁථ а¶Па¶ХබගථаІЗ а¶єаІЯ ථඌ; а¶Єа¶ЃаІЯ а¶≤а¶Ња¶ЧаІЗа•§ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶≠ගටа¶∞аІЗ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЫаІЛа¶Я а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶ња¶≤ථඌаІЯටථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ХаІЛථа¶Яа¶њ а¶ђаІЬ а¶ЄаІЗඁගථඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ, а¶ХаІЛථа¶Яа¶њ ඙ඌආа¶Ъа¶ХаІНа¶∞аІЗа¶∞а•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗ බаІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗථ а¶ШаІБа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ШаІБа¶∞а¶њаІЯаІЗа•§
а¶ЖඐබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶є а¶Жа¶ђаІБ а¶Єа¶ЊаІЯаІАබ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Хටඌа¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶Хඐගටඌ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Ја¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ බපа¶ХаІЗ вАШа¶Ха¶£аІНආඪаІНа¶ђа¶∞вА٠඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶У а¶Єа¶ЃаІН඙ඌබථඌ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Уа¶З ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Њ а¶Іа¶∞аІЗ а¶ЙආаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Ја¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ බපа¶ХаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Єа¶Ња¶∞а¶ња¶∞ а¶Ха¶ђа¶њ а¶У а¶≤аІЗа¶Ца¶ХаІЗа¶∞а¶Ња•§ ඙а¶∞аІЗа¶∞ බаІЗаІЬа¶ѓаІБа¶Ч а¶ЃаІЗටаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶Яа¶ња¶≠а¶њ а¶ЪаІНඃඌථаІЗа¶≤аІЗ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶У ඐගථаІЛබථඁаІВа¶≤а¶Х а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ථඌ ථගаІЯаІЗа•§ ඙а¶∞ගපаІАа¶≤ගට а¶∞аІБа¶Ъа¶ња¶∞ බа¶∞аІНපа¶Х а¶ЧаІЬаІЗ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ ඙аІЗа¶ЫථаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Еඐබඌථ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Хටඌ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Єа¶Ња¶Ђа¶≤аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ђа¶≤аІНа¶ѓ а¶Еа¶Ча¶£а¶®а¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ, а¶Е඙а¶∞а¶ња¶ЃаІЗаІЯ а¶Па¶ђа¶В а¶Ха¶ња¶ВඐබථаІНටаІАටаІБа¶≤аІНа¶ѓ ! а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБ ථගаІЯаІЗ а¶ЃаІЗටаІЗ ඕඌа¶Ха¶ЊаІЯ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶ња¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඁථаІЛа¶ѓаІЛа¶Ч බගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ а¶®а¶ња•§ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶ЄаІМа¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ХаІБපа¶≤ඌබග а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶Па¶Цථ а¶Ха¶њ а¶Ха¶њ ඙аІЬа¶ЫаІЗථ, а¶ђа¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶ња¶∞ а¶Ха¶њ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶≤аІЗ , а¶єа¶Ња¶Єа¶ња¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАШ а¶ґаІЛථ а¶єаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶ЯаІБ а¶ђаІЗපаІА а¶Ха¶∞аІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤аІЗ а¶Уа¶З බඌаІЬа¶ња¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶Њ а¶≠බаІНа¶∞а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ ( ඙аІЬаІБථ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ ආඌа¶ХаІБа¶∞) а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Ња¶Ха¶Ња¶Ыа¶њ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶£ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞ටඌඁ!вАЩ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІЗа¶Й а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞а¶≤, вАШ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶£ а¶ђаІЗපаІА а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶З а¶Ха¶њ а¶Єа¶ђ? а¶ЧаІБа¶£а¶Чට ඁඌථ ථඌ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶£ а¶ђаІЗපаІА බගаІЯаІЗ а¶Ха¶њ а¶єа¶ђаІЗ?вАЩ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, вАШа¶≠аІБа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗа¶У ථඌ а¶ХаІЛаІЯඌථаІНа¶Яа¶ња¶Яа¶њ ථගа¶ЬаІЗа¶У а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ХаІЛаІЯа¶Ња¶≤а¶ња¶Яа¶ња•§вАЩ
ඪටаІНа¶ѓа¶ња¶З , а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ථඌථඌ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶ЃаІЗටаІЗ ඕඌа¶Ха¶ЊаІЯ, ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Х ඪටаІНටඌа¶ХаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථථග а•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЖаІЬа¶Ња¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶∞аІЗа¶Х ඪටаІАа¶∞аІНඕ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶≤аІЗа¶Ца¶Х ඪටаІНටඌа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х-а¶ЄаІБа¶≤а¶≠ а¶ЙබаІНබаІА඙а¶Х а¶ђа¶ХаІНටаІГටඌ а¶У а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶Ха¶Ња¶£аІНа¶° а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ђаІЗපаІА а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶У а¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ѓа¶Ха¶∞а•§ ටඌ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Жа¶∞аІЛ බපа¶Ьථ а¶≤аІЗа¶Ца¶ХаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ටගථග ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶њ ථගаІЯаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНට ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ඙аІЗටඌඁ а¶ХаІЛඕඌаІЯ? ටඌа¶З а¶ѓа¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶ђаІГයටаІНටඁ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶∞аІНඕаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа¶З а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗ ඪථаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ ඙аІМа¶Ба¶ЫඌථаІЛа¶∞ а¶Хඕඌ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶У а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ බаІЗа¶∞аІА а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ ඥඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЯаІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶Ђа¶ња¶ХаІЗ а•§ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶ЄаІА ඐථаІНа¶ІаІБа¶∞а¶Њ ඥඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶Ђа¶ња¶ХаІЗа¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග ඥඌа¶Ха¶Ња¶∞ ඃටаІНа¶∞ටටаІНа¶∞ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ ථаІЛа¶Ва¶∞а¶Њ а¶Жа¶ђа¶∞аІНа¶Ьථඌ а¶У ඥඌа¶Ха¶Ња¶∞ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶Жа¶Ъа¶∞а¶£-а¶ђаІЛа¶І , а¶Єа¶ња¶≠а¶ња¶Ха¶ЄаІЗථаІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Еа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Уආඌа¶≤а•§ а¶Ьථඪа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Ъඌ඙ ථඌа¶Ха¶њ а¶ЕථаІНа¶ѓа¶ХаІЛථ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌа¶Ша¶Ња¶ЯаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ ඕаІБටаІБ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶£ а¶ђаІЗаІЬаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ , а¶ХаІЗ а¶ЬඌථаІЗа•§ а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶ња¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ බаІЗපаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Жа¶Зථ а¶ЃаІЗථаІЗ а¶Ъа¶≤а¶њ, ථගа¶ЬаІЗа¶∞ බаІЗපаІЗ ආගа¶Х ටඌа¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶ЯаІЛа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ බаІЗපаІЗ а¶Еа¶Ђа¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶єаІЯа•§ а¶Па¶З ඃඌටаІНа¶∞а¶Ња¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶ђаІЗපаІАа¶∞а¶≠а¶Ња¶Ча¶З а¶Па¶Ѓа¶ња¶∞аІЗа¶ЯаІНа¶Є а¶ПаІЯа¶Ња¶∞а¶≤а¶Ња¶ЗථаІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЂаІНа¶≤а¶Ња¶За¶ЯаІЗ බаІБа¶ђа¶Ња¶З-а¶П а¶ЯаІНа¶∞ඌථа¶Ьа¶ња¶Я ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Уа¶З а¶ЂаІНа¶≤а¶Ња¶За¶Яа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶Па¶Цථ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ђа¶Ња¶ЬаІЗа¶Я а¶ЂаІНа¶≤а¶Ња¶За¶Я а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶ЄаІА පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶ХаІЗа¶∞а¶Њ а¶ЗබඌථаІАа¶В а¶Па¶Ѓа¶ња¶∞аІЗа¶ЯаІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЂаІНа¶≤а¶Ња¶За¶Я ටаІЗඁථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶Ѓа¶ња¶∞аІЗа¶ЯаІНа¶Є а¶Па¶Ха¶Єа¶ЃаІЯ а¶Йа¶ЪаІНа¶ЪඐගටаІНට , а¶Ѓа¶ІаІНඃඐගටаІНට ථගඁаІНථඐගටаІНට а¶Єа¶ђа¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ ඃඌටаІНа¶∞аІАа¶∞ ඙аІНа¶∞඲ඌථ ඐඌයථ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЗබඌථаІАа¶В а¶Йа¶ЪаІНа¶ЪඐගටаІНට а¶У а¶Ѓа¶ІаІНඃඐගටаІНට ඃඌටаІНа¶∞аІАබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඌ඲ඌථаІНа¶ѓ а¶ђаІЗපаІАа•§ ටаІЛ а¶ђа¶Ыа¶∞ ඙ඌа¶Ба¶ЪаІЗа¶Х а¶Жа¶ЧаІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ХаІНа¶≤ඌථаІНට а¶єаІЯаІЗ ඥඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶За¶Ѓа¶ња¶ЧаІНа¶∞аІЗපථ ඙ඌа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶≤а¶Ња¶ЧаІЗа¶Ь а¶ђаІЗа¶≤аІНа¶ЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶њ ඁඌටаІНа¶∞а•§ а¶Уа¶З а¶ЂаІНа¶≤а¶Ња¶За¶ЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ња¶Ва¶єа¶≠а¶Ња¶Ч а¶≠а¶Ња¶Ч ඙аІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶ЄаІА පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Ха•§ ඙аІНа¶∞ටග а¶ЂаІНа¶≤а¶Ња¶За¶ЯаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Па¶БබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ ථඌ а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ а¶Па¶ЃаІНа¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶ХаІЗපථ а¶Ђа¶∞аІНа¶Ѓ а¶Ђа¶ња¶≤ඌ඙ а¶Ха¶∞аІЗ බගටаІЗ а¶єа¶§а•§а¶ѓа¶Ња¶З а¶єаІЛа¶Х, а¶≤а¶Ња¶ЧаІЗа¶Ь а¶ђаІЗа¶≤аІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ බаІЗа¶Ца¶њ а¶Па¶Х ඙аІНа¶∞а¶ђа¶Ња¶ЄаІА පаІНа¶∞а¶Ѓа¶ња¶Х а¶єаІБа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ а¶Єа¶ња¶Ча¶Ња¶∞аІЗа¶Я а¶Іа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ යටа¶≠а¶ЃаІНа¶ђ ! а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶Єа¶ња¶Ча¶Ња¶∞аІЗа¶Я а¶Ца¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗථ а¶ХаІЗа¶®а•§ ටаІЛ , а¶ЄаІЗ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ ටඌа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЙටаІНටа¶∞ බගа¶≤а•§ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ а¶ђаІБа¶Эа¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, බаІБа¶ђа¶Ња¶З а¶ПаІЯа¶Ња¶∞඙аІЛа¶∞аІНа¶ЯаІЗ а¶ХаІЛඕඌаІЯ а¶Єа¶ња¶Ча¶Ња¶∞аІЗа¶Я а¶Іа¶∞а¶Ња¶≤аІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЯබගථ බаІБа¶ђа¶Ња¶ЗаІЯаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ , ථගаІЯа¶Ѓ а¶ЃаІЗථаІЗ а¶Ъа¶≤а¶≤аІЗථ ; а¶ѓаІЗа¶З ථඌ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤ඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЯගටаІЗ ඙ඌ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа¶ЫаІЗථ, а¶Єа¶ђ ථගаІЯа¶Ѓа¶ХඌථаІБථ а¶≠аІЗа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗ а¶За¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Ха¶∞а¶≤? а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЙටаІНටаІЗа¶Ьගට ඐඌබඌථаІБඐඌබаІЗ а¶ПаІЯа¶Ња¶∞඙аІЛа¶∞аІНа¶Я ඙аІБа¶≤ගප а¶Па¶ЄаІЗ ඙аІЬа¶≤аІЗ, а¶Ша¶Яථඌа¶∞ а¶Уа¶ЦඌථаІЗа¶З පаІЗа¶Ј а¶єаІЯа•§ а¶ѓаІЗ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶Яа¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶Йа¶Ъа¶њаІО, а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ђаІЯа¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ පඌඪаІНටගඃаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІЗа¶∞ а¶≠аІЯ බаІЗа¶Ца¶њаІЯаІЗ а¶Хටа¶Цඌථග а¶Єа¶Ња¶Ђа¶≤аІНа¶ѓ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа•§ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ђ ඕаІБටаІБ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶≠ගටа¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶Йа¶Ъа¶њаІОа•§ а¶Еа¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓ а¶ЬаІАа¶ђа¶Ња¶£аІБ а¶Ха¶Ђ ඕаІБටаІБа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬа¶ЫаІЗ ; а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНටඐаІЯа¶ЄаІНа¶ХබаІЗа¶∞ ථඌ а¶ђаІБа¶Эа¶њаІЯаІЗ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗ а¶ђаІЛа¶ЭඌථаІЛ а¶Йа¶Ъа¶њаІОа•§ ඕаІБටаІБ-а¶Ха¶Ђ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Њ, ඃටаІНа¶∞ටටаІНа¶∞ а¶ЃаІВටаІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶Ња¶Ч а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶ња¶∞а¶Њ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶Ха¶Цථа¶З а¶Ха¶∞аІЗ ථඌ ; බаІЗපаІЗ а¶Еа¶ђа¶≤аІАа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ЬඌථаІЗ, ථගаІЯа¶Ѓ а¶≠а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶Яа¶Ња¶З ථගаІЯа¶Ѓа•§ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶ња¶У а¶Ъа¶Ха¶≤аІЗа¶Я а¶Яа¶Ђа¶ња¶∞ а¶ЃаІЛаІЬа¶Х а¶ЖපаІЗ඙ඌපаІЗ ඐගථ-а¶ђа¶ХаІНа¶Є ථඌ ඙аІЗа¶≤аІЗ ඙а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ බගа¶З, ඃඕඌඪаІНඕඌථаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ! а¶ЄаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶ња¶З а¶єаІЯටаІЛ ඥඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌаІЯ а¶ѓа¶Њ а¶За¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ටඌа¶З а¶ЂаІЗа¶≤а¶Ыа¶њ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Па¶Яа¶Ња¶З ථගаІЯа¶Ѓ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ьථа¶Ча¶£аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙ඌඐа¶≤а¶ња¶Х а¶ЯаІЯа¶≤аІЗа¶Я а¶ђа¶Њ ඐගථ-а¶ђа¶ХаІНа¶Є а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З ථаІЗа¶З а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶З а¶Ъа¶≤аІЗа•§
а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶ња¶∞ а¶Жа¶≤а¶ЄаІНа¶ѓ ථගаІЯаІЗ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЩаІНа¶ЧඌටаІНа¶Ѓа¶Х а¶Хඕඌ а¶ђа¶Ња¶∞аІНටඌ а¶Жа¶ЧаІЗа¶У පаІБථаІЗа¶Ыа¶њ, а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ පаІБථа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ХаІЗа¶Й а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЯаІЯа¶≤аІЗа¶ЯаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІНа¶ЫථаІНථටඌа¶∞ ඙аІНа¶∞පа¶Ва¶Єа¶Њ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ , а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶њаІЯаІЗ බගа¶≤аІЗථ а¶Па¶З а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶У а¶ђа¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶≤аІАа¶∞ а¶Жа¶≤а¶ЄаІНа¶ѓ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶Ь පаІЗа¶Ј а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞, ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶За¶Йа¶∞ගථඌа¶≤ а¶ЂаІНа¶≤аІНඃඌප а¶Ха¶∞ටаІЗа¶У а¶Па¶БබаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤а¶ЄаІНа¶ѓ а¶≤а¶Ња¶ЧаІЗа•§ а¶ђа¶Ња¶ІаІНа¶ѓ а¶єаІЯаІЗ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ,඙а¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІНа¶ЫථаІНථටඌ а¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІАබаІЗа¶∞ а¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ ඙аІНа¶∞ටග аІІаІ¶-аІІаІЂ ඁගථගа¶Я ඙а¶∞඙а¶∞ а¶ѓаІЗථ а¶ЯаІЯа¶≤аІЗа¶Яа¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶ХаІЗ а¶ЂаІНа¶≤аІНඃඌප а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶єаІЯа•§
а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ ඥඌа¶Ха¶Њ පයа¶∞ ටаІЛ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඐගපඌа¶≤ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඁටаІЛа•§ а¶ЕථаІНа¶ѓ ඙аІБа¶∞ථаІЛ පයа¶∞аІЗа¶∞ ඁටаІЛ බаІАа¶∞аІНа¶Ша¶ЄаІНඕඌаІЯаІА а¶∞аІБа¶Ъа¶ња¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶ЧаІЬаІЗ а¶Уආඌа¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч ඙ඌаІЯ а¶®а¶ња•§ а¶ЃаІВа¶≤ а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ѓа¶Ђа¶Га¶ЄаІНа¶ђа¶≤аІЗа¶∞ а¶∞аІБа¶Ъа¶ња¶Єа¶ЃаІН඙ථаІНථ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටගඐඌථබаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶У а¶ђаІЗපаІА ඙аІНа¶∞ඌබаІБа¶∞аІНа¶≠а¶Ња¶ђ ඐගපаІБබаІНа¶І а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІНа¶ѓ а¶Ьථа¶Ча¶£аІЗа¶∞а•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ ඙аІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶Еඕඐඌ ථඌ ඙аІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ටඌа¶ЧගබаІЗ а¶Па¶Х ඐගපඌа¶≤ а¶ЬථඪаІНа¶∞аІЛට а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗ ඥඌа¶Ха¶ЊаІЯ а•§ ටඌа¶З а¶Па¶З а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІНа¶ѓ ඥඌа¶Ха¶Ња¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶∞ ථඌа¶Ча¶∞а¶ња¶Х а¶Єа¶ЪаІЗටථටඌ а¶ЧаІЬаІЗ а¶ЙආටаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶≤а¶Ња¶Ча¶ЫаІЗа•§
а¶Жа¶∞аІЛ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඐබа¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Еа¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ЙආаІЗ а¶Па¶≤аІЛ а¶Жа¶≤аІЛа¶ЪථඌаІЯ а•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶ЩаІБа¶≤ а¶Ѓа¶Яа¶ХඌථаІЛа¶∞ а¶Еа¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶Є а¶Жа¶ЫаІЗ а•§ а¶Па¶З а¶ђа¶Ња¶ЬаІЗ а¶Еа¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶Єа¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶У а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ХаІЛථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶З ථගඣаІНа¶ХаІГටග ඙ඌа¶За¶®а¶ња•§ а¶ХටаІЛ а¶ЬථаІЗ а¶≤а¶ЬаІНа¶Ьа¶Њ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, ටඐаІБ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ථඌа¶Ха¶њ , а¶Па¶Яа¶њ ථගаІЯаІЗ а¶ХаІЛථ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙а¶∞а¶Ња¶Ѓа¶∞аІНප а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶°а¶Ња¶ХаІНටඌа¶∞ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ යටඌප а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶ЫаІЗථ, вАШа¶ЫаІЛа¶Я а¶ђаІЗа¶≤а¶Њ а¶єа¶≤аІЗ а¶ЃаІБа¶∞а¶ђаІНа¶ђаІА а¶Ха¶Ња¶∞аІЛ а¶Па¶Х а¶Іа¶Ѓа¶ХаІЗа¶З а¶Па¶Яа¶Њ а¶ЄаІЗа¶∞аІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶§а•§ а¶Па¶З а¶ђаІЯа¶ЄаІЗ а¶Па¶Цථ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ ථаІЯа•§вАЩ
а¶Па¶З а¶Хඕඌа¶∞ යඌට а¶Іа¶∞аІЗа¶З а¶ЄаІБа¶ЄаІНඕ а¶Еа¶≠аІНа¶ѓа¶Ња¶Є а¶ЧаІЬаІЗ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ХаІЛаІЯඌථаІНа¶Яа¶Ња¶Ѓ а¶У а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Ьඌටа¶ХаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Па¶ЄаІЗ ඙аІЬа¶≤а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ථගа¶ЬаІЗа¶У а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶Еа¶ђа¶Ња¶Х а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶З а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ ඐඌටගа¶Ша¶∞, ටඌа¶Ба¶∞ а¶ХаІЗථ а¶ХаІЛаІЯඌථаІНа¶Яа¶Ња¶Ѓ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђаІЗප а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶≠а¶ња¶°а¶ња¶У а¶ХаІНа¶≤ග඙ а¶ђа¶ХаІНටаІГටඌ а¶За¶Йа¶Яа¶ња¶Йа¶ђаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ХаІЛаІЯඌථаІНа¶Яа¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞පа¶Ва¶Єа¶ЊаІЯа•§ а¶ѓа¶Њ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ , а¶ђаІЗප а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ යආඌаІО а¶Ха¶∞аІЗ а¶ХаІНа¶≤ඌථаІНටග а¶≠а¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХаІЛථ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶З а¶Уа¶Ьථ බаІНа¶∞аІБට а¶Ха¶ЃаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Еඕа¶Ъ а¶ХаІЛථ а¶Еа¶ЄаІБа¶ЄаІНඕටඌ ථаІЗа¶За•§ ඁථаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤, а¶Па¶Яа¶Ња¶З а¶ђаІЛа¶Іа¶єаІЯ а¶ЄаІЗа¶З вАШа¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶Іа¶ХаІНа¶ѓвАЩ ! а¶ЕඐපаІЗа¶ЈаІЗ а¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶Іа¶ХаІНа¶ѓ а¶Ъа¶≤аІЗа¶З а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ХаІЛаІЯඌථаІНа¶Яа¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ පයаІАබ а¶Жа¶≤ а¶ђаІБа¶Ца¶Ња¶∞аІАа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ а¶ЕථаІЗа¶ХබගථаІЗа¶∞а•§ ටගථග а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ЖඁථаІНටаІНа¶∞а¶£ а¶ЬඌථගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІАа¶У а¶ХаІЛаІЯඌථаІНа¶Яа¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ ඪ඙аІНа¶∞පа¶Ва¶Єа•§ а¶Ха¶њ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Па¶Хබගථ а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞ а¶єа¶≤аІЗථ а¶ХаІЛаІЯඌථаІНа¶Яа¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа•§ ඙аІНа¶∞ඕඁබගථаІЗа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Х а¶Ша¶£аІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶Йථග а¶ђаІБа¶ЭаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗථ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Яа¶Њ а¶ХаІЛඕඌаІЯа•§ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶Ьа¶ЧටаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶Ѓа¶∞аІНඁඌථаІНටගа¶Х а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶ѓаІЗඁථ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЄаІМථаІНබа¶∞аІНа¶ѓа¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗ ථඌ ; а¶ѓаІЗඁථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЪаІЛа¶Ц ථගа¶ЬаІЗ а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБ බаІЗа¶ЦටаІЗ ඙ඌаІЯ , а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗ ඙ඌаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶Ѓа¶ЄаІНටගඣаІНа¶Ха¶У ආගа¶Х ටаІЗඁථග а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶ЕථаІНа¶ѓа¶ХаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶≤ථඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶≤ථඌ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ХаІЗа¶Й ථаІЗа¶З ! а¶Ѓа¶ЄаІНටගඣаІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ъа¶∞а¶£ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ ථගа¶∞аІНа¶ђаІЛа¶ІаІЗа¶∞ ඁටа¶З ඁථаІЗ а¶єаІЯа•§ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ඃබග а¶≠аІБа¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђаІЛа¶ЭඌථаІЛ а¶ѓа¶ЊаІЯ , а¶ЄаІЗ а¶ђаІБа¶ЭаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа•§ а¶ХаІЛаІЯඌථаІНа¶Яа¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶њ а¶єаІЯටаІЛ ටඌа¶За•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶ђа¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶Іа¶ХаІНа¶ѓ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Па¶З а¶Еа¶ЯаІЛ а¶Єа¶Ња¶ЬаІЗපථ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶ња¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶≠ඌඐගට а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤ ටඌа¶Ба¶∞ පа¶∞аІАа¶∞аІЗа•§ а¶ѓаІЗа¶З ථඌ ටගථග а¶Йа¶≤аІНа¶ЯаІЛ а¶≠а¶Ња¶ђа¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗථ а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞ ටඌа¶∞аІБа¶£аІНа¶ѓаІЗа•§
а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඌටаІНа¶ѓа¶єа¶ња¶Х а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЖඁථаІБа¶Ја¶ња¶Х а¶Ъඌ඙, ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНටග а¶Е඙аІНа¶∞ඌ඙аІНටගа¶∞ а¶ЧаІЬа¶Ѓа¶ња¶≤ , යථаІНа¶ѓаІЗ а¶єаІЯаІЗ а¶ЫаІБа¶ЯаІЗ а¶ђаІЗаІЬඌථаІЛ а¶Жа¶∞ ථගа¶∞а¶ђа¶ЪаІНа¶ЫගථаІНථ යටඌපඌа¶∞ а¶ЬаІАа¶ђа¶®а•§ а¶ХаІЗථ а¶ПටаІЛ යටඌපඌ а¶Ъа¶Ња¶∞ගබගа¶ХаІЗ? а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНටගа¶У ටаІЛ а¶Ха¶Ѓ ථаІЯ ! ටඐаІБ а¶ХаІЗථ ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНටගа¶∞ ටаІБа¶≤ථඌаІЯ а¶Е඙аІНа¶∞ඌ඙аІНටගа¶ХаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ПටаІЛ а¶єа¶Њ а¶єаІБа¶§а¶Ња¶ґа•§ а¶ѓаІЗ а¶Хඕඌа¶Яа¶Њ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶Па¶ђа¶В ඙аІНа¶∞а¶£а¶ња¶Іа¶Ња¶®а¶ѓаІЛа¶ЧаІНа¶ѓ , а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ аІѓаІЂ а¶≠а¶Ња¶Ча¶З а¶Жපඌа¶∞ ඁඌටаІНа¶∞ аІЂ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶ђа¶Њ ටඌа¶∞а¶У а¶Ха¶Ѓ а¶єаІЯටаІЛ ථගа¶∞ඌපඌа¶∞а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ථගа¶∞ඌපඌа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶ња¶ХаІЗ ථගаІЯаІЗ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ђаІЗපаІА а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶ЄаІЗа¶Яа¶њ ඁථаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦаІЗ බаІАа¶∞аІНа¶Ша¶¶а¶ња¶®а•§
а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ а¶ЄаІЗа¶З аІѓаІ¶ а¶Єа¶Ња¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶Ѓа¶Ња¶Эа¶ЦඌථаІЗ බаІАа¶∞аІНа¶Ш а¶ђа¶ња¶∞ටගටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ аІ®аІ¶ а¶ђа¶Ыа¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛа¶ЃаІБа¶Ца¶њ а¶Жа¶°аІНа¶°а¶Ња•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ђ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ ථගаІЯаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌа¶ХаІЗ ඪඃටаІНථаІЗ а¶ПаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Па¶З а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶ђа¶Ыа¶∞ ඙а¶Ба¶ЪගපаІЗа¶Х а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶ХаІЗථ а¶Ьඌථග ඁථаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Уа¶З а¶Хඕඌа¶Яа¶Њ а•§ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ ඐගපаІНඐඪඌයගටаІНа¶ѓ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗ ඙аІЬඌථаІЛ а¶єаІЯ ඙аІГඕගඐаІАа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට а¶≤аІЗа¶Ца¶ХබаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶ЧаІБа¶≤аІЛ вАУටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ХаІЗа¶Й ටаІЛ а¶Жа¶∞ ටඕඌа¶Хඕගට а¶Іа¶Ња¶∞аІНа¶Ѓа¶ња¶Х а¶ђа¶Њ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа¶ЧаІБа¶∞аІБ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІЬටаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ъа¶ња¶∞а¶ЊаІЯට ඐගපаІНඐඪඌයගටаІНа¶ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶ња¶∞а¶ЊаІЯට а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඪඌයගටаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ђаІЗа¶ЫаІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶ЧаІБа¶≤аІЛа•§ а¶Уа¶З а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶ђ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඪබаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНа¶ЂаІБа¶Яගට ඁථаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ ඙аІЬаІЗа¶ЫаІЗа¶За•§ а¶Іа¶∞аІНඁපගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІБа¶∞аІЛ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶У а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶ЙආаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶≤аІЗа¶ЧаІЗа¶За¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ටඌа¶З а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ а¶Еа¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ ථගаІЯаІЗ ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶Цථа¶З а¶ђа¶≤аІЗа¶®а¶®а¶ња•§
а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЃаІЛа¶≤аІНа¶≤а¶Њ ඙аІБа¶∞аІЛයගටа¶∞а¶Њ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶ЬаІАඐථ ඙аІНа¶∞а¶Чටගа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ, а¶Єа¶Ха¶≤ ඙аІНа¶∞පаІНථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗа•§ а¶Жපගа¶∞ බපа¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶Жපа¶Ва¶Ха¶Њ а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶ѓаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ ථඌ , ටඌ ථаІЯа•§ а¶Уа¶З а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶У а¶ХаІЛථ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ЃаІЗа¶Іа¶Ња¶ђаІА а¶≤аІЗа¶Ца¶Ха¶ХаІЗ а¶ђа¶Њ а¶ХаІЛථ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌථа¶ХаІЗ а¶ХаІЛථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа¶ђа¶ња¶∞аІЛа¶ІаІА ටа¶Ха¶Ѓа¶Њ а¶≤а¶Ња¶Ча¶њаІЯаІЗ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤аІЗ ටඌа¶Ба¶∞ බ඀ඌа¶∞а¶Ђа¶Њ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓаІЗට ; а¶ЄаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶єаІБа¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ බаІЗа¶Ца¶Ња•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ටඌа¶З , ථගа¶Цඌබ ඪඌයගටаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ХаІЛථ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶≤ටаІЗථ а¶®а¶Ња•§ යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ථගа¶∞аІНа¶ЬаІАа¶ђ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ ථගаІЯаІЗ а¶Жа¶≤аІЛа¶ЪථඌаІЯ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЙаІОа¶Єа¶Ња¶єа¶У а¶Ыа¶ња¶≤а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶≤аІЛа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЄаІН඙а¶∞аІНපаІЗ а¶Па¶≤аІЗ а¶Ха¶Ња¶Йа¶ХаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Ха¶∞аІЗ ඙ඕ බаІЗа¶Ца¶њаІЯаІЗ බගටаІЗ а¶єаІЯ ථඌ а•§ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЬаІНа¶ђа¶Ња¶≤ඌථаІЛ а¶Жа¶≤аІЛටаІЗ ඙ඕ а¶ЦаІБа¶Ба¶ЬаІЗ ථගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶∞а¶Њ, а¶ЄаІЗа¶З ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶У а¶ѓаІЗඁථ а¶ЕථаІЗа¶Х ඙аІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Яа¶ња¶Єа¶ња¶В а¶Іа¶Ња¶∞аІНа¶Ѓа¶ња¶Х а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ а¶Жථඌа¶ЧаІЛථඌ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа•§ а¶Па¶ЦථаІЛ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඐථаІНа¶ІаІБබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х ඙аІНа¶∞аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶Яа¶ња¶Єа¶ња¶В а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ а¶Жа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ХаІЛථ බаІНа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶З а¶Ша¶£аІНа¶Яа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶Ша¶£аІНа¶Яа¶Њ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ХаІЗа¶ЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ඐගපаІНඐඪඌයගටаІНа¶ѓ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§
а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЫඌටаІНа¶∞පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Пඁථ ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЗа¶ЫаІЗ а¶Еа¶ђа¶≤аІАа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Па¶Цථ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Хඕඌа¶З а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶Є а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶њ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња•§ ඙а¶ЮаІНа¶Ъඌප а¶У а¶Ја¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ බපа¶ХаІЗ ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗа¶∞ පඌඪථඌඁа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶™а¶Ња¶£аІНධඌබаІЗа¶∞ а¶Й඙බаІНа¶∞а¶ђ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටඌ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІАඁඌඐබаІНа¶І а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶њ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯа•§ а¶™а¶Ња¶£аІНධඌබаІЗа¶∞ ඃථаІНටаІНа¶∞а¶£а¶Ња¶∞ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІБа¶ЄаІНඕ, ඙а¶∞ගපаІАа¶≤ගට а¶Ѓа¶ІаІНඃඐගටаІНට а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶ЧаІЬаІЗ а¶ЙආаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶єа¶ња¶Ьа¶Ња¶ђ, а¶ђаІЛа¶∞а¶Ца¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІЛ඙ а¶ђа¶Њ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ ථගаІЯаІЗ вАШа¶ЧаІЗа¶≤ а¶ЧаІЗа¶≤вАЩ а¶∞а¶ђ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶Цථ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Еа¶∞аІНа¶І පටඌඐаІНබаІА ඙ඌа¶∞ а¶єаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ, а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶™а¶Ња¶£аІНධඌබаІЗа¶∞ а¶Й඙බаІНа¶∞а¶ђ а¶ѓаІЗඁථа¶Яа¶њ а¶ђаІЗаІЬаІЗа¶ЫаІЗ ; ඙аІНа¶∞а¶ЧටගපаІАа¶≤а¶∞а¶Њ а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶ХаІЛа¶£а¶†а¶Ња¶Єа¶Њ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа¶ЫаІЗа•§ ථගඁаІНථඁ඲аІНඃඐගටаІНට, а¶Ѓа¶ІаІНඃඐගටаІНට а¶У а¶Йа¶ЪаІНа¶ЪඐගටаІНටаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶єа¶ња¶Ьа¶Ња¶ђ, ඙а¶∞аІНබඌа¶∞ ඁටаІЛ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ а¶ђаІБа¶ЭаІЗ ථඌ а¶ђаІБа¶ЭаІЗ а¶ЂаІНඃඌපථаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶ЬаІЗа¶Ба¶ХаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶З ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶њаІЯаІЗ බගа¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶Ја¶Ња¶ЯаІЗа¶∞ බපа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶У а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІЛ඙ а¶ПටаІЛ а¶ђаІЗපаІА а¶ХаІЗථ, а¶ПටаІЛ а¶Іа¶Ња¶∞аІНа¶Ѓа¶ња¶Х а¶≤аІЛа¶Х ටඐаІБ а¶ХаІЗථ а¶ПටаІЛ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАаІЯ а¶Еа¶Єа¶єа¶ња¶ЈаІНа¶£аІБටඌ ? а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ПаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶ѓаІЗа¶ЯаІБа¶ХаІБ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, ටඌа¶Ба¶∞ ඁටаІЗ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ ඙аІБа¶∞аІЛ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶єаІАථඁථаІНඃටඌаІЯ а¶≠аІБа¶Ча¶ЫаІЗа•§ а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ බаІЗප а¶За¶Ьа¶∞а¶Ња¶За¶≤, аІђ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њаІЯථ а¶Ьථඪа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ ථගаІЯаІЗ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Жа¶∞а¶ђ ඐගපаІНа¶ђа¶ХаІЗ ටаІНа¶∞а¶ЄаІНට а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ ඐගපаІНа¶ђаІЗ ඃඌබаІЗа¶∞ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Ыа¶ња¶Яа¶њаІЯаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶Ьථа¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІА а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ аІІаІЂ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њаІЯථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶§а•§ а¶ЄаІЗа¶З ටаІБа¶≤ථඌаІЯ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Њ ඐගපаІНа¶ђаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ аІІ.аІђ а¶ђа¶ња¶≤а¶њаІЯථ ( аІІаІђаІ¶аІ¶ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њаІЯථ) а•§ а¶ЄаІН඙ඣаІНа¶Яට: а¶За¶єаІБබаІАබаІЗа¶∞ ටаІБа¶≤ථඌаІЯ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ а¶Жа¶ЫаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ аІІаІ¶аІ¶ а¶ЧаІБа¶£ ! а¶ХගථаІНටаІБ а¶Уа¶З а¶ЧаІБа¶Яа¶ња¶ХаІЯаІЗа¶Х а¶За¶єаІБබаІАබаІЗа¶∞ බඌ඙а¶ЯаІЗ ඙аІБа¶∞аІЛ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь ටа¶Яа¶ЄаІНඕ а•§ а¶За¶Ьа¶∞а¶Ња¶За¶≤а¶У а¶ЬඌථаІЗ, а¶ХаІЛථ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ බаІЗපаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£а¶ђа¶ња¶Х а¶Еа¶ЄаІНටаІНа¶∞ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඁඌථаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЄаІНටගටаІНа¶ђ පаІЗа¶Ј ! а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІБа¶За¶Ъ , а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶Ња¶ЯථаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ ඙ගටаІГа¶≠аІВа¶Ѓа¶њ а¶ІаІВа¶≤а¶ња¶Єа¶ЊаІО а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ ; ටඌа¶З ඙аІНа¶∞а¶Ња¶£а¶™а¶£аІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ ඕඌа¶ХаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶Єа¶∞аІНа¶ђаІЛа¶ЪаІНа¶Ъ а¶ЃаІЗа¶Іа¶Њ а¶У පа¶ХаІНටග බගаІЯаІЗ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ХаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£а¶ђа¶ња¶Х පа¶ХаІНටගඁටаІНටඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІБа¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња•§ а¶Па¶З а¶Па¶Х а¶Еа¶ЄаІНටගටаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶Ха¶ЯаІЗа¶∞ බаІЛа¶ЯඌථඌаІЯ ථඌථඌ а¶Ѓа¶∞аІНඁඌථаІНටගа¶Х а¶Ша¶Яථඌ а¶Ша¶ЯаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶ђа¶≤аІЗа¶З ථаІЯ, а¶ѓа¶Цථа¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ј а¶єаІАථඁථаІНඃටඌаІЯ а¶≠аІЛа¶ЧаІЗ а¶ЄаІЗ а¶ђаІЗපаІА а¶Ха¶∞аІЗ ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІБа¶∞ථаІЛ ඐඌටගа¶≤ а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ, а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶ХаІГටග а¶Жа¶Ба¶ХаІЬаІЗ а¶Іа¶∞аІЗа•§ а¶ђаІЗපаІА а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථගටаІНа¶ђ බаІЗа¶ЦඌථаІЛ, а¶єа¶ња¶Ьа¶Ња¶ђ а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Й඙а¶Ьඌට а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ ඪථаІНටаІНа¶∞ඌඪඐඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶За¶Ьа¶∞а¶ЊаІЯаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ථඌ ඙аІЗа¶∞аІЗ а¶Уආඌа¶∞ а¶єаІАථඁථаІНа¶ѓа¶§а¶Ња•§
а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶њ а¶ХаІЛථ බаІВа¶∞ ඙аІНа¶∞ඌථаІНටаІЗа•§ а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ථගඣаІН඙аІЗа¶Ја¶£аІЗ а¶ЖඐබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶є а¶Жа¶ђаІБ а¶Єа¶ЊаІЯаІАබ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Њ ඐගපаІНඐඪඌයගටаІНа¶ѓ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЦаІЛа¶Ба¶Ь а¶Ца¶ђа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶єаІЯаІЗ а¶УආаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯ; а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶£аІЗ а¶Хටපට ථටаІБථ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶Ц а¶Жа¶ЄаІЗ ඙аІНа¶∞ටගඐа¶Ыа¶∞а•§ ඙аІБа¶∞ථаІЛබаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ ථаІЗа¶За•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶њаІЯаІЗ බගа¶≤аІЗථ, ඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶Ча¶£аІНа¶°а¶њ ඙аІЗа¶∞ථаІЛа¶∞ ඙а¶∞ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤ ඙ඌа¶∞ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞, а¶ХаІЗа¶Й а¶Ха¶њ а¶За¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶З а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Жа¶ЄаІНටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ? а¶ХаІЗа¶Й ඃබගа¶У а¶Жа¶ЄаІЗ, а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶єа¶ђаІЗ а¶Ѓа¶∞аІНඁඌථаІНටගа¶Х а¶У а¶єа¶Ња¶ЄаІНа¶ѓа¶Ха¶∞а•§ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞а¶ХаІЗ , а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ХаІЗ а¶ѓа¶Цථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьථ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶Ыа¶ња¶≤ , а¶Па¶Цථ а¶Жа¶∞ ථаІЗа¶За•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ ථаІЗа¶З, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ђаІНа¶∞ඌටаІНа¶ѓ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶≤аІЗа¶ЫаІЗථ а¶ЧаІБа¶∞аІБ බаІНа¶ђа¶ња¶ђа¶ња¶І а¶єаІЯ, а¶Па¶Ха¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ а¶ЧаІБа¶∞аІБ පගඣаІНа¶ѓа¶ХаІЗ а¶Пඁථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЃаІЛа¶єа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫථаІНථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦаІЗ ; а¶Па¶Х ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЧаІБа¶∞аІБ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ පගඣаІНа¶ѓ පаІНඐඌඪ඙аІНа¶∞පаІНа¶ђа¶Ња¶Єа¶У ථගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶∞аІЗа¶Х а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶ЧаІБа¶∞аІБ а¶Жа¶ЫаІЗථ, а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ පගඣаІНඃබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ а¶Пඁථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶ЃаІЯ බаІЗථ , ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗථ , а¶Па¶Х ඙а¶∞аІНа¶ѓа¶ЊаІЯаІЗ පගඣаІНа¶ѓа¶∞а¶Њ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ධඌථඌаІЯ а¶ЙаІЬටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට: а¶Еඕඐඌ а¶ЄаІЗа¶З බаІНඐගටаІАаІЯ පаІНа¶∞аІЗа¶£аІАа¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Х а¶ѓа¶Ња¶БබаІЗа¶∞ පගඣаІНඃබаІЗа¶∞ ධඌථඌаІЯ а¶УаІЬа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЧаІБа¶∞аІБа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ ඕඌа¶ХටаІЗ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х ඙аІБа¶∞ථаІЛ а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶∞а¶Њ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЃаІЗа¶Іа¶Ња¶∞ ඪආගа¶Х а¶ЃаІВа¶≤аІНа¶ѓа¶ЊаІЯථ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶®а¶ња•§ а¶Жа¶ђаІНබаІБථ ථаІБа¶∞ ටаІБа¶Ја¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶Хඕඌа¶З а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ПටаІЛ а¶ђа¶єаІБа¶ЃаІБа¶ЦаІА ඙аІНа¶∞ටගа¶≠а¶Њ ථගаІЯаІЗа¶У а¶ХаІЛථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ ටаІБа¶Ја¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶З ඁථаІЛа¶ѓаІЛа¶Ч බගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ а¶®а¶ња•§
а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶У а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ѓа¶Цථ а¶Хඕඌ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶≤аІЗа¶ЫаІЗථ ටගථග а¶Па¶Ха¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ аІІаІ¶-аІІаІ®а¶Яа¶њ а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶Іа¶∞а¶£аІЗа¶∞, а¶ђа¶ња¶≠ගථаІНථ а¶≤аІЗа¶Ца¶ХаІЗа¶∞ а¶ђа¶З ඙аІЬа¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටථ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඁථаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Па¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶≤аІЗа¶Ца¶ХаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග а¶ЕථаІНа¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЛථ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶≤аІЗа¶Ца¶ХаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ ඁථаІЛа¶ѓаІЛа¶Ч බගаІЯаІЗ ඙аІЬа¶Њ а¶Йа¶Ъа¶њаІОа•§ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶≤аІЗа¶Ца¶ХаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Па¶Ха¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙аІЬа¶≤аІЗ, а¶ХаІЛථ а¶Па¶Ха¶Ьථ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶≤аІЗа¶Ца¶ХаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶За¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЃаІВа¶≤аІНа¶ѓа¶ЊаІЯථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶ња¶У а¶Па¶З а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ а¶ЦаІЗаІЯа¶Ња¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶Жа¶Єа¶≤аІЗа¶З ටаІЛа•§
а¶ђаІЗа¶Ба¶ЪаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ ථගаІЯаІЗ ටаІАа¶ђаІНа¶∞ а¶Жපඌඐඌබ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶Єа¶ЃаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤, ටඌ а¶Па¶З බаІБа¶З а¶Жа¶°аІНа¶°а¶ЊаІЯ ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЙආаІЗ а¶Па¶≤аІЛа•§ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНඣගටаІЗ а¶Па¶З ඁයඌඐගපаІНа¶ђ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Ха¶њ а¶ђа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Хටа¶Цඌථග ටаІБа¶ЪаІНа¶ЫඌටගටаІБа¶ЪаІНа¶Ы а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶У а¶ђаІЬ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶њ ථගа¶ЬаІЗ а¶Па¶З ඐගපඌа¶≤ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ѓа¶ЬаІНа¶ЮаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Еа¶Вප යටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Йබඌයа¶∞а¶£ බගа¶≤аІЗථ , а¶ѓаІЗ а¶Жа¶Хඌපа¶ХаІЗ а¶Па¶З а¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНටаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ බаІЗа¶Ца¶Ыа¶њ, а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Хඌප !
බගථ බපаІЗа¶Х ඙а¶∞аІЗа¶З බаІНඐගටаІАаІЯ а¶Жа¶°аІНа¶°а¶ЊаІЯ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ ඃඕඌа¶∞аІАටග බаІЗа¶∞аІАа•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь඙ටаІНа¶∞ ථගаІЯаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНට а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Жа¶Єа¶≤, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЂаІЗа¶ЯаІЗа¶∞а¶њаІЯа¶Њ а¶ђа¶Њ а¶ХаІНඃඌථаІНа¶ЯගථаІЗ ඕඌа¶Ха¶Ыа¶ња•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£ ඙а¶∞аІЗ යඌටаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶ЄаІЗа¶∞аІЗ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞ а¶єа¶≤аІЗථ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ъа¶≤ටග а¶Жа¶°аІНа¶°а¶ЊаІЯ а•§ а¶ХаІЗа¶Й а¶ХаІЗа¶Й а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ, а¶ЕථаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЂаІЗа¶Єа¶ђаІБа¶Х а¶ЧаІНа¶∞аІБ඙аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ІаІНа¶ѓа¶ЃаІЗа¶З а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Ња•§ а¶єаІБа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶ЃаІЛаІЬ ථගа¶≤аІЛ а¶ЂаІЗа¶Єа¶ђаІБа¶ХаІЗа•§ а¶ХаІЗ а¶Ха¶ња¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶Ха¶∞аІЗ, а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗа•§
а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЄаІЛа¶Ьа¶Њ а¶Хඕඌ, а¶ЂаІЗа¶Єа¶ђаІБа¶Х ඁඌථаІБа¶Ја¶ХаІЗ а¶Еа¶ЄаІНටගටаІНа¶ђаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶Ха¶Я а¶У а¶Жа¶За¶°аІЗථаІНа¶Яа¶ња¶Яа¶њ а¶ХаІНа¶∞а¶Ња¶За¶Єа¶ња¶Є ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЃаІБа¶ХаІНටග බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶∞а¶Ња¶ЄаІНටඌаІЯ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єа¶≤аІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶∞ ටаІБа¶Ѓа¶њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З ටаІЛ а¶Па¶ХаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІЛа¶Ха¶Ња¶Ѓа¶Ња¶ХаІЬаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ђаІЗපаІА а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶®а¶Ња•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЂаІЗа¶Єа¶ђаІБа¶Х а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ ටаІБа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞ටаІЗа•§ а¶ЄаІБපаІНа¶∞аІА а¶Ыа¶ђа¶њ, а¶Ъа¶≤ටග а¶єа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЃаІБа¶Ъа¶ЃаІБа¶ЪаІЗ а¶ђа¶ХаІНа¶∞аІЛа¶ХаІНටග а¶ПථаІЗ බගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶≤а¶Ња¶За¶Х, а¶Ха¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Єа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЗа¶Й а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІНа¶ђа¶ЄаІНටග а¶ЕථаІБа¶≠аІВටග а¶ПථаІЗ බаІЗаІЯ а¶ЂаІЗа¶Єа¶ђаІБа¶Ха•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Єа¶Ња¶ЃаІЯа¶ња¶Х а¶ЄаІНа¶ђа¶ЄаІНටගа¶∞ а¶ЂаІЗа¶Єа¶ђаІБа¶Х а¶ЃаІВа¶≤ට: а¶Еа¶ЄаІНඕගа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа¶ХаІЗ а¶Жа¶∞аІЛ а¶Еа¶ЄаІНඕගа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ ටаІЛа¶≤аІЗа•§ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯ, ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ЂаІЗа¶Єа¶ђаІБа¶Х ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІБа¶∞аІЗ ඕඌа¶Ха¶Ња¶З а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа•§ а¶ђаІЬ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ , а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ඙аІЗටаІЗ а¶єа¶≤аІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶≤аІН඙ඁаІЗаІЯඌබаІА а¶ЂаІЗа¶Єа¶ђаІБа¶ХаІЗа¶∞ а¶≤а¶Ња¶За¶Х а¶У а¶ЖටаІНඁ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶ЄаІНටගа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶∞аІЗ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶≠а¶Ња¶≤а•§
а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ча¶≤аІН඙ а¶Ьа¶ЃаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ѓа¶Цථ а¶ХаІНඃඌථаІНа¶ЯගථаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ђа¶Єа¶≤аІЗථ, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Хඕඌа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶ХаІЗ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶ХаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶£ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Хඕඌ පаІЛථඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЄаІНටඐаІНа¶І а¶єаІЯаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ ඕඌа¶Ха¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ХаІНඣගටаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђаІЯа¶Є а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ථගа¶ЬаІЗබаІЗа¶∞ а¶Ча¶≤аІН඙ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶ња¶Ха¶Њ ඐථаІНа¶ІаІБ , а¶ѓаІЗ а¶Па¶Ха¶З а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ පගа¶ХаІНа¶ЈаІЯගටаІНа¶∞аІА , а¶ЧаІГа¶єа¶ња¶£аІА, а¶Ѓа¶Њ а¶У ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Еа¶Ва¶ґа•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЃаІБපа¶Ха¶ња¶≤ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶ЄаІЗ а¶ЂаІЗа¶Єа¶ђаІБа¶ХаІЗ а¶ѓа¶Ња¶З а¶≤аІЗа¶ЦаІЗ ථඌ а¶ХаІЗථ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ ථගаІЯаІЗ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶£ ටа¶Яа¶ЄаІНඕ ඕඌа¶ХටаІЗ а¶єаІЯаІЗ, а¶ХаІЗ а¶Ха¶њ а¶≠а¶Ња¶ђа¶≤а•§ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Хඐගටඌ а¶≤а¶ња¶Ца¶≤аІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІА а¶ђаІЗа¶Ъа¶Ња¶∞а¶Њ ථඌ а¶≠аІЗа¶ђаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ, ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ха¶ђа¶њ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІА а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶Хගථඌ ! а¶ХаІЛථ а¶Е඙а¶ЫථаІНබаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ, а¶ХаІЛථ ටаІАа¶ђаІНа¶∞ටඌа¶∞ а¶Хඕඌ а¶≤а¶ња¶ЦටаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶≠ඌඐටаІЗ а¶єаІЯ– а¶ПටаІЛ а¶ЫඌටаІНа¶∞ а¶ЫඌටаІНа¶∞аІА а¶Жа¶ЫаІЗ ; ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Па¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶Ха¶ња¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ථаІЗа¶ђаІЗа•§ а¶Пඁථа¶У а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ЄаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Еа¶ЄаІНа¶ђа¶ЄаІНටග ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЃаІБа¶ЫаІЗа¶У а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶ЫаІЗа•§
а¶≤аІЗа¶Ца¶ња¶Ха¶Њ ඐථаІНа¶ІаІБ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЂаІЗа¶Єа¶ђаІБа¶ХаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶ња¶∞ а¶Еа¶Х඙а¶Яටඌа¶ХаІЗ а¶Єа¶Ња¶ІаІБඐඌබ а¶Ьඌථඌа¶≤аІЛа•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶њ а¶єаІБа¶Я а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Жа¶Ь ඙а¶∞аІНඃථаІНට, а¶ХаІЛථ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЃаІБа¶ЫටаІЗ а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ඙аІБа¶∞аІБа¶Ј-පඌඪගට а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ а¶Па¶Яа¶Њ а¶ЖඁබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ња¶≠а¶ња¶≤аІЗа¶Ьа•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶Хඐගටඌ а¶ђа¶Њ а¶Ча¶≤аІН඙ ථаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ථගටඌථаІНටа¶З а¶Ха¶∞аІН඙аІЛа¶∞аІЗа¶Я а¶Еа¶ђаІНа¶Ьа¶Ња¶∞аІНа¶≠аІЗපථ а¶ђа¶Њ а¶ЯаІБа¶Ха¶Яа¶Ња¶Х а¶ЄаІНа¶ЃаІГටගа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£ а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Еа¶∞аІНඕаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ , а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඐථаІНа¶ІаІБ-ටඌа¶≤а¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ඐථаІНа¶ІаІБබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග а¶Жа¶Ѓа¶њ ටаІЗඁථ а¶ХаІЛථ බඌаІЯඐබаІН඲ටඌ а¶ђаІЛа¶І а¶Ха¶∞а¶њ ථඌ а•§
а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЛа¶ЃаІБа¶Ца¶њ а¶Па¶Ха¶Ьථ ඐථаІНа¶ІаІБ а¶ђа¶ЄаІЗ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ, ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ѓаІМථටඌ ථගаІЯаІЗ а¶ѓаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ња•§ а¶ЂаІЗа¶Єа¶ђаІБа¶ХаІЗ а¶єаІЯටаІЛ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ පඌа¶≤аІАථටඌ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶ђа¶≤а¶њ; а¶ХගථаІНටаІБ а¶ђа¶≤а¶њ , а¶ХаІЛථ බаІНа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Ња¶З а¶ђа¶≤а¶ња•§
а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶ња¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඁථаІНටඐаІНа¶ѓ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶≤аІЗа¶Ца¶ХබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х බඌаІЯඐබаІН඲ටඌа¶∞ а¶ЄаІАа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶Ца¶Њ а¶Еටගа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓ а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶≤а¶ња¶ЦටаІЗ а¶єаІЯа•§ ථටаІБа¶ђа¶Њ а¶Жа¶ђаІБа¶≤ а¶Ха¶Ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Жа¶ЬඌබаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ , а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶∞ аІ®аІЂ а¶ђа¶Ыа¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶ѓаІЗථ ටඌ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶єаІЯ ! а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶£ ඙ඌආа¶ХаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶≠аІЗа¶ђаІЗ а¶≤а¶ња¶ЦටаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ вАШථගа¶ЬаІЗа¶∞вАЩ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶єа¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ ආගа¶Х а¶Па¶З а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Ња¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЂаІЗа¶Єа¶ђаІБа¶Х ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІБа¶∞аІЗ ආаІЗа¶≤аІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ ඙ඌආа¶Х а¶У ඐථаІНа¶ІаІБබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Па¶ХаІНඪ඙аІЗа¶Ха¶ЯаІЗපථ ඕඌа¶ХаІЗа•§а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶£ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ , ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Хඕඌ, а¶Еа¶Ђа¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ЪගථаІНටඌ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єаІЯ ; а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІНඃඌථаІНа¶Є а¶Ха¶∞аІЗ, а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗ ථඌа¶ЦаІЛප ථඌ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶ЦаІБපаІА а¶Ха¶∞аІЗ а¶≤а¶ња¶ЦටаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ ථගа¶Ьа¶ЄаІНඐටඌ ඕඌа¶ХаІЗ а¶®а¶Ња•§
а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙а¶Х а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ЙආටаІЗа¶З , а¶Йථග а¶Еа¶Х඙а¶ЯаІЗ а¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ, а¶Пටа¶ЧаІБа¶≤аІЛ ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ, а¶Яа¶ња¶≠а¶њ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ථඌа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯа¶ХаІЗ а¶Йථග а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ђаІЗපаІА а¶Й඙а¶≠аІЛа¶Ч а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Жපගа¶∞ බපа¶Х ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶ђа¶ња¶Яа¶ња¶≠а¶њ ථගаІЯаІЗ а¶ЃаІЗටаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЄаІМа¶≠а¶Ња¶ЧаІНа¶ѓ а¶єаІЯථග а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ බаІЗа¶Ца¶Ња¶∞а•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Жа¶∞аІНа¶Ха¶Ња¶За¶≠ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ХаІЛථ а¶Па¶Х ඁයඌ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶Ња¶≤а¶ХаІЗа¶∞ ථගа¶∞аІНа¶ђаІБබаІН඲ගටඌаІЯ ඪ඙аІНට а¶°а¶ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞ а¶Єа¶ђ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶°а¶ЧаІБа¶≤аІЛа¶ХаІЗ ඙аІБථа¶Г а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඁඌථаІЗ, ඙аІБа¶∞ථаІЛ ඀ගටаІЗ а¶ЃаІБа¶ЫаІЗ ටඌа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ථටаІБථ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ а¶∞аІЗа¶Ха¶∞аІНа¶° а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ! ටඌа¶З а¶ХаІЛථ а¶ЄаІНа¶ЃаІГටග а¶Жа¶∞ а¶ЕඐපගඣаІНа¶Я ථаІЗа¶За•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЬථаІНа¶Ѓ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶њ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶Жපගа¶∞ බපа¶ХаІЗа¶∞ а¶Иබ а¶ЖථථаІНබඁаІЗа¶≤а¶ЊаІЯ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶ХаІЯаІЗа¶Х ඁගථගа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Еටගඕග а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗа•§ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ а¶ХаІЯаІЗа¶Х ඁගථගа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕගටගටаІЗа¶З а¶ЖඐබаІБа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶є а¶Жа¶ђаІБ а¶Єа¶ЊаІЯаІАබ බа¶∞аІНපа¶Ха¶ХаІЗ а¶ђаІБа¶Эа¶њаІЯаІЗ බගටаІЗථ , а¶ХаІЗථ ටගථග а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ђаІНඃටගа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа•§
а¶ХаІЗථ а¶Яа¶ња¶≠а¶њ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ බගа¶≤аІЗථ, а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ЃаІГටගа¶Ъа¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞аІЛ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶®а•§ ටගථග а¶ЃаІВа¶≤ට: පගа¶ХаІНа¶Ја¶Хටඌ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ඪඌබඌඁඌа¶Яа¶Њ ඙ඌа¶ЮаІНа¶Ьа¶Ња¶ђаІА ඙ඌаІЯа¶Ьа¶Ња¶Ѓа¶Њ ඙аІЬටаІЗа¶®а•§ а¶Яа¶ња¶≠а¶ња¶∞ а¶ХаІЛථ а¶Па¶Х а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Цඌටගа¶∞аІЗа¶З ටගථග а¶єа¶Ња¶≤а¶Ха¶Њ а¶Ха¶Ња¶∞аІБа¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶Њ ථаІАа¶≤ а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶ЮаІНа¶Ьа¶Ња¶ђа¶њ ඙аІЬаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ඙а¶∞аІЗа¶∞බගථ ඥඌа¶Ха¶Њ а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Еа¶≠ගඁඌථаІА а¶ЫඌටаІНа¶∞ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶°аІЗа¶ХаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІЛපඌа¶ХаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Ж඙ටаІНටග ටаІБа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶Яа¶њ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶њаІЯаІЗ බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ , а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ а¶Єа¶ђ а¶ЫඌටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Йа¶Ба¶ЪаІБ а¶ЄаІНඕඌථаІЗ ; а¶Жа¶∞ බපа¶Ьථ а¶Ѓа¶ња¶°а¶њаІЯа¶Њ а¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІАа¶∞ ඁට ථаІЯа•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ , а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ බаІБа¶Зබගа¶Х а¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤ටаІЗ а¶єаІЯ ටඌа¶Ба¶ХаІЗа•§ а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶Яа¶њ ථඌа¶Ха¶њ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤, ටඌයа¶≤аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ ථаІЗа¶З, а¶Ж඙ථග а¶Уа¶З а¶Ьа¶ЧටаІЗа¶З ඕඌа¶ХаІЗа¶®а•§ а¶Па¶З а¶Ша¶Яථඌ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶ХаІЗ а¶Яа¶ња¶≠а¶њ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶ЊаІЯ ඙аІНа¶∞а¶≠ඌඐගට а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА а¶Єа¶ЃаІЯа¶ЯаІБа¶ХаІБ ටගථග ථගа¶∞а¶ђа¶ЪаІНа¶ЫගථаІНථ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ බගаІЯаІЗа¶ЫаІЗථ а¶Еа¶ІаІНඃඌ඙ථඌаІЯ, а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶њ а¶У ඐගපаІНඐඪඌයගටаІНа¶ѓ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶ЧаІЬаІЗ ටаІЛа¶≤а¶ЊаІЯа•§
а¶Уа¶З а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶Яа¶ња¶≠а¶њ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ ඁඌථ а¶Жа¶∞ а¶Па¶З а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ ඁඌථаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Йආа¶≤аІЗ, а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Па¶Х а¶ХඕඌаІЯ а¶Єа¶ЊаІЯ බගа¶≤а¶Ња¶Ѓ , ඪටаІНටаІБа¶∞ а¶Жපගа¶∞ බපа¶ХаІЗа¶∞ а¶Яа¶ња¶≠а¶њ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථаІЗа¶∞ ඁඌථ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඪඌබඌа¶Ха¶Ња¶≤аІЛ а¶Яа¶ња¶≠а¶њ а¶ђа¶≤аІЗа¶З ථаІЯ, а¶Яа¶ња¶≠а¶њ а¶Єа¶ђа¶Єа¶ЃаІЯ а¶ЗථаІНа¶ЯаІЗа¶≤аІЗа¶Ха¶ЪаІБаІЯа¶Ња¶≤බаІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ, а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶ђа¶Њ а¶ЄаІБථаІНබа¶∞аІА යටаІЗа¶З а¶єа¶ђаІЗ ; а¶∞а¶Ща¶Ъа¶ЩаІЗ ඙аІЛපඌа¶Х ඙аІЬටаІЗа¶З а¶єа¶ђаІЗ ටඌ ථаІЯа•§ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙а¶Х ඃබග ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЧаІНඁගටඌ බගаІЯаІЗ බа¶∞аІНපа¶Ха¶ХаІЗ а¶ЃаІБа¶ЧаІНа¶І а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІЛපඌа¶Х а¶У а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶Іа¶∞аІНටඐаІНа¶ѓ а¶єаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶ЄаІЗа¶З а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶ЕඁඌථаІБа¶Ја¶ња¶Х ඙а¶∞ගපаІНа¶∞а¶ЃаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶≠аІЗа¶ђаІЗ පගа¶Йа¶∞аІЗ а¶Йආа¶≤аІЗථ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞а•§ ඙аІНа¶∞ටග ඪ඙аІНටඌයаІЗ аІ≠аІЂ ඁගථගа¶ЯаІЗа¶∞ а¶ЕථаІБа¶ЈаІНආඌථ а¶Ха¶∞а¶Њ, ථගටаІНඃථටаІБථ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ ථගаІЯаІЗ, а¶Ъа¶Ња¶ЯаІНа¶Яа¶њ а¶Цඌථග а¶Хඕඌ ථаІЯа•§
а¶ШаІБа¶∞аІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶Ч а¶Ъа¶≤аІЗа¶З а¶Жа¶ЄаІЗа•§ а¶≤аІЗа¶Ца¶Х а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ බаІБа¶З а¶ЬඌටаІЗа¶∞ ; а¶Па¶Х а¶ЬඌටаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Х а¶Жа¶ЫаІЗථ а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Х а¶єаІЯаІЗа¶З а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶ЫаІЗථ, ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З а¶≤аІЗа¶Ца¶Ха•§ а¶Ха¶Ња¶ЬаІА ථа¶Ьа¶∞аІБа¶≤ а¶За¶Єа¶≤а¶Ња¶Ѓ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ЬඌටаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ха•§ а¶Жа¶∞аІЗа¶Х а¶ЬඌටаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Х а¶Жа¶ЫаІЗථ, а¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ а¶≤а¶ња¶ЦටаІЗ а¶≤а¶ња¶ЦටаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Х, а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ ආඌа¶ХаІБа¶∞, а¶ЬаІАඐථඌථථаІНබ බඌප බаІНඐගටаІАаІЯ а¶ЬඌටаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ха•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ вАШ а¶ђа¶ња¶ЄаІНа¶∞а¶ЄаІНට а¶Ьа¶∞аІНථඌа¶≤вАЩ– а¶ђа¶За¶Яа¶њ а¶Чට а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІН඲ථ а¶У а¶Єа¶ВපаІЛ඲ථ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Па¶За¶ђа¶Ња¶∞ а¶У ථඌа¶Ха¶њ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞ඐථаІНа¶ІаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђ а¶ђа¶З а¶ХගථаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶єаІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶њ ; а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶Уа¶З а¶ђа¶За¶Яа¶Њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ХගථටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶Ха¶ња¶ЮаІНа¶Ъа¶њаІО а¶Йа¶ЈаІНа¶Ѓа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ , а¶Па¶∞ පаІЗа¶Ј а¶ХаІЛඕඌаІЯ? ඙аІНа¶∞ටගඐа¶Ыа¶∞ а¶Па¶Ха¶З а¶ђа¶З а¶Єа¶ВපаІЛ඲ථ а¶У ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІН඲ථ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ඙ඌආа¶ХаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඐඌа¶∞а¶З а¶ХගථටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ а¶Еඕඐඌ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ђа¶ЮаІНа¶Ъගට а¶єаІЯаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђ а¶Єа¶∞аІНඐපаІЗа¶Ј а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗа•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞а¶њаІЯаІЗ බගа¶≤аІЗථ , а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ ආඌа¶ХаІБа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶ЊаІЯ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶Ња¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња¶Яа¶њ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ а¶≤аІЗа¶≠ ටа¶≤а¶ЄаІНටаІЯ вАШ а¶УаІЯаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЕаІНඃඌථаІНа¶° ඙ගඪвА٠ථඌඁаІЗа¶∞ ඐගපඌа¶≤ а¶Ха¶≤аІЗа¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶За¶Яа¶њ ථඌа¶Ха¶њ аІІаІ® ඕаІЗа¶ХаІЗ аІІаІ© а¶ђа¶Ња¶∞ ඙аІБථа¶∞аІНа¶≤а¶ња¶Цථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶ЊаІЯ ටаІГ඙аІНටග ථඌ а¶Жа¶Єа¶Њ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Йථග ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶єаІЯටаІЛ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶З а¶Уа¶З а¶Ѓа¶єа¶Њ а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓа¶ња¶Х а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Жа¶Ь а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶Ѓа¶єаІАа¶∞аІБа¶єаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІНඁඌථ ථගаІЯаІЗ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗа•§
а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЬаІАඐථඌථථаІНබаІЗа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶њ а¶Хඐගටඌа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶ѓаІЗа¶Яа¶њ а¶ЬаІАඐථඌථථаІНබ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ ඙аІБථа¶∞аІНа¶≤а¶ња¶Цථ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඙аІНа¶∞ටගа¶Яа¶Њ а¶Хඐගටඌа¶∞ පඐаІНබа¶ЪаІЯථ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶≤аІЗа¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ටඌа¶Ба¶∞ පඐаІНබ а¶ЪаІЯථ а¶ПටаІЛ а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶ПටаІЛ а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓа¶ња¶Х, а¶ѓа¶Ња¶З а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗථ ඙аІНа¶∞ටගඐඌа¶∞ а¶ЄаІЗа¶Яа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ЃаІБа¶ЧаІНа¶І а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЬаІАඐථඌථථаІНබ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Хඐගටඌ а¶єаІЯටаІЛ а¶ХаІЛථ а¶ЫаІЛа¶Я ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶ЊаІЯ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Ыඌ඙ඌ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ ථගа¶ЬаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗа¶З ඁථаІЗ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗ, ආගа¶Х а¶єаІЯа¶®а¶ња•§ а¶Йථග а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ЕඐපаІЗа¶ЈаІЗ а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓаІЗ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶Жа¶∞аІЛ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ПටаІЛ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ ඙а¶∞ගපаІНа¶∞а¶ЃаІЗа¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶З а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗ а¶Уа¶З а¶ЕබаІНа¶≠аІБට а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа¶≤а¶Ња¶Ча¶Ња¶∞ а¶Хඐගටඌа¶∞ а¶≤а¶Ња¶Зථа¶ЧаІБа¶≤аІЛа•§
а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞, ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶ЬථаІЗа¶∞ а¶ЄаІН඙аІГයඌටаІЗ ථඌа¶ЦаІЛප а¶®а¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђа¶ХаІНටඐаІНа¶ѓ а¶Ъа¶≤ඁඌථ а¶ЬаІАඐථаІНට а¶≤аІЗа¶Ца¶ХаІЗа¶∞а¶Ња¶З а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞аІНа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ЃаІГට а¶≤аІЗа¶Ца¶ХබаІЗа¶∞ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ ථаІЯа•§
ටа¶≤а¶ЄаІНටаІЯ ථඌа¶Ха¶њ පаІЗа¶ХаІНඪ඙ගаІЯа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ъථඌ а¶≠а¶Ња¶≤а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ පගа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ පаІЗа¶ХаІНඪ඙ගаІЯа¶Ња¶∞ ඙аІЬаІЗ ටа¶≤а¶ЄаІНටаІЯ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ පаІЗа¶ХаІНඪ඙ගаІЯа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶Ъථඌа¶∞ බප а¶≤а¶Ња¶Зථ ඙а¶∞аІЗа¶З ථඌа¶Ха¶њ а¶Еа¶ѓаІМа¶ХаІНටගа¶Х а¶Хඕඌ а¶Па¶ЄаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶Йථග а¶Па¶Ча¶Ња¶∞аІЛ а¶≤а¶Ња¶Зථа¶У а¶ѓаІБа¶ХаІНටග а¶Іа¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа¶®а¶®а¶ња•§ පаІЗа¶Ј а¶ђаІЯаІЗа¶ЄаІЗ ටа¶≤а¶ЄаІНටаІЯ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙аІЗа¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ , ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗа¶У а¶ђаІЗපаІАа¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶ѓаІБа¶ХаІНටග බගаІЯаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶®а¶Ња•§ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶Єа¶ЃаІЯ ඙а¶∞ ඙а¶∞ а¶Еа¶ѓаІМа¶ХаІНටගа¶Х а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Па¶ЄаІЗа¶З а¶ѓа¶ЊаІЯа•§
а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБ а¶У а¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶Іа¶ХаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶Ч а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Жа¶≤аІЛа¶ЪථඌаІЯа•§ බаІНа¶∞аІБට а¶Еටගа¶ХаІНа¶∞ඌථаІНට а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶Еа¶ђа¶Іа¶Ња¶∞ගට а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶Іа¶ХаІНа¶ѓ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІА а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ а¶У а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБ а¶Жටа¶ЩаІНа¶Х ථගаІЯаІЗ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ ඪඌඁථаІЗ а•§ а¶ХаІАа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Па¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ђа¶Єа¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђа•§ а¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶Іа¶ХаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЧаІБа¶£а¶ХаІАа¶∞аІНටථ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶ђа¶ХаІНටаІГටඌаІЯа•§ а¶Жа¶Ьа¶У а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථа¶ХаІЗ බаІЗа¶Ца¶њаІЯаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶Жа¶Ѓа¶њ ටаІЛ ටаІЛඁඌබаІЗа¶∞ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ , ටаІЛඁඌබаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§а¶ња•§ ටаІЛа¶Ѓа¶∞а¶Њ ටаІЛ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶З а¶ђаІЯаІЗа¶ЄаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁටаІЛа¶З යටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶Уа•§ а¶ѓа¶Њ ටаІЛа¶Ѓа¶∞а¶Њ යටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За¶Ы, а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶За•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶ђа¶Ња¶∞аІНа¶Іа¶ХаІНа¶ѓ ථගаІЯаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ХаІЛථ а¶єаІБටඌපථ ථаІЗа¶За•§
඙аІНа¶∞а¶њаІЯа¶Ьථ а¶єа¶Ња¶∞ඌථаІЛа¶∞ а¶ђаІЗබථඌ, а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶∞ а¶ђаІЗබථඌ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ а¶ЫගථаІНථа¶≠ගථаІНථ а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶Па¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Ха¶ња¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Єа¶єа¶Ња¶ђа¶ЄаІНඕඌථ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ ? а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ђаІЯа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ђаІЗබථඌඐаІЛа¶І а¶Ха¶ЃаІЗ ථඌ, а¶єаІЯටаІЛ а¶ђа¶ЊаІЬටаІЗа¶З ඕඌа¶ХаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ ටඌа¶ХаІЗ а¶ЃаІЗථаІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඪයථපаІАа¶≤ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞ඌ඙аІНටඐаІЯа¶ЄаІНа¶Хටඌ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶ЄаІЗа•§ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ ආඌа¶ХаІБа¶∞ вАЬа¶Ѓа¶∞а¶£ а¶∞аІЗ, ටаІБа¶Ба¶єаІБ а¶Ѓа¶Ѓ පаІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶®а•§вАЭ а¶ѓа¶Цථ а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶≠ඌථаІБ а¶Єа¶ња¶Ва¶єаІЗа¶∞ ඙බඌඐа¶≤аІА а¶ЫබаІНඁථඌඁаІЗ, ටа¶Цථ ටගථග ථගටඌථаІНටа¶З а¶ѓаІБа¶ђа¶Ха•§ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶ХаІЗ а¶Жа¶≤а¶ња¶ЩаІНа¶Чථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶∞ а¶єа¶Ња¶єа¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ ථගаІЯаІЗ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ђаІЯඪටаІЛ а¶ЄаІЗа¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ ටඐаІЗ а¶ХаІЗථ ටගථග а¶єа¶Ња¶єа¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗථ? а¶ђа¶∞а¶В а¶ђаІГබаІНа¶І а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕаІЗа¶∞ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶Уа¶З а¶єа¶Ња¶єа¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ ඃඕаІЛ඙ඃаІБа¶ХаІНට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЃаІВа¶≤ට: а¶ђаІЯа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඪයථපаІАа¶≤ටඌ а¶ђаІЗаІЬаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ЃаІЗථаІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ , а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶ЬථаІЗа¶∞ а¶ХаІНඣඁටඌ а¶ђаІЗаІЬаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶З ඙аІНа¶∞аІМаІЭටаІНа¶ђаІЗ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБ ථගаІЯаІЗ а¶ХаІЛථ а¶≠а¶Ња¶ђа¶Ња¶≤аІБටඌ а¶Ыа¶ња¶≤ථඌ а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕ ආඌа¶ХаІБа¶∞аІЗа¶∞а•§
а¶Жа¶°аІНа¶°а¶Њ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ а¶ЙආටаІЗ а¶За¶ЪаІНа¶ЫаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ а¶®а¶Ња•§ ඁථаІЗ а¶єаІЯ а¶Хට а¶Хඕඌ а¶Еа¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНට а¶∞аІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶∞ඌට а¶Єа¶ЊаІЬаІЗ а¶Па¶Ча¶Ња¶∞аІЛа¶Яа¶Њ а¶ђа¶Њ а¶ђа¶Ња¶∞аІЛа¶Яа¶Њ а¶ђаІЗа¶ЬаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶ЙආаІЗ ඙аІЬටаІЗа¶З а¶єаІЯ а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЧථаІНටඐаІНа¶ѓаІЗа•§а¶Ђа¶ња¶∞ටග ඙ඕ а¶ЬаІБаІЬаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа¶≤а¶Ња¶Ча¶Ња¶∞ а¶∞аІЗප ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Єа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗа•§
а¶Єа¶ђа¶Ња¶За¶ХаІЗ аІ®аІ¶аІІаІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶њ ථඐඐа¶∞аІНа¶ЈаІЗа¶∞ පаІБа¶≠аІЗа¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ !
඙аІНа¶∞а¶Хඌපа¶Ха¶Ња¶≤а¶Г а¶°а¶ња¶ЄаІЗа¶ЃаІНа¶ђа¶∞,аІ®аІ¶аІІаІ≠
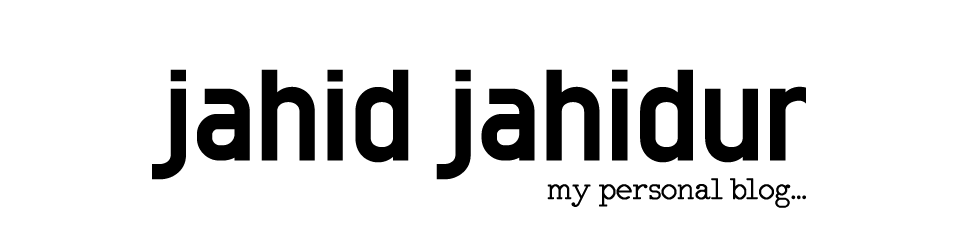
а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞ටගа¶Х ඁථаІНටඐаІНа¶ѓ